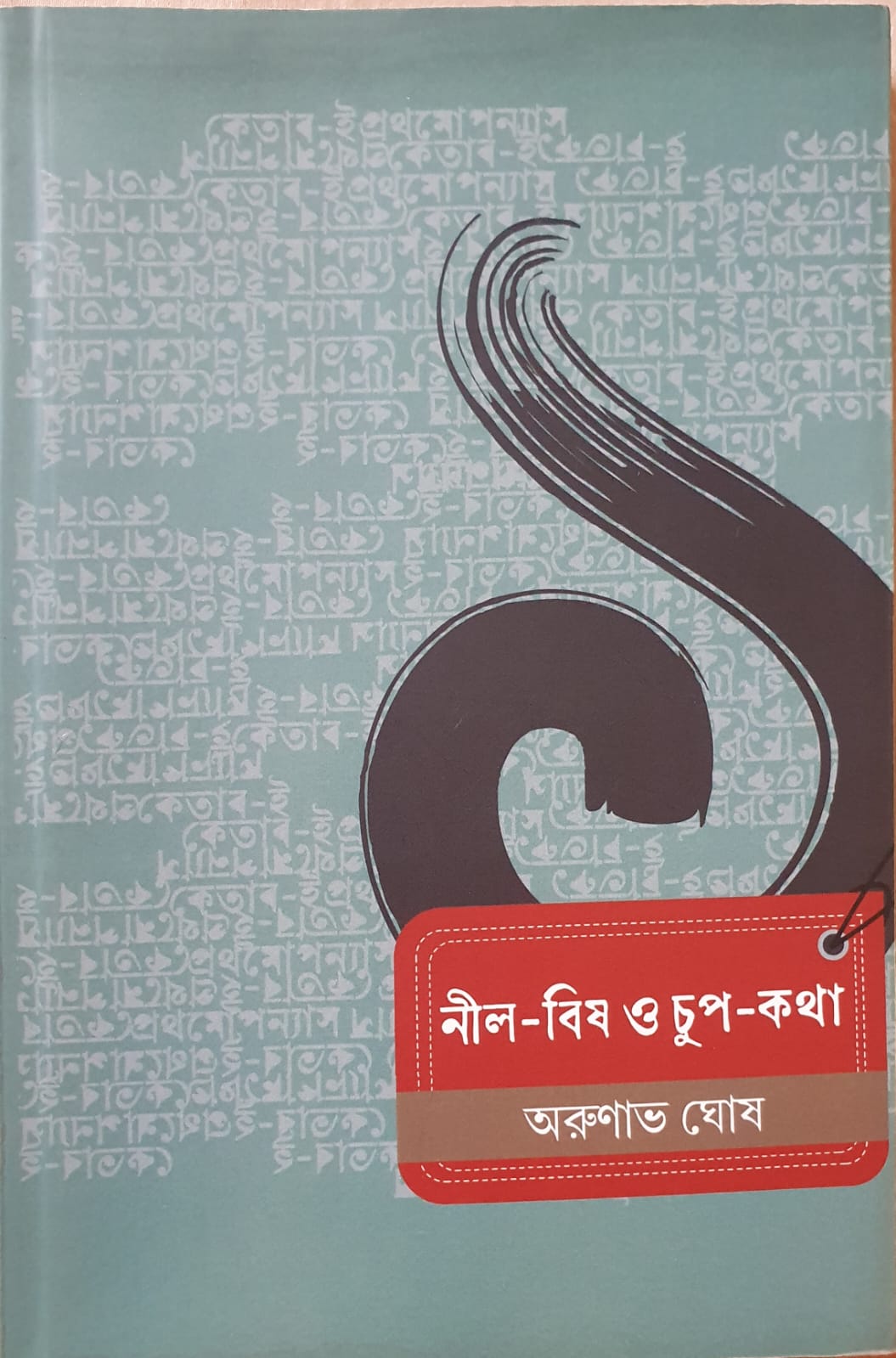
নষ্ট সময়ের কেতাবী আখ্যান
রূপশ্রী ঘোষ
উপন্যাস—‘নীল – বিষ ও চুপ – কথা’ লেখক - অরুনাভ ঘোষ প্রচ্ছদ- সুপ্রসন্ন কুণ্ডু প্রকাশক - কেতাব মূল্য – ৩৫০/-
‘ভিতরটা খুব গুমোট। আস্তে সুস্থে শার্টের বোতাম খুলছিল দীর্ঘদেহী ব্লন্ড, যেন বেশ ভাবনা চিন্তা করে। তার ভারী স্তনযুগল ফ্রিল দেওয়া ব্রা থেকে উপচে পড়ছে। ব্রাটা মনে হয় যেন দু-সাইজ ছোটো। ব্রায়ের হুক খুলে গেল এবার, একইরকম ধীরে ধীরে। মেয়েটি পাউট করল’।
নীল-বিষ ও চুপ-কথা উপন্যাসটি শুরুই হচ্ছে সিনেমার মতো করে। হ্যাঁ, নীল ছবির বর্ণনা দিয়ে। কিন্তু সে বর্ণনা এতটাই ছবির মতো যে, কেউ বই পড়ছে নাকি নীল ছবিই দেখছে সেটা বোঝা কঠিন হয়ে যায় লেখকের বর্ণনার পারিপাট্যের কাছে। বাংলার বাইরের এক গ্রাম, কুমরিয়া। কুমরিয়ার জীবন যাপন, সেখানকার ভাষা, সংস্কৃতি, চালচলন সবটাই খুব সাবলীলভাবে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখক তাঁর ক্যামেরার চোখ দিয়ে নিজে আড়ালে থেকে যেভাবে উপন্যাসটি রচনা করেছেন, তা পাঠক মাত্রই উপন্যাসের পরতে পরতে উপলব্ধি করতে পারবেন।
গ্রামের সহজ সরল মানুষের চাওয়া পাওয়া, চিন্তা ভাবনা যে কতটা সহজ তা এই উপন্যাসে নিহিত আছে। পশ্চিমবঙ্গের কোনো গ্রামের সঙ্গে সেই জীবন যাপনের কোনো কোনো অংশে মিল না পাওয়ায়, পড়ার আগ্রহ বেড়ে যায় উপন্যাসের শুরুতেই। ধীরে ধীরে শুরু হয় যন্ত্রণাময় জীবন এবং হতাশার দৃশ্য। এর পিছনে সেই একটাই বিষয়, ‘লোভ’। যৌন লালসা, যৌন উন্মাদনা, যৌন কৌতূহল যা মানুষকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যায়, তা সেই বিষয়ের মধ্যে লিপ্ত থেকে অনুভব করা সম্ভব নয়, এ উপন্যাস তারই কথা বলে।
‘নিডর’ নামের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মেয়েদের জন্য কাজ করে। তাদের কাছে খবর ছিল এই কুমরিয়া গ্রামে পর্নোগ্রফির শো দেখানো হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তিন মহিলা সেই গ্রামে যান, এটা ওটা ওখানকার মেয়ে বা মহিলাদের উপর কোনো খারাপ প্রভাব ফেলছে কিনা তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার জন্যই। তাদের মধ্যে একজন মার্কিন নাগরিক, অধিবাসী ভারতীয় কলকাতায় এসেছে এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে কাজ করতে। নাম জয়িতা। সে এই সামাজিক কাজে কুমরিয়া যায়। তার উপরই সেই খারাপ প্রভাবটা এসে পড়ে। ওই গ্রামের চারজন ছেলে তাকে ধর্ষণ করে। শারীরিক তো বটেই, সেই মানসিক যন্ত্রণা কীভাবে জয়িতার জীবনে প্রভাব ফেলে এ তারই গল্প। গল্প নয়, একেবারেই বাস্তব। এটা ২০০৩ সালের প্রেক্ষাপটে লেখা হলেও আজ ২০২৫ সালে তা কতটা বাস্তব তা এই উপন্যাসেই ধরা আছে।
অন্য ভাবনায়, কোনটা বাস্তব আর কোনটা নয়, তাও যেন এই উপন্যাস আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সামাজিক উপন্যাস আধুনিক সময়ের প্রেক্ষিতে খুব কমই লেখা হয়েছে। লেখা হলেও, তা প্রকৃত অন্ধকার দিকটিকে উন্মোচন করেনি কখনো। এই উপন্যাস সেই অন্ধকার দিকটিকে উন্মোচন করে। এই উন্মোচন পর্বে তাই উপন্যাসের ভিতরে সমাজ এবং চরিত্রগুলির এক নিখুঁত চালচিত্র ফুটে ওঠে। যা, আমাদের সামনে উন্মোচন করে এক ক্লেদাক্ত অথচ সত্য পৃথিবীর।
বিশেষ করে চরিত্রগুলোর মুখের ভাষা, নাম এবং পাশাপাশি তাদের ভিতরের ইচ্ছা, অনীচ্ছা, ভালোলাগা, মন্দলাগা প্রত্যেকটা বিষয় এত নিঁখুতভাবে বর্ণিত যা উপন্যাসটিকে সেই স্থানের একটি জীবন্ত প্রতিবিম্বে রূপান্তরিত করেছে। উপন্যাসে বুঢন চালওলাকে টাকা না দিয়ে তা থেকে কিছুটা টাকা সরিয়ে নীল ছবি দেখে। তার ফল স্বরূপ হাটের চালওলার মুখের ভাষা, ““তোর চুতিয়া বাপকে বলবি গণপরামকে যেন ধোঁকা দেবার চেষ্টা না করে। আজ অথবা কাল গান্ডুটাকে আমার কাছে আসতে হবে আর তখন ওর বিচি কেটে নেব। মনে থাকে যেন””। [পৃঃ ৪] ভাষা যেকোনো উপন্যাসের একটি প্রধান আধার। এই উপন্যাসে চালওয়ালার মুখে রাগের ভাষার পাশাপাশি যদি থানেদারের ভাষা পাশাপাশি মিলিয়ে নেওয়া যায় তাহলে বোঝা যায় উপন্যাসটি কতটা জীবন্ত রূপে প্রতিফলিত দেখে নেওয়া যাক,
“গ্রামের মুখিয়া সরপঞ্চের কাছে ব্লু-ফ্লিম কবে দেখানো হয় জানতে চেয়েও খুব নোংরা ইঙ্গিতে কথা বলেন থানেদার, থানার এস এইচ, রামধারী সিং, “শরীরে না হলেও মনের দিক থেকে বুড়িয়ে গেছেন”। বলেই ঠাট্টা করে হাসলো থানেদার। “ওই ফিলিম যদি দু – একটা দেখতেন তাহলে – ওই ফিলিম – তাহলে এত যোশ এসে যেতো যেকোনো মেয়েছেলেকে সামনে পেলে লাগিয়ে বসতেন। আর শহুরে মেয়েকে একা পেলে তো কথাই নেই”। [পৃঃ ১৫৫] এ তো উদাহরণ মাত্র। কিন্তু এটা সত্যিই বাস্তব নয়?
উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের ভাষা বিশেষত থানার সব বাবুদের শারীরিক এবং মুখের ভাষার ব্যবহারে লেখক যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এর পাশাপাশি কলকাতার শিক্ষিত সমাজের ভাষাও আলোচ্য। ভাষার ব্যবহারে বা প্রয়োগে লেখক ভীষণই দক্ষতা দেখিয়েছেন।
আইনের খুঁটিনাটির ঘাঁতঘোঁত, এবং নারী জীবনের অসহায়তার ছবিও স্পষ্ট এই উপন্যাসে। তবে নারীর অসহায় হয়ে কাটানোর কথা নেই, আছে প্রতিবাদী সত্তাও। কিন্তু সেসব পদক্ষেপ নিতে গিয়ে পুরুষতন্ত্র দ্বারা কতটা অপমানিত সে বর্ণনা ও তার দৃষ্টান্তও লক্ষণীয়, “আমি কী করতে পারি আপনার কোনো আইডিয়া নেই ম্যাডাম। এটা আমার থানা, আমিই থানেদার। আমার নিরাপত্তা আর সহযোগিতা ছাড়া এখানে কিছুই করতে পারবেন না। বুঝেছেন?” [পৃঃ ১৩২] ক্ষমতার হুমকির সঙ্গে কম-বেশি প্রত্যেকেই পরিচিত, এখানেও তার অন্যথা হয়নি। এ প্রসঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের ‘দেবীগর্জন’ নাটকের প্রভঞ্জনের হুমকি, ‘আমি রাজা, আমারই নীতি, ইটাই রাজনীতি’ সংলাপের কথাও মনে করিয়ে দেয়। কালে কালে ক্ষমতার হুমকিতেই বাঁচে সাধারণ মানুষ।
থানায় ধর্ষিতাকে জিজ্ঞাসাবাদের বর্ণনা এতটাই নিখুঁত যে তা পড়ার পরেও যেন গা গুলিয়ে ওঠে। থানায় তাকে প্রশ্ন করা হয় ধর্ষণ সে উপভোগ করেছে কিনা, তার পোশাক কেমন ছিল…।
““আপনার কি মনে হয় এরকম একটা জায়গায় ঘরের বাইরে এমন পোশাক পরা ঠিক হয়েছে? আমার এই নালায়ক কনস্টেবল হরিরাম, ওই যে সেন্ট্রি ডিউটিতে আছে, সে পর্যন্ত এমন পোশাক দেখলে বলাৎকারী হয়ে উঠতে পারে”। নিজের নোংরা রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে ওঠে থানেদার”। [পৃঃ ১৩৭] নারীদের পোশাকের জন্যই যে ধর্ষণ একশো শতাংশ দায়ি এ নিয়ে কারোর সন্দেহ থাকার কথাই নয়।
আরও ঘৃণিত কিছু বাক্যালাপ যা, এই বইয়ের মধ্য দিয়ে এই সমাজকেই বুঝে নিতে সাহায্য করে। ধর্ষিত নারী কতটা তার নিজের জন্য ধর্ষিত এবং ধর্ষকের কোনো দায় না থাকা, এ তো এ যুগেও সত্যি। শেষ পর্যন্ত কোথাও নতি স্বীকার, হেরে যাওয়া নয়, মূল চরিত্রের উদারতাকেই ফুটিয়ে তুলেছে। এটা এক ধরনের প্রতিবাদ। যেখানে গোটা সমাজ ধর্ষক সেখানে এই কটা অল্পশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত নাবালক ছেলেদের শাস্তি দেওয়ারই বা কী আছে। গোটা সমাজটাই বদলানো দরকার। এই কয়েকজন বুঢন বা কার্তিক নয়। দর্শকামের মধ্য দিয়ে ধর্ষকামের যে যাত্রা তা যেকোনো পাঠক মাত্রই আজকের সমাজের সঙ্গে তফাৎ করতে পারবেন না। এ উপন্যাস আজও কেন প্রাসঙ্গিক তা মিলিয়ে নেওয়া খুব সহজ। উপন্যাসে সিস্টার নিজেও অসহায়। তাঁরও ঈশ্বরে আস্থা রাখা ছাড়া যেন কোনো উপায় নেই,
“গভীর সংকটে পড়েছেন সিস্টার রেজিনা। ‘নিডর’ – এর থেকে চারজন মেয়ে এসেছিল দেখা করতে সকাল পেরিয়ে। ওদের বিচার পাওয়ার অধিকার তিনি বোঝেন। তবুও তাঁর বিবেক বলে ধর্ষণের জন্য ছেলেগুলো যতটা না দায়ি তার চেয়ে বেশি দায়ি একটা নীতিহীন অসৎ সমাজ ব্যবস্থা। এলাকাটা অন্নুনত – শিক্ষার সুযোগ সীমিত, একটা হাসপাতাল নেই, বিদ্যুৎ দুর্লভ, রাস্তাঘাটের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ এখানে পর্নোগ্রাফি সহজলভ্য। মাঝে মাঝে চরম হতাশা জাগে মনে তবু পরম কারুণিক এক ঈশ্বরে অবিচল আস্থা থাকার ফলে বিষাদে ডুবে যান না সিস্টার”। [পৃঃ ১৮৪]
ধর্ষিতার, ধর্ষকদের বিরুদ্ধে কেস তুলে নেওয়ার মধ্যে যে প্রতিবাদ, তা একটা সামাজকে শিক্ষা দিতে চাওয়ারই নামান্তর। কামতাড়িত হয়ে কয়েকটি নাবালক ধর্ষণ করল, সেটা যতটা না অপরাধ তার থেকে অনেক বেশি অপরাধ এই নোংরা শো’য়ের ব্যাবসা যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁদের। এই রাঘববোয়ালদের শাস্তিটাই দরকার। কিন্তু সমাজ কতটা বুঝবে, বা আদৌ কি বুঝছে? এই ঘটনা তো অহরহ ঘটেই চলেছে, খোদ কলকাতাতেও। এখানে বিদ্যুৎ, শিক্ষা, ভালো রাস্তা কোনোকিছুরই তো ঘাটতি নেই। জনমানব তো অন্তত এই আফসোস করতে পারবে না। সর্বত্র আছে কেবল মানসিকতার অভাব এবং ক্ষমতাই লড়াই। এবং তার শিকার নারী। নারীবাদের স্বর যতই দৃপ্ত এবং স্পষ্ট হোক না কেন এর যোগ্য বিচার কবে হবে কারুর জানা নেই।
এ উপন্যাস অত্যন্ত আধুনিক একটি উপন্যাস। এর ভাষা, এর আঙ্গিকেই তা স্পষ্ট। লেখক যেভাবে আইনের খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ করেছেন তা তাঁর আইন সংক্রান্ত জ্ঞানকেই প্রকাশ করে। উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায় কোনো সংখ্যা চিহ্নে দাগানো নয়, অধ্যায়গুলির প্রতীকি এবং প্রকট নাম আছে। এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যাত্রা একটা অনন্য অভিজ্ঞতা বলা যায়। বহু অজানা বিষয় থেকে জ্ঞান আহরণও সম্ভব বলে মনে হয়েছে।
সবশেষে বলা যায়, এই উপন্যাস প্রকৃতপ্রস্তাবেই এই সময়ের একটি আয়না। ফলে, যদি কেউ মনে করেন, এই সময়কে একঝলক দেখে নেবেন, তিনি এই উপন্যাস পড়তে পারেন। যিনি এই উপন্যাসের লেখক, তিনিও এই উপন্যাসে রয়েছেন। আখ্যানকারীর সেই নির্মোহ উচ্চারণ আমাদের নিয়ে যায় এক তথ্যচিত্রের কাছে, যা আসলে আখ্যান। ফলে, এই উপন্যাসকে আখ্যানের তথ্যচিত্রও বলা যেতে পারে।
সুচারু প্রচ্ছদ ( প্রচ্ছদশিল্পী – সুপ্রসন্ন কুণ্ডু), ছিমছাম প্রোডাকশন এই গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণ করেছে।

