
এই সময়ের বিকল্প সত্য ও বিকল্প রাজনৈতিক চেতনার নাট্যকার
হিন্দোল ভট্টাচার্য
ব্রাত্য বসুর সাহিত্য অকাদেমি প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে একটি ঘটনা। তাঁকে আমাদের অভিবাদন জানাই। বাস্তব রাজনীতির মধ্যে থেকে রাজনীতি, ভাষা, ইতিহাস এবং সত্যকে বারবার ভেঙেচুরে গভীর ভাবে দেখেছেন ব্রাত্য তাঁর নাট্যসাহিত্যে। সেই সাহিত্যকে তিনি দৃশ্যকাব্যেও পরিণত করেছেন। অর্থাৎ অজান্তে একটা ভিন্ন স্বরের রাজনৈতিক এবং ইতিহাসচেতনা তৈরি হয়েছে আমাদের মধ্যে। এই কাজটি এক বিকল্প সাংস্কৃতিক চেতনার জন্ম দেয়, যা আগামী দিনে মানুষের মধ্যে জেগে উঠতে পারে, তাঁদেরও এমন সংশয়াচ্ছন্ন, প্রশ্নে কীর্ণ করে তুলতে পারে। উত্তর আমাদের জানা নেই, কিন্তু প্রশ্নগুলি যে তোলা যায়, বিকল্প ইতিহাস বা বিকল্প সত্য নিয়ে ভাবা যায়, সে বিষয়ে ব্রাত্য আমাদের সচেতন করেছেন তাঁর নাট্যসাহিত্যের মাধ্যমেই।
বাংলা নাটকের যে গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে, তাতে অনেক আগেই সংযোজিত হয়েছিল কিছু নতুন স্পর্ধার কাজ। সেই সব স্পর্ধার কাজের সঙ্গে
আমরা পরিচিত। যেমন ভুলতে পারব না সুমন মুখোপাধ্যায়ের ‘তিস্তা পারের বৃত্তান্ত’ বা ‘মেফিস্টো’, যেমন ভুলতে পারব না দেবশঙ্কর হালদারের অভিনয় বা গৌতম হালদারের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ তেমনই আরও এমন উজ্জ্বল উদাহরণ না বাড়িয়ে বলা যায় ভুলতে পারব না ব্রাত্য বসুর নাট্যসাহিত্যকে। আমরা যখন বিশ্বসাহিত্য পড়তে বসি, তখন শেক্সপীয়র বা ব্রেষট বা পিন্টার বা বার্নার্ড শ কিংবা শেকভ বা মায়ারহোল্ড বা স্তানিস্লাভস্কি সাহিত্য হিসেবেই পড়ি। আর সেই সাহিত্য আমাদের রক্তের ভিতর, স্নায়ুর ভিতর মিশে যায়। নাট্যসাহিত্যের আঙ্গিক মিশে যায় কবিতার ভিতর। আবার কবিতাও মিশে যায় নাট্যসাহিত্যে। সফোক্সিস থেকে আওনেক্সো পর্যন্ত আমরা দেখেছি কী অপূর্ব ভাবেই এই মিথষ্ক্রিয়া ঘটে। বাংলা নাটকে রবীন্দ্রপরবর্তী (ডাকঘর, রক্তকরবী, রাজা, অচলায়তনের টেক্সট-কে সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় জায়গায় রাখা ছাড়া আমাদের উপায় কী) মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকার সমৃদ্ধ করেছেন। শম্ভু মিত্রের ‘চাঁদ বণিকের পালা’-র কথা বা উৎপল দত্তের আজীবনের কাজের কথা কেই বা ভুলতে পারে!
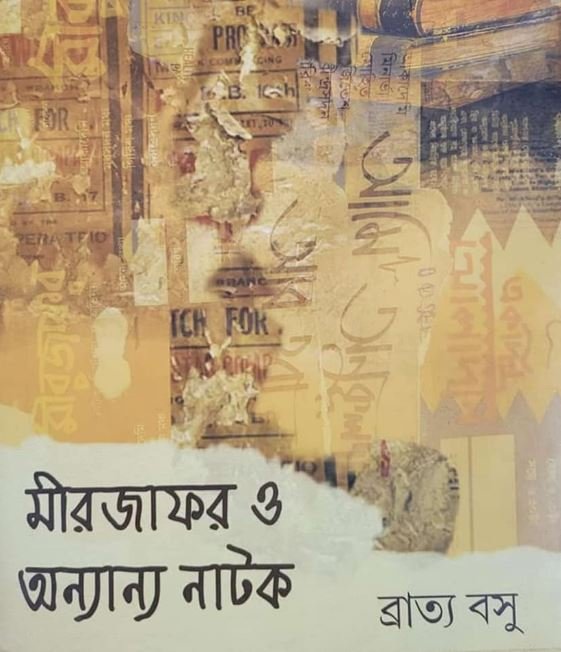
এই ঐতিহ্যে এক অধুনান্তিক ভাষ্য আনলেন ব্রাত্য। যা তাঁর প্রথম জীবনের নাটক ‘অশালীন’-এই টের পাওয়া গিয়েছিল। ‘কথ্য ভাষা’ এবং ‘ভাষার বিশেষীকরণ’ যে একটি নাটকের বিষয় হতে পারে, তা তার আগে কেউ ভেবেছেন কিনা জানি না। অন্তত বাংলা ভাষায় তো আমি এর নজির খুঁজে পাইনি। কিন্তু ব্রাত্যর ক্ষমতার জায়গাটি হল ব্রেষটীয়। অর্থাৎ, তিনি যে বিষয়ের অবতারণা করবেন, তা মানুষকে মোহিত করবে। এই অশালীন নাটকের মধ্যে রয়েছেন কামু, রয়েছে আউটসাইডার, রয়েছে জন অসবোর্নের সেই জিমি পোর্টারের রাগ, রয়েছে সমাজের যে নানান ক্ষমতার ত্রিভুজ, তাকে উলটে দেওয়ার প্রবণতা। কিন্তু এই সমস্ত আলাদা আলাদা প্রবণতাই এই নাটকের মধ্যে এসে মিশে গেছে এবং সৃষ্টি করেছে এক নতুন নাট্যভাষা।
অশালীনের পরে ব্রাত্য একের পর এক এক ক্ষুরধার নাট্যভাষায় রচনা করেছেন এমন সব নাটক, যেগুলিকে আমরা বার্নার্ড শ-এর ভাষায় বলতে পারি ‘প্রবলেম প্লে’। এবং অসবোর্নের লুক ব্যাক ইন অ্যাংগারের মতোই তাঁর নাটকগুলি সম্পর্কে বলা যায়, এই নাটকগুলি বার্তা দেয়, সমস্যাকে চিহ্নিত করে কিন্তু স্লোগান হয়ে ওঠে না। এই বৈশিষ্ট্য একজন আধুনিক ও একজন অধুনান্তিক নাট্যকারের শক্তি। কারণ তিনি যে যে বিষয় নিয়ে নাট্যসাহিত্য রচনা করেছেন,প্রযোজনা করেছেন, পরিচালনা করেছেন, সেই সব নাটকে এই প্রবণতা সহজেই আসতে পারত। হয়ে উঠতে পারত সংশয়ের বা চিন্তার বার্তার জায়গায় নির্দিষ্ট পথের ঈশ্বর বা সঙ্ঘ নির্দেশিত স্লোগান। রাজনৈতিক নাটকের এই বিষয়টি অধুনান্তিক নাটকের বিষয় নয়। আমরা কেউ জানি না কোথায় চলেছি। ফলে, অশালীনের সেই ব্যক্তি, যিনি আসলে সংশয়াচ্ছন্ন, প্রশ্ন করে চলেছেন, সেই ব্যক্তি ঘুরে ফিরে আসছেন অরণ্যদেব এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাটক উইঙ্কিল টুইঙ্কিলেও।
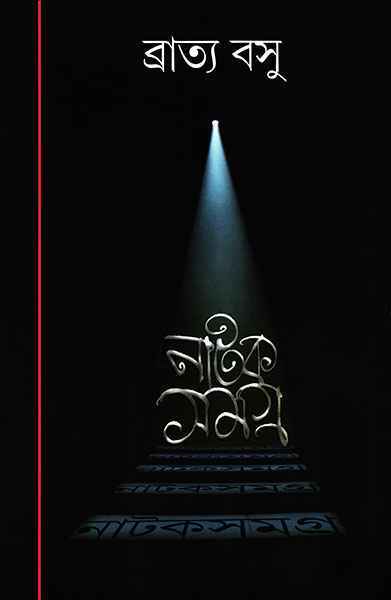
শীতঘুম থেকে উঠে ভিন্ন সময়ে জেগে ওঠা একজন মানুষ আর ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক ভাষার সমীকরণগুলিকে বুঝতে পারছেন না। ‘কমিউনিকেশন’ এবং কথা বলার ভাষাতেও এসে গেছে প্রচুর পরিবর্তন। সমাজের যেন মেটামরফোসিস হয়েছে, কিন্তু তাঁর হয়নি। ফলে তিনি আরও একা হয়ে পড়ছেন। এই একা হয়ে পড়াই তাঁর নিয়তি, তাঁর ব্যক্তিগত দর্শনের নিয়তি, তাঁর অবস্থানের নিয়তি। এ এক অধুনান্তিক রাজনৈতিক নাটক।
‘যারা সন্ত্রাস করে, তারা সবচেয়ে বেশি সন্ত্রস্ত’ জাতীয় রাজনৈতিক বোধের গভীরতার সংলাপ আমরা পাই তাঁর প্রতিটি নাটকেই। তাঁর একটি নাটকও অরাজনৈতিক নয়। আর তাঁর নাটকের রাজনীতি কখনওই যে রাজনীতিকে আমরা চোখে দেখি, কানে শুনি, খবরকাগজে পড়ি, তার মতো নয়। বরং তাঁর নাটক বারবার প্রচারিত বা উৎপাদিত সত্যকে আক্রমণ করে, প্রশ্ন করে, আমাদের মনের মধ্যে অস্বস্তি তৈরি করে। এক তীব্র অস্বস্তি নিয়ে আমরা যখন হল থেকে বেরোই, বা টেক্সট পড়া শেষ করি, তখন আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, আমরাও এই প্রশ্নগুলি তুলছি।
ব্রাত্য বসু উৎপাদিত সত্যের বিপরীতেও যে ইতিহাস রয়েছে, সেই ইতিহাসকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন বারবার তাঁর নাটকে। তা সে ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত-ই হোক বা ‘মীরজাফর’। আর এখানে এসেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় এক অল্টারনেটিভ স্পেস তৈরি হচ্ছে আমাদের ভাবনার জগতে। আর তার পর যখন আমরা ভাবি যে এই অল্টারনেটিভ স্পেস বা বিকল্প সত্য বা বিকল্প ইতিহাসের অনুসন্ধানের আবহ তৈরি হয়ে গেছে নাট্যজগতে, তখন আমাদের অবাক লাগে। কারণ এই বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন কাজ। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির বাইরের রাজনৈতিক ভাবনা নিয়ে আসা বা প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস চেতনার বাইরে বিকল্প ইতিহাসচেতনা নিয়ে আসা নয়ের দশকের শুধু না, বেশ কয়েক দশকের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
বাস্তব রাজনীতির মধ্যে থেকে রাজনীতি, ভাষা, ইতিহাস এবং সত্যকে বারবার ভেঙেচুরে গভীর ভাবে দেখেছেন ব্রাত্য তাঁর নাট্যসাহিত্যে। সেই সাহিত্যকে তিনি দৃশ্যকাব্যেও পরিণত করেছেন। অর্থাৎ অজান্তে একটা ভিন্ন স্বরের রাজনৈতিক এবং ইতিহাসচেতনা তৈরি হয়েছে আমাদের মধ্যে। এই কাজটি এক বিকল্প সাংস্কৃতিক চেতনার জন্ম দেয়, যা আগামী দিনে মানুষের মধ্যে জেগে উঠতে পারে, তাঁদেরও এমন সংশয়াচ্ছন্ন, প্রশ্নে কীর্ণ করে তুলতে পারে। উত্তর আমাদের জানা নেই, কিন্তু প্রশ্নগুলি যে তোলা যায়, বিকল্প ইতিহাস বা বিকল্প সত্য নিয়ে ভাবা যায়, সে বিষয়ে ব্রাত্য আমাদের সচেতন করেছেন তাঁর নাট্যসাহিত্যের মাধ্যমেই।
ব্রাত্য বসুর সাহিত্য অকাদেমি প্রাপ্তি তাই একপ্রকার ভিন্ন স্বরের সাহিত্য অকাদেমি প্রাপ্তি। নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, তাঁর নাট্যসাহিত্যের এই সন্দর্ভ ( ডিসকোর্স) ভারতবর্ষের নাট্যসাহিত্যেই এক অধুনান্তিক ধারা। একধরনের সাবভার্সন আছে, যা সঠিক ভাবে বুঝলে অস্বস্তিই হবে ক্ষমতাকাঠামোর।
একজন হ্যামলেট থাকে ব্রাত্য বসুর নাটকে। তাকে দেখা যায় না। কিন্তু সে থাকে আর সামাজিক সব ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়।


দারুণ লেখা। শেষ দুটি লাইন কবিতার সত্য।