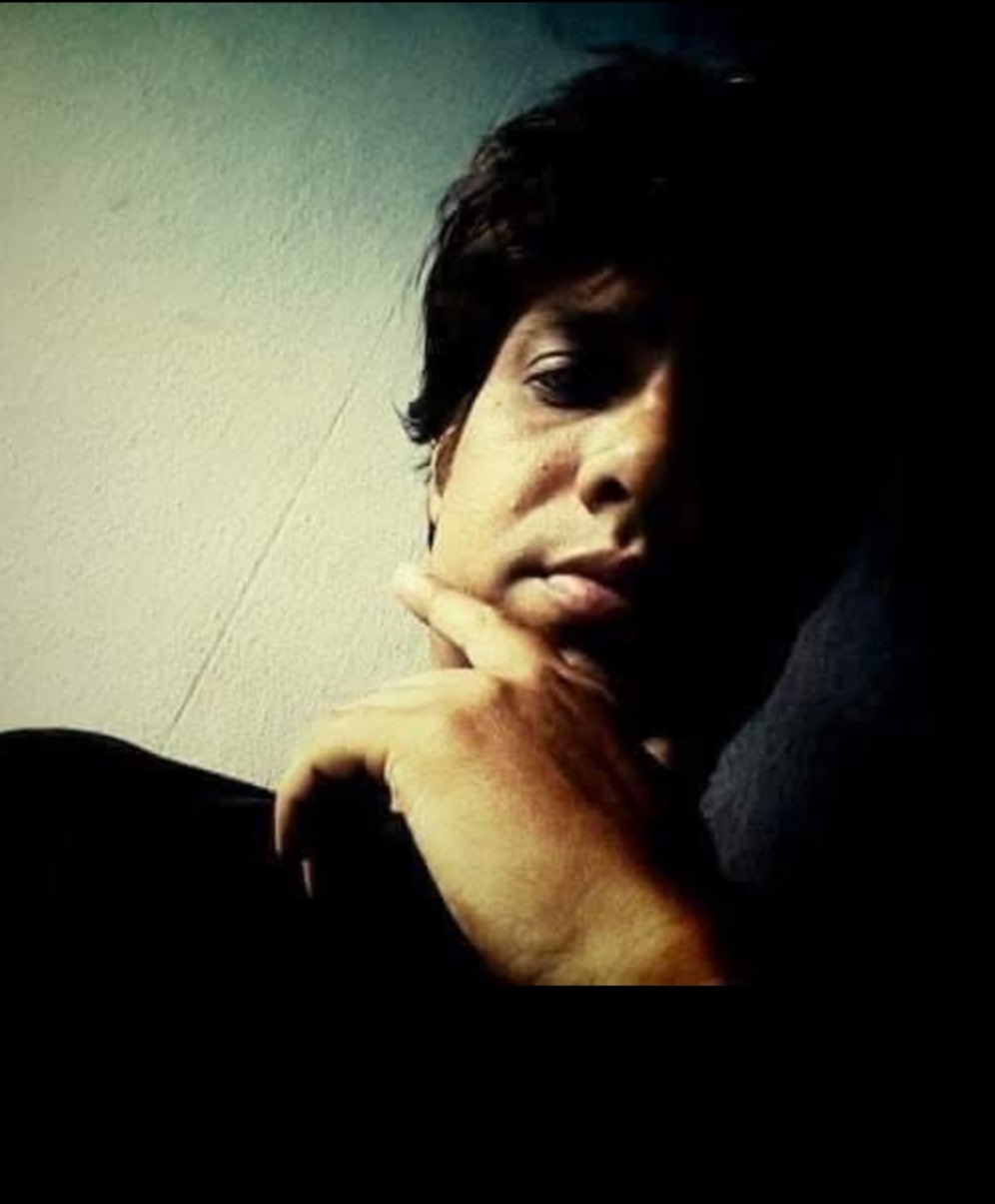
গালিব ও বেদিল
শুভ চক্রবর্তী
" বেদিল ফার্সি কবিতার এমন এক ঐতিহাসিক অধ্যায় যাকে আমরা ভারতীয় ফার্সি ভাষায় সূচনা হিসেবে দেখতে পারি। তিনি এমন এক ধারার প্রবাহকে প্রতিষ্ঠিত করছেন যা একদিকে যেমন চিন্তার জটিল বৌদ্ধিক ধারনাকে প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে ভারতীয় চেতনার উপলব্ধি এক ভিন্ন স্তরে প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি এমন এক ভারতীয় জীবনচর্যার সাধনা করেছেন যাকে আমরা সুফী বলতে পারি। কিন্তু সুফী বলতে আমরা যে জগতের কথা জানি তার থেকে বেদালের জগৎ ভিন্ন। আর এখানেই গালিব সেই জগতের সন্ধান করেছেন ভিন্ন এক আঙ্গিকে। তাহলে কি গালিবকে আমরা সুফী কবি বলতে পারি? গালিবের কবিতার ভিন্নতাকে একটু তলিয়ে দেখে কেউ কেউ এইরকম প্রশ্ন যে করবেন এতে অস্বাভাবিক কিছু নয় বরং এটাই স্বাভাবিক যে তাঁর কবিতা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলবেন শুধু এই কারণে যে গালিব একজন সুফী সাধক! আর এই কারণে যেমন বেদিলের কবিতা দর্শনের এক অমূল্যসম্পদ ঠিক একই ভাবে গালিবের কবিতা এক আত্মউত্তরণের দর্শন। আর এটা তো সত্যি যে বেদিলের মতো উপমাকে সেভাবে কেউ এর আগে ব্যবহার করেননি। তাঁর কবিতায় আমরা পাই এক ভিন্ন দর্শন, অমূল্য উপমা ও রূপকের ভান্ডার। আর বাক্যাংশের সামঞ্জস্য এমন এক প্রতিমায় বিস্তারিত হয় যাকে আমরা একটা ছোটো পাহাড়ী ঝর্ণার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। "
বেদিলের চেতনার প্রতি আমার গভীর নিষ্ঠার কারণেই আমার নিজের লেখায় ভবিষ্যদ্বাণীমূলক একটা গুণ দেখা যায়। বেদিল যেহেতু দেবদূতের মতো আমার পথপ্রদর্শক, তাই আমি অজানা পথে হাঁটতে এবং কোনও জায়গায় আটকে যাওয়ার ভয় পাই না। –গালিব
আমরা জানি গালিবের যখন উনিশ বছর বয়স তখনই অর্থাৎ ১৮১৬ সালে তাঁর প্রথম উর্দু দীওয়ানের পাণ্ডুলিপি এবং ১৮২১ সালে তাঁর দ্বিতীয় দীওয়ানের পাণ্ডুলিপি যখন তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল চব্বিশ বছর। অর্থ্যাৎ গালিব তাঁর জীবনের সূচনা পর্বেই লিখেফেলেছেন তাঁর সমগ্র জীবনের বৌদ্ধিক সাধনার প্রবাহ। এই সময়ের সব লেখাই কি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে আমাদের কাছে বিবেচিত হয়েছে? শুধু যে বিবেচিত হয়েছে তাই নয় তাঁর লেখায় যে রহস্যময় চেতনা রয়েছে তার প্রতি পাঠে আমাদের বিচলিত করেছে। ঠিক তেমনই পাশাপাশি আমাদের চিন্তার গলিপথ বিস্তারিত হয়েছে । আর এটাই তো স্বাভাবিক যে একজন কবির সাধনার ধারা একজন পাঠকের জীবনের পথকে প্রশস্ত করবে। না হলে আমরা কবিতা পড়ব কেন ? আর এইখান থেকেই তো আমাদের জীবনের বোধ গাঢ় হয়। হয় না কি? না হলে আমরা আজও কেন গালিবের কবিতা পাঠ শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি। কেন মনে হয় তাঁর ওই কবিতায় মন আবিষ্ট হয়ে থাকতে চায় ? আসলে আমাদের মনের অসংখ্য গলি পথ আছে, যে পথে আমদের ‘বোধ’ সাধনার প্রবাহ আমাদের মনকে বিস্তারিত করে।এই পথ সৃষ্টির ‘আমি’র পথ। যেখানে আমরা সেই বোধের প্রবাহকেই পথ খুলে দিই । যে বোধ আমাদের মনের সুরেকে মিশিয়ে ভিন্ন এক সুর তৈরি করে, যাকে বিশ্ব ‘আমি’র সুর বলা যায়। অর্থাৎ এমন এক সুর যা সমগ্র মনের সুর। যে কেউই সেই সুরের প্রবাহকে স্পর্শ করতে পারেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে গালিবের কবিতায় আমরা রহস্যময় চেতনা উপলব্ধি করি যা পাঠকের কাছে অচেনা এক পথের পথ বলে মনে হয় । ঠিক পাশাপাশি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আমাদের আরও বিভ্রান্ত করে। এই ভিন্নতা একজন কবির কাছে যেমন খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় তেমনই একজন পাঠকের কাছেও। এটা ঠিক যে গালিবের কবিতায় আমরা পাই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ। অর্থ্যাৎ গালিবের অভিপ্রায়ে যে শব্দ কবিতায় কবিতাকে ভিন্ন এক বৌদ্ধিক সাধনার প্রবাহে আমাদের মনের ভিন্নতাকে প্রকাশ করেছেন তার উপলব্ধি আমাদের কখনও কখনও বিচলিত করে। এটা তো হয়ই। হয় না কী? যখন আমরা কোনও অচেনা জায়গায় গিয়ে এক শিহরণ অনুভব করি ? অনেক সময় তো আমাদের জীবনে এইরকম কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যা আমদের মনকে বিচলিত করে শুধু এই কারণে যে আমার মন সেই বোধের কাছাকাছি গিয়েও সে বোধের সুরকে নিজের মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারছি না।
আর সে কারণেই যেন আমরা তাঁর কবিতার শব্দের অর্থ খোঁজার চেষ্টা করি তাঁর জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে। আর এখানেই আমরা যে শুধু ভুল করি তাই নয়, তাঁর কবিতার বিচার করি ভিন্ন এক বৌদ্ধিক সাধনার। আমরা যদি গালিবের কবিতায় এই যে ভিন্নতা বিকাশের বিবর্তন সে সম্পর্কে আলোচনা করতে যাই তাহলে প্রথমে আমাদের বুঝে নিতে হবে গালিবের কবিতা লেখার সূচনা পর্বের ভিন্নতা। অর্থ্যাৎ গালিব তাঁর কবিতাকে পাঠকের কাছে কী অভিপ্রায়ে প্রকাশ করছেন। কেন তিনি সেই সময়ের কবিদের থেকে ভিন্ন ?
এ-প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে যাই তাঁর কবিতার মধ্যেই। তবুও আমরা একটা সম্ভাবনাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করব। যেখানে আমরা গালিবের কবিতায় প্রকাশ আঙ্গিক কিছুটা হলেও বুঝতে পারব। গালিব যখন নিজেই সেকথা বলছেন: মহোদয়, প্রথমে বেদিল, আসির বা শওকতের কবিতার আদলে রেখতা গজল লিখতাম। তাই এই স্বীকারোক্তি দিয়ে আমার একটি গজল শেষ করলাম:
طرز بیدل میں ریختہ کہنا
اسد اللہ خاں قیامت ہے
তর্জ-এ বেদিল মে রেখতা কহনা
আসাদুল্লাহ খাঁ কয়ামত হ্যায়
বেদিলের মতো গজল লেখা
আসাদুল্লাহ খাঁ অলৌকিক
এই যে আমরা গালিবের একটি দ্বিপদী উল্লেখ করলাম তা এই কারণে যে গালিবের লেখায় আমরা যে রহস্যময়তা উপলব্ধি করি তার একটা সুতো হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। অর্থ্যাৎ আমরা এই দ্বিপদী থেকে কিছুটা অনুমান করতে পারব গালিবের ভিন্নতা ঠিক কোন পর্যায়ের। উপরের দ্বিপদী গালিব লিখিছিলেন তাঁর প্রথম দীওয়ানের বিরল পাণ্ডুলিপির শীর্ষে (যা প্রায় এক শতাব্দী পরে ভোপালের একটি প্রাচীন বইয়ের দোকানে থেকে পাওয়া গিয়েছিল ),তিনি আলংকারিক ক্যালিগ্রাফিতে মির্জা আবদুল কাদির বেদিলের (১৬৪৪-১৭২০) স্মৃতির প্রতি তাঁর সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। এমনকি তাঁর লেখা প্রতিটি শব্দ বেদিলের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধানিবেদনে ভরে উঠত। তাছাড়া গালিব হযরত আলী এবং পবিত্র পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্মানসূচক নাম লিপিবদ্ধ করার পর তাঁর গুরু মির্জা আব্দুল কাদির বেদিলের নাম দিয়ে শেষ করেছিলেন। পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া শেষ কথায় গালিব নিজেকে ফকির-ই বেদিল (বেদিলের একজন ভক্ত) বলে অভিহিত করেছেন।
গালিবের প্রথম দিকের রেখতা (উর্দু) কবিতা, যা তিনি ঊনিশ বছর বয়সে লিখেছিলেন (পরে নুসখা-ই ভোপাল আউয়াল, প্রথম উপস্থাপনা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), যদিও তিনি বলেছেন যে তিনি সেই পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে ফেলেছিলেন এবং প্রথম দিকের কবিতাগুলো ফেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু দেখা গেল গালিব তা করেননি। কারণ তাঁর কাছে আরও একটি পাণ্ডুলিপি ছিল। এমনকি তিনি এও বলেছিলেন যে তিনি পরবর্তী দীওয়ানের জন্য প্রথম পাণ্ডুলিপির নমুনা হিসাবে দশ থেকে পনেরোটি দ্বিপদী রেখে দিয়েছিলেন ।
‘আমার যৌবনের এই কয়েক বছরে আমি একটি দীওয়ানের জন্য যথেষ্ট কাব্য রচনা সংগ্রহ করেছি। তারপর দীওয়ানের চিন্তা একপাশে রেখে সেইসব পাতা ছিঁড়ে ফেললাম। আমার পূর্ববর্তী কবিতার নমুনা হিসেবে আমি আমার দীওয়ানের জন্য প্রায় দশ-পনেরোটি লেখা রেখে দিয়েছিলাম।’ – গালিব, আবদুর-রাজ্জাক শাকির (গালিব ১৯২০: ২০৪)
কিন্তু এটাও বাস্তবে সত্য নয় । কারণ প্রকাশিত দীওয়ানে পর্যাপ্ত সংখ্যক সম্পূর্ণ গজল পাওয়া যায়। তাহলে গালিব এমন কথা কেন বলেছিলেন তাঁর পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে? কেউ কেউ মনে করতে পারেন সেকথা, কেননা কথাগুলো আসলে তো পরস্পরবিরোধী তথ্য যা আমদের বিভ্রান্ত করে । আমরা জানি যে গালিব তাঁর যৌবনে বেদিল যেভাবে পড়েছেন তা তাঁর সচেতন ও অবচেতন আত্মার অংশ হয়ে উঠেছিল। আর এই কারনেই গালিব তাঁর প্রথম দিকের লেখায় বারবার বেদিলের কথা উল্লেখ করেছেন।তিনি বেদিলের লেখা থেকে নিজের কবিতার আঙ্গিক সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছিলেন । সমসাময়িক কবিতার থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন এই কারণে যে তিনি যা তাঁর কবিতায় পেতে চাইছিলেন তা এখনও তাঁর কবিতায় নেই । আর এটাই স্বাভাবিক যে একজন কবির প্রভাব পরবর্তী কবির লেখায় পড়বে। আমরা জানি যে তিনি বেদিলকে অন্য যে কোনো ভারতীয় বা ইরানি কবির চেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। তার কারণ বেদিলের লেখায় ভিন্ন এক প্রবহমান রহস্য। গালিব বেদিলের কবিতা পড়তে পড়তে হারিয়ে যেতেন । হয়ত এই কারণে গালিবকে লিখতে হয়েছিল:
আসাদ হর জা সুখন নে তরহ্- এ বাগ – এ তাজা ডালি হ্যায়
মুঝে রঙ্গ- এ বাহার ইজাদী – এ বেদিল পসন্দ আয়া
অর্থাৎ গালিব নিজেকেই বলছেন যে তিনি বেদিলের বসন্তের মতো সৃজনশীলতার প্রেমিক। কেননা কত মনোমুগ্ধকর আর রঙিন তার বাগানের সতেজতা! আমরা জানি নুসখা-ই-হামিদিয়ায় (তাঁর মৃত্যুর বাহান্ন বছর পর ভোপালের একটি লাইব্রেরিতে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় সংস্করণ। যার মধ্যে চব্বিশ থেকে পঁচিশ বছর বয়সের লেখা কবিতা রয়েছে । পরে সেই পাণ্ডুলিপি ভোপাল সরকার নুসখা-ই-হামিদিয়া শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে)
এই সময় গালিব বেদিলের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং বারবার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশের জন্য গালিব ( সেই সময়ে গালিব নিজের আসাদ ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন) এগারোটি দ্বিপদী অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শুধু তাই নয় গালিব তরজ-ই-বেদিলের প্রশংসা করেন এবং তিনি বেদিলের এই কবিতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান। কারণ তিনি সেই কবিতা পাঠ করে নিজের কবিতার ভিন্নতাকে প্রকাশ করতে পেরেছেন । গালিবের নিজের এই নজমগুলি ছিল বেদিলের (নাগমা-ই-বেদিল) গানের প্রভাব । বেদিলের প্রতি তাঁর এই স্বর্গীয় আকর্ষণ হলো (বাহার ইজাদি-ই-বেদিল) বেদিলের উদ্ভাবনের বসন্ত। আর তাই গালিব বেদিলের নাজমকে মহান আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক বা খিজ্র বলেছেন। গালিব তাঁকে ‘তীরহীন নদীর’ সঙ্গে তুলনা করেছেন । সেইসব লেখার চিরন্তন অর্থের উপহার দেওয়ার জন্য বারবার প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে বেদিল যদি ‘একটি কুঁড়িকে ফুলে’ রূপান্তরিত করেন, তবে তাঁর আশীর্বাদে গালিবের সম্ভাবনাও ভিন্ন এক উচ্চতা স্পর্শ করবে (ঘানি ১৯৮২: ৫০-১)।
দুই
বেদিল ফার্সি কবিতার এমন এক ঐতিহাসিক অধ্যায় যাকে আমরা ভারতীয় ফার্সি ভাষায় সূচনা হিসেবে দেখতে পারি। তিনি এমন এক ধারার প্রবাহকে প্রতিষ্ঠিত করছেন যা একদিকে যেমন চিন্তার জটিল বৌদ্ধিক ধারনাকে প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে ভারতীয় চেতনার উপলব্ধি এক ভিন্ন স্তরে প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি এমন এক ভারতীয় জীবনচর্যার সাধনা করেছেন যাকে আমরা সুফী বলতে পারি। কিন্তু সুফী বলতে আমরা যে জগতের কথা জানি তার থেকে বেদালের জগৎ ভিন্ন। আর এখানেই গালিব সেই জগতের সন্ধান করেছেন ভিন্ন এক আঙ্গিকে। তাহলে কি গালিবকে আমরা সুফী কবি বলতে পারি? গালিবের কবিতার ভিন্নতাকে একটু তলিয়ে দেখে কেউ কেউ এইরকম প্রশ্ন যে করবেন এতে অস্বাভাবিক কিছু নয় বরং এটাই স্বাভাবিক যে তাঁর কবিতা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলবেন শুধু এই কারণে যে গালিব একজন সুফী সাধক! আর এই কারণে যেমন বেদিলের কবিতা দর্শনের এক অমূল্যসম্পদ ঠিক একই ভাবে গালিবের কবিতা এক আত্মউত্তরণের দর্শন। আর এটা তো সত্যি যে বেদিলের মতো উপমাকে সেভাবে কেউ এর আগে ব্যবহার করেননি। তাঁর কবিতায় আমরা পাই এক ভিন্ন দর্শন, অমূল্য উপমা ও রূপকের ভান্ডার। আর বাক্যাংশের সামঞ্জস্য এমন এক প্রতিমায় বিস্তারিত হয় যাকে আমরা একটা ছোটো পাহাড়ী ঝর্ণার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। কেননা এইসব ছোটো ছোটো সূক্ষ্ম প্রতিমা সবসময় আমাদের মনের দোড়গোড়ায় এসে পৌঁছায় না। আর এই কারণে আমাদের মনের ভাষায় সেই কবিতা অনুবাদও করতে পারি না। এখানে যেমন অনুবাদ আবার অন্য কোনোও জায়গায় আমরা সেই কথাই উপলব্ধি হিসেবে দেখব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বেদিলের কাব্য সংকলনে আমরা কীভাবে সেই প্রতিমাকে মনের অলিন্দে নিয়ে আসতে পারি? আমরা জানি যে তাঁর কাব্য সংকলনে তিনি নতুন এবং উদ্ভাবনী বিষয় নিয়ে আসেন। এবং এও জানি যে তিনি তাঁর কবিতায় অস্বাভাবিক লিরিসিজম অর্জন করেছিলেন । যদিও তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জটিলতা এবং বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর সংযোগ আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। তাঁর কবিতায় রহস্যের অন্তর্ধারা থাকা সত্ত্বেও শব্দের এমন মসৃণ প্রবাহ, এমন আনন্দময় উচ্ছ্বাসের নেশা যে পাঠক সমগ্র বিশ্বজগতের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করবেন এটাই স্বাভাবিক। তাঁর কবিতা নিছক দার্শনিক চিন্তার সংগ্রহের বাইরে গিয়ে ভিন্ন এক আত্মপরিচয়ের গভীরে প্রজ্ঞার গান হয়ে ওঠে। আর এখানেই সেই আমির বোধ আমাদের সেই গভীরতাকে উপলব্ধি করতে একটা প্রবাহকে নিরন্তর আমাদের মনের উপরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আর তখনই কেউ কেউ এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন, কেন এই রহস্যময় জটিলতা? অবশ্যই এমন সমালোচকও ছিলেন যারা তাঁর কবিতায় একটি অদ্ভুত রহস্যের অনুভূতি এবং তাঁর চিন্তাভাবনার জটিলতা সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু সত্যটা হল এই যে বেদিলের প্রভাব চিন্তাবিদ ও কবিদের প্রজন্মের মধ্যে বিস্তারিত হয়েছিল। ভারতের শেষ দুই মহাকবি গালিব ও ইকবাল যে তাঁর মাহাত্ম্যকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তা এই কারণে। ইকবাল তাঁকে প্রত্যয় ও কর্মের কবি বলেছেন আর গালিবের জন্য তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক। অর্থাৎ একজন কবি তিনি তাঁর কবিতার আধারকে আরও গাঢ় করেছেন বেদিলের কবিতা পাঠ করে। একটু একটু করে গালিব তাঁর কবিতায় সেই ভিন্নতাকে ধরার চেষ্টা করবেন। বিশেষজ্ঞরা একমত যে গালিবের ফার্সি কবিতা তুলনামূলকভাবে সহজ এবং সরল, যেখানে তিনি তার মাতৃভাষা উর্দুতে যা লিখেছেন তা যে জটিল শুধু তাই নয় বরং বলা যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং মুক্ত প্রকাশের প্রবাহ ছিল। তারমানে আমরা আরও একটা কথা জানতে পারলাম যে গালিবের ফারসি ভাষার প্রতি টান থাকলেও তিনি কবিতা রচনা করলেন উর্দু ভাষায়। অর্থ্যাৎ গালিব যে কবিতার ভাষার সন্ধান করছিলেন এ বিষয়ে গালিবের সমালোচকরা একমতে আসতে পেরেছেন। আর সেটা সম্ভব হয়েছে বেদিলের কবিতা পাঠ করে। সেই কবিতাই তাঁর একান্ত জগৎ যেখানে গালিব তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তার পথের পথে নিজেকে এগিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যে বেদিলের কবিতা একটা বাগানের মতো, যার দুটি দরজা রয়েছে- একটির নাম উর্দু এবং অন্যটি ফারসি। আর আমরা এও জানি তিনি যে উর্দুর চেয়ে ফার্সি কবিতা বেশি পছন্দ করেন তা বলার সুযোগ তিনি কখনোও হাতছাড়া করেননি। এটাও সত্য যে গালিবের ‘মুঠঠি ভর উর্দু শায়রি’ অন্য যেকোনো কবির চেয়ে বেশি সমালোচনার শিকার হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি ওয়ারিস কিরমানি মূল্যায়নের পথের ধারে দাঁড়াই তাহলে শুনতে পাবো : ‘গালিব কে বুঝতে হলে আমাদের তার অবচেতন চিন্তার প্রক্রিয়ার লুকানো স্তরগুলিতে গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে হবে।’ অর্থাৎ কিরমানি আমাদের গালিবের ভিন্নতা বোঝাতে গিয়ে বললেন দ্বিপদী কবিতার তুলনা করে গালিবকে ধরা অসম্ভব। এটা ঠিক যে কিরমানি এমন এক রহস্যময় জটিলতার ভেতরে গিয়ে গালিবকে বুঝতে চাইছেন তা আমদের কাছে কোনও অংশেই অযৌক্তিক নয়। কেননা তিনি এও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে বেদিলের মতো, তিনিও বারুণ শুদান এর অর্থ হচ্ছে যে দরজা দিয়ে আপনি যেতে পারেন কিন্তু বের হতে পারবেন না। প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন, যা আরও বিশদে আলোচনা করা প্রয়োজন। ইয়াগানা গালিবের সবচেয়ে খারাপ সমালোচকদের একজন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে তিনি তাঁর সমালোচনার মাধ্যমে গালিবকে কিছুটা হলেও নিচে নামিয়েছেন। শেক্সপিয়ার এবং রুমির মতো মহান কবিরাও চুরির অভিযোগ থেকে রেহাই পাননি। কিন্তু এভাবে ভাবা অজ্ঞতা। বেদিল এবং গালিবের মধ্যে একটি খুব গভীর সম্পর্ক । আমরা যদি শুধুমাত্র গালিবের দ্বিপদী উল্লেখ করে আলোচনা করি তাহলে তা আত্মঘাতীর সমান। কেননা গালিব অনেক নতুন বাক্যাংশ তৈরি করেছিলেন এবং এমন অদ্ভুত সমন্বয়ের কথা ভেবেছিলেন যা অন্য কোনও কবি সেইসময় দাঁড়িয়ে তা করার সাহস করতে পারেননি। তখন গালিবের এই ভাষা সমন্বয়ের বিষয়টিকে উদ্ভাবনী বলে মনে করা হতো না। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর সেই উদ্ভাবনী একটি আংটির উপর সূক্ষ্ম হীরার কাজ বলে মনে করা হয়। আর এই কারণে গালিবকে আমরা বলি ভাষা সমন্বয়ের জাদুকর।
একই সঙ্গে বিশেষজ্ঞরাও এগিয়ে এসেছেন সব ধরনের প্রশংসায়। গালিবকে নিয়ে যত বেশি লেখা হয়, ততই তার কাজ দেখার নতুন পথ খুলে যায়। সূক্ষ্ম রূপক ও শৈল্পিকতায় পরিপূর্ণ এই কবিতা একের পর এক স্তরে স্তরে জড়ানো । এই অনুভূতি পাঠক এড়াতে পারেন না। কারণ তাঁর কবিতায় ভাষার সামঞ্জস্য। যদিও কোনো ব্যাখ্যাই পরম বা চূড়ান্ত নয়। আর এটাও তো সত্যি যে প্রতিটি ব্যাখ্যাই কিছু না কিছু রেখে যায় আমদের জন্য। গালিবের কবিতার অর্থের গভীরতা ধরা সহজ মনে হলেও বাস্তবে তা খুবই কঠিন। তার হৃদয়হীনতার সঙ্গে এই গুণটিও রয়েছে। বেদিলের সঙ্গে গালিবের সম্পর্ক গঠনমূলক, কিন্তু প্রাণহীন নয়। তিনি বেদিলের কাছ থেকে আহরণ করেছেন তা সত্ত্বেও, তিনি নিজের কবিতার জগৎ তৈরি করেছিলেন ভিন্ন এক আঙ্গিকে। উভয়ই একই উৎস থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করলেও কিন্তু তাঁদের নিজস্ব সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর পরে, তাদের পথ ভিন্ন হতে শুরু করে । সমালোচকরা তুলনা করতে ভালোবাসেন। যাঁরা বেদিল ও গালিবের কাজ দেখেছেন তাঁরা দু’ই কবির মধ্যে মিল লক্ষ্য করেছেন। এটা একটা প্রাথমিক প্রবণতা। যদিও মিলগুলি বেশিরভাগ রূপক, উপমা এবং ব্যবহারে প্রসারিত।
তিন
ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থান ঔরঙ্গজেব আলমগীরের মৃত্যুর বছরকেই ক্ষমতার পতনের সূচনা বলে মনে করা হয়, একইভাবে মুসলমানদের মুসলিম সাহিত্যের ভাষা হিসেবে ফারসি ভাষাও একইসঙ্গে বিলুপ্ত হয়।এর একটা প্রাথমিক অনুমান করা যেতেপারে যেহেতু
দিল্লি এবং আশেপাশের এলাকার লোকেরা সম্ভবত শাহজাহানের রাজত্বকাল থেকেই তাঁদের দৈনন্দিন কথোপকথনে উর্দু বা হিন্দি ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। কিন্তু এটাও ঠিক যে ১৭০৭ সাল পর্যন্ত রাজা এবং অভিজাতরা নিশ্চিতভাবে কথা ফারসি ভাষায় কথা বলতেন। মির্জা নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ রঙ্গিলা ( রোশন আখতার ) সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যিনি উর্দু ভাষাকে সর্বস্তরে ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ দেন ।এই কারণেই মুহম্মদ শাহের আমলে ভারত ও তার আশেপাশে উর্দু কবিতার সূচনা হয়েছিল। এর কয়েক বছরের মধ্যে দাক্ষিণাত্য থেকে কবি ওয়ালী মুহম্মদ ওয়ালী
চলে আসেন এবং দিল্লী জয় করেন :
ওয়ালীর হৃদ্য় দাঁতি ছিনিয়ে নিয়েছে
কোনও মুহম্মদ শাহ নয়
ওয়ালী এমন এক মনস্তাত্ত্বিক মুহুর্তে দিল্লিতে এসেছিলেন যখন দিল্লীতে উর্দু গজলের সমসাময়িকতা নষ্ট হয়েগিয়েছিল। ওয়ালী তাঁর আবেগপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির রচনা উপহার দিয়েছিলেন ঠিক সেই সময়েই। আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে তাঁর এই সময়ের দিল্লী ভ্রমণ ভিন্ন এক ঐতিহ্যকে পুনরায় তার জায়গায় ফিরিয়ে দিয়েছিল । উর্দু ভাষার গৌরব’ রেখতা ‘ যেন আবার নতুন করে তার সৌন্দর্য পাঠক মহলে সমাদৃত হচ্ছিল। কেউ কেউ মনে করেন ওয়ালী দিল্লিতে দাক্ষিণাত্য মুশাইরার প্রবর্তন করেছিলেন। যার ফলে উর্দু গজলের একটা সম্ভাবনার পথ খুলে গিয়েছিল। নতুন ভাষায় কবিতার দ্রুত জনপ্রিয়তার পেছনে এটাই ছিল রহস্য। যদিও সেই সময়ের ফার্সি কবিতার ধরনও সম্ভবত এই বিপ্লবের জন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিল। নতুন কবিতা যখন দরবারে সমাদৃত হয়, তখন দিল্লির রাজপথ আরও বেশি উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানায়। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের পঞ্চাশ বছর কবিতা ও কবিতার জন্য বিশেষ অনুকূল ছিল না। কিন্তু এও জানা যায় যে, সিংহাসনে আরোহণের আগে, আলমগীর ভালো কবিতা উপভোগ করাকে লজ্জাজনক মনে করতেন না। কিন্তু সেই সময়েও, কবিতার প্রতি তার বিতৃষ্ণা এবং ধার্মিকতার প্রতি তার আগ্রহ এতটাই পরিচিত হয়েছিল যে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে তাঁর কাব্যিক পরিপূর্ণতা প্রকাশ করা তাঁর জন্য সম্মানের মাধ্যম ছিল না।
দীর্ঘ নীরবতার পর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর বারো বছর পর নতুন শাসক সাম্রাজ্যের প্রধান হন এবং তিনি গত অর্ধ শতাব্দীর নিয়ম-ভিত্তিক এবং নীতিগত অনুশীলনের ভেঙে দেন। জনসাধারণ ষাট এবং সত্তর বছরের কঠোর অনুশাসনের সঙ্গে তাদের আবেগকে উদ্বেলিত করে। ওয়ালী এবং তাঁর অনুগামীরা সাহিত্য চর্চার মধ্যে উর্দু ভাষা তৈরি করছিলেন। আর এই কারণে ভাষাকে আয়ত্ত করার জন্য এবং ফারসি ভাষার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য উর্দুতে শৈলীগত আর অভিব্যক্তি প্রদানের দিকেই তাঁদের মনোযোগ ছিল।আর তা ছিল যুক্তিগত রুচির কবিতা, যে গজলে রয়েছে সৌন্দর্য ও প্রকাশের স্বচ্ছতা এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ শব্দ। এবং কাসিদাতেও শক্তিশালী শব্দের নিজস্ব মূল্য আছে। ধারণা বা বর্ণহীন আবেগ যতই দুর্বল হোক না কেন বিপরীতে, আঠারো শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মীর-এর মহান শিল্প হল যে, তাঁর কথায় আবেগ ও অভিব্যক্তির সবচেয়ে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রয়েছে । কিন্ত তাঁর সেরা কবিতায় তা কখনও পাওয়া যায় না। তাঁরা যে কোনো একটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দী শুরুতে কবি মীরের রেখতার কাব্যিক পরিপূর্ণতার দানে সরলতা ও কমনীয়তা সম্পর্কে ওয়ালি যে ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা উর্দু সাহিত্যের ভিন্ন এক অধ্যায় যা বিশ্বে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয়েছিল। কবিতার এই নবজাত ঐতিহ্যের সঙ্গে আরও একটি সাহিত্য ধারা ছিল যার শৈলী ছিল উর্দু ভাষার বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ও অভিবাদনের সম্পূর্ণ বিপরীত। যা ছিল পরবর্তী ফার্সি কবিদের সম্প্রদায়। তাঁরা মনে করতেন সহজ কল্পনা এবং বক্তব্য উদ্ভাবনকে পরিপূর্ণতা দেয়। ফার্সি কবিতা অনেক আগেই তার প্রারম্ভিক সরলতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে গত অর্ধ শতাব্দীতে ফারসি কবিতা হারিয়ে যায়। ওয়ালীর ফার্সি সমসাময়িকদের মধ্যে মির্জা আব্দুল কাদির বেদিল এবং নাসির আলী সিরহান্দি ছিলেন এই কাব্যশৈলীর শ্রেষ্ঠ কবি।
চার
গালিব সম্পর্কে যা আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হলো তিনি পারস্যের কবিদের সরাসরি বংশধর। ওয়ালী ও মীর প্রজন্মের সঙ্গে তাঁর কোনোও সম্পর্ক নেই। অন্তত তার আগের যুগে। গালিবের প্রথম দিকের কবিতাগুলো দেখলে মনে হয় যে মীর নামে একজন মানুষ ছিলেন তাও তিনি অবগত ছিলেন না। মুহম্মদ শাহের শাসনের সময় থেকেই ফার্সি ও ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে ব্যবধান ছিল অনেকটাই। পরের নব্বই বছরে তা অনেকাংশে বিস্তৃত হয়েছিল। গালিব যখন খুব কম বয়স তখনই তাঁর মনে হয়েছিল তিনি ঠিক কোন পথে যাবেন । এই নিয়ে তিনি বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর একশো বছর পরে ১৮০৭ সাল থেকে এক শতাব্দী পিছিয়ে যান এবং সেখানে পৌঁছে যান যেখানে
ঔরঙ্গজেবের যুগের শেষ কবি ছিলেন। তিনি ভিন্ন কোনও পথ অনুসরণ করার কথাও ভাবেননি যা রেখতা কবিরা ফারসি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। তিনি উর্দুতে কবিতা লেখেন কিন্তু উর্দু ও ফারসি ভাষার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য করেন না। প্রকৃতপক্ষে, মুহাম্মদ শাহী যুগের পর প্রথম একজন উর্দু কবি এক শতাব্দী ভুলে সরাসরি ফারসি ভাষার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন । ফার্সি কবিদের সঙ্গে রেখতে কবিদের ঐতিহ্যের বৈসাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্ত এটা এমন একটা আন্দোলন ছিল যা ফলপ্রসূ হয়নি । যা শুধুমাত্র একজন অনভিজ্ঞ এবং অতি-উৎসাহী যুবকের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে পারে। আর যে কবিতার ঐতিহ্য ছিল একশো বছরের প্রবাহ । আর সে কারণেই সম্ভবত ১৮১৫ সালে গালিব তাঁর কবিতার ভিন্নতাকে এক ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। এখন এখানে আমদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে এই যে বলা হলো ভিন্ন এক আঙ্গিক, কেমন সেই আঙ্গিক যে কারণে গালিবের কবিতাকে দুর্বোধ্য এবং রহস্যময় বলে অভিহিত করা হয়েছিল? এখানে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার আগে আমদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন
যে গালিব ঠিক কী কারণে সমসাময়িক কবিদের থেকে আলাদা। অর্থাৎ গালিব যা বলতে চেয়েছিলেন তাঁর কবিতায় তা সেই সময়ের প্রচলিত ভাষায় বলা যেত না। এমনকি ফার্সির মতো ভাষাও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। আর আমরা জানি যে বেদিল তাঁর কবিতায় এমন সব শব্দ, বাগধারা, উপমা ব্যবহার করতেন যা সাধারণ কথ্য ভাষার থেকে আলাদা ছিল যে কারণে বেদিলের কবিতা স্থানীয় ফার্সি ভাষাভাষীদের জন্য বোঝা কঠিন ছিল । আর তাই বেদিলকে মূলধারার থেকে আলাদা বলে মনে করা হতো। গালিবের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল… অনেকে মনে করেন গালিব কি অত্যন্ত উদ্ভাবনী ও রূপক ভাষা এবং শৈলী ব্যবহার করে উর্দুকে নষ্ট করেছিলেন, নাকি তিনি উর্দু কবিতাকে ভিন্ন স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা শুধু বলতে পারি গালিবের মধ্যে এমন কিছু ক্ষমতা ছিল যা গালিবকে গালিবে হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। আমরা জানি তাঁর অসম্ভব ক্ষমতা ছিল গ্রহণ ও আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে। সাহিত্যের উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছানোর জন্য গালিবকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। অবশ্যই বেদিলের কাছ থেকে তিনি যা কিছু অর্জন করেছেন, তা মূলত তাঁর আকাঙ্খার আগুন এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলেই। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে নিখুঁত করার জন্য দিনের পর দিন পরিশ্রম করেছেন। গালিবের কবিতায় আমরা যে কণ্ঠস্বর শুনতে পাই তা সম্পূর্ণরূপে তার নিজস্ব। গালিব ‘আমার থেকে আমার কাছে’ এই উক্তির উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর কবিতার বিশেষত্ব হল তিনি সবকিছুকে নিজের ভেতরে ধারণ করেন এবং তাঁর স্বভাবের মণির মতো স্পষ্ট করে বলবার ধরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক রহস্যময় জগৎ সৃষ্টি করেন।
উর্দু-ফারসি ভাষার আটশো বছরের সাহিত্যের ইতিহাসে, আমরা এমন দু’জন কবি খুঁজে পাই না যাঁরা বেদিল এবং গালিবের মতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ছিলেন। গালিব হাফিজ, সাদী, ফিরদৌসী, জামি বা নিজামীর মতো অ-ভারতীয় কবিদের সঙ্গে ধর্মীয় সম্পর্ক গড়ে তোলেননি। যেমন তিনি বেদিলের সঙ্গে করেছিলেন, যদিও সেই সময়ে ইরানী কবিদের মহান হিসেবে বিবেচনা করা হত। আমরা কিছু আগে দুজনের মধ্যে মেজাজী এবং কাব্যিক সখ্যতার কথা বলেছি। কিন্তু, যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও কিছু পার্থক্যও রয়েছে। মন ভালো নেই ,গালিব তো গালিবই। বেদিল নিজেকে সুফি, সাধু এবং আধ্যাত্মিক প্রবণতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে যুক্ত করতেন। কিন্তু গালিব ছিলেন বিশ্ববাসীর একজন মানুষ। তিনি তাঁর জীবন অন্যদের উদারতার উপর নির্ভর করে কাটিয়েছেন। তিনি পার্থিব সুখ, সম্মান, প্রতিপত্তি, মর্যাদা এবং রাজসভায় স্থান চেয়েছিলেন।
অন্যদিকে বেদিল ছিলেন রুমি এবং ইকবালের মতো একজন কবি। কিন্তু গালিব কোনও পরিবর্তন করতে চাননি। এই সময়টা ছিল সুফিবাদের যুগ এবং এর বিষয়বস্তু সেই সময়ের কবিতায় কেন্দ্রীয়ভাব ছিল। তবে, গালিবের সুফি আকাঙ্ক্ষাযে ছিল না এটা বলা ঠিক হবে না । আমরা শুনেছি যে, সেই সময়ে প্রচলিত রীতি অনুসারে তারা চিশতিয়া তরিকার একজন সুফি পীর মিয়াঁ গোলাম নাসিরউদ্দিন, যাকে কালে সাহেব নামেও ডাকা হতো। গালিব তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তার মায়ের দিক থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে শিয়া ধর্ম পেয়েছিলেন। আমরা এও জানি যে হযরত গাউস আলী শাহ কলন্দরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। কিন্তু বাস্তবে গালিব না সুফি ছিলেন না দরবেশ ছিলেন, না কলন্দরও ছিলেন, না কিছু বিশিষ্ট সুফি ব্যক্তিত্ব বা রহস্যবাদীদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা। মাতাল হওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না।
আবদুল গনি যখন বলেন:
‘গালিব রহস্যময় বিষয় নিয়ে কথা বলেন এবং তিনি ঈশ্বরকে এমনভাবে সম্বোধন করেন যেন, তাঁর জন্য ব্যবস্থা না করেই সর্বশক্তিমান নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করেছেন। এটা স্পষ্ট যে রহস্যবাদ এবং বস্তুবাদের মধ্যে কোন মিল নেই । বেদিলের উচ্চ ধারণা সম্রাট এবং অভিজাতদের মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু মির্জা ছিলেন একজন মুক্তমনের মানুষ এবং মূলত একজন অ-অনুসারী। এটাই গালিবের একটা ভিন্ন গুণ বলা যায় আর এটাই তার জনপ্রিয়তার রহস্য। এই রহস্য তার ব্যক্তিত্বকে কিছুটা জটিল, বহুমুখী এবং সকলের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। এই কারণেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ – পণ্ডিত থেকে সাধারণ মানুষ, বিশ্বাসী থেকে পাপী, এবং তপস্বী থেকে মুক্ত চিন্তার মানুষ পর্যন্ত – গালিবের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ স্বভাব এবং সৌন্দর্যের ব্যাখ্যার প্রশংসা করেন। তার ভক্ত এবং অনুসারীরা সকলেই উপভোগ করেন যখন তিনি বলেন:
হুয়ে মর কে হাম জো রুসবা,হুয়ে কিউ ন গর্ফ এ দরিয়া
ন কভী জানাজা উঠতা, ন কভী মাজার হোতা।
অর্থাৎ গালিব বললেন: অপমান এড়াতে আমি কেন নদীতে ডুবে মরলাম না? এতে তো একটা কফিন, একটা সমাধি এবং একটি পাথর খোদাই রক্ষা পেত।
আর গালিবের এইরকম করে বলবার ধরণ দেখে একটা জিনিস স্পষ্ট: গালিব তার স্বাধীনতাকে অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি মূল্য দেন। সঙ্গীতের সুরের ভেতর থেকে পরাজয়ের ধ্বনি শোনা এবং নিজের আকাঙ্ক্ষার ভাঙন প্রত্যক্ষ করা সকলের কাম্য নয়। আর এইখান থেকে আমরা যদি একটু গালিবের কবিতা পর্বের সূচনার দিকে এগিয়ে যাই তাহলে দেখব তাঁর কাব্যজীবনের সূচনা খুব সহজ ছিল না । এই পরাজয়ের পরেও তরুণ কবি উর্দু ভাষার দিকে মাথা নত করেননি । তিনি ফারসি ভাষার সঙ্গে গভীর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক প্রকাশ করতে উদগ্রীব ছিলেন। যে কারণে তিনি পাঁচ-ছ’ বছর ধরে তাঁর সমালোচকদের বিরুদ্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। এই নীরবতায় গালিব বিরক্ত হয়ে পরচর্চার ক্ষেত্র থেকে দূরে গিয়ে তাঁর নিজের কল্পনাকে ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবর্তন করেন। এই অঙ্গীকার শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা যায়নি। প্রায় দশ বছর পরে, ১৮৫০ সালে, যখন বাহাদুর শাহের দরবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। গালিব আবার উর্দুতে কবিতা লিখতে শুরু করেন । এবং ১৮১৫ সালে যেভাবে লিখছিলেন একই পরিবর্তিত শৈলীতে লিখতে থাকেন। যাইহোক, এই পরিবর্তন সেভাবে এতটা বৈপ্লবিক ছিল না। গালিব উর্দু ভাষার ঐতিহ্যকে সম্মান করতেন, কিন্তু ফারসি ভাষার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা সর্বদা তাঁর সঙ্গে ছিল। ফলে ফারসির প্রতি গালিবের এই অনুরণন বৃথা যায়নি। আঠারো শতকে ফারসি ভাষা এত দ্রুত আমাদের সংবেদনশীলতা এবং কল্পনা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল যে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা ছিল গালিবের শক্তিশালী হাতের কাজ। যদি ওয়ালী- জৌক ও দাগের ঐতিহ্য গালিবের ভিন্নতায় ভেঙে না যেত, তাহলে আমাদের সময়ের উর্দু সাহিত্য অবশ্যই তার বর্তমান রূপ থেকে ভিন্ন হতো।
অতএব, গালিবের উর্দু কবিতার প্রথম যুগের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে, প্রথম থেকেই বলা উচিত যে আমরা আসলে ফার্সি কবিতার একটি বিশেষ রূপ অধ্যয়ন করছি। এই সময়ের অনেক কবিতা আছে যেখানে একটি হিন্দি শব্দ নেই। যেমন:
اسد خسته گرفتار دو عالم اوہام
مشکل آسان کن یک خلق ! تغافل تا چند ؟
আসাদ খাস্তাহ্ গ্রীফতার দো আলম ওহাম
মুসকিল আসান কিউ এক খলক ! তগাফিল তা চন্দ?
অর্থ্যাৎ গালিব বলেছেন যে তিনি এমন দুই মায়াবী জগতকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন
যাকে খুব সহজ করে বলা সম্ভব নয়! কত আর না দেখা করব?
কিন্তু আমরা এও জানি যে গালিবের যেসব কবিতায় কখনও কখনও হিন্দি শব্দও এসেছে।
সেখানে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব উর্দু কবিতায় ফারসি পরম্পরা জড়িয়ে আছে। অর্থ্যাৎ গালিব উর্দু কবিতা রচনা করলেও তার মধ্যে রয়েছে ফারসি অনুভূতি। এটা গালিব কীভাবে সম্ভব করেছিলেন? কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে তাহলে গালিবের কবিতা কি আসলে ফারসি কবিতারই এক ভিন্ন রূপ যা আসলে উর্দু কবিতা ?
আমরা যদি তাঁর এই কবিতাটি দেখি তাহলে বুঝতে পারব :
شمار سحہ مرغوب بت مشکل پسند آیا
تماشائی به یک کف بردن صد دل پسند آیا
শুমার শাহ মরগুব বাত মুসকিল পসন্দ আয়া
তামাশাহী বাহিয়াক কফ বরদন সদ দিল পসন্দ আয়া
এই কবিতাগুলির উপাদান কেবল ফার্সি ভাষা দ্বারা নির্মিত নয়, বরং বলা যায় তার শৈলী যার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে তা মীর এবং তার অনুসারীদের পরিবর্তে ফার্সি কবিদের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত । এই কবিদের মধ্যে বেদিল আজিম আবাদী। গালিব শওকতের থেকে বেদিলের লেখা বেশি পড়তেন বলে আমরা জানি এবং বেদিলের মতো লেখার চেষ্টাও করতেন। আর এর কারণ হিসেবে আমাদের মনে হতে পারে কল্পনার ভিন্নতা। এটা ঠিক যে মীরের চেয়ে গালিব বেদিলের কবিতায় নিজেকে খুঁজে পেতেন। আর এই কারণেই কি বেদিলের আঙ্গিক থেকে বেরিয়ে আসার পরও গালিবের কবিতায় আঙ্গিক পরিবর্তন হয়নি । অর্থাৎ গালিবের প্রথম দিকের কবিতায় যেমন গালিব শব্দ চয়ন অথবা রূপকের ব্যবহার করতেন পরের দিকের কবিতায় সেই একই ধরন ছিল। তাহলে কি বেদিলের সঙ্গে গালিবের সম্পর্ক শুধুমাত্র তাঁদের শব্দ চয়ন? এটা ঠিক যে বেদিলের সঙ্গে গালিবের সম্পর্ক তাঁদের রচনায়, কিন্ত ভিন্নতাও এমনই যে তাঁদের সমগ্র রচনার মধ্যে সেইসব ইঙ্গিত ছড়িয়ে রয়েছে। আবার কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে বেদিলের কিছু দোহা গালিব নিজের বলে চালিয়েছেন। আমরা যদি এইভাবে ভাবতে বাধ্য হই তাহলে চিন্তার বৌদ্ধিক বিস্তার সীমিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। আমরা জানি
বেদিল ও গালিব একই ধারার প্রবাহর উত্তরণ। আমরা যদি দুজনের সমগ্র রচনার দিকে তাকাই তাহলে বুঝতে পারব তাঁদের রাস্তা একটা সময়ের পর আলাদা হয়ে গিয়েছে। এইবার আমরা বলতে পারি যে তিনি যদি বেদিলের লেখা থেকে কিছু গ্রহণ করেছেন সে হবে দর্শনের এক অধ্যায়। আরও একটু তলিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই গালিবের প্রথম দিকের কবিতায় কিছু শব্দ, যেমন জোহর, আরজ, মুতা’আলিয়া-ই বাতিন, পারফিশান, বাল-ই তাবিদান, কাগজ-ই আতিশ জাদা, দামান-ই খেয়াল।
ঘুঁনচা ফির লাগা খিলনে আজ হামনে আপনা দিল
খুন কিয়া হুয়া গুম কিয়া হুয়া পায়া
অর্থ্যাৎ গালিব বলছেন: ফুল এমন ভাবে ফুটেছে যেন আমার হৃদয় গভীর ক্ষতে ভরে উঠেছে। ক্ষত আর রক্ত ঝরুক পরোয়া করো না কেননা আনন্দ এই যে কিছু হারিয়ে যাওয়া তো ফিরে এলো।
গালিব মনে করেন হৃদয় এক বিন্দু রক্ত ছাড়া কিছুই নয়। এই রূপক আমরা পাই তাঁর অগ্রজ বেদিলের কাছেই।
য আহভাল -এ দিল – গম দিদা- এ বেদিল চ ভী পুরসি
কা হস্ত ইন কাতরা – এ চুম ঘুঁনচা মহেরুম অজ চাকিদান হা
অর্থাৎ বেদিলের এই কথার সূত্র হলো : কেন তুমি শইতানের মনের দুঃখ জানার চেষ্টা করছ ? আমার হৃদয় গোলাপের মতো যে কারণে রক্তের মতো ঝরবে না।
এই দ্বিপদী ও তাঁর পরের কবিতার দিকে তাকালে আমাদের অনুমান করতে ইচ্ছে হয় যে গালিব ততদিন পর্যন্ত বেদিলকে অনুসরণ করেছিলেন যেখানে গালিব তাঁর নিজের কবিতাকে ভিন্ন এক পম্পরায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই সহজ কাজটি এত সহজ ছিল না। গালিব নিজেকে বারবার ভাঙবার চেষ্টা করেছেন। কেননা গালিব নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন যে বেদিলের মতো কবিতা লেখা একটা অলৌকিক ব্যাপার। আর এটা ঠিক যে গালিব বেদিলকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারছিলেন না। কিন্তু আমরা হালির কথা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে বুঝতে পারব গালিব ঠিক কোথায় গালিব। হালি মনে করেন গালিব ‘একটি নতুন কিন্তু অনুরূপ’ আঙ্গিকে নিজের লেখার উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা জানি গালিব তাঁর সমগ্র জীবনে কবিতা নিয়ে একরকম অশান্তিতে কাটিয়েছেন। কেননা যখনই তিনি বেদিলের কবিতার কথা চিন্তা করতেন বড় অস্থির হয়ে পড়তেন। জীবনের শেষ দিকে তাঁর শিষ্য কবি হরগোপাল তফতাকে এক চিঠিতে লেখেন ‘ সময় সবসময় আবর্তিত হয়। যা হবার ছিল তাই হচ্ছে। যদি আমি আমার তেমন ক্ষমতা থাকত তো আমি এই বিষয়ে কিছু করতে পারতাম। যদি কিছু বলার থাকত তো বলতে পারতাম। মির্জা আব্দুল কাদির বেদিল খুব সুন্দর বলেছেন :
রাঘবাত – এ জাহ চো ও নফরত – এ আসবাব কুদাম
জিন হাবস – হা ব গুজরানা মাগজুর, মি গুজরাদ
অর্থাৎ তুমি ক্ষমতা আর বৈভব ভালোবাসো
আর তুমি পদ ও ধন অর্জন করেছ।
তুমি এইসব ধরে রাখতে পারো
বা ছেড়েও দিতে পারো –
কিন্ত একদিন সব অতীত হয়ে যাবে।
১৮৫৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর তফতাকে লেখা ওই একই চিঠিতে লিখছেন: আমাকে দেখো, আমি মুক্ত
নই না বন্দী,না অসুস্থ,না সুস্থ, না খুশী, না অখুশী, না মৃত, না জীবিত। কথা বলতেই থাকি তো বলতেই থাকি। মদ সময় সময় পান করি। যখন মৃত্যু আসবে মরে যাব। না ধন্যবাদ দেওয়ার আছে, না কোনও অভিযোগ, আর প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লালসা ! সেটা কী ভাই?
আমরা জানি যে কলকাতায় পৌঁছানোর আগেই গালিব ফারসি ভাষায় এতটাই দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁর সমসাময়িকরা তাঁকে একজন গুরু হিসেবে দেখতে শুরু করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে গালিব
ফারসি ভাষায় ভারতীয় কবিদের সম্পর্কে সামান্য হলেও বলতে পারতেন। যেখানে বেদিলও রয়েছেন।
কারণ তিনি কখনও মনে করতেন না যে তিনি শ্রেষ্ঠ বরং তিনি মনে করতেন তাঁদের থেকে কিছু অংশে কম নন। যদিও বেদিলের প্রতি তাঁর ভিন্ন একটা আকর্ষণ আছে। আর এই আকর্ষণ গালিব নিজের মধ্যে আত্মস্থ করেছেন খুব কম বয়সেই। কিন্তু দুজনের মধ্যে পার্থক্য আছে। বেদিল যেন বিশ্বকে সুফি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন এবং তিনি জীবনের ভিন্নতাকে একটা উত্তরণের উপায় হিসেবে দেখেছেন। অন্যদিকে গালিব তাঁর লেখায় জড়িয়ে আছে আমির আমির উত্তরণ অর্থাৎ গালিব পার্থিব জীবন, তার আনন্দ এবং সম্মানের প্রতি অনুরাগী এবং তাঁর বিশ্বদৃষ্টি মূলত অস্তিত্ববাদী ধারণা থেকে এসেছে। কেউ কেউ মনে করেন তাঁর বলবার ধরণ এমন যে একজন সাধারন পাঠকের কাছে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে। আর এখানেই গালিব তাঁর জাগতিক অস্তিত্ববাদী ধারণা থেকে যেন সরে আসেন। এটা ভাবলে আমরা শুধু ভুলই করব তাই নয় আমরা গালিবের আমিকেও স্পর্শ করতে পারব না।


