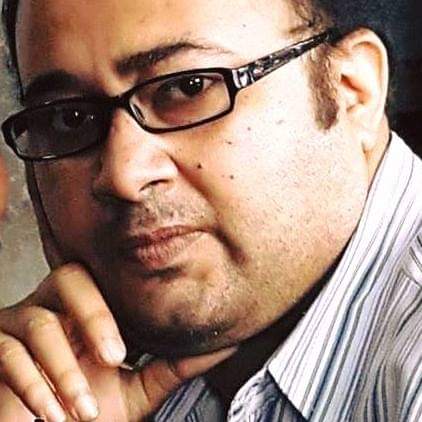
ছিন্ন- বিচ্ছিন্ন
পর্ব -২
সন্দীপন চক্রবর্তী
[এ লেখা কোনো দস্তুরমাফিক প্রবন্ধ নয়। নিজে সামান্য লেখালিখির চেষ্টা করতে গিয়ে, লেখালিখির একেবারে প্রাথমিক যেসব চিন্তার যেসব জালে আটকা পড়ে গেছি, যার পূর্ণ সমাধান আমার নিজের জানা নেই আজও, সেইরকমই কিছু খুচরো প্রশ্নের উত্থাপন শুধু এই লেখায়। তার বেশি কিছু নয়।]
লেখা না-লেখার দ্বন্দ্বে
কোনো লেখকের কি কম লেখা উচিত? নাকি নিয়মিত বেশি করে লেখা উচিত? নানা মুনির নানা মত। একদিকের যুক্তি, বেশি লেখার ফলে, আমরা আমাদের ছোট ছোট ভাস্কর্যের দাবীকে অনেকসময়েই অগ্রাহ্য করে বা উপেক্ষা করে তাকে ছড়িয়ে যেতে দিই তরলতায়, তার মধ্যে তখন গড়ে উঠতে পারে না কোনো দিব্য সংহতি। আবার আরেকদিকের যুক্তি, লোহাকে নিয়মিত ব্যবহার না করে রেখে দিলে তাতে যেমন জং ধরে যায়, তেমনই নিয়মিত লেখার অভ্যেস না রাখলে, নিজের ক্ষমতার অনেকটাই জং পড়ে নষ্ট হয়ে যায়, তার optimum utility হয় না। এবার প্রশ্ন ওঠে, নিয়মিত লেখার অভ্যাস করলে বা বেশি লিখলেও, তার সবটা কি প্রকাশ করা উচিত? কতটা প্রকাশ করা উচিত? প্রকাশের মধ্যে আবার কতটা গ্রন্থভুক্ত করা উচিত? এসব চিন্তা মাঝেমাঝেই মাথার ভিতর কিলবিল করে। অনেকসময়ে অল্প লিখেও সে লেখা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না, আবার বেশি লিখেও সে লেখা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে বইয়ের সংখ্যার হিসেব দিয়ে, বা থেমে যেতে পারার উদাহরণ দিয়ে সাহিত্যের কতটা বিচার সত্যিই করা যায়? এটা একটা প্রবণতা। তবে, হ্যাঁ, জীবনের সব ক্ষেত্রেই সময় বুঝে থেমে যেতে পারা নিঃসন্দেহে এক বিরল গুণ। আরেকটু বাড়িয়ে নিয়ে ভাবছিলাম যে, এই প্রবণতা দিয়ে সাহিত্যমূল্য বিচার করা যায় কিনা সবসময়ে। আসলে, একটা নির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ডে সবসময়ে সাহিত্যমূল্যের বিচার চলে না। স্থান-কাল-পাত্র বলে বাংলায় যে কথাটি আছে, তার ভেদে বোধহয় অনেকসময়ে ওই মানদণ্ডও পাল্টে পাল্টে যায়। তাহলে নিজের ক্ষেত্রে কীভাবে বিচার করবো, সেটা বুঝবো কীভাবে?
আবার এই বেশি লেখা বা কম লেখা নিয়ে আরেকধরণের সমস্যাও আছে। লেখার উৎসে মূলত দুইধরণের প্রবণতা থাকে। কী বলতে হবে আর কী করে বলতে হবে। এই ‘কী বলতে হবে’-র ভাণ্ডার যেসব লেখকের ক্ষেত্রে বিরাট থাকে, তাঁদের ক্ষেত্রে লেখার পরিমাণও বেশি হতে বাধ্য। তাঁর অনেক কথা বলার আছে। তাই তাঁর ক্ষেত্রে ‘কী করে বলতে হবে’-টা বাধ্যতই কোনো কোনো সময়ে গৌণ হয়ে যায়। এর হাতে গরম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। এখানেও অবশ্য প্রশ্ন তোলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথও কি নিজের পুনরাবৃত্তি করেননি? তাঁর লেখাও কি তরলায়িত হয়ে যায়নি কখনো কখনো? অবশ্যই কখনো কখনো সেসব ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও। কিন্তু সব মিলিয়ে, এক সামগ্রিকতার ভিত্তিতে যদি দেখি, তাহলে দেখবো যে, সেগুলো সরিয়ে রেখে দিলেও যা পড়ে থাকে, সেই সৃষ্টিও পরিমাণে কী বিপুল অথচ মানে কী শিখরস্পর্শী! কিন্তু যে লেখকদের ‘কী বলতে হবে’-র ভাণ্ডার খুবই সীমিত, তাদের মূল ঝোঁক পড়ে ‘কী করে বলতে হবে’-র উপর। তাই তাঁদের ঠিকমতো সময়ে না থামলে তরলায়িত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে বোধহয়। এইখানে বোধহয় এসে পড়ে লেখকের ক্ষমতাভেদেরও কথা। কিন্তু এই ভাণ্ডার কার কেমন, সেটা জীবিতকালে তাঁর নিজের পক্ষে বোঝা বা নির্ধারণ করা কতটা সম্ভব?
তারপরেও আরেক সমস্যা আসে। তারও যথাযথ উত্তর আমি জানি না। একজন লেখক তাঁর জীবিত অবস্থায় সম্পাদনা করে নিজের যে যে লেখা গ্রন্থভুক্ত করেন না বা করতে চান না, তাঁর মৃত্যুর পর সেগুলি গ্রন্থভুক্ত করে জনসমক্ষে আনা কতটা উচিত কাজ? তাতে হয়তো – তাঁর হেঁসেলের ভাঁড়ারের খোঁজ পেলে – তাঁর অন্যান্য লেখা বোঝার ক্ষেত্রে একটা সুবিধা হয়। কিন্তু তাঁর যে ইন্টেনশন ছিল, সেটাও তো ব্যাহত হয়। দেশ-বিদেশের অনেক লেখকের ক্ষেত্রেই এটা এক সমাধানহীন সমস্যা। কাফকার বন্ধু তাঁর কথামতো তাঁর সব লেখা নষ্ট করে দিলে, এই কাফকাকে তো আমরা পেতাম না। আবার এভাবে অনেক লেখকের ক্ষেত্রেই যে লেখা তিনি নিজে ভাবতেন যে প্রকাশ করা উচিত না, সে লেখাও এভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়। এটা সামগ্রিকভাবেই সাহিত্যজগতের একটা সমস্যা। এখন, আরেকটা কথাও উঠতে পারে — যে লেখা লেখক প্রকাশ করছেন না বা প্রকাশিত হলেও গ্রন্থভুক্ত করছেন না, তা কি নেহাৎ উদ্যোগের অভাবে করছেন না? নাকি সে লেখার কথা গ্রন্থভুক্তির সময়ে খেয়াল পড়েনি? নাকি তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিতে চাইছেন বলেই অন্তর্ভুক্ত করছেন না? যদি উদ্যোগের অভাবও হয়, তাহলেও কি মনের অগোচরে সেটা আসলে বাদ রাখতে চান বলেই ওই উদ্যোগের অভাব? জানি না। এইখানে আরেকটাও প্রশ্ন ওঠে। লেখকের অভিপ্রায়ই কি তাঁর লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নির্ধারক? নাকি পাঠক বা অনুরাগীদের অভিপ্রায় থেকেই তার নির্ধারণ হওয়া উচিত? সমস্যাটা এইখানে। কোনটার উপর নির্ভর করবো বা কোনটার উপর কতখানি নির্ভর করবো এক্ষেত্রে? সমস্যার গিঁট সেইখান থেকে শুরু হয়।
ফলে, লেখা না-লেখা, লিখলে তার প্রকাশ অপ্রকাশ, প্রকাশিত হলে তার গ্রন্থভুক্তি বা অগ্রন্থিত রাখা, এসবের মধ্যে কি নির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুযায়ী আদৌ কোনো ঔচিত্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব? জানি না। শুধু এইটুকু টের পাই যে, সব মিলিয়ে ভাবতে গেলে, এ এক বিরাট জটিল ডিজাইন। এর তল খুঁজে পাওয়া মুশকিল।
(ক্রমশ)

