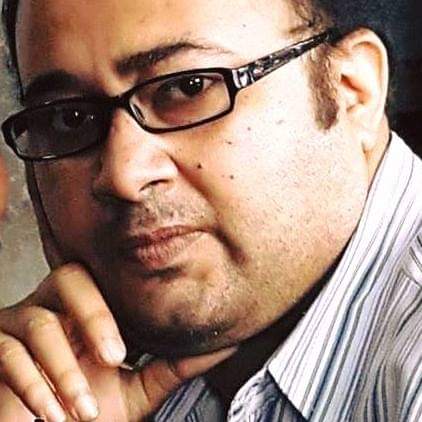
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন
পঞ্চম পর্ব
সন্দীপন চক্রবর্তীর জার্নাল
শ্রীজাতর লেখা উপন্যাস ‘যে-কথা বলোনি আগে’ পড়তে পড়তে এই কথাগুলোই মনে হচ্ছিলো বারবার। আমাদের এই জীবন, এই পরিবার, এই সমাজ, এই সভ্যতা যে কত ভঙ্গুর...যে গোপনতার ফাঁস তাকে অটুট রাখে, সে ফাঁস খুলে গেলেই যে সে কত অসহায়...অথচ এত ভঙ্গুর এত অনিশ্চিত বলেই যে এ জীবন এত সুন্দর...তা আশ্চর্যভাবে জেগে উঠেছে শ্রীজাতর এই উপন্যাসে।
জানি না, হয়তো জীবনানন্দের ভাষা ধার করে, একেই বলা যায় ‘সময়গ্রন্থি’। অথবা হয়তো তাও ঠিক নয়, স্থান আর কাল – এ দুটোরই হরেক বিভিন্নতা মিলে এই গ্রন্থি রচনা করেছে। এক সময়ের পেটের মধ্যে কী সহজ মসৃণভাবে সেঁধিয়ে গেছে আরেক সময়, বা এক স্থানের পেটের মধ্যে আরেক স্থান। খুব সহজেই সেখানে খিষ্টপূর্ব ১৩৯৩ সালের উত্তর চিনের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে পারে এই সময়ের নরওয়ের বর্গেন শহর, অথবা এই সময়ের কলকাতা বা দার্জিলিং। এমনকি সেখানে বাস্তবতার পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে কল্পনা, অনিবার্য নশ্বরতার পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে গোপনতা-মুক্তির বোধ। শ্রীজাতর লেখা উপন্যাস ‘যে-কথা বলোনি আগে’ পড়তে পড়তে এই কথাগুলোই মনে হচ্ছিলো বারবার। আমাদের এই জীবন, এই পরিবার, এই সমাজ, এই সভ্যতা যে কত ভঙ্গুর…যে গোপনতার ফাঁস তাকে অটুট রাখে, সে ফাঁস খুলে গেলেই যে সে কত অসহায়…অথচ এত ভঙ্গুর এত অনিশ্চিত বলেই যে এ জীবন এত সুন্দর…তা আশ্চর্যভাবে জেগে উঠেছে শ্রীজাতর এই উপন্যাসে। আমাদের এই যে নিছক একটা গোল গপ্পো-বলা বা গ্যাদগ্যাদে ভাবালুতায় চপচপ-করা বা শুষ্ক মগজের প্যাঁচ মেরে ভাষার ভাঁজ দেখানো বাংলা গল্প-উপন্যাসের বাজার, তার থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকে এই লেখা। যে সত্যজিতের ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’-র নানা সংলাপ রেফারেন্স হিসাবে উঠে আসে এই উপন্যাসে, সে ছবির মতোই, ঘটনাকে পেরিয়ে এক বোধ, এক গাভীন মন্থরতা ছড়িয়ে থাকে এখানেও। এ যেন সোজাসুজি খাড়াই বেয়ে ওঠা নয়, যেন পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে বেয়ে, ঘুরতে-ঘুরতে, চারপাশকে চিনতে-চিনতে ওঠা। এর ভাষাভঙ্গীর মধ্যে, বর্ণনার মধ্যে রয়ে গেছে এক আশ্চর্য সিনেম্যাটিক কোয়ালিটি। কোনো কোনো মুহূর্ত যেন অনেকটা স্ট্রেচ হয়ে উঠে আসে স্লো-মোশনের মতো, বা আটকে যায় খানিক – ত্রুফোর ফ্রিজ শটের মতো। আর এর ঠিক পাশাপাশিই জেগে থাকা মিডিয়ার ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের পাশেই তাকে যেন আরও বেশি মন্থর লাগে তখন। আবার কেউ হয়তো বলতে পারেন যে এর ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে এত সমাপতন কেন? তা কি একে মেলোড্রামাটিক করে দিচ্ছে না? না। আমার তা মনে হয়নি। আর হলেই বা ক্ষতি কী? মেলোড্রামাও একধরণের ফর্ম অফ আর্ট, যেখানে সামাজিক বা রাষ্ট্রিক পরিসর প্রতিস্থাপিত হয়ে ধরা দেয় ব্যক্তিক বা পারিবারিক পরিসরে। ইচ্ছে করেই সেই ফর্মকে ব্যবহার করতে পারে কোনো শিল্পী। ঋত্বিকের ফিল্মই তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ধরাবাঁধা দৈনন্দিন বাস্তবের ক্রীতদাস নয় শিল্প। শিল্পীর কাজ বাস্তবকে অনুসরণ নয়, বোধের জাগরণ। বাস্তব সেখানে উপলক্ষ্যমাত্র, সেই বোধের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সিঁড়ি মাত্র। কাজেই সেই সিঁড়ি গড়তে গিয়ে যদি কিছু সমাপতন ঘটাতে হয় তো ঘটানোই উচিত একজন শিল্পীর। কারণ তিনি বাস্তবের প্রতি দায়বদ্ধ নন, বোধের উত্তরণের প্রতি দায়বদ্ধ। ফলে, উপন্যাসের শেষদিকে – প্রায় যেন তারকোভস্কির ছবির দৃশ্যের মতোই – কবরখানায় এসে নানা পেশার বিশেষজ্ঞরা সমবেত হয়ে খুলে ফেলেন সব পোশাক, খুলে পড়ে যেন বাস্তবের সব খোলস, আর তার অন্তরালবর্তী সত্য উদ্ঘাটনের সেই মুহূর্তে তাঁরা পড়তে থাকেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা, আর তা পড়তে পড়তেই তাঁরা পরিণত হন পাথরের মূর্তিতে। শ্রীজাতর এ লেখাটা শেষ করে, আমিও অনেকটা ওইরকমই পাথরের মূর্তি হয়ে গেছিলাম। নতুন কোনো উপন্যাস পড়ে এরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হইনি বহুদিন। বিরাট একটা চাঁদ মাথায় নিয়ে এরকম খাদের কিনারে এসে, তুষারপাতের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো জ্যোৎস্নায় ভিজে যেতে যেতে, আমি মৃত্যুর মুখোমুখি জীবনকে রেখে দেখিনি অনেকদিন।

