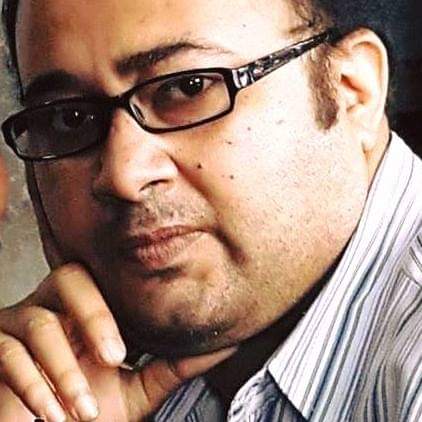
ছিন্ন- বিচ্ছিন্ন
অষ্টম পর্ব
ধারাবাহিক ব্যক্তিগত জার্নাল
সন্দীপন চক্রবর্তী
যে কোনো শিল্পই শেষ বিচারে সাবজেক্টিভ। যেমন ধরুন, ফিল্মের ক্ষেত্রে, আমার অনেক বন্ধুরই প্রিয় গোদারের ছবি। কিন্তু আমার গোদার ভালো লাগে না। আমার অনেক বেশি প্রিয় তারকোভস্কি। কিন্তু সেটা হয়তো অন্য অনেকের আবার বিরক্তিকর লাগে।
এমন কি কখনো হয়নি যে কোনো বিখ্যাত লেখক বা কবির লেখা, যা অনেক বিদগ্ধ ও রসিক মানুষেরও ভালো লাগে, কিন্তু সে লেখা আপনার ভালো লাগছে না? আমার তো অনেকক্ষেত্রেই এরকম হয়। তাহলে কি লেখার এই ভালো বা খারাপ অথবা লেখকের এই ছোট বা বড়র বিচার শেষপর্যন্ত ব্যক্তিসাপেক্ষ নয়? শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে – একাডেমিক আলোচনার ক্ষেত্র বাদ দিলে – কি কোনো অবজেক্টিভ প্যারামিটার ব্যবহার করা সম্ভব? যে হয়তো আপনার কাছে বিরাট বড় কবি, সে হয়তো আমার কাছে তেমন কবিই না…হয় না কি এরকম? ব্যক্তিভেদে তো তাদের বোধের জগৎও আলাদা। ফলে যে লেখা হয়তো আপনার বোধের উন্মেষ ঘটায়, তা হয়তো আমার বোধকে তত নাড়াই দিতে পারে না। যেমন ধরুন, বাংলা সাহিত্যের এক বিখ্যাত কবি বিষ্ণু দে-র কবিতা আমার বোধের কোনো উন্মেষ ঘটায় না। বরং পড়তে গেলেই মনে হয় যে, কবিতা থেকে একজন পণ্ডিত বা ওস্তাদ বেরিয়ে এসে কলার তুলে বলছে — ‘দ্যাখ, কেমন দিলাম!’ আবার আমার খুব প্রিয় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের লেখা। কিন্তু তাঁর লেখা নিয়েও হয়তো অন্য কারো আবার ঠিক এইরকমই মনে হয়। অথচ আমরা দুই পাঠকই অল্প হলেও খানিক তো দীক্ষিত। তাহলে এবার এই দুই কবির মধ্যে ভালো বা খারাপ অথবা ছোট বা বড় — এটা নির্ধারণ হবে কী করে? ফলে অবজেক্টিভ আলোচনা এই ক্ষেত্রে অচল, কারণ যে কোনো শিল্পই শেষ বিচারে সাবজেক্টিভ। যেমন ধরুন, ফিল্মের ক্ষেত্রে, আমার অনেক বন্ধুরই প্রিয় গোদারের ছবি। কিন্তু আমার গোদার ভালো লাগে না। আমার অনেক বেশি প্রিয় তারকোভস্কি। কিন্তু সেটা হয়তো অন্য অনেকের আবার বিরক্তিকর লাগে। ফলে এইসব নিয়ে তাই কথা বলতে গেলেই, আমার খালি মনে পড়ে প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর একটি কবিতা —
‘সমস্ত চলুক।
কাকে যে কবিতা বলে
তা কি আমরা স্পষ্টভাবে জানি?
সবাই যে যার মতো কবিকে সংগ্রহ করে
বাড়ি চলে যাক।
কফি হাউসে, বাচ্চা-কবিরা সব
টেবিল-চেয়ার নেড়ে
নস্যাৎ করুক একে ওকে।
তারপর অন্ধকারে বৃষ্টি নেমে এলে
ভিজে পায়ে হেঁটে যেতে যেতে
আমরা হঠাৎ হয়তো কবিতার দেখা পেয়ে যাব।’
এবং এ লেখাও এসে শেষ হচ্ছে এই সিদ্ধান্তে –
‘সমস্ত চলুক। সব কিছু।
সবাইকে সবার মতো কথা বলতে দাও।।’
ফলে, এ প্রশ্ন থেকেই যায় যে, শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে কোনো নিরপেক্ষতা সত্যিই কি সম্ভব? নিরপেক্ষ সমালোচনার নামে যে ধরণের শিল্পসমালোচনার কথা বলা হয়, সেখানেও কিন্তু শিল্পসমালোচক ভাবেন যে, তিনি হয়তো ব্যক্তিনিরপেক্ষতার খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে কথা বলছেন বা দেখছেন। কিন্তু সত্যিই কি সেটা পারে কোনো মানুষ? নিজের ব্যক্তিসত্তার খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে ভাবা যায় কি সত্যিই? সে হয়তো চেষ্টা করে এবং নিজে ভাবে যে, সে ওই খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে ভাবছে। কিন্তু সেটাও তো একান্তভাবে তারই মনে হওয়া। কিন্তু সত্যিই কি তা পারে কেউ? তবে হ্যাঁ, একেবারে খাজা কোনো লেখা আর পছন্দ না হলেও কোনো বড় লেখকের লেখা — এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যটা অবশ্য বোঝা যায়। যেমন — আমার যেকোনো কবিতার থেকে যে রবীন্দ্রনাথের যে কোনো গানের কথা যে অন্তত এক কোটি গুণ ভালো, সেটা চোখ বুজে নিশ্চিন্তে যে কেউ বলে দিতে পারে। বা নিজের প্রসঙ্গ সরিয়ে রেখে বলা যায় যে, জসীমউদ্দীনের চেয়ে যে রবীন্দ্রনাথ অনেক অনেক বড় কবি, সেটাও যে কোনো দীক্ষিত পাঠকই বুঝবে। এখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, এক্ষেত্রে কেন সাবজেক্টিভ বিচারকে এড়িয়ে যাচ্ছি আমি? আসলে যে কোনো শিল্পের ক্ষেত্রেই একটা স্তর পর্যন্ত স্কিলের মাস্টারশিপ প্রয়োজন হয়। স্কিলের সেই মিনিমাম মাস্টারশিপের অভাব জসীমউদ্দীনে। কিন্তু, স্কিলটাই তো আর শিল্প নয়। সেটা উপায়। লক্ষ্য নয়। ফলে আজকাল মাঝেমাঝেই মনে হয় যে, স্কিলের চূড়ান্ত মাস্টারশিপ হলো সমস্তটা দুর্দান্তভাবে আয়ত্ত করে, তারপর সেটা ভুলে যাওয়া বা ভেঙে ফেলা। কিন্তু সেটা পারে খুব কমজন। সত্যেন দত্ত তাই ছন্দের জাদুকর হয়েই থেকে যান। ছন্দমিলের এই স্কিলের খেলা দেখানোর ধারাবাহিক শিকার রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে অনেক কবিই। তাঁরা অনেকেই অত্যন্ত প্রতিভাবান, কিন্তু এই স্কিলের মোহে অনেকসময়েই তাঁদের লেখায় স্কিলের জাগলিংটাই মুখ্য হয়ে ওঠে আর কবিতার আত্মা চলে যায় পিছনের সারিতে। ফলে তাঁদের নিজেদের পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় স্কিলের প্রতি তাঁদের এই মোহ। এসব বলতে বলতে মনে পড়ছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটা কবিতা —
কে জানে কেমন করে ছন্দের বারান্দা ভাঙা হবে?
মিস্তিরি মজুত, কাছে শাবল গাঁইতি সবই আছে।
লোকবল আছে, আছে ভাঙনের নিশ্চিত নির্দেশ,
ভাঙার ক্ষমতা আছে, প্রয়োজনও আছে।
বারান্দাও জেনে গেছে : সবাই ভাঙনে নয় দড়!
ভাঙারও নিজস্ব এক ছন্দ আছে, রীতি-প্রথা আছে,
এবড়োখেবড়োভাবে ভাঙলে, ভাঙার বিজ্ঞান থুতু দেবে
গায়ে আর লোকে বলবে, একেই তছনছ করা বলে।
অশিক্ষাও বলে কেউ, বলে, মূর্খ, ভাঙা শিখতে হয় —
অপরূপভাবে ভাঙা, গড়ার চেয়েও মূল্যবান
কখনো-সখনো!

