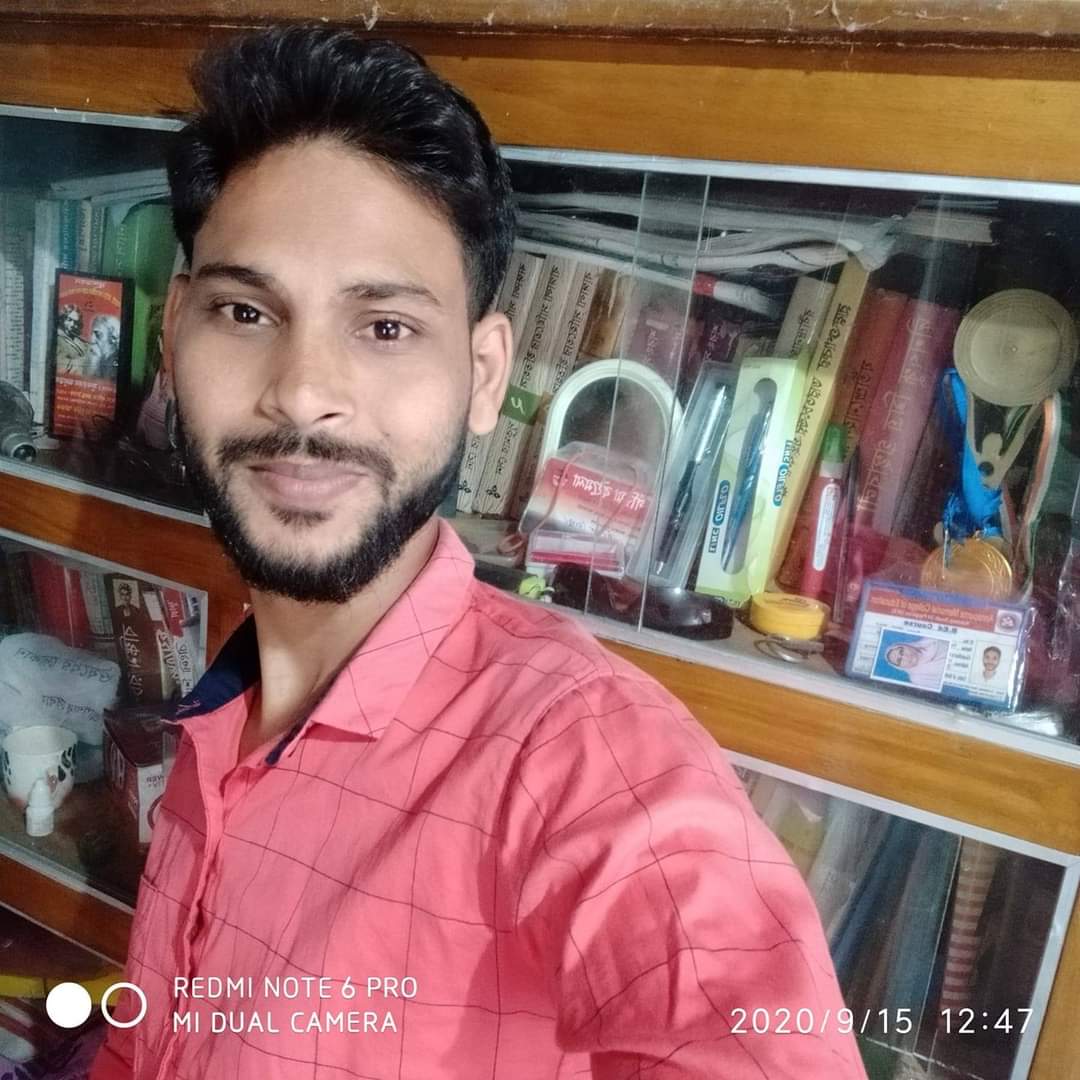
এক আহত কবি আল মাহমুদের মৌলিকতা
ইউসুফ মোল্লা
এক সাক্ষাৎকারে কবি অভিমান করে বলেছিলেন, “আমার কাঁধে বিরাট সংসার। আমার রোজগার দিয়ে ছেলেমেয়েদের বড় করতে হয়েছে। ভালো কোনো চাকরি আমাকে কেউ দেয়নি। প্রচুর শ্রম দিতে হয়েছে। নানা ধরনের গদ্য লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু করতে পারলাম না। বন্ধুদের, কবিদের দেওয়া মানসিক চাপ উপেক্ষা করে সমাজে জায়গা করে নিতে হয়েছে আমাকে। কেউ কোনো স্পেস আমাকে দিতে চায়নি। অনেক ধাক্কা খেয়েছি, মুক্তিযুদ্ধ করেছি, জেলও খেটেছি। আমাকে বলো, একজন কবি আর কী কী করতে পারে? আমাকে স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়নি। এখন কোনো কিছুতেই আমার আর আফসোস নেই।”
“কবিতা তো মক্তবের মেয়ে, চুল খোলা আয়েশা আক্তার।“
—কবিতার বিষয় যে এইভাবে রোজ ঘটে যাওয়া পাড়ার ঘটনা, তা এর আগে কেউ তুলে ধরেননি। তৎসম-তদ্ভবের সাথে লোকজ, বিশেষ করে মুসলিম জবানের অন্তরঙ্গ শব্দরাজির সহাবস্থান ঘটিয়েছেন কবি আল মাহমুদ। একান্ত ঘরোয়া সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা হলেও এর সাহিত্য গুণ আছে। তাইতো পুঁথি সাহিত্যের বিস্মৃত সৌরভ সহজেই শুঁকতে পারা যায় এই শব্দসমূহ থেকে। কিছু শব্দবন্ধ এইরকম— নালৎ, গতর, জবান নাপাক, কবুল, নাদানের রোজগার, কসুর ইত্যাদি। কবির আন্তরিক উচ্চারণের টানেই এই শব্দগুলো উঠে এসেছে বলে মনে হয়। এই মুখের ভাষা আসলে অন্তরের, অকৃত্রিম, এমনকি অসংস্কৃত। শাহীন রেজা একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মক্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আক্তার কীভাবে কবিতা হলেন? তখন তিনি স্মিত হেসে বলেছিলেন, ‘এই যে জীবন, এই যে মহাজাগতিক সবকিছু, এই যে নদী নারী প্রকৃতি, এমনকি এই যে মহান প্রভু- যার ইশারায় আমাদের সৃষ্টি- কবিতার রসদ তো আমরা সঞ্চয় করি এসবেরই মধ্য থেকে। আয়েশা আক্তার তো এ রকমই একটি অনুষঙ্গ, যা অনিবার্যভাবে উঠে আসতে পারে আমাদের কবিতায়; এবং এসেছেও। ছোটোখাটো সুখ-দুঃখ, অনুভব- অনুভূতি, জীবনের মৃদু খুনসুটি, আত্মার অবয়ব— এসব নিয়েই তো আমাদের লেখালেখি। জীবনকে জীবনের চোখ দিয়ে খুঁজতে হয়। আর খুঁজতে খুঁজতে সাধারণ আয়েশা আক্তারও একসময় অসাধারণ ‘কবিতা-চরিত্র’ হয়ে ওঠেন।‘
রবীন্দ্র-বিরোধী তিরিশের কবিরা বাংলা কবিতার মাস্তুল পশ্চিমের দিকে ঘুরিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন; আল মাহমুদ উত্তর-আধুনিক বাংলা কবিতাকে বাংলার ঐতিহ্যে প্রোথিত করেছেন মৌলিক কাব্যভাষার দ্বারা। আর তাই শামসুল রহমান, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখেরা তাঁর সহযাত্রী হলেও এইখানে তিনি ব্যতিক্রমী ও প্রাগ্রসর। নাগরিক চেতন ও চিন্তায় আল মাহমুদ মাটিজ অনুভূতিতে গ্রামীণ শব্দপুঞ্জ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প সংশ্লেষ করে উত্তর-আধুনিক বাংলা কবিতায় নতুন দিগন্ত রেখায়িত করেছেন। আল মাহমুদ গ্রাম বাংলার সৌন্দর্যকে আশ্চর্য শক্তিময় শব্দ বিন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। যা দেখে আমার মনে হয়, একমাত্র জীবনানন্দ দাশ ছাড়া আর কেউ সেই পথের যাত্রী ছিলেন না। তাই বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় বলেছেন, ‘সমকালীন যে দু’জন বাঙালি কবির দুর্দান্ত মৌলিকতা এবং বহমানতা আমাকে বারবার আকৃষ্ট করেছে তাদের মধ্যে একজন হলেন বাংলাদেশের আল মাহমুদ, অন্যজন পশ্চিমবঙ্গের শক্তি চট্টোপাধ্যায়।‘ একটি সাক্ষাৎকারে কবি নিজেই বলেছেন, ‘রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বাংলা ভাষা বহু কবির বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে। তিরিশ, চল্লিশ থেকে শুরু করে সত্তর দশক পর্যন্ত কবিরা যে শব্দরাজি তাদের কাব্যে ব্যবহার করে এসেছেন তা মূলতঃ রবীন্দ্রনাথেরই। জীবনানন্দ দাশ সমস্যাটা উপলব্ধি করে কিছু আঞ্চলিক শব্দে তার কবিতার শরীর নির্মাণ করলেও এ ব্যাপারে তার খুব বেশি কোনো সচেতন প্রয়াস ছিল না। আমি বাংলা একাডেমী প্রকাশিত আঞ্চলিক ভাষার বৃহদাকার দু’খানি অভিধান দেখে প্রথমে অভিভূত হয়েছিলাম। কারণ আঞ্চলিক ভাষা মানেই হলো জীবন্ত ভাষা। আমি ভেবেছিলাম যদি আধুনিক বাংলা ভাষার স্ট্রাকচারের মধ্যে প্রচুর আঞ্চলিক শব্দ উপযুক্ত মর্যাদায় ব্যবহার করা যায় তাতে আমাদের সাহিত্য গতিময় হয়ে উঠবে। আমি ঠকিনি।‘
আর একটি মারাত্মক অভিযোগ আছে আল মাহমুদকে নিয়ে। যদিও সেটার মধ্যে আমি খারাপ কিছু দেখছি না। তিনি নাকি শেষের দিকে ইসলামী ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের আগে বামধারা দেখা গেলেও ১৯৭৪ সালের পর থেকে ইসলামী ভাবধারাও লক্ষ্য করা যায়। কবির নিজের ভাষায় উঠে এসেছে সেই প্রসঙ্গ। এখানে সেটি উল্লেখ করছি—
“আমি এক বছর বিনা বিচারে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক থাকার সময় একখানা পবিত্র কুরআন আমার স্ত্রী আমাকে জেলখানায় দিয়ে এলে আমি তা অর্থসহ আদ্যোপান্ত পাঠ করা শুরু করি। আর প্রথম পাঠেই আমার শরীর কেঁপে ওঠে। এর আগে কোনো গ্রন্থ পাঠে আমার মধ্যে এমন ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়নি। যেন এক অলৌকিক নির্দেশে আমার মস্তক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।“
মূলত এরপরই কবি মার্ক্সবাদী দর্শন ত্যাগ করে ইসলামী জীবনদর্শনে উদ্বুদ্ধ হন । ইতিহাসে বামপন্থা থেকে ডানপন্থায় কনভার্টেড হওয়ার দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। সেই হিসেবে কবির এই প্রত্যাবর্তন অনেকটা অপ্রত্যাশিত এবং অকল্পনীয়ই বটে। দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে যে বামপন্থী চিন্তাচেতনা তিনি আকড়ে ধরে ছিলেন সেটা ত্যাগ করে হয়ে হয়ে গেলেন পুরোদস্তুর ডানপন্থী! তবে তার এই পরিবর্তন দেশের সেক্যুলার সমাজ স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে পারেনি। তারা আল মাহমুদকে বর্জন করতে লাগল। আর সেইসময় বামপন্থীদের বিরাদভাজন হয়ে কোন কবি-সাহিত্যিকই টিকে থাকতে পারেন না। অধিকাংশ সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেল বামপন্থী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার কারনে মিডিয়াতে কবিকে দীর্ঘদিন ধরে ব্ল্যাকলিস্টেড করে রাখা হয়েছে। নতুন প্রজন্ম যাতে তাঁর সম্পর্কে জানতে না পারে সেজন্য পাঠ্যবই থেকেও তাঁর কবিতাও অপসারন করা হয়েছে।
আবার আরও একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন ,
দাড়ি রাখলে আর ধর্মভীরু হলেই যদি মৌলবাদী হয়, তবে অবশ্যই আমি মৌলবাদী। কিন্তু জামায়াত-শিবিরের সভায় যাই বলে আমাকে যদি মৌলবাদী বলা হয়, তাহলে অবশ্যই অন্যায় হবে।
এখানে একটা কথা না বললেই নয়, বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে আল মাহমুদ ছিলেন সাম্যবাদী বামপন্থী দলের সমর্থক। ১৯৭৪ সালে জাসদ সমর্থিত ‘দৈনিক গণকণ্ঠ’-এর সম্পাদক থাকা অবস্থায় রক্ষীবাহিনী এবং বঙ্গবন্ধু সরকারের সমালোচনা করার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারাগার জীবনটা তার জন্য শাপে বর হয়ে দেখা দেয়।
মাত্র ১৮ বছর বয়স ১৯৫৪ সালে সংবাদপত্রে লেখালেখির সূত্র ধরে কবি ঢাকা আসেন। তখন থেকেই তাঁর কবিতা প্রকাশ পেতে থাকে। আজীবন আত্মপ্রত্যয়ী কবি ঢাকায় আসার পর কাব্য সাধনা করে একের পর এক সাফল্য লাভ করতে থাকেন। কবি নিজেই বর্ণনা করেছেন সে অভিজ্ঞতা। দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত ইমরান মাহফুজ’র নেয়া এক সাক্ষাৎকারে গ্রাম থেকে শহরে আসা নিয়ে কবি বলেন- “আমি ঢাকায় এসেছিলাম খদ্দরের পিরহান গায়ে, পরনে খদ্দরের পায়জামা, পায়ে রাবারের স্যান্ডেল, বগলের নিচে গোলাপফুল আঁকা ভাঙা সুটকেস নিয়ে। এসেছিলাম অবশ্যই কবি হতে। আজ অনেক বছর শহরে আছি। আমার সুটকেসের ভেতর আমি নিয়ে এসেছিলাম বাংলাদেশের সবগুলো নদী, পাখি, পতঙ্গ, নৌকা, নর-নারীসহ বহমান আস্ত এক বাংলাদেশ। যেমন, জাদুকররা তাঁদের দ্রষ্টব্য দেখান। আমার ভাঙা সুটকেস থেকে জাতিকে দেখিয়েছি। আমার দ্রষ্টব্য দেখে বাংলার মানুষ কখনো কখনো হাততালি দিয়েছেন, আবার কখনো অশ্রুসিক্ত হয়েছেন। আমি এখনো এই শহরেই আছি। আমি যখন এসেছিলাম তখন আমার বন্ধুদের বগলের নিচে থাকতো সিলেক্টেড পয়েমস জাতীয় ইউরোপের নানা ভাষার নানা কাব্যগ্রন্থ। আমি যেমন আমার ভাঙা সুটকেস থেকে আমার জিনিস বের করে দেখিয়েছি তারাও তাঁদের বগলের নিচের পুঁজি থেকে নানা ভেলকি দেখিয়েছেন। এখনো আমি এই শহরেই আছি। আমার সেসব বন্ধুদের সৌভাগ্য হয়নি। এই মহানগরীতে তাঁদের নাম তরুণরা উচ্চারণ করেন না।”
বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত বিখ্যাত ‘কবিতা’ পত্রিকায় লেখালেখির সুবাদে কলকাতার পাঠক এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত ‘সমকাল’ পত্রিকায় লেখার কারণে ঢাকার পাঠকদের কাছে অতি সুপরিচিত হয়ে ওঠে; ফলে তাঁকে নিয়ে দুই বাংলায় নানা আলোচনার শুরু হয়। ১৯৬৩ সালে ‘লোক-লোকান্তর’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে স্বনামধন্য কবিদের পাশে তাঁর জায়গা হয়ে যায়। তারপর একে একে ‘কালের কলস’, ‘সোনালি কাবিন’, ‘মায়াবী পর্দা দুলে উঠো’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হলে তিনি প্রথম সারির কবি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। এরপর ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর তাঁকে শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সহপরিচালক পদে চাকরি দেন। দীর্ঘদিন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের ফলে পরিচালক পদে উন্নীত হন। পরিচালক হিসাবে ১৯৯৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন।
এই কবি যেন কিছুটা অবহেলিত! কবির প্রাপ্য সম্মানের অনেকটাই হয়তো তিনি পান নি; অন্তত – কবির ধারণা এমনই।
তাঁর প্রবন্ধ সংকলন ‘সাহসের সমাচার’ গ্রন্থে তিনি বারবার এই কথাটাই বলেছেন।
“তোমরা আমাকে বোঝোনি। আমি বলি না বুঝবে না, বুঝবে। তবে তখন আমি আর থাকবো না। তবে এটা মনে রেখো, বাংলা সাহিত্যে যারা কিছু করতে চাও, আমাকে তোমার পাঠ করতেই হবে। এটা আমার আত্মবিশ্বাস।”
এক সাক্ষাৎকারে কবি অভিমান করে বলেছিলেন, “আমার কাঁধে বিরাট সংসার। আমার রোজগার দিয়ে ছেলেমেয়েদের বড় করতে হয়েছে। ভালো কোনো চাকরি আমাকে কেউ দেয়নি। প্রচুর শ্রম দিতে হয়েছে। নানা ধরনের গদ্য লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু করতে পারলাম না। বন্ধুদের, কবিদের দেওয়া মানসিক চাপ উপেক্ষা করে সমাজে জায়গা করে নিতে হয়েছে আমাকে। কেউ কোনো স্পেস আমাকে দিতে চায়নি। অনেক ধাক্কা খেয়েছি, মুক্তিযুদ্ধ করেছি, জেলও খেটেছি। আমাকে বলো, একজন কবি আর কী কী করতে পারে? আমাকে স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়নি। এখন কোনো কিছুতেই আমার আর আফসোস নেই।”
সোনালি কাবিন কাব্যগ্রন্থে কবি বলেছিলেন, ‘পরাজিত হয় না কবিরা’। সত্যিই আল মাহমুদকে পরাজিত করা যাবে না। পাঠকের হৃদয়ে জায়গা পাওয়া কবি অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন। আজ থেকে কয়েক শতাব্দী পরেও বাংলা সাহিত্যের কোনো একজন গবেষক যখন কবিতায় কাদের অবদান আছে, এই বিষয়ে আলোচনা করবেন, তখন একটি নাম তাদের অবশ্যই লিখতে হবে। তিনি মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ মোল্লা। যাকে আমরা কবি আল মাহমুদ হিসেবেই চিনি। তাঁর কবিতা দিয়েই এই আলোচনা শেষ করছি—
পোকায় ধরেছে আজ এ দেশের ললিত বিবেক
মগজ বিকিয়ে দিয়ে পরিতৃপ্ত পন্ডিত সমাজ।
ভদ্রতার আবরণে কতদিন রাখা যায় ঢেকে
যখন আত্মায় কাঁদে কোনো দ্রোহী কবিতার তাজ?
(মাতৃছায়া)
ঋণ স্বীকারঃ
১) আধুনিক কবি আল মাহমুদ— ইমরান মাহফুজ
২) সাক্ষাৎকার আল মাহমুদ— সাজ্জাদ বিপ্লব সম্পাদিত
৩) কবি আল মাহমুদ:স্মৃতিকথা— নির্মলেন্দু গুণ
৪) আল মাহমুদের সোনালি কাবিন— খোন্দকার আশরাফ হোসেন
৫) আল মাহমুদ: জীবনটাই তো একটা গল্প— শাহীন রেজা

