
উলফগ্যাঙ ওয়েরচ-এর একটি কবিতা, এজরা পাউন্ড, ফ্যাসিবাদ এবং আমরা
হিন্দোল ভট্টাচার্য
উলফগ্যাং ওয়েরচ-এর একটি কবিতার শিরোনাম 'এজরা পাউন্ড'। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, ইংরেজি এবং বিশ্বসাহিত্যের এই মহান কবির ইহুদি বিদ্বেষ ও নাজিবাদকে সমর্থনের কথা অপরিচিত নয়। তেমনই, এও অপরিচিত নয়, এজরা পাউন্ডের এই সক্রিয় অবস্থানের জন্যই তিনি ভালবাসা হারিয়েছিলেন ইউরোপ এবং আমেরিকার মানুষ ও কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের। ওয়েরচ-এর এই কবিতাটি মনে পড়িয়ে দেয় পাউন্ডের এই অন্ধকার সত্তাকে। তেমনই, বর্তমানের হিন্দু-ফ্যাসিবাদের চরম হিংস্র হয়ে ওঠার এই সময়ে, মনের মধ্যে প্রশ্ন আসে, আমাদের করণীয় কী? আমরা কি সক্রিয় ভাবে বিরোধিতা করব না তাঁদের, যাঁরা সক্রিয় ভাবেই ফ্যাসিবাদের সমর্থক? ইতিহাসের কাছ থেকে তো এ শিক্ষা পেয়েছি, যে, ফ্যাসিবাদের হিংস্র অন্ধকার টেকে না। টিকতে পারে না। তবে কি চুপ করে থাকাই আমাদের অস্ত্র? না কি প্রতি মুহূর্তে কথা বলে যাওয়া? লেখাটি আবহমানের সম্পাদকীয়ও হতে পারত। কিন্তু, যেহেতু এটি একটি ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ, তাই তা ব্যক্তিগত থাকাই ভাল।

এজরা পাউন্ড
এজরা পাউন্ড
ইতালির একটা শহরের মধ্যে
একটি খাঁচায়, প্রদর্শিত
পায়ের তলায় দুর্গন্ধময় পাথর
তার উপরে কটূ গন্ধের ঘোড়ার চামড়ার কম্বল
ঠান্ডায় জমে, কারণ শীতকাল,
নির্লিপ্তভাবে কাঁপছেন
আমেরিকার সৈন্যরা তাকে টাঙিয়ে রেখেছে
যারা তাঁকে ঘিরে কটূক্তি করছে, থুথু ফেলছে
গরাদের বাইরে থেকে লাথি মারছে
এজরা পাউন্ড,
কেন্নোদের দিকে তাকিয়ে আছেন
বুট, পিস্তল, ইউনিফর্ম-এর কীটেদের দিকে
তাকিয়ে আছেন
আমেরিকান কেন্নো, রাশিয়ান কেঁচো, নাজি কীট,
নাসের কীট
কারণ ছাড়াই যারা কীট, ফলাফল ছাড়াই যারা কেঁচো
দেশ ছাড়া, ঘর ছাড়া, দর্শন ছাড়া, জ্ঞান ছাড়া,
ভুল ছাড়া, ভ্রান্তি ছাড়া, ত্রুটি ছাড়া, ভুলত্রুটি অস্বীকার ছাড়া
এজরা পাউন্ড,
দুর্গন্ধময়, শীতে বরফ হয়ে যাওয়া, কম্পিত
চিন্তিত
নিজেকে ভাগ্যবান মনে করুন
এই কারণে, যে আমি কোনও কবিতা লিখছি না
যদি আমি একটি কবিতা লিখতাম
আর কেউ সেই লেখার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করত
আমি তাকে হত্যা করতাম
কিন্তু আমি কোনও কবিতা লিখছি না
আমি কোনও কবিতা লিখতে পারি না
কারণ আমি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করছি
ভুল ছিলাম কিনা
কেন্নো আর কেঁচোদের ঘেরাটোপের মধ্যে
আমার বিচারের সময়, বন্দি অবস্থায়, আবদ্ধ অবস্থায়
আমি ভুল ছিলাম কিনা
প্রশ্ন করছি নিজেকেই
উলফগ্যাং ওয়েরচ ১৯০৭ সালে জার্মানির কনিগসবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। এই কবিতাটি তাঁর ডাই স্পার নামক কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা, ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত। কবি নিজে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাশিয়ায় বন্দি হন। যুদ্ধবন্দি অবস্থায় কাটান বেশ কিছুদিন। ফিরে আসেন হামবুর্গে যুদ্ধের পরে। একটি প্রকাশনা সংস্থায় চাকরি নেন। ১৯৪৬ থেকে ৭২ পর্যন্ত অজস্র কাব্য এবং গদ্য গ্রন্থের কবি ও লেখক এই কবি রাজনৈতিক ভাবে ছিলেন নৈরাজ্যবাদী। এই কবিতাটি যখন লিখেছিলেন, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যাঁরা জার্মানির এই কুখ্যাত নাজি এবং ফ্যাসিস্ট শক্তিকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের বিচারও হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই, স্বাভাবিক ভাবেই, আসে সেই সময়কার ইউরোপ ও আমেরিকার এক অত্যান্ত শক্তিশালী কবি এজরা পাউন্ডের কথা। অনস্বীকার্য এজরা পাউন্ডের কাব্যব্যক্তিত্ব। অনস্বীকার্য কবিতা ও কাব্যতত্ত্বে তাঁর অবদান। চিত্রকল্প বিষয়ে আধুনিক কবিতায় এজরা পাউন্ডকে এড়িয়ে কিছুই করা যাবে না বলেই সকলের অভিমত। কিন্তু এজরা পাউন্ডের অন্ধকার দিকটি হল তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্টদের সক্রিয় ভাবে সমর্থন করেছিলেন। এজরা পাউন্ডের এই সমর্থন এবং ইহুদী বিদ্বেষ সমগ্র ইউরোপের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদেরই বিস্মিত করেছিল। পাউন্ডের ফ্যাসিস্ট শক্তির সমর্থনে রচিত ক্যান্টো কবিতার দিক থেকে যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন, যতই উচ্চমার্গের কবিতা হোক না কেন, এই কবিতাগুলিকে বিশ্বসাহিত্য ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। কেউ অস্বীকার করতে পারেনি, সেই কবিতাগুলির অসামান্য কাব্যগুণের কথা। কিন্তু কাব্যগুণের বাইরেও তো কিছু থাকে। আর তা কাব্যগুণ যে কাব্যের আধারে রচিত হচ্ছে, যে দর্শনের আধারে রচিত হচ্ছে, তা কতটা সম্মান এবং শ্রদ্ধার যোগ্য। কিছু উন্মাদ হত্যাকারীর সমর্থনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প রচিত হলেও, তা মানব-ইতিহাসে মানুষের হিংস্র নির্মম অন্ধকারযাত্রার প্রতীক হিসেবেই থেকে যাবে। উলফগ্যাং ওয়েরচ যেভাবে এই কবিতায় নিজেকেই প্রশ্ন করছেন, যুদ্ধকে প্রশ্ন করছেন, যেভাবে নিজের বিদ্ধ নিঃস্ব সত্তায় ফ্যাসিস্ট এবং ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরোধী যে সব শক্তি, তাদের মধ্যেকার হিংস্র ফ্যাসিজমকেও প্রশ্ন করছেন, তা থেকে একটি বিষয় প্রমাণিত, উলফগ্যাং ওয়েরচ-ই শুধু না, বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপেও ছড়িয়ে গিয়েছিল এই যুগপৎ প্রতিশোধ, ঘৃণা, হিংসা এবং সংশয়ের আবহ।
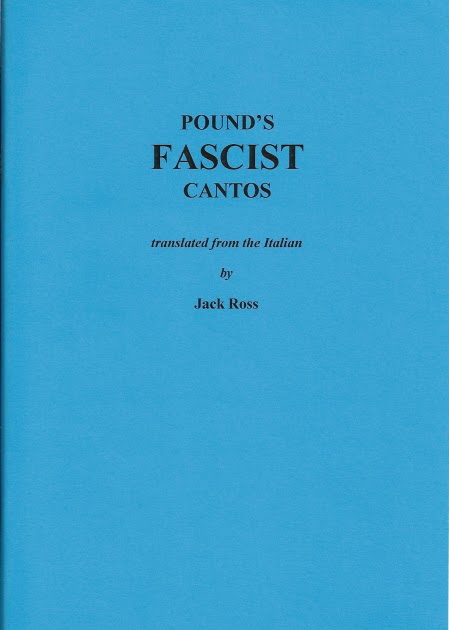
একটা ইউটোপিয়া বলে, কবি কখনও ফ্যাসিবাদী হতে পারেন না। শুধু কবি কেন, কোনও শিল্পী, দার্শনিক, বিজ্ঞানীই ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করতে পারেন না। জাতি ঘিরে, ধর্ম ঘিরে, সম্প্রদায় ঘিরে যে তীব্র হিংস্র অহং এবং মানবাত্মার প্রতি আক্রমণ সেই ফ্যাসিবাদের মধ্যে থাকে, যে, সেই নির্মমতার অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যায় তাঁদের সমস্ত সৃষ্টির আলোই। অবশ্যই প্রশ্ন আসে, হিটলার বা নাজিবাদকে যাঁরা সমর্থন করেছিলেন, তাঁরাই মানবজাতির শত্রু, আর সোভিয়েত বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সোভিয়েত-অধিকৃত কমিউনিস্ট দেশগুলিতে কমিউনিস্টরা যে ফ্যাসিবাদ চালিয়েছিলেন, তার সমর্থকদের আমরা চিহ্নিত করব না কেন? কেন সেই সময়ও কমিউনিজমকে সমর্থনকারী একজন কবি বা লেখককে আমরা বলব না ইউরোপ জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যার দায় যে কমিউনিজমের, তাকে সমর্থন করা এবং তাকে বিরোধিতা না করে চুপ করে বসে থাকাও সমান পাপ? কেন সেই সময়ে বরিস পাস্তেরনাকের উপর যে কমিউনিজমের সন্ত্রাস নেমে এসেছিল, বা রাশিয়ায় আলেকজান্ডার ব্লক, গুমিলেভকে যে রাশিয়ান ফ্যাসিজমের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব না কেন? কেন স্তালিনকে সমান আসনে বসানো হবে না হিটলারের সঙ্গে?
ওয়েরচের এই কবিতায় যে যুদ্ধোন্মাদদের কেঁচো বলা হয়েছে, অর্থাৎ, নাজিবাদের সমর্থক এবং বিরোধী দুই শক্তিকেই কীটের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তা মনে হয় ইউরোপের প্রেক্ষিত থেকে না দেখে বোঝা সম্ভব নয়। আমরা তো জানি, ইউরোপে পূর্ব এবং মধ্য ইউরোপের যে সব দেশে নাজি-শাসন ছিল, সেই সব দেশে সোভিয়েত শাসন শুরু হওয়ার পরে চালু হয়েছিল আরেক ফ্যাসিস্ট শাসন। আর অন্যদিকে আমেরিকার জাপানে ফেলা পরমাণু বোমা আর দীর্ঘদিন ধরে পুঁজিবাদের ক্রমশ ভয়ংকর রূপ ধারণ করাটাও কম ভয়ংকর নয়। গ্লোবালাইজেশন তো একপ্রকার পুঁজির দুর্বৃত্তায়ন, যার প্রভাবে এখনও আমরা ভুগছি। কিন্তু কথা হল, এজরা পাউন্ডের মতো যে সমস্ত কবি ফ্যাসিবাদকে সক্রিয় সমর্থন করেন, তাঁদের প্রতি আমাদের অবস্থান কী হওয়া উচিত?
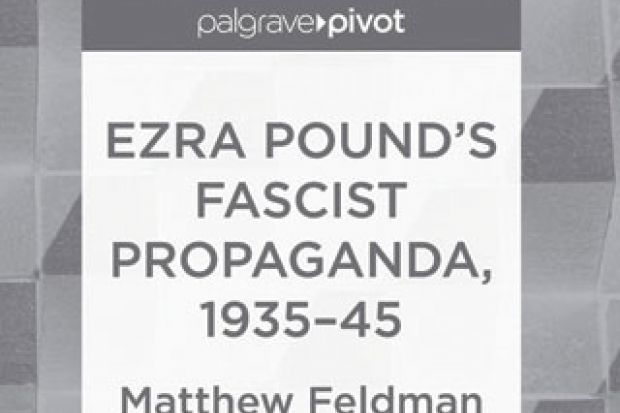
এমনটা নয়, একেবারেই নয়, যে, সেই সব শিল্পীদের বয়কট করা উচিত। বয়কট করা যাবেও না। কারণ তাঁরা ক্রমশ শক্তিশালী হবেন। তাঁদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য নিয়ে তো প্রশ্ন তোলা যাবে না। বরং, আমরা যেন তাঁদের শিল্পীসত্তাকে স্বীকার করি, সম্মান দিই, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা এবং তর্ক যেন বজায় থাকে। আগামী দিনে যদি মানুষ ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করার জন্য তাঁদের প্রতি হিংস্র প্রতিশোধস্পৃহায় ভোগেন, তাহলে, আমরা, যাঁরা বেঁচে থাকলেও থাকতে পারি, আমাদের দায়িত্ব পড়ে তাঁদের বাঁচানোর। কারণ, তাঁরা তাঁদের বিশ্বাস এবং মতবাদকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এই গণতান্ত্রিকতা তাঁদের মধ্যে আমরা আশা করতে পারব না। আশা করা উচিত নয়। এ কথাও আমাদের মেনে নেওয়া প্রয়োজন।
এজরা পাউন্ডকে সাহিত্যের ইতিহাস মনে রেখেছে তাঁর কাব্যপ্রতিভার কারণে। তাঁর মতাদর্শের কারণে নয়। এখানেও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনোকিছুই শিল্পের বেঁচে থাকার পথে অন্তরায় হতে পারে না, যদি সেই শিল্প প্রকৃত শিল্প হয়। কিন্তু পাউন্ডের ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করা ক্যান্টোগুলি কি প্রকৃত শিল্প? শিল্পনৈপুণ্য এবং শিল্প কি এক বিষয়? ক্যান্টোগুলির মধ্যে অভূতপূর্ব সব জায়গা রয়েছে যেগুলি পাউন্ডের পক্ষেই লেখা সম্ভব। কিন্তু যেভাবে নেরুদার কবিতা বা বোদল্যের-এর কবিতা বা মিশো বা হোলুব বা পাররার কবিতা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, পাউন্ডের ক্যান্টোগুলি ততটা নয়। একমাত্র কবিতার মনোযোগী ছাত্রই বারবার ক্যান্টোগুলি পড়বেন, চর্চা করবেন। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত কথাগুলি আমাদের আলোচনার বিষয় হবে না। ক্যান্টোগুলি রাজনৈতিক কবিতা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই রাজনীতি যে মানুষকে নিধনের রাজনীতি, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। সুতরাং, যত নিপুণ শিল্পই তা হোক, পাউন্ডকে ক্যান্টোগুলির জন্য শ্রদ্ধা করা যাবে না। যে শিল্প শ্রদ্ধেয় নয়, তা, বয়নে যতই নবম আশ্চর্যের বিষয় হোক না কেন, আসলে, তা শিল্প নয়। এ যেন ঈশ্বরের হাতে সৃষ্টি সেই গরল, যা পান করে নীলকণ্ঠ হতে হবে কোনও মহাদেবকেই।
কথা হল, আমরা কী করব! বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের যে নাজি-ফ্যাসিবাদ, আজ তো আমাদের দেশেও নাম বদলে গেছে তার। একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিন্দু-ফ্যাসিবাদ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। মনকেও দখল করে নিচ্ছে। আজ বা কাল হয়তো দেখব আমাদের এই বাংলা ভাষার কবি-শিল্পী-ভাবুকরাও সেই নৃশংস হিন্দু-ফ্যাসিবাদের সমর্থক। তখন আমাদের কী ভূমিকা নেওয়া উচিত? এজরা পাউন্ডের মতো কোনও বড় কবি নাজিবাদকে যেভাবে সক্রিয় ভাবে সমর্থন করেছিলেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত যুক্তি দিয়েই করেছিলেন। সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতায় তো হস্তক্ষেপ করা যায় না। আবার তাঁর ব্যক্তিগত অভিমতের জন্য তাঁকে আক্রমণ করাটাও তো হয়ে যাবে ফ্যাসিস্ট-সুলভই। তাহলে আমাদের কী করা দরকার? আমরা তো জানি, মানবাত্মার বিরোধী এই হিন্দু-ফ্যাসিবাদও একটা সময় ভেঙে পড়ে যাবে। তা নাজিবাদের মতোই টিকবে না। মানুষ তাকে ঘৃণাভরে দাঁড় করাবে শাস্তির কাঠগড়ায়। ততদিনে হয়তো প্রাণ হারাবে অনেক মানুষ। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও ফ্যাসিবাদ টিকে থাকেনি।
বরং, সক্রিয় ভাবে কোনও এজরা পাউন্ড যদি ঠান্ডা মাথাতেই হিন্দু-ফ্যাসিবাদের সমর্থক হন, আমরা আমাদের অবস্থানে আরও অটল থাকব। আর বলব, শিল্পের নৈপুণ্য দিয়ে শিল্পের অন্তর্বস্তু যদি সেই হিন্দু-ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করে, তার বিরোধিতা করব। কিন্তু সেই বিরোধিতাকে আরেক ফ্যাসিবাদের আওতায় পড়তে দেব না।
জার্মানির সাত-এর দশকের আরেক কবি অ্যাডালফ এন্ডলারের একটি কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে–
ভয়
আমরা হিংসাকে ভয় পাই
কারণ
আমাদের মধ্যে
আমরা ভয় পাই
তার অস্ত্র
সে, গোপন অসুখের মতো থাকে
গ্রন্থসূত্র– 1) German Modern Poetry, Penguin, Third edition
2) German Poetry (1910-1975) An anthology in German & English Edt- Michael Hamburger
অনুবাদ- লেখক



লেখাটা পড়লাম। লেখাটা এই সময়ের ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য।
অসামান্য লেখা । এ প্রসঙ্গে রিলকের শেষ জীবনে নাজিদের সমর্থন ও দালির প্রিয় বন্ধু লোরকা সম্বন্ধে নীরবতা আমাদের ভাবনাজগতের এক একটি বিস্ময় ।কিংবা ধরুন যে শক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একটি মন্বন্তর তৈরি করে কয়েক লাখ মানুষ মেরে ফেলল , আর এক বাঙালি এন সি মজুমদার তাঁর সাম্রাজ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে একখানা বইই উৎসর্গ করে ফেললেন … হ্যাঁ হিংসা নয় ,ডিসকোর্স এবং তা পক্ষপাতহীন —-বড়োই দরকার । কারণ হিন্দু ফ্যাসিবাদী এই শক্তি যদি ঘটিয়েছে গুজরাট দাঙ্গা , তাহলে তাদের উল্টোপিঠে কংগ্রেসও শিখ জাতিদাঙ্গা তৈরি করেছিল । যা কোনও অংশে কম বীভৎস নয়। যে প্রসঙ্গে ভারতরত্ন রাজীব গান্ধী র সেই অমর বচন মনে পড়ে — যখন কোনও বড়ো গাছ পড়ে যায় ,তখন চারপাশের মাটি কেঁপে ওঠে!!
এর থেকে বেরোনোর একমাত্র উপায় হয়ত আলোচনা আর ‘বেঁধে বেঁধে থাকা’ । কারণ ভাবনার মধ্যেও হয়ত পাওয়া যাবে এক একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প অথবা গুলাগ । সঠিক ডিসকোর্সই প্রকৃত প্রস্তাবে ডিক্লাস করতে পারে আমাদের । এগিয়ে দিতে একটা পক্ষপাতহীন মনের দিকে ।
চমৎকার অনুবাদ।
বড়ো কবি সবসময়ই বড়ো থাকবেন এমনটা যুক্তি বলেনা। এজরা পাউন্ড এক সময়ের আলোড়ন ফেলা কবি। কিন্তু যে কবি মানুষের তথা নিজের হৃদয়, মন, সত্তা, বিশ্বাস ছুঁতে চান তিনি কি করে এগুলোকে হত্যার কাজে নিমগ্ন একটি মতাদর্শকে সমর্থন করেন – এটা সহজ ব্যাখ্যায় আসেনা। এবং একে ব্যক্তিগত বলেও থেমে থাকা যায়না। কারণ আমরা তাঁর আগের সৃষ্টিগুলোকে সমষ্টিগত করেছি।
বিজ্ঞানীরা মূলত নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান থেকে তাঁদের অভীষ্টের দিকে এগোন। এজন্য তাঁরা যেকোন “বাদ”-কে সমর্থন করলে অবাক হবার কিছু নেই।
খুব প্রাসঙ্গিক আলোচনা। ঋদ্ধ হলাম
এই লেখাটি পড়ে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মনে পড়ে গেল। আমার অন্যতম প্রিয় কবি আল মাহমুদ। তাঁর সোনালি কাবিন আমার এখনো মুখস্ত। যাই হোক তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন আগে আমি বাংলাদেশে যাই এবং আমার প্রয়াস ছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করবার। কিন্তু আমার বেশ কিছু কবিবন্ধু যারা সেখ হাসিনাকে সমর্থন করেন, তাঁরা আমাকে নিরস্ত করার যথেষ্ট চেষ্টা করেন, যার একমাত্র কারণ তিনি ছিলেন জামাতিদের সমর্থক, এবং সেই সময়ের কয়েকদিন পরেই ছিল ইলেকশন। যাই হোক শেষে আমি ও অরণ্যা মগবাজারে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিলাম। তাঁর রাজনৈতিক মতকে আমি সমর্থন করিনা। কিন্তু আজও সোনালি কাবিন আমার অন্যতম প্রিয় বই।
অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়। যথাযথ আলোচনা। স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। খুব ভালো লেখা।
খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধ পড়লাম । সমৃদ্ধ হলাম ।
খুব ভালো এবং সময়োপযোগী আলোচনা। এজরা পাউন্ড বা জার্মান কবিতা সম্পর্কে আমার একেবারেই ধারণা ছিল না। লেখককে অনেক ধন্যবাদ।।
যথার্থ এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা। ভালো লাগল।
ভালো লাগল ঝরঝরে অনুবাদ
তুখোড় এবং প্রয়োজনীয় লেখা। অনুবাদও অসাধারণ