
অজিত সিং বনাম অজিত সিং
সপ্তবিংশতিতম পর্ব
তৃষ্ণা বসাক
অজিত সিং বনাম অজিত সিং দ্বাবিংশতি পর্ব তৃষ্ণা বসাক অজিত সিং প্রথমে ছিল বঙ্গলক্ষ্মী চানাচুর, তারপর এল আজাদ হিন্দ চানাচুর, তারপর একের পর এক বিপ্লব চানাচুর, সর্বহারা চানাচুর, উন্নততর সর্বহারা চানাচুর, এখন চলছে বিশ্ববাংলা। এখানেই কি ভাবছেন গল্প ফুরিয়ে গেল? এবার আসছে একে ফিফটি সিক্স চানাচুর। নাম যাই হোক, সোল এজেন্ট আমি।’ ‘বেওয়ারিশ’ গল্পের চানাচুরওলা এবার ঢুকে পড়েছে বাংলার শিল্পক্ষেত্র থেকে শিক্ষাজগতের ক্ষমতার অলিন্দে।খুন, যৌনতা, প্রতিশোধ, নিয়তিবাদের রুদ্ধশ্বাস সুড়ঙ্গে সে টের পাচ্ছে- -বহুদিন লাশের ওপর বসে বারবার হিক্কা তুলেছি আমরা -বহুদিন মর্গের ভেতরে শুয়ে চাঁদের মুখাগ্নি করেছি আমরা -অন্ধ মেয়ের মউচাক থেকে স্বপ্নগুলো উড়ে চলে গেছে (জহর সেনমজুমদার) এই সবের মধ্যে বাংলার কি কোন মুখ আছে আদৌ? থাকলে কি একটাই মুখ? না অনেক মুখ, সময়ের বিচিত্র রঙে চোবানো? বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে বাংলার অজস্র মুখের ভাঙ্গাচোরা টুকরো খুঁজে চললেন তৃষ্ণা বসাক, তাঁর নতুন উপন্যাস ‘অজিত সিং বনাম অজিত সিং’-এ । সব কথনই রাজনৈতিক, সেই আপ্তবাক্য মেনে একে কি বলা যাবে রাজনৈতিক থ্রিলার? সিটবেল্ট বাঁধুন হে পাঠক, ঝাঁকুনি লাগতে পারে। প্রকাশিত হল উপন্যাসের ২৭ তম পর্ব। এই উপন্যাসের সব চরিত্র কাল্পনিক।
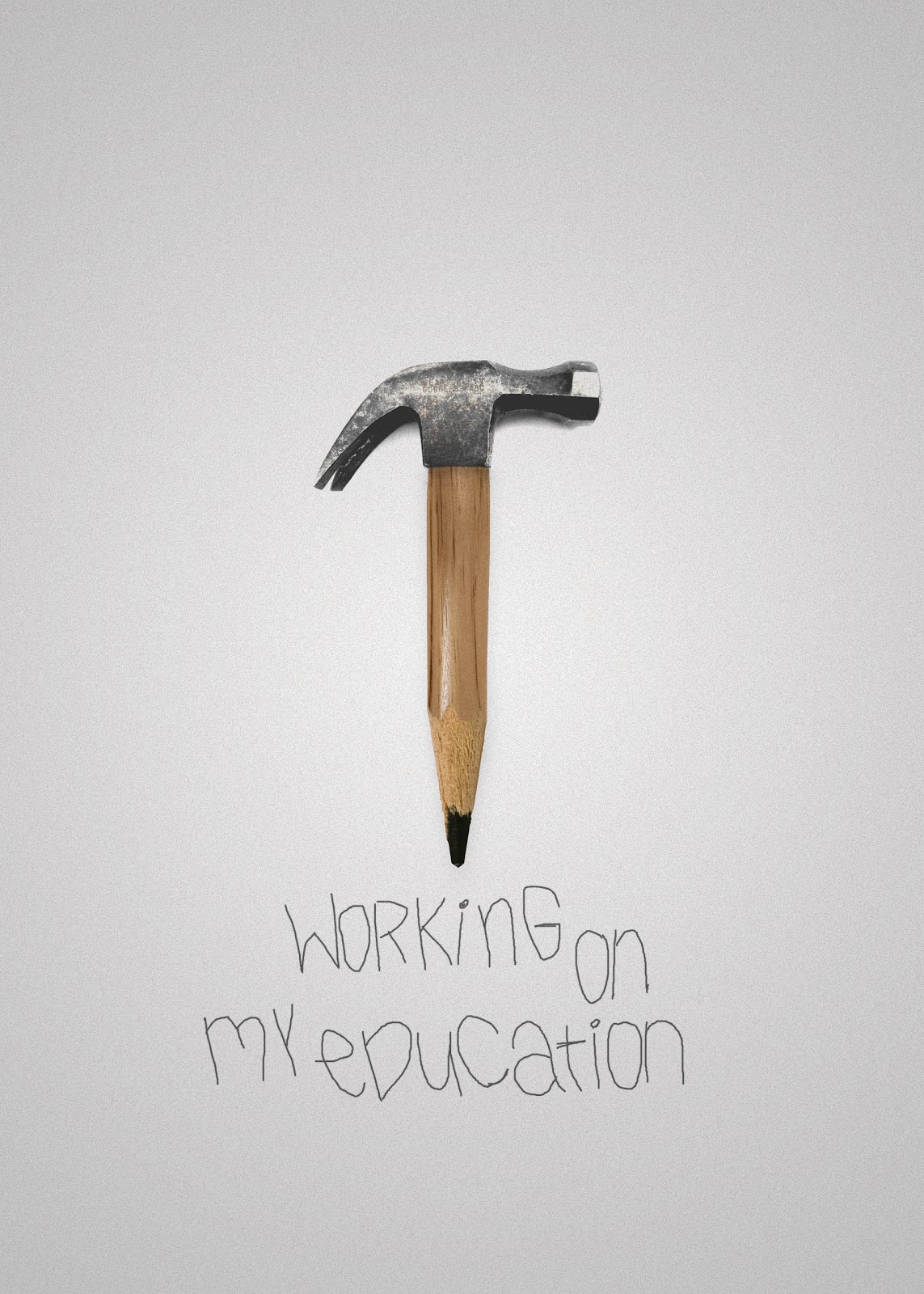
২৭
অমরনাথ বসু ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে দেখলেন কে যেন এসেছে নিচে, বাগানে ঘুরছে। অমনি তাঁর মনে হল আজ কী বার? রবিবার তো নয় আজ। রবিবার করে হাঁসার আসার দিন। হাঁসা তাঁর মালীর নাম। ঠিক নাম নয়। প্রচণ্ড চড়া ফর্সা বলে ওকে হাঁসা বলে ডাকত গ্রামের সবাই। সেটাই চলে আসছে। ওর আসল নাম যুধিষ্ঠির বেরা। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে অষ্টপাড়া গ্রামে বাড়ি, ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে এদিকে চলে আসে, বাবা বাগানের কাজ করত, ছেলে সঙ্গে সঙ্গে থাকত,ঘাস পাতা উপড়ে নিত ছোট ছোট হাত দিয়ে, শুখনো পাতা ঝেড়ে ফেলত, মাটি ঝুরো ঝুরো করত বসে বসে। জল বয়ে নিয়ে আসত বালতি করে। তারপর কী ভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়, আসলে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। তাঁকে মা বলে ডাকে যুধিষ্ঠির, আর তাঁর দেওয়া বাসি রুটি চায়ে ডুবিয়ে খেতে খেতে আবদার করে বাবুর তো অনেক চেনাশোনা, তাঁকে বলে একটা চাকরি করে দিতে। সেই কথা তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলতে থাকে সুযোগ পেলেই। সুপর্ণা এমনিতে ঘরের কোন ব্যাপারেই তাঁর সাহায্য চায়নি কখনো। বুদ্ধিমতী তো, বুঝত, চেয়েও লাভ নেই। এইসব ছোটখাট ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সময় অমরনাথের ছিল নাকি? এসব তো মেয়েদের কাজ, মেয়েরাই ভালো বোঝে, এই নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করলে সংসারে অশান্তিই বাড়বে। সংসার চালানোর ব্যাপারে তাঁর অপদার্থতা নিয়ে কথা শোনালেও এইসব বিষয়ে তাঁর যে এলেম আছে, তা স্বীকার করেন সুপর্ণা, আর এই জন্যেই সব সাংসারিক অকর্তব্য ক্ষমা ঘেন্না করে দেন বরাবর। চেয়ারে থাকতে থাকতেই ক্লাস ফোর স্টাফ হিসেবে হাঁসাকে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন তিনি। একটা জীবন গড়ে দিয়েছেন, ভাবলে একটু মনের মধ্যে শ্লাঘা বোধ হয় বৈকি। সুভাষগ্রাম স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে ছোট্ট একটা বাড়িও করেছে হাঁসা। এখন আর জায়গাটাকে গ্রাম বলা যায় না, শহরের পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেছে, বরং শহরের সুবিধের সঙ্গে গ্রামের খোলামেলা পরিবেশ পাওয়া যাচ্ছে, সেটা একটা বাড়তি লাভ। সেখানে বৌ ছেলে নিয়ে থাকে হাঁসা । ওর বাপ মা কবেই মরে গেছে।
সারা সপ্তা অফিস করে হাঁসা, সময় হয় না, তাই রবিবার করে আসে তাঁর বাগানের দেখভাল করতে। তাঁর স্ত্রী এবং তিনিও বারণ করেছেন বহুবার, প্রতি রবিবার আসার দরকার নেই, এখন বৌ ছেলে হয়েছে, ওদের সঙ্গে ছুটির দিন কাটাতে হয় তো, ওদেরও তো আবদার থাকে কিছু। তাই প্রতি রবিবার আসার দরকার নেই, মাসে একদিন দুদিন এলেই চলবে। তাঁদের আবাসনে দুজন মালীর কাজ করে, তাদের ডেকে নেবেন দরকার হলে। কিন্তু হাঁসা সেসব কোন কথাই শুনবে না। সে খুব ভোরবেলা এসে হাজির হয় প্রতি রবিবার, তার জন্য সুপর্ণাকে উঠে গেট খুলে দিতে হয়। সুপর্ণার কষ্ট হয় নিশ্চয়, কখনোই তাঁদের কারোই ভোরে ওঠার অভ্যেস নেই, তারপর অনেক রাতে মেয়ে স্কাইপে কথা বলে অনেকক্ষণ, ওদের তখন সকাল, তাই আটটার আগে ওঠে না সুপর্ণা, মর্নিং ওয়াক করা হয় না, তার বদলে ইভনিং ওয়াক করেন আজকাল। মাথায় ঢুকেছে একটু হাঁটা দরকার, বয়স হচ্ছে। তাই সকালটা একটু দেরিতেই শুরু হয় তাঁদের। যদিও দুজনেই রিটায়ার করেছেন, রবিবার বলে আলাদা কিছু নেই, রোজই রবিবার, কিন্তু নাতনির কল্যাণে রবিবারের আমেজ আবার পাচ্ছেন নতুন করে।ওর স্কুলে শনিবার রবিবার ছুটি, এই দুটো দিন তাই ভোরে উঠে স্কুলবাস ধরানোর তাড়া নেই, শনিবার তাও গান আর সাঁতারে নিয়ে যেতে হয়, রবিবার ওসব কিছু নেই, ইচ্ছে করেই রাখা হয়নি, যাতে একটা দিন অন্তত রুটিনের বাইরে মাথাটা ছুটি পায়। কিন্তু হাঁসার জন্যে রবিবার খুব ভোরেই উঠে পড়তে হয়। পাঁচটা, সোয়া পাঁচটাতেই সে হাজির হয় আর চা জলখাবার খেয়ে আটটার মধ্যে বেরিয়ে যায়। তার যত্নে বাগানটা ঝলমলে থাকে। সুপর্ণার একটু পরিশ্রম যায় অবশ্য। একে তো খুব ভোরে উঠতে হয় বেচারিকে, আর শুতে পারেন না, হাঁসার সঙ্গে লেগে থাকেন সমানে। তারপর অত সকালে রান্নার লোক আসে না, তাই হাঁসার টিফিনটা তাঁকেই করে দিতে হয়। আগের মতো বাসি রুটি আর চা দেওয়া যায় না, হাঁসা এখন সরকারি চাকুরে, একই বিশ্ববিদ্যালয়ে, সহকর্মীই বলা যায় তাকে, যদিও তাকে খাবারটা এখনো ডাইনিং টেবিলে দেওয়া হয় না, একটা মোড়ায় বসে হাতে নিয়ে সে খেয়ে নেয়, কখনো মেঝেতেই বসে পড়ে। তবে তাকে এখন টাটকা কিছু করে দিতে হয়। হাঁসা আবার পাঁউরুটি খায় না, কী যে করে দেন তাকে? সে সমস্যার সমাধান অবশ্য হাঁসাই করে দিয়েছে। বলেছে ‘মা আমার জন্যে আগের রাতে ভাতে একটু জল দিয়ে রেখে দেবে, একটা শুখনো লঙ্কা পোড়া করে দিলে পেঁয়াজ দিয়ে তাই খেয়ে নেব।’ কিন্তু তাই কখনো দেওয়া যায়? তার ওপর রাতে তাঁরা সবাই রুটি খান, ভাতে জল দিয়ে রাখা মানে দুপুরে হওয়া ভাতে জল দিতে হয়। সবদিন মনে করে বেশি ভাত নেওয়া হয় না, নেওয়া হলেও তাতে জল দেওয়ার কথা মনে থাকে না। রুটি করতে গেলে অন্তত আট দশ খানা রুটি করতে হয়, হাঁসার তার কমে পেট ভরে না, সে তাঁর পক্ষে একেবারে অসম্ভব।তাই একটা উপায় করেছেন সুপর্ণা। তিনি একেবারে ভাত করে দেন গরম গরম, আগের রাতের ডাল, মাছ, মাংস দিয়ে গরম গরম ভাত তৃপ্তি করে খেয়ে বাড়ি চলে যায় হাঁসা, সুপর্ণাও শান্তি পান। কিন্তু আজ রবিবার নয়, সকালও নয়। সন্ধে হয়েছে সবে। এখন হাঁসা আসবে কোত্থেকে? তাছাড়া বাগানে যাকে দেখলেন বলে মনে হল, সে তো একটা মেয়ে।
অমরনাথ চিৎকার করে উঠলেন। ‘কে?কে?’ কই, কেউ নেই তো।ভালো করে দেখলেন আবার। না নেই, কেউ নেই। তবু নিচে নেমে এলেন।কোথাও কেউ নেই, শুধু একটা বেড়াল পাঁচিলে শুয়ে ঝিমোচ্ছিল।তাঁকে দেখে ভারি বিরক্ত হয়ে পাঁচিল থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে গেল। রাস্তার ওপারেই দিঘি। একপাশে বড় স্কুল, বাকি তিনপাশ খোলা, মাঝে মাঝে বেঞ্চ পাতা আছে, ইচ্ছে করলে বসে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত উপভোগ করা যায়।কিন্তু করবে কে? এই আবাসনের তো সবাই ছুটছে। মর্নিং বা ইভনিং ওয়াক করে অবশ্য দু একজন বৃদ্ধ বৃদ্ধা ওখানে বসেন, এছাড়া যারা বসে, তারা সবাই মিস্ত্রি মজুর ক্লাসের, এই আবাসনে বা আশেপাশে নতুন বাড়ি উঠছে তো উঠছেই, তারা সারাদিনের কাজ সেরে গা হাত পা ধুয়ে এইসব বেঞ্চে বসে গজল্লা করে, এছাড়া আছে কাজের মাসিরা, যারা এক বাড়ির কাজ সেরে অন্য বাড়ির কাজে যাবার মাঝের সময়টুকু এখানে বসে একটু জিরিয়ে নেয়, কখনো কয়েকজন জুটলে জমে ওঠে আড্ডা, ভালো বাড়ির কাজের সন্ধানও এখানে মেলে। রীতিমতো শপ টক।
বেড়ালটা নেমে কোথায় গেল দেখতে পেলেন না অমরনাথ। তিনি গেটের কাছে এসে দাঁড়ালেন একটু। নিচের ঘরে নাতনী গান গাইছে, ওর দিদা পাশে বসে কাগজ বা বই পড়ে এসময়। এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করে না সে নাতনীকে। বলেইছে, ওকে কেরিয়ারে জুতে দিয়ে তবে ছুটি। তবে অমরনাথ জানেন, সুপর্ণা সেইধরনের মহিলা, যাঁরা কোনদিন ছুটি নিতে পারবেন না। যদি বেঁচে থাকেন, তবে দেখা যাবে হয়তো নাতনির সন্তান মানুষ করছেন, আর সে নিশ্চিন্তে কেরিয়ার করছে। এইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সুপর্ণার সুরক্ষা চক্র সবাইকে ঘিরে থাকবে। ভালই তো। সুপর্ণা ছিল বলেই তো তিনিও নিশ্চিন্তে কাজ করে যেতে পারলেন।
তাঁর নাতনী গাইছে ‘সারাজীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ’ । গান তিনি তেমন বোঝেন না, তবে গলা তেমন সুরে বলছে না সেটা বুঝতে পারছেন। সুপর্ণা বলছিল, ভোকালে তেমন সম্ভাবনা নেই, দু এক বছর পরে ওকে পিয়ানোয় দিয়ে দেবেন, বিদেশে পড়তে গেলে এগুলো সাইডে থাকলে ভালো। পিয়ানো, চেলো বা ভায়োলিন। বিদেশি বন্ধুদের সঙ্গে জেল করতে সুবিধে হয়। মেয়ে ওকে রেখে তিন বছরের জন্য লিয়েন নিয়ে বাইরে গেছে, পোস্ট ডক শেষ করতে। তাঁদের এইটুকু সাপোর্ট ছাড়া মেয়েটা কাজটা শেষ করতে পারবে না।
প্রথম থেকেই তো এই চলছে। তাঁর স্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন, ‘সারাজীবন কলেজ আর পার্টির কাজ নিয়ে পড়ে থেকেছ, বাজারের থলিটা কেমন দেখতে, রান্নার লোক না এলে কী খাওয়া হবে, মেয়ের স্কুলের পেরেন্টস টিচার মিটিং- কোনটাই করতে হয়নি। মেয়ের হায়ার স্টাডিজ অব্দি আমি টেনে দিলাম, এবার কেরিয়ার, চাকরি, পি এইচ ডি- এইসব তোমার দায়িত্ব। এইটুকু যদি করতে না পারো, তবে এত বছর সংসার ফাঁকি দিয়ে কী করলে?’
বাড়িতে সরস্বতী আর লক্ষ্মী পুজো হয় তাঁদের। বাইরে বলে থাকেন স্ত্রীর পুজো, সেখানে অবিশ্যি পুজোর বাজার তাঁকে করতে হয় না, প্রসাদ খান যদিও, দীপান্বিতা লক্ষ্মী পুজোর ভোগের খিচুড়ি, পাঁচ ভাজা, লুচি পায়েস, কিংবা সরস্বতী পুজোর পরের দিনের শীতল ষষ্ঠীর গোটা সেদ্ধ –সে তো অমৃত।
মেয়ের কেরিয়ারটাও স্ত্রীর পুজোর মতো, তবে এখানে বাজার থেকে মন্ত্রপাঠ, ফল কাটা থেকে ভোগ রাঁধা সব তিনি একাই করেছেন। তিনি ছাড়া আর কেই বা এত জানবে? কখন ভ্যাকেন্সি হচ্ছে, কবে কাগজে বিজ্ঞাপন যাবে, প্রার্থী তালিকা থেকে সম্ভাব্য থ্রেট যারা, তাদের কীভাবে বাদ দিতে হবে, কীভাবে এক্সপার্টস লিস্ট তৈরি করতে হবে, এ সব তিনি করছেন সুচারু দক্ষতায়, যে দক্ষতায় জলের তলায় কুমীর চুপচাপ পা কেটে নিয়ে চলে যায়। এই যন্ত্রটি এত মসৃণ হয়ে গেছে, মনে হয় যেন একটা অ্যাপ-ই বানিয়ে ফেলা যাবে। তাঁর স্ত্রীর প্রতি সারাজীবন তিনি অনেক অবিচার করেছেন। সংসারের কুটোও তো নাড়তে হয়নি, উপরন্তু কোন আত্মীয় স্বজনের বিয়ে বা কোন অনুষ্ঠানে তাঁকে স্ত্রী কন্যার সঙ্গে যেতে দেখা যায়নি। এমনকি মেয়ের জন্মদিন বা বিয়ের তারিখ মনে রাখার প্রয়োজন মনে করেননি তিনি। সুপর্ণা একা হাতে সংসার, মেয়ে, লৌকিকতা আর নিজের কলেজ সামলেছে। তাই মেয়েকে লেকচারারশিপে ঢোকানোটা তাঁর স্ত্রীর জন্য একটা ছোট্ট ঋণ শোধের চেষ্টা আর কি। একটা থ্যাংক ইউ নোটের মতো মেয়ের অ্যাপ্যেন্টমেন্ট লেটারটা যেদিন সুপর্ণার হাতে তুলে দিতে পারলেন, বুক থেকে যেন কত বছরের ভার নেমে গেল। যাক, স্ত্রী মেয়ের জন্যে, সংসারের জন্যে কিছু তো করতে পারলেন শেষ পর্যন্ত। কোনদিন যে মেয়ের স্কুলে যাননি, সুপর্ণা বা মিঠির জন্যে বই ছাড়া কোন উপহার কিনে আনেন নি, সেসব ওই একখানা কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া গেল। এরপর তিনি মুক্ত, মেয়ে তরতর করে এগিয়ে চলেছে, এবার সুপর্ণা নাতনীকে নিয়ে পড়েছে।রিটায়ারমেন্টের পর নাতনী আর বাগান- এই তার ধ্যানজ্ঞান। মেয়ে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারছে। জামাইও তো সেই কোথায় রয়েছে, সিডনিতে। তিন তিনটে মহাদেশে ছড়িয়ে থাকা সংসার বেঁধে রেখেছে সুপর্ণা। ওদের জন্যে যে ফ্ল্যাট কিনে রেখেছিলেন, সেটা কি বেহাত হয়ে যেতে পারে? কবে ওরা ফিরবে, একজায়গায় হবে, কবে ওই ফ্ল্যাটে সংসার পাতবে কে জানে। আদৌ ফিরবে কিনা। ওখানে প্লেসমেন্ট পেয়ে গেলে এখানে ফেরার কোন মানে হয় না।ল্যাবগুলোর যা অবস্থা। খুব সাধারণ জিনিসের রিকিউজিশন দিয়ে ছ মাস হাঁ করে বসে থাকতে হয়, ফাইনান্স অফিসারের ঘরে গিয়ে ধর্না দিতে হয় দিনের পর দিন, তারপর তো কোন ল্যাব অ্যাসিস্টেন্টকে দিয়ে কাজ করানো এক অসম্ভব ব্যাপার।
সুপ্রতিম কে জিগ্যেস করেছিলেন একবার। সে খুব প্রফুল্ল মুখে বলেছিল ‘কোন কাজে আটকে গেলে বলবেন, একটা নাম্বার দেব। একবার ফোন করলেই সব মিটে যাবে। আমাকে তো আর এত ছোটখাট ব্যাপারে মাথা ঘামাতেই হয় না। একেবারে ডায়াল আ ফ্রেন্ড-র মতো’
নাম্বারটা নিয়ে রাখতে হবে। মেয়ে যদি এখানে ফিরে আসে, পুরনো চাকরিতে…
গেটের কাছে এসে দাঁড়ালেন অমরনাথ। এখনো অন্ধকার ঘন হয়নি। আকাশের প্যালেটে এলোমেলো রক্তলাল রঙ ব্রাশ করেছে কে যেন। আরেকটা দিন শেষ হয়ে গেল! চলে যাওয়া দিনের সামনে দাঁড়িয়ে কেমন যেন প্রণত হতে ইচ্ছে হল তাঁর। শুধু তাই নয়, কতদিনের জমে থাকা কান্না যে উঠে আসতে চাইল তাঁর ভেতর থেকে। এই প্রথম তাঁর মনে হল, সত্যিই কী করেছেন তিনি জীবনে, বলার মতো? কী করেছেন, যার জন্যে মানুষ তাঁকে মনে রেখে দেবে? দুচারজনকে চাকরি দিয়েছেন, হ্যাঁ তার জন্যে ঘুষ নেননি ঠিকই, কিন্তু মনে মনে তো চেয়েছেন সে সারাজীবন অনুগত আর কৃতজ্ঞ থাকুক, শুধু কৃতজ্ঞ নয়, কৃতার্থও। তার মানে তিনি তো জানেন, আরও অনেক যোগ্যতর প্রার্থী ছিল, তাদের বঞ্চিত করে তিনি যাকে চাকরি দিয়েছেন, সে সারাজীবন তাঁর পায়ে পড়ে থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। মুখে তিনি বলেন হাঁসাকে, প্রতি রোববার আসার দরকার নেই, কিন্তু যেবার ওর ছেলের খুব অসুখ করল, এক মাসের ওপর আসতে পারল না হাঁসা, তখন মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন তিনি, সুপর্ণা তো বলেই ফেলেছিল, ছেলেকে তো হসপিটাল থেকে রিলিজ করে দিয়েছে, এই রোববার তো এলেই পারত, বাগানটা যে জঙ্গল হয়ে গেল’। ওরা সবাই মিলে যখন সাউথ ইন্ডিয়া ঘুরতে গেল, পরপর দু দুটো রবিবার আসতে পারল না, তখনো তাঁরা একটুও খুশি হতে পারেন নি।তিনি কি মনে করেছেন এইসব সার্ভিস হাঁসা মন থেকে খুশি হয়ে দ্যায়? কৃতজ্ঞতা কি বোঝার মতো হয়ে যায় না, ওর কি কখনো মনে হয় না, শালা একটা চাকরি দিয়ে এই লোকটা আমাকে জন্মের মতো কিনে নিয়েছে?’ ওর না হোক, ওর বউয়ের নিশ্চয় মনে হয়। খুব ভোরে উঠে স্বামী যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, ঘুম চোখে দরজা বন্ধ করতে করতে ও নিশ্চয় গজগজ করে ‘কীরকম লোক এরা, চাকরি দিয়েছে বলে রবিবারের ঘুমটাও কেড়ে নিতে চায়!’
কান্না পেল, কিন্তু কাঁদতে পারলেন না। গেটে দাঁড়িয়ে দেখলেন, দিঘির জলে দু তিনজন মজুর সারাদিনের শেষে স্নান করতে এসেছে। কী একটা কথায় খুব হাসছে ওরা। দুটো ছেলে গাইতে গাইতে যাচ্ছে ‘টুম্পপা সোনা দুটো হাম্পি দেনা’
সবকিছুই তো স্বাভাবিক, রোজকার মতো। কিন্তু তিনি হঠাৎ কাকে দেখলেন? শুধু আজ বলে না, সবসময় মনে হয় কেউ পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। পর্দার আড়ালে। একটা মেয়ে। কাজের মাসি জাতীয় না, সেলস গার্ল টাইপও না, একটা চোখে পড়ার মতো সুন্দরী মেয়ে, সালোয়ার কুর্তি পরা, চোখ দুটি কিছু চাইতে জানেনা, উদাস সারল্যে ভরা। একে কোথাও দেখেছেন বলে মনে পড়ে তাঁর।কিন্তু কোথায়, তা কিছুতেই মনে করতে পারেন না।
আবার, আবার সেই মুখটা, একবার এই মুখ দেখেই কি তিনি বলেছিলেন ‘আই নো হার’ তাহলে এখন কেন বুঝতে পারছেন না?
ওরা স্নান করে উঠে আসছে, উঠে আসতে আসতে ওরা একটু থমকে দেখল, তারপর নিজেদের গা ঠেলাঠলি করে জলের ধারের বেঞ্চের দিকে ইশারা করল। এতক্ষণ লক্ষ্য করেননি অমরনাথ। বেঞ্চে কে যেন বসে আছে না? একটা মেয়ে, আর মেয়েটা আচমকা পেছন ফিরে সোজা তাঁর দিকে তাকাল আর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল অমনি। আই নো হার। বহুবছর আগে বিশাল ওভাল টেবিলে এর উল্টোদিকে বসে বলেছিলেন। তাঁর পা দুটো মাটিতে গেঁথে গেল।


আমি নিয়মিত পাঠক। খুব ভাল লাগে