‘বয়স যেন মহিষদেহে বৃষ্টিধারা’
: গৌতম বসু
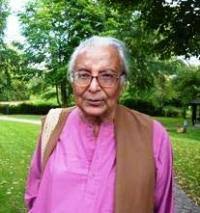
কবে, কোথায় যেন চিত্রী ম্যাক্স লিবারমান-এর একটি উক্তি কুড়িয়ে পেয়ে টুকে রেখেছিলাম; তিনি বলছেন, আমি যখন ফ্রান্স হাল্স-এর কাজ দেখি, প্রবল ইচ্ছা হয় ছবি আঁকবার, আর, যখন একটা রেম্ব্রান্ট-এর সামনে এসে দাঁড়াই, সব কিছু ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবি। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র কবিতা, ওই দ্বিতীয় চেহারাটি নিয়ে দীর্ঘকাল আমার জীবনে উপস্থিত। একটা প্রভেদ নিজের ভিতর গজিয়ে উঠেছে মাঝপথে, সেটাও টের পাই; ডেকে-ডেকে তাঁর লেখা কাউকে শোনাই না আর, কান-ফাটানো কবিতা বেজে চলেছে, কে শুনবে এই ক’টি লাইন:
‘এখন আমার হাত ছড়ে গেলে শিশির বেরোয়
আর সেই অবকাশে
দূর দূর থেকে আবালবৃদ্ধ এবং বনিতা
আমাকে দেখতে আসে।
আর তখনই রক্তগঙ্গা বয়ে যায় যত
অভুক্ত ঘাসে ঘাসে,
আর তক্ষুনি পৌরসংস্থা থেকে দমকল
রক্ত নেভাতে আসে।’
[‘নিসর্গ আজ মানুষের মতো কাঁদে’ / কাব্যগ্রন্থ: ‘নিরীশ্বর পাখিদের উপাসনালয়ে’/ ২০১৩]
কবিতার হওয়া না-হওয়া, বোধের না হলেও, বুদ্ধির এলাকার বাইরের অবস্তু ব’লে মনে হয়, যার সঙ্গে নিরন্তর প্রয়াসের একটা সম্পর্ক থাকলেও, তোলপাড় ক’রে খুঁজে বেড়ালে যাকে পাওয়া অসম্ভব, বাইরের সমস্ত আয়োজন ও উদ্যোগকে যেখানে মুখ থুবড়ে প’ড়ে থাকতে দেখা যায়। নীরবে উপস্থিত হয় কবিতা, নিজেকে সে প্রত্যাহার ক’রে নেয় নীরবেই, গায়ে চিমটি কেটে নিজেকে যিনি জাগিয়ে রাখলেন, ঘুমে ভারি হয়ে-আসা তাঁর দু’চোখের সম্মুখেই কখনও-কখনও কবিতা আবির্ভূত হয়; এই সুবন্দোবস্তের কোনও বিকল্প নেই।
দোতলা বাসের প্রথম সারিতে খোলা জানালার সামনে, পা ছড়িয়ে ব’সে তাঁর কবিতার লাইন উচ্চস্বরে আওড়াতাম আমরা যখন, আমাদের তরুণ বয়সে ─ ‘হাওয়ার ভিতরে কার ক্ষমা ঐ কাজ ক’রে যায়’ ─ তখন, সে-উচ্ছ্বাসে, এক বিস্ময়বালকের রকমসকম বুঝে না-উঠতে পারার বাতাবরণ ছড়িয়ে থাকত। তাঁর কবিতার পাঠক হিসেবে আমি একলা হয়ে গেলাম এর পরে, যখন লক্ষ করলাম আমার চারপাশ থেকে মধ্যবয়সী অলোকরঞ্জন-এর কবিতার প্রতি সেই অনুরাগ যেন ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে। এখন অনুমান করি, সেদিনের পাঠক গগনবিহারী কবির রুক্ষ মাটিতে অবতরণকে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁদের হয়তো এমন একটা প্রত্যাশা জন্মেছিল যে, একটা ‘যৌবন বাউল’, একটা ‘নিষিদ্ধ কোজাগরী’, একটা ‘রক্তাক্ত ঝরোখা’ বারবার লিখিত হোক।
আমার আরও মনে হয়েছে, আমাদের মনোযোগ এখনও জড়িয়ে রয়েছে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র অলৌকিক বাচনভঙ্গিমায় ও শৈলীপ্রয়োগে; আমাদের পঠন তাঁর ভিতরের অবিরল রক্তক্ষরণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি। বস্তুত, তাঁর বিবর্তন, একটা পুরানো পরিচয় বদলে ফেলে নতুন পরিচয়ে প্রবেশ করার কোনও যুগপৎ বুদ্ধিদীপ্ত ও চমকপ্রদ পদক্ষেপ নয়; তাঁর শোকাহত কৌতুকপ্রিয়তা আজও তেমন মর্মভেদী রয়ে গেছে, রূপান্তর কেবল একটাই, রিখিয়া পেরিয়ে, বাবুডির মাঠ পেরিয়ে, কল্যাণেশ্বরীর হাট পেরিয়ে, সেই শোকোত্তর কৌতুক এই হতশ্রী বর্তমানকালে এসে উপস্থিত হয়েছে। মানুষকে তাঁর চরম দুর্দশা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য তাঁকে দশটা পঙ্ক্তিও ব্যয় করতে হয় নি, এই কথাটি যতবার ভাবি, ততবার বেচারা ভাগ্যহত ম্যাক্স লিবারমান-এর জায়গায় নিজেকে দেখতে পাই। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত লিখছেন:
‘পুরোহিত মহোদয়,
এমন বীভৎসভাবে ছিটিয়ে দেবেন না শান্তিজল,
চোখ বড় জ্বালা করে।
আপনি তো জানেন শান্তিজলে
লুকিয়ে থাকতে পারে আণবিকতার আবর্জনা
ল্যাবরেটরিতে গিয়ে অনিরুদ্ধ প্রমাণ পেয়েছে
বৃষ্টির জলেও আজ অ্যাসিডের ছিল পরিচয়
তাই তো বাড়ির পথে মীরার দুচোখ ঝলসে গেছে,
বৃষ্টির অ্যাসিডে, বৃষ্টি তাহলে কি ধর্ষকাম নয়?’
[‘আর পৌরোহিত্য নয়’ / কাব্যগ্রন্থ: ‘চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো’ / ২০১৫]
বাঙলা লিরিকের ভিতরে ও বাইরে একাধিক নতুন চিন্তাসূত্রের প্রবর্তন আমরা দেখি যেখানে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত নামটি খোয়া গেলেও, তিনি রয়ে গেছেন সূক্ষ্মশরীরে। এ-আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে বাঙলা লিরিকের ভিতরের ঘরে প্রবেশ ক’রা অসমীচীন হবে, আমি কেবল কবিতার বাইরের জগতের দু’টি প্রথার উল্লেখ এখানে করছি। এক, একই পাঠ্যবস্তুতে দু’রকম ‘টাইপ’ ─ ‘স্মল পাইকা’ এবং ‘বর্জাইস’ ─ একইসঙ্গে ভাবে ব্যবহার ক’রে,(আজকের পরিভাষায় যথাক্রমে যা, ১২ নম্বর ও ১০ নম্বর ফন্টের সমতুল্য), তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।
‘ “ইচ্ছা মিটে যাওয়ার পরেও ঘৃণিত শয়তান
কেন অমন ইচ্ছা বানায়, উত্তাল মশারি
ছিঁড়ে কেন পালিয়ে যায় সকল নক্তনারী ?”
দীপির্ দাং দীপির্ দাং দীপির্ দীপির্ দাং।।
[‘নগরপ্রশ্ন ও সাঁওতালি প্রত্যুত্তর’ / কাব্যগ্রন্থ: ‘নিষিদ্ধ কোজাগরী’/১৯৬৭ ]
দুই, আজকের তরুণ কবিরা প্রায় ব্যতিক্রমহীন ভাবে তাঁদের কবিতার বই একটি ‘বিভাব’ কবিতা দিয়ে শুরু করেন, এ-তথ্য হয়তো না জেনেই যে, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, ধারাবাহিক ও আত্মবিশ্বাসী প্রয়োগের দ্বারা বাঙলা কবিতায় এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন।
*
তাঁর সঙ্গ আমি হারয়েছি বহুকাল; তাঁকে শেষবার প্রণাম করবার বয়স যখন দু’বছর ছুঁই-ছুঁই, ঠিক তখন, এই প্রয়াণসংবাদ কাচের শার্সির মতো আমার গায়ের উপর ভেঙে পড়ল। কে জানে কত বছর, মাত্র কুড়ি-পঁচিশটি বইয়ের ভিতর দিয়েই আমাদের মধ্যে সংযোগ অক্ষত রয়ে গেছে, তিনি কথক, আমি শ্রোতা। বই কটা নামিয়ে ফেললাম আবার, কিন্তু পড়তে পারলাম কই? ভাবলাম, লিখতে যিনি পারেন, তিনি অক্লেশে এবং বারংবার পারেন, আর লিখতে যিনি পারেন না, তাঁর হয়তো চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই, কিন্তু কলমখানা তাঁর বারেবারে ভেঙে যায়। মনে প’ড়ে গেল, টিউববন্দী দাড়ি কামাবার সাবান ব্যবহার করার রেওয়াজ যখন আসে নি, যখন সাবানের গোলাকার ঢ্যালা দিয়েই কাজ চ’লে যেত, সেই সুদূর অতীতে তিনি আমায় ফরিদ্উদ্দিন আত্তর পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যে শবানুগমনে আমায় অংশগ্রহণ করতে হল না, সে-মৃত্যুও সম্পূর্ণ অলীক হয়ে থাক আমার জীবনে। বইয়ের পাতা ওলটাবার কাজে আবার ফিরে গেলাম। পাতা ওলটাতে-ওলটাতে যে-ক’টি জায়গায় আমায় আবার থেমে যেতে হচ্ছিল, তারই দু’টি পৃষ্ঠা আজকের নবীন পাঠকের জন্য তুলে ধরছি:
‘এই চিন্তা
শেকভের সমাধির মতো
ছোটো
তুলসীতলার চেয়ে
ক্ষুদ্রতর
জননী মেরীর গর্ভগৃহের চেয়েও
ক্ষুদ্র
গৃহগর্ভের চেয়েও
‘চৈতন্যচরিতামৃত’ রচয়িতা যেইখানে রেখেছেন দেহ
আর তার মরবার পরিসর এতই ছোটো যে
যেন তিনি কখনো-কিছুই
লেখেননি
লিখলেও
এতই ছোটো যে
তার মতো বৃহৎ কিছুই নেই ’
[‘শেকভের সমাধির মতো’/ কাব্যগ্রন্থ: ‘ঝরছে কথা আতসকাঁচে’ / ১৯৮৫]
এবং
‘ততোক্ষণ মাথা ঝুঁকে প’ড়ে থাকো ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ─
যদি বই পাওয়া যায়, আর যদি না-ও পাওয়া যায়
চেয়ে দ্যাখো কার্ল মার্ক্স পড়তেন কোন্ প্রান্তে ব’সে,
ইউনেস্কোর উচিত ঐ জায়গাটাকে তীর্থ ব’লে প্রতিপন্ন করা।
কোনো বই পাওয়া যায়নি? এসে যায় না, এই চেয়ে দ্যাখো
শুধুই আজকের জন্য প্রদর্শিত হয়েছে এখানে
কীট্সের হাতে লেখা চিঠি:
“পিসা থেকে এক ভদ্রলোক, শেলি, চিঠি লিখেছেন
ওঁর কাছে যেতে।”
অন্তত এ চিঠিখানি সংরক্ষিত আছে সভ্যতায়
এসো, এই কথা ভেবে আত্মহত্যা মুলতুবি রাখি ।
[‘চেয়ে দ্যাখো’/ কাব্যগ্রন্থ: ‘ঝরছে কথা আতসকাঁচে’ / ১৯৮৫]

