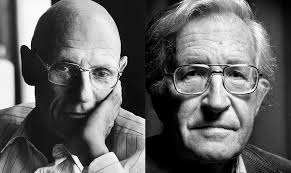
নোম চমস্কি ও মিশেল ফুকো-র বিতর্ক অনুবাদ– হিন্দোল ভট্টাচার্য
১৯৭১ সালে ডাচ টেলিভিশনে অনুষ্ঠিত একটি ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন দুটি বিশিষ্ট চিন্তাবিদ — নোয়াম চমস্কি এবং মিশেল ফুকো। এই বিতর্কটি “Human Nature: Justice versus Power” শিরোনামে অনুষ্ঠিত হয় এবং এটি পরিচালনা করেছিলেন দার্শনিক ফন্স এল্ডার্স। সংশ্লিষ্ট আলোচনায় তাঁরা এমন এক চিরন্তন প্রশ্নের মুখোমুখি হন: আমাদের কি কোনো “জন্মগত মানব প্রকৃতি” আছে? আমরা কি কেবল আমাদের অভিজ্ঞতা এবং বাইরের প্রভাবগুলোর ফলাফল, নাকি সেই অভ্যন্তরীণ স্বরূপ রয়েছে যা আমাদের মানুষ হিসেবে চেনাতে পারে? চমস্কি ভাষাবিজ্ঞান থেকে তার যুক্তি শুরু করেন — তার মতে, মানুষের ভাষা শেখার প্রক্রিয়া দেখায় যে আমাদের মনের মধ্যে এমন একটি অন্তর্নিহিত কাঠামোর উপস্থিতি রয়েছে, যা অভিজ্ঞতার খুব সীমিত “ডেটা”- থেকেও সিস্টেম্যাটিক ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান গড়ে তুলতে পারে। ফুকো অন্যদিকে বলেন যে “মানব প্রকৃতি”, “ন্যায়বিচার” এবং “সত্তা”–র ধারণাগুলো আসলে সামাজিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক প্রথা, এবং ক্ষমতার ব্যবস্থার অংশ; অর্থাৎ, এই ধারনাগুলো সরলভাবে ইউনিভার্সাল নয়, বরং ইতিহাসিকভাবে গঠিত। এই বিতর্ক একদিক যেমন একটি দার্শনিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিতর্ক, অন্যদিকে এটি গভীর রাজনৈতিক প্রভাবও তৈরি করে — কারণ চমস্কি এবং ফুকো উভয়েই শুধু তত্ত্ব নয়, তাঁদের রাজনীতিক চিন্তাভাবনাও যুক্ত করেছেন।
মানব প্রকৃতি: ন্যায় বনাম ক্ষমতা
নোম চমস্কি ও মিশেল ফুকো-র বিতর্ক
১৯৭১
সঞ্চালক (এলডার্স):
শ্রদ্ধেয় মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রলোকগণ, আন্তর্জাতিক দার্শনিক প্রকল্পের তৃতীয় বিতর্কে আপনাদের স্বাগত। আজকের বিতর্কের দুই আলোচক হলেন ফ্রান্সের কোলেজ দ্য ফ্রঁসের অধ্যাপক মিশেল ফুকো এবং ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক নোম চমস্কি। এই দুই দার্শনিকের চিন্তাধারায় যেমন মিল আছে, তেমনি রয়েছে ভিন্নতাও। হয়তো তাদের তুলনা করার সবচেয়ে যথাযথ উপায় হলো — তাদেরকে ভাবা এক পাহাড়ের দুই দিক থেকে সুড়ঙ্গ খননকারী হিসেবে। তারা ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে, ভিন্ন ভিন্ন সরঞ্জাম দিয়ে, এমনকি একে অপরের দিকে এগোচ্ছেন কিনা সেটাও না জেনে নিজেদের কাজ করে চলেছেন।
তবুও দু’জনই একেবারে নতুন ধরনের চিন্তা নিয়ে, দর্শন ও রাজনীতির প্রতি সমান দায়বোধ নিয়ে, গভীরতম সম্ভব জায়গায় খনন করে চলেছেন— এবং এটাই, আমার মতে, আমাদেরকে এক অত্যন্ত আকর্ষণীয় দর্শন ও রাজনীতি বিষয়ক বিতর্কের প্রত্যাশা করার যথেষ্ট কারণ।
সুতরাং, আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না এবং একটি কেন্দ্রীয় ও চিরন্তন প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে চাই: মানব প্রকৃতির প্রশ্ন।
মানুষ বিষয়ক সব গবেষণা— ইতিহাস থেকে ভাষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান— এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হয় যে, শেষ পর্যন্ত আমরা কি নানান বহির্বর্তী উপাদানের ফলাফল? নাকি আমাদের পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমরা ‘মানব প্রকৃতি’ বলতে পারি— যার দ্বারা আমরা একে অপরকে মানুষ হিসেবে চিনি?
তাই আমার প্রথম প্রশ্নটি আপনার প্রতি, অধ্যাপক চমস্কি। কারণ আপনি মানব প্রকৃতি ধারণাটি প্রায়ই ব্যবহার করেন এবং এই প্রসঙ্গে আপনি “জন্মগত ধারণা” ও “জন্মগত গঠন” — এ ধরনের শব্দও ব্যবহার করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানের মাধ্যমে আপনি কোন যুক্তির ভিত্তিতে মানব প্রকৃতি ধারণাটিকে এত কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দেন?
চমস্কি:
তাহলে আমি একটু প্রযুক্তিগত দিক থেকে শুরু করি।
যে ব্যক্তি ভাষা অধ্যয়ন করতে আগ্রহী, সে একটি খুব স্পষ্ট বাস্তব অভিজ্ঞতামূলক সমস্যার মুখোমুখি হয়। সে মুখোমুখি হয় এক জীব — এক প্রাপ্তবয়স্ক বক্তার — যার মধ্যে কীভাবে যেন একটি বিস্ময়কর ক্ষমতা-সমষ্টি গড়ে উঠেছে। এই ক্ষমতাগুলি তাকে বিশেষভাবে সক্ষম করে তোলে— সে যা বলতে চায় তা বলতে, অন্যেরা তাকে যা বলে তা বুঝতে, এবং তা করতে পারে এক অত্যন্ত সৃষ্টিশীল (creative) পদ্ধতিতে। অর্থাৎ, মানুষ তার দৈনন্দিন সংলাপে যা বলে তার একটি বড় অংশই নতুন; আমরা যা শুনি তারও অনেক কিছুই একেবারেই নতুন— যা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃ্য রাখে না। তবুও এই নতুন আচরণ এলোমেলো নয়; বরং পরিস্থিতির সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ— তবে সেই সামঞ্জস্যের প্রকৃতি বর্ণনা করা খুবই কঠিন। এবং প্রকৃতপক্ষে এর অনেক বৈশিষ্ট্যই রয়েছে যা আমি নিঃসন্দেহে ‘সৃজনশীলতা’ বলে উল্লেখ করব।
এখন, যে ব্যক্তি এই জটিল, সুসংগঠিত, বহুস্তরযুক্ত দক্ষতাগুলির সমষ্টি— অর্থাৎ যাকে আমরা ভাষাজ্ঞান বলি— অর্জন করেছেন, তিনি জীবনের পথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অভিজ্ঞতা পেয়েছেন; ভাষার সঙ্গে তার সরাসরি অভিজ্ঞতার কিছু তথ্য তিনি পেয়েছেন।
এই ব্যক্তির কাছে যে তথ্য-উপাত্ত উপলব্ধ হয়েছে, আমরা সেগুলি তদন্ত করতে পারি; এবং তা করার পর, নীতিগতভাবে, আমরা এক স্পষ্ট ও নির্ধারিত বৈজ্ঞানিক সমস্যার সামনে দাঁড়াই— সেই সমস্যাটি হলো: শিশুকে যে তথ্য দেওয়া হয় তা প্রকৃতপক্ষে খুবই অল্প, এবং গুণগত দিক থেকেও অনেকটাই অসম্পূর্ণ; অথচ সেই স্বল্প তথ্য থেকেই শিশু যে সুগঠিত, সুবিন্যস্ত, গভীরভাবে সংগঠিত জ্ঞান অর্জন করে, তার মধ্যকার বিশাল ফাঁকটাকে ব্যাখ্যা করা।
অধিকন্তু, আমরা লক্ষ্য করি যে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও একই ভাষার বিভিন্ন বক্তা প্রায় একই ধরনের ভাষাগত কাঠামোয় উপনীত হন। দুই ইংরেজি ভাষাভাষী ব্যক্তি তাদের সম্পূর্ণ আলাদা অভিজ্ঞতা থেকে যে ভাষাজ্ঞান তৈরি করেন, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এতটাই সঙ্গতিপূর্ণ যে একজন যা বলেন, অন্যজন তা অনায়াসে বুঝতে পারেন।
আরও বিস্ময়কর হলো— আমরা দেখি যে বহু বৈচিত্র্যময় ভাষাতেও— প্রকৃতপক্ষে যেসব ভাষা নিয়ে গভীর গবেষণা করা হয়েছে— সেখানে ভাষাজ্ঞানের কাঠামো যে ধরনের হয়, তার উপর বিস্ময়কর রকমের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। অর্থাৎ মানুষ যত ভিন্ন অভিজ্ঞতাই পাক না কেন, ভাষার চূড়ান্ত রূপে একধরনের সাধারণত্ব ও কাঠামোগত মিল আমরা দেখতে পাই।
এত বিস্ময়কর ঘটনার একটাই ব্যাখ্যা সম্ভব — এবং সেটা আমাকে বেশ সংক্ষিপ্ত রূপরেখায় বলতে হবে — তা হলো এই অনুমান যে ব্যক্তি নিজেই এই জ্ঞানের সাধারণ কাঠামোতে, এমনকি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুতেও, একটি বিশাল অংশ যোগ করে। অর্থাৎ ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকা অতি সীমিত অভিজ্ঞতা থেকে যে জ্ঞান সে শেষ পর্যন্ত অর্জন করে, তার মূল ভিত্তি সে নিজে নিয়ে আসে।
যে ব্যক্তি একটি ভাষা জানে, তার ভাষাজ্ঞান অর্জিত হয় কারণ সে শেখার অভিজ্ঞতার দিকে এগিয়ে যায় একটি খুব স্পষ্ট ও বিশদ জন্মগত কাঠামো (schematism) নিয়ে— যা তাকে জানায়, সে যে ভাষার সংস্পর্শে আসছে সেটি কী ধরনের ভাষা হতে পারে। সহজ করে বললে: শিশু শেখার শুরুতেই জানে না যে সে ইংরেজি, ডাচ, ফরাসি বা অন্য কোনও ভাষা শুনছে। কিন্তু সে শুরু করে এই জেনে যে— সে একটি মানব-ভাষা শুনছে, যা খুবই নির্দিষ্ট ধরনের— যেখানে ভিন্নতার পরিসর খুব সংকীর্ণ।
এবং ঠিক এই অত্যন্ত সংগঠিত ও সীমাবদ্ধ কাঠামো নিয়েই শিশু ছড়িয়ে থাকা অসম্পূর্ণ তথ্য থেকে এক সুবিন্যস্ত গভীর জ্ঞানের দিকে বিশাল লাফ দিতে সক্ষম হয়। আরো যোগ করব: আমরা যথেষ্ট দূর পর্যন্ত— আসলে বেশ দীর্ঘ পথ পর্যন্ত— বর্ণনা করতে পারি সেই ভাষাগত গুণাবলি, যা আমি ‘জন্মগত ভাষা’ বা শিশুর ‘সহজাত জ্ঞান’ বলব, অর্থাৎ ভাষা শেখার সময় শিশুর মস্তিষ্কে আগে থেকেই থাকা সংগঠনী নীতি। এবং আমরা অনেকটা দূর পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতে পারি সেই মানসিক কাঠামো, যা সে ভাষাজ্ঞান অর্জনের পর গড়ে ওঠে।
আমি বলব, এই সহজাত জ্ঞান— বা এই জন্মগত কাঠামো— যা অতি সামান্য তথ্যের ভিত্তিতে জটিল এবং সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জনকে সম্ভব করে— সেটাই মানব প্রকৃতির একটি মৌলিক উপাদান। বিশেষত ভাষা যোগাযোগের জন্যই শুধু নয়— চিন্তার প্রকাশ এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্যও অপরিহার্য ভূমিকা রাখে বলেই এটি মৌলিক।
আর আমি ধরে নিই যে মানব বুদ্ধিমত্তার অন্যান্য ক্ষেত্রেও— মানবচিন্তা, আচরণ এবং জ্ঞানের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেও— একই ধরনের নীতিই কার্যকর হয়।
সুতরাং এই যে জন্মগত সংগঠনী নীতির সমষ্টি— যা আমাদের সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ব্যক্তিগত আচরণকে পরিচালিত করে— আমি সেই ধারণাকেই “মানব প্রকৃতি” বলে উল্লেখ করি।
সঞ্চালক (এলডার্স):
আচ্ছা, মঁসিয়ে ফুকো, আপনার বই The History of Madness এবং Words and Objects (মূলত The Order of Things বোঝানো হয়েছে) পড়লে আমার মনে হয় আপনি যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক স্তরে কাজ করছেন এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও যেন একেবারেই বিপরীত। মানব প্রকৃতির প্রসঙ্গে “স্কিমাটিজম” শব্দটি নিয়ে ভাবলে মনে হয় আপনি যেন বিভিন্ন যুগের জন্য বিভিন্ন স্কিমাটিজম ব্যাখ্যা করতে চাইছেন। এ বিষয়ে আপনার মত কী?
ফুকো:
আচ্ছা, যদি আপত্তি না থাকে, আমি ফরাসিতে উত্তর দেব, কারণ আমার ইংরেজি খুবই দুর্বল; ইংরেজিতে উত্তর দিলে আমি নিজেই লজ্জা পাব।
এটা সত্যি যে আমি “মানব প্রকৃতি” ধারণাটিকে কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখি— এবং তার কারণ হলো এটাই: আমি বিশ্বাস করি, কোনো বিজ্ঞানের ব্যবহৃত ধারণাগুলি বা কনসেপ্টগুলি সবসময় একই মাত্রায় বিশদভাবে পরিশীলিত হয় না। এবং সাধারণভাবে, এগুলির ভূমিকা, কার্যকারিতা এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ব্যবহারের ধরনও এক নয়। উদাহরণ হিসেবে জীববিজ্ঞানকে ধরা যাক। সেখানে কিছু ধারণা থাকে শ্রেণিবিন্যাস করার জন্য, কিছু ধারণা থাকে পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য, আবার কিছু ধারণা থাকে বিশ্লেষণমূলক কাজের জন্য। কিছু ধারণা আমাদের কোনো বস্তু শনাক্ত করতে সাহায্য করে— যেমন “টিস্যু” ধারণাটি; কিছু ধারণা উপাদান আলাদা করতে সাহায্য করে— যেমন “বংশগত বৈশিষ্ট্য”; আবার কিছু ধারণা সম্পর্ক নির্ধারণ করে— যেমন “রিফ্লেক্স” ধারণাটি।
একই সময়ে, এমন কিছু উপাদানও থাকে যা বৈজ্ঞানিক বয়ানের ভেতরে এবং যুক্তিক্রম নির্মাণের নিয়মসমূহে ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর বাইরে “পার্শ্ববর্তী” বা peripheral ধারণাও আছে— যেগুলোর মাধ্যমে বিজ্ঞান নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে, অন্যান্য জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে নিজেকে পৃথক করে, নিজের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নির্ধারণ করে এবং ভবিষ্যতের কাজের ব্যাপ্তি নির্দেশ করে। “জীবন” (life) ধারণাটি কোনো এক সময় জীববিজ্ঞানে এই ধরনের ভূমিকাই পালন করেছে।
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে প্রকৃতি অধ্যয়নে “জীবন” ধারণাটি খুব বেশি ব্যবহৃত হতো না। সেই সময় জীবিত ও অজীব সব কিছুকেই এক বিশাল শ্রেণিবিন্যাসে রাখা হতো— যেখানে নিচে খনিজ পদার্থ এবং উপরে মানুষ। খনিজ আর উদ্ভিদ/প্রাণীর মধ্যে স্পষ্ট সীমানা তখনও স্থির ছিল না। জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিছুকে চিরস্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে স্থাপন করা।
অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে, উন্নত যন্ত্র ও নতুন কৌশলের সাহায্যে প্রকৃতির বিবিধ সত্তার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ এক নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কার করল— বস্তুসমূহ, সম্পর্কসমূহ এবং প্রক্রিয়াসমূহের এক পুরো ক্ষেত্র, যার ফলে প্রকৃতির জ্ঞানতন্ত্রে “জীববিজ্ঞান”কে আলাদা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হলো। তাহলে কি বলা যায় যে জীবন নিয়ে গবেষণাই জীববিজ্ঞানকে গড়ে তুলল? জীবন ধারণাই কি জীববৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সংগঠনের উৎস? আমি তা মনে করি না।
আমার মতে বরং উল্টো— অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে জীববৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যে রূপান্তর হলো, একদিকে তা একটি সম্পূর্ণ নতুন বিশ্লেষণভিত্তিক ধারণা-সমষ্টি তৈরি করল, এবং অন্যদিকে “জীবন”–এর মতো একটি ধারণার জন্ম দিল— যা আমাদেরকে বৈজ্ঞানিক আলোচনার একটি বিশেষ পরিসরকে আলাদা করে নির্দেশ ও সীমাবদ্ধ করতে সক্ষম করল। আমি বলব, “জীবন” কোনো বৈজ্ঞানিক ধারণা নয়; বরং একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক সূচক— যার শ্রেণিবিন্যাসমূলক, সীমাঙ্কনমূলক ও অন্যান্য ভূমিকা বৈজ্ঞানিক আলোচনার পদ্ধতিতে প্রভাব ফেলেছে; কিন্তু বিজ্ঞান যে বিষয় নিয়ে কথা বলছে, তার উপর নয়।
ফুকো:
আমার মনে হয় “মানব প্রকৃতি” ধারণাটিও সেই একই ধরনের। মানব প্রকৃতি গবেষণা করতে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা ব্যঞ্জনের পরিবর্তন-নিয়ম (laws of consonant mutation) আবিষ্কার করেননি; ফ্রয়েডও মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে স্বপ্ন-বিশ্লেষণের নীতি খুঁজে পাননি; সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদরাও মানব প্রকৃতি অধ্যয়ন করে মিথের গঠন উদ্ঘাটন করেননি। জ্ঞানের ইতিহাসে “মানব প্রকৃতি” ধারণাটি আসলে আমার কাছে মূলত এক ধরনের জ্ঞানতাত্ত্বিক সূচক (epistemological indicator) — যা ধর্মতত্ত্ব, জীববিদ্যা বা ইতিহাসের মতো ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত বা তাদের বিরোধী কিছু ধরনের বক্তৃতাকে চিহ্নিত করে। আমি এটাকে কোনো বৈজ্ঞানিক ধারণা হিসেবে দেখতে অসুবিধা বোধ করি।
চমস্কি:
প্রথমেই বলি— যদি আমরা স্নায়ুনেটওয়ার্কের (neural networks) ভাষায় সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারি মানুষের জ্ঞান-গঠন (cognitive structure)-এর সেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে— যেগুলো শিশুকে জটিল ভাষাগত ব্যবস্থা শিখতে সক্ষম করে— তাহলে আমি অন্তত কোনোরকম দ্বিধা ছাড়াই বলব, সেগুলো মানব প্রকৃতির একটি মৌলিক উপাদান। অর্থাৎ এখানে এমন কিছু জীববৈজ্ঞানিকভাবে প্রাপ্ত ও অপরিবর্তনীয় বিষয় আছে— যা আমাদের মানসিক ক্ষমতা দিয়ে আমরা যা করি তার ভিত্তি।
তবে আপনার বলা দিকটিকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই— যে ধারণাটি আপনি উল্লেখ করলেন: জীববিজ্ঞানে “জীবন” ধারণার সংগঠনী ভূমিকা। এ বিষয়ে আমি পুরোপুরি একমত।
আমার মনে হয়, আমরা আরেকটু কল্পনা করতে পারি— বিশেষ করে যেহেতু আমরা অতীত নয়, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি— যে মানব প্রকৃতি, বা জন্মগত সংগঠনী প্রক্রিয়া (innate organising mechanisms), বা মানসিক কাঠামো (intrinsic mental schematism)— যাই বলি না কেন (আমার মনে হয় নামগুলোর মাঝে তেমন পার্থক্য নেই)— সংক্ষেপে একে মানব প্রকৃতি বলি— জীববিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রার পরবর্তী শিখর হতে পারে। জীববিজ্ঞানীরা হয়তো ইতোমধ্যেই (অবশ্য এটি বিতর্কযোগ্য) “জীবন কী” প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেয়েছেন— তার পরে যে শিখর তাদের সামনে থাকতে পারে তা হলো— মানব প্রকৃতি।
অর্থাৎ, স্পষ্ট করে বললে— আমরা কি জীববৈজ্ঞানিক বা পদার্থগত ব্যাখ্যা দিতে পারব—
▪️ শিশুর জটিল জ্ঞানের কাঠামো অর্জনের ক্ষমতার?
▪️ এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ— এই জ্ঞান অর্জনের পর, সেটিকে যে সে স্বাধীন, সৃজনশীল এবং বিস্ময়কর বৈচিত্র্যপূর্ণ উপায়ে ব্যবহার করে— তার ব্যাখ্যাতেও?
আমরা কি জীববৈজ্ঞানিক ভাষায়— শেষ পর্যন্ত পদার্থবিদ্যার ভাষায়— এই দুই বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হব? আমার কাছে মনে হয়— এরকম আশা করার কোনো যুক্তি নেই। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন— যেহেতু বিজ্ঞান অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করেছে, তাই এটিও করবে— কিন্তু আমার মতে এটি মূলত তাদের বিশ্বাস, নিশ্চিত জ্ঞান নয়।
কিছু অর্থে বলা যায়, এটি শরীর–মন সমস্যার (body/mind problem) একটি ভিন্ন রূপ। তবে যদি আমরা ইতিহাসের দিকে তাকাই— কীভাবে বিজ্ঞান তার বিভিন্ন শিখর জয় করেছে— এবং কীভাবে “জীবন” ধারণাটি দীর্ঘ সময় বিজ্ঞানী দৃষ্টির বাইরে থাকা সত্ত্বেও শেষে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আওতায় এসেছে— তাহলে আমরা দেখতে পাই, বিশেষ করে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের দিকে, বহু ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ঘটেছে কারণ ভৌত বিজ্ঞানের ক্ষেত্র নিজেই বিস্তৃত হয়েছিল।
একটি ক্লাসিক উদাহরণ নিউটনের মহাকর্ষ–বল।
কার্তেসীয় দৃষ্টিতে দূর থেকে প্রভাব বিস্তার (action at a distance) ছিল সম্পূর্ণ রহস্যময় ধারণা— এমনকি নিউটনের কাছেও এটি একধরনের অদৃশ্য গুপ্তগুণ বলে মনে হয়েছিল, যা বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না।
কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের “স্বাভাবিক বোধ”-এর মধ্যেই এই দূর-প্রভাব বিজ্ঞানের অন্তর্গত হয়ে গেল।
অর্থাৎ, “দেহ” বা “ভৌত” বিষয়ক ধারণাটিই পরিবর্তিত হয়ে গেল।
একজন কঠোর কার্তেসীয় যদি আজকের দিনে আসতেন— তিনি আকাশীয় বস্তুদের আচরণ ব্যাখ্যা করতে পুরোপুরি অক্ষম হতেন।
আরো স্পষ্টভাবে বললে— বিদ্যুত্চুম্বকীয় বল দিয়ে যে সব ঘটনা ব্যাখ্যা করা হয়, সেগুলোর কোনো ব্যাখ্যাই তার কাছে সম্ভব হতো না।
নতুন ধারণাগুলোকে গ্রহণ করে— যা আগে ভৌত বিজ্ঞানের মধ্যে ছিল না— বিজ্ঞান ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান জটিল কাঠামো নির্মাণ করতে পেরেছে, যা ক্রমশ আরও ব্যাপক ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছে।
উদাহরণস্বরূপ— কার্তেসীয় পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে যেমন মৌলিক কণাদের আচরণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, তেমনি “জীবন” ধারণাও বোঝানো যায় না।
ঠিক তেমনি, প্রশ্নটা তোলা যায়— আজকের জীববিদ্যা ও পদার্থবিজ্ঞান কি নিজেদের মধ্যে সেই নীতি ও ধারণা ধারণ করে, যা মানুষের জন্মগত বৌদ্ধিক ক্ষমতার ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম?
আরও গভীরভাবে— সেই ক্ষমতাগুলিকে স্বাধীনতার পরিস্থিতিতে মানুষ যেভাবে অসাধারণ সৃজনশীলতায় ব্যবহার করে, তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম?
আমি মনে করি— এমন বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে জীববিদ্যা বা পদার্থবিজ্ঞান বর্তমানে সেই ধারণাগুলি ধারণ করে।
আর সম্ভবত পরবর্তী শিখরে উঠতে চাইলে— বিজ্ঞানের নতুনভাবে মনোনিবেশ করতে হবে এই সংগঠনী ধারণার দিকে (organising concept), এবং হয়তো নিজেদের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত করতেই হবে— যাতে মানববুদ্ধির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মোকাবিলা করা যায়।
ফুকো:
হ্যাঁ।
সঞ্চালক (এলডার্স):
সম্ভব হলে আমি একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন করার চেষ্টা করি— আপনাদের দু’জনের উত্তরের সূত্র ধরে— কারণ আমি ভয় পাচ্ছি, না হলে বিতর্কটা খুব বেশি প্রযুক্তিগত হয়ে যাবে। আমার ধারণা আপনাদের প্রধান পার্থক্যের একটি নিহিত আছে পদ্ধতিগত পার্থক্যে।
আপনি, মঁসিয়ে ফুকো, বিশেষভাবে আগ্রহী এই ব্যাপারে— একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীরা কীভাবে কাজ করেন, কীভাবে চিন্তা করেন।
অন্যদিকে মি. চমস্কি বেশি মনোযোগী সেই তথাকথিত “what-questions”-এ:
আমাদের ভাষা কেন আছে?
শুধু ভাষা কীভাবে কাজ করে তা নয়, বরং ভাষা থাকার উদ্দেশ্য কী?
একটু বিস্তৃতভাবে বললে:
আপনি, মঁসিয়ে ফুকো, অষ্টাদশ শতকের র্যাশনালিজমকে সীমাঙ্কিত করছেন—
আর আপনি, মি. চমস্কি, অষ্টাদশ শতকের র্যাশনালিজমকে স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতা ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন।
সম্ভবত আমরা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের উদাহরণ দিয়ে এই পার্থক্য আরও স্পষ্ট করতে পারি।
চমস্কি:
প্রথমে বলি— ক্লাসিক্যাল র্যাশনালিজমকে আমি বিশ্লেষণ করি না বিজ্ঞান বা দর্শনের ইতিহাসবিদ হিসেবে; বরং আমি একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এগোই— একজন বিজ্ঞানী হিসেবে, যার কিছু বৈজ্ঞানিক ধারণা রয়েছে, এবং যিনি দেখতে চান অতীতের কোনো এক পর্যায়ে মানুষ কীভাবে সেই ধারণাগুলোর দিকে এগোচ্ছিল— হয়তো সম্পূর্ণ না জেনে, বা না বুঝেই, কোন দিকে তারা পৌঁছাতে চাইছিল।
অর্থাৎ আপনি বলতে পারেন— ইতিহাসকে আমি দেখি না একজন প্রাচীন-সন্ধানী (antiquarian) হিসেবে, যিনি সপ্তদশ শতকের চিন্তাভাবনাকে পুরোপুরি নির্ভুলভাবে পুনর্গঠন করতে চান—
আমি সেই কাজকে ছোট করে দেখতে চাই না— কিন্তু সেটি আমার কাজ নয়।
আমি ইতিহাসকে দেখি একজন শিল্পপ্রেমীর মতো— যিনি সেই যুগে তাকান মূল্যবান কিছু খুঁজে বের করতে; আর সেই মূল্য অংশত আসে এই বর্তমান দৃষ্টিকোণ থেকে, যেটা দিয়ে তিনি অতীতকে বিচার করছেন।
এবং আমি মনে করি— অন্য পদ্ধতির বিরোধিতা না করেও— আমার এই পদ্ধতি মোটেই অযৌক্তিক নয়।
আমরা বর্তমান বুঝের ওপর দাঁড়িয়ে অতীতের বৈজ্ঞানিক চিন্তার দিকে ফিরে তাকাতে পারি, এবং দেখতে পারি— সেই যুগের মহান মেধাবীরা, তাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে, কীভাবে এমন ধারণার দিকে হাতড়ে এগোচ্ছিলেন— যেগুলোর পূর্ণতা সম্পর্কে তারা নিজেরাও সচেতন ছিলেন না।
উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—
এই কাজটি যে কেউ নিজের চিন্তা সম্পর্কেই করতে পারেন—
অবশ্যই নিজেকে অতীতের মহামনীষীদের সঙ্গে তুলনা না করেও।
এলডার্স:
কেন নয়?
চমস্কি:
…দেখা যেতে পারে…
এলডার্স:
কেন নয়?
চমস্কি:
ঠিক আছে [হেসে], যে কেউ এখন যা জানেন তা বিবেচনা করে প্রশ্ন করতে পারেন— বিশ বছর আগে তিনি কী জানতেন? তখন তিনি অস্পষ্টভাবে হলেও এমন কিছু বুঝতে চেষ্টা করছিলেন— যার সত্যিকারের অর্থ তিনি এখন বুঝতে পারছেন… যদি তিনি সৌভাগ্যবান হন!
ঠিক তেমনই আমি মনে করি— অতীতের দিকে তাকানো সম্ভব, তা বিকৃত না করেও। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি সপ্তদশ শতকের দিকে তাকাতে চাই। যখন আমি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতককে দেখি, তখন বিশেষভাবে নজরে আসে— কীভাবে ডেকার্ত ও তাঁর অনুসারীরা মন-কে শরীর থেকে আলাদা একটি চিন্তাশীল সত্তা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।
যদি আমরা দেখি কেন তাঁরা এই দ্বিতীয় সত্তা— মন বা চিন্তাশীল উপাদানের ধারণা গ্রহণ করলেন—
কারণ ডেকার্ত নিজেকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিলেন (সঠিক বা ভুল— সে প্রসঙ্গ এখানে প্রাসঙ্গিক নয়)—
যে শারীরিক জগতের ঘটনা— এমনকি আচরণ ও মনোবিজ্ঞানের অনেক অংশও— যেমন সংবেদন— ব্যাখ্যা করা যায় তাঁর মতে পদার্থবিদ্যার নিয়ম দিয়ে—
যদিও আজ আমরা জানি এটি ভুল—
অর্থাৎ বস্তু একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খায়, ঘোরে, নড়ে— এ ধরনের যান্ত্রিক নীতির সাহায্যে।
তিনি মনে করতেন এমন যান্ত্রিক নীতির দ্বারা কিছু ঘটনার ব্যাখ্যা সম্ভব—
কিন্তু পরে তিনি লক্ষ্য করলেন— কিছু ঘটনা আছে যেগুলিকে এই নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।
তাই তিনি একটি সৃজনশীল নীতি প্রস্তাব করেন— সেই বিভ্রান্তিকর ক্ষেত্রের ব্যাখ্যার জন্য—
মনের নীতি—
যার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
পরে তাঁর অনুসারীরা— এমনকি যারা নিজেদের কার্তেসীয় বলতেন না কিংবা বিরোধী-যুক্তিবাদী বলতেন—
তারা “নিয়মের ভিতরে সৃষ্টি” (creation within a system of rule)-এর ধারণাটি আরও বিকশিত করেন।
আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাব না—
কিন্তু আমার নিজস্ব গবেষণা আমাকে শেষ পর্যন্ত উইলহেম ভন হামবোল্টের কাছে নিয়ে গেছে—
যিনি নিজেকে কখনও কার্তেসীয় মনে করেননি—
তবুও ভিন্ন ঐতিহাসিক সময়, ভিন্ন কাঠামো ও ভিন্ন অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে—
এক বিস্ময়কর ও স্থায়ী গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে—
“অভ্যন্তরীণ রূপ” (internalised form) ধারণাটি বিস্তৃত করেন—
যা মূলত নিয়মের ভেতরে স্বাধীন সৃষ্টিশীলতা—
কার্তেসীয়দের একই সমস্যাগুলোর মোকাবিলায়—
তাদের পথেরই এক পরিবর্তিত উন্নত রূপে।
এখন আমি বিশ্বাস করি— এবং এ ক্ষেত্রে অনেক সহকর্মীর সঙ্গে আমার মতভেদ আছে—
ডেকার্তের “দ্বিতীয় সত্তা” (মন) প্রতিষ্ঠা করা মোটেই অতিবিদ্যাগত বা বিজ্ঞানের বিরোধী পদক্ষেপ ছিল না—
বরং এটি ছিল একটি বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ।
এটি বহু ক্ষেত্রে নিউটনের সেই বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির মতো—
যখন নিউটন “দূর-প্রভাব” (action at a distance) ধারণা প্রস্তাব করেন।
তখন সেও ছিল রহস্যময়, প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বাইরে—
কিন্তু লক্ষ্য ছিল—
এই অজানা ক্ষেত্রকে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের মধ্যে একীভূত করা—
একটি নতুন তত্ত্বের সাহায্যে—
যেখানে এই ধারণাগুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা ও স্পষ্ট করা সম্ভব।
আমার মনে হয়, ডেকার্ত যখন মনকে দ্বিতীয় এক সত্তা হিসেবে প্রস্তাব করলেন, তখন সেও মূলত একই ধরনের বৌদ্ধিক পদক্ষেপই নিয়েছিলেন। অবশ্য যেখানে নিউটন সফল হয়েছিলেন, ডেকার্ত সেখানে ব্যর্থ হন; অর্থাৎ তিনি মনের জন্য এমন একটি গাণিতিক তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করতে পারেননি—যেমনটি নিউটন ও তাঁর অনুসারীরা পদার্থগত সত্তার জন্য করেছিলেন, যেখানে দূর থেকে প্রভাব বিস্তার কিংবা পরে তড়িৎচুম্বকত্বের মতো একসময় “রহস্যময়” বলে বিবেচিত ধারণাগুলিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু এই ব্যর্থতা আমাদের সামনে একটি কাজ নির্ধারণ করে দেয়—যদি বলা যায়—মনের এই গাণিতিক তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও উন্নত করা। অর্থাৎ, এমন একটি তত্ত্ব যা নিখুঁতভাবে সংজ্ঞায়িত হবে, স্পষ্টভাবে রূপায়িত হবে, বিমূর্ত হবে, এবং যার বাস্তবভিত্তিক ফলাফল থাকবে—যার সাহায্যে আমরা জানতে পারব তত্ত্বটি সঠিক না ভুল, সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে কি পথভ্রষ্ট হচ্ছে। এবং একই সঙ্গে তাতে থাকবে গাণিতিক বিজ্ঞানের সব বৈশিষ্ট্য—কঠোর যুক্তিবদ্ধতা, নির্ভুলতা, আর এমন একটি কাঠামো যার সাহায্যে অনুমান থেকে সিদ্ধান্ত導 করা যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের দিকে ফিরে তাকাই, এবং কিছু বিন্দু শনাক্ত করার চেষ্টা করি—যা আমার মতে সত্যিই সেখানে উপস্থিত, যদিও আমি স্বীকার করি এবং জোর দিতেও চাই—যে সেই সময়ের চিন্তাবিদেরা নিজেদের যুগে হয়তো বিষয়টিকে এভাবে দেখেননি।
এল্ডার্স– মঁসিয়ে ফুকো, আমি ধরে নিচ্ছি এই বিষয়ে আপনার কঠোর সমালোচনা থাকবে?
ফুকো —
না… কেবল এক–দুটি ছোট ঐতিহাসিক ব্যাপার আছে। আপনি তাদের কারণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে আমার মূল আপত্তি নেই। তবে একটি বিষয় অবশ্যই যোগ করা যেতে পারে: আপনি যখন ডেকার্তের চিন্তায় সৃজনশীলতার ধারণা আরোপ করেন, তখন মনে হয় আপনি হয়তো এমন একটি ধারণা তাঁর ওপর বসাচ্ছেন যা প্রকৃতপক্ষে তাঁর উত্তরসূরি অথবা কিছু সমসাময়িক চিন্তাবিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পাওয়া যায়। ডেকার্তের মতে মন খুব বেশি সৃষ্টিশীল নয়—মন শুধু দেখে, উপলব্ধি করে এবং প্রমাণের আলোতে আলোকিত হয়।
ডেকার্ত যে সমস্যাটি কখনও সমাধান করতে পারেননি, কিংবা পুরোপুরি আয়ত্তে আনতে পারেননি, সেটি হলো—কীভাবে মন একটি স্বচ্ছ ও স্বতন্ত্র ধারণা থেকে আরেকটিতে পৌঁছায়, এবং এই যাত্রাপথকে কোন প্রামাণ্য অবস্থান দেওয়া হবে। তাই আমি ডেকার্তের দর্শনে সেই মুহূর্তে কোনো সৃজনশীলতা দেখি না যখন মন সত্যকে উপলব্ধি করে, কিংবা এক সত্য থেকে আরেক সত্যে যাওয়ার ক্ষেত্রেও কোনো প্রকৃত সৃষ্টির দর্শন দেখি না।
বরং, আপনি যা খুঁজছেন তার অনেক কাছাকাছি জিনিস পাওয়া যাবে পাস্কাল এবং লাইবনিজের দর্শনে। পাস্কাল ও খ্রিস্টীয় অগাস্টিনীয় চিন্তাধারায় মনকে দেখা হয় গভীর আত্ম-অন্তরালময় এক সত্তা হিসেবে—যা নিজের ভেতর ভাঁজ হয়ে থাকে, এক ধরনের অচেতনের স্পর্শে স্পর্শিত হয়, এবং আত্মগভীরতার মধ্য দিয়ে নিজের সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায়। এই কারণেই আপনি যে Port Royal ব্যাকরণের কথা বলেছেন—সেটি আমায় কার্তেসীয়ের তুলনায় অনেক বেশি অগাস্টিনীয় বলে মনে হয়।
আর লাইবনিজের চিন্তায় আপনি নিশ্চয়ই এমন একটি বিষয় পাবেন যা আপনার আগ্রহের—মনের গভীরে যুক্তির এক সুসংগঠিত জাল পূর্বলিখিত থাকে, যা একধরনের বৈবেকিক অচেতনতা—যুক্তির সেই রূপ, যা এখনো পুরোপুরি স্পষ্ট হয়নি। মোনাড বা সত্তা ধীরে ধীরে তাকে উন্মোচন করে এবং তার সাহায্যে সে গোটা বিশ্বকে বুঝতে সক্ষম হয়। ঠিক এই জায়গাতেই আমি একটি ছোটখাটো সমালোচনা রাখতে চাই।
এল্ডার্স:
মি. চমস্কি, এক মুহূর্ত দয়া করে।
আমি মনে করি না এটা কোনো ঐতিহাসিক সমালোচনা করার প্রশ্ন; বরং এই মৌলিক ধারণাগুলি সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মতামত গঠন করার ব্যাপার…
ফুকো:
কিন্তু নিজের মৌলিক মতামত তো এমন নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের মাধ্যমেই প্রমাণ করা যায়।
এল্ডার্স:
হ্যাঁ, ঠিক আছে। কিন্তু আমি আপনার History of Madness-এর কয়েকটি অংশ মনে করতে পারি, যেখানে আপনি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীকে দমন, দমন-পীড়ন এবং বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করেছেন; অথচ মি. চমস্কির কাছে এই সময়টা সৃজনশীলতা ও স্বতন্ত্রতার ভরপুর এক যুগ।
কেন আমরা সেই সময়েই প্রথমবারের মতো বন্ধ মানসিক হাসপাতাল বা উন্মাদাগার দেখতে পাই? আমার মনে হয় এটি খুবই মৌলিক একটি প্রশ্ন…
ফুকো:
…হ্যাঁ, সৃজনশীলতা নিয়ে!
কিন্তু আমি জানি না—হয়তো মি. চমস্কি এ বিষয়ে কথা বলতে চাইবেন…
এল্ডার্স:
না, না, না, দয়া করে আপনি চালিয়ে যান। বলুন।
ফুকো:
না, আমি এই কথাটি বলতে চাই: ঐতিহাসিক গবেষণাগুলিতে যা আমি করতে পেরেছি বা করার চেষ্টা করেছি, সেখানে আমি নিঃসন্দেহে খুবই সামান্য জায়গা দিয়েছি সেই বিষয়টিকে, যাকে আপনি ব্যক্তি-মানুষের সৃজনশীলতা বলতে পারেন—তাদের সৃষ্টিশক্তিকে, নিজে নিজে উদ্ভাবন করার ক্ষমতাকে, স্বতন্ত্রভাবে ধারণা, তত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক সত্য উদ্ভাবনের যোগ্যতাকে।
কিন্তু আমি মনে করি আমার সমস্যা মি. চমস্কির সমস্যার থেকে ভিন্ন। মি. চমস্কি ভাষাতাত্ত্বিক বেহেভিয়ারিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছেন—যে ধারাটি বক্তার সৃজনশীলতাকে প্রায় কিছুই মনে করত না; বক্তাকে ধরে নেওয়া হতো এমন এক পৃষ্ঠতল হিসেবে, যেখানে সামান্য সামান্য করে তথ্য জমা হয়, পরে সে সেগুলো মিলিয়ে নেয়।
কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে, বা আরও সাধারণভাবে বললে ভাবনার ইতিহাসে, সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।
জ্ঞান-ইতিহাস বহুদিন ধরে দুটি দাবিকে মানার চেষ্টা করেছে। প্রথম দাবি হলো আরোপের দাবি: প্রতিটি আবিষ্কারকে শুধু নির্দিষ্ট স্থান-কালেই স্থাপন করা নয়, বরং তা কার—এটিও নির্ধারণ করতে হবে; এর একজন উদ্ভাবক থাকবে, একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি থাকবে। অন্যদিকে সমষ্টিগত বা সামগ্রিক ঘটনা—যেগুলো সংজ্ঞা অনুযায়ী “কারও” বলে আরোপ করা যায় না—সেগুলো সাধারণত গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হয়: সেগুলোকে আজও বর্ণনা করা হয় “ঐতিহ্য”, “মানসিকতা”, “প্রবণতা” ইত্যাদি শব্দে; এবং এগুলোকে উদ্ভাবকের “মৌলিকতা”-র পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা হয়। সংক্ষেপে, এটি হলো জ্ঞান-ইতিহাসে ‘অধিকারী বিষয়ের সার্বভৌমত্ব’-এর নীতি।
দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে এমন এক দাবি যা আর বিষয়টিকে (subject) রক্ষা করে না, বরং সত্যকে রক্ষা করে: ইতিহাস যাতে সত্যকে কলুষিত না করতে পারে, তার জন্য প্রয়োজন এই নয় যে সত্য ইতিহাসের মধ্যেই গঠিত হবে; বরং সত্য ইতিহাসে কেবল প্রকাশিত হবে। সত্য মানুষের চোখের আড়ালে, কিছু সময়ের জন্য অধরা অবস্থায়, অন্ধকারে স্থির হয়ে থাকবে—উন্মোচিত হওয়ার অপেক্ষায়। সত্যের ইতিহাস মূলত তার বিলম্ব, তার পতন, অথবা সেই বাধাগুলির অপসরণ—যেগুলো তাকে আজ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখাতে বাধা দিয়েছে। জ্ঞানের ঐতিহাসিক মাত্রা সত্যের তুলনায় সর্বদাই নেতিবাচক বলে বিবেচিত হয়েছে।
এই দুই দাবিকে কীভাবে একে-অন্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা বোঝা কঠিন নয়: সমষ্টিগত ক্রমের ঘটনাগুলি—যেমন “সাধারণ চিন্তাভাবনা”, একটি যুগের “পূর্বাধারণ”, “মিথ”—এসব গঠন করে সেই প্রতিবন্ধকতা, যেগুলো জ্ঞান-বিষয়কে অতিক্রম করতে হয় বা অগ্রাহ্য করতে হয় সত্যে পৌঁছানোর জন্য; তাকে সত্য “আবিষ্কার” করতে হলে থাকতে হয় এক “অকেন্দ্রিক” অবস্থানে। এক দিক থেকে এটি বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে একধরনের “রোমান্টিকতা” আহ্বান করে: সত্যের মানুষের একাকিত্ব, ইতিহাসের ভিতর দিয়ে এবং তাকে পাশ কাটিয়ে “আদি”-র দিকে ফিরে যাওয়া মৌলিকতার উন্মোচন।
আমার মনে হয় আরও গভীরভাবে দেখলে বিষয়টি হলো—জ্ঞানতত্ত্ব (theory of knowledge) এবং জ্ঞানের বিষয় (subject of knowledge)–কে জ্ঞান-ইতিহাসের উপরে আরোপ বা চাপিয়ে দেওয়া।
বং যদি বিষয় (subject) ও সত্যের সম্পর্ককে বোঝা—আসলে জ্ঞানেরই এক ধরনের ফল হয়? যদি ‘বোঝা’ হয় এক জটিল, বহুবিধ, অ-ব্যক্তিক গঠন—যা “বিষয়ের অধীন” নয়, বরং সত্যের প্রভাব উৎপন্ন করে? তাহলে আমাদের উচিত হবে বিজ্ঞানের ইতিহাস যে সমগ্র মাত্রাটিকে এত দিন নেতিবাচক বলে বিবেচনা করেছে, তাকে ইতিবাচকভাবে সামনে আনা; জ্ঞানকে একটি সমষ্টিগত অনুশীলন হিসেবে তার উৎপাদনক্ষমতা বিশ্লেষণ করা; এবং ফলত ব্যক্তিদের ও তাদের “জ্ঞান”-কে এমন এক জ্ঞানের বিকাশের মধ্যে পুনরায় স্থাপন করা, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে—এবং যেগুলো আমরা নথিবদ্ধ ও বর্ণনা করতে পারি।
আপনি হয়তো বলবেন যে মার্কসবাদী বিজ্ঞান-ইতিহাসবিদরা তো অনেকদিন ধরেই এ কাজ করছেন। কিন্তু তাদের কাজের ধরন দেখলে—বিশেষত তারা চেতনা, আদর্শবাদ (ideology) ও বিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে যেভাবে ব্যবহার করেন—দেখা যায় যে তারা মূলত জ্ঞানতত্ত্বের থেকে কমবেশি বিচ্ছিন্ন।
যাই হোক, আমার আগ্রহ আসলে এটাই: জ্ঞানের আবিষ্কারগুলির ইতিহাসের জায়গায় ‘বোঝার’ রূপান্তরগুলিকে রাখা। তাই সৃজনশীলতার প্রসঙ্গে মি. চমস্কির তুলনায় আমার অবস্থান আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কারণ আমার উদ্দেশ্য হলো ‘জ্ঞানী বিষয়ের’ দ্বিধাকে মুছে দেওয়া, আর তার উদ্দেশ্য হলো ‘বক্তা বিষয়’-এর দ্বিধাকে পুনরায় উপস্থিত করা।
কিন্তু তিনি যদি সেই দ্বিধাকে আবার ফিরে আনতে পারেন, যদি তিনি তা বর্ণনা করতে পারেন, তা সম্ভব হয়েছে কারণ তিনি তা করতে সক্ষম। ভাষাবিদরা বহুদিন ধরেই ভাষাকে একটি সমষ্টিগত মূল্যের ব্যবস্থা হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু ‘বোঝার’—অর্থাৎ এমন এক সমষ্টিগত নিয়মসমষ্টি, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জ্ঞান উৎপাদনকে সম্ভব করে—এমন ধারণাকে খুব কমই কেউ অধ্যয়ন করেছেন। তবু এটি পর্যবেক্ষকের কাছে স্পষ্ট কিছু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে।
উদাহরণস্বরূপ ধরুন অষ্টাদশ শতকের শেষে চিকিৎসাবিদ্যাকে। ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ সালের মাঝামাঝি যেকোনো কুড়িটি চিকিৎসা-গ্রন্থ পড়ুন, তারপর ১৮২০ থেকে ১৮৩০ সালের কুড়িটি গ্রন্থ পড়ুন—আর আমি বলব, একেবারে এলোমেলোভাবে বললেও, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই সবকিছু বদলে গেছে: কী নিয়ে কথা হচ্ছে, কীভাবে বলা হচ্ছে, শুধু ওষুধ-প্রতিকার বা রোগ ও তার শ্রেণিবিন্যাসই নয়, দৃষ্টিভঙ্গি পর্যন্ত। এর জন্য দায়িত্বশীল কে? এর রচয়িতা কে? আমার মনে হয়, বিছা-কে (Bichat) দায়ী করা—বা একটু প্রসারিত করে প্রথম অ্যানাটমিক্যাল ক্লিনিশিয়ানদের দায়ী করা—অস্বাভাবিকভাবে সরলীকৃত হয়। এটি আসলে চিকিৎসাবিদ্যার ‘বোঝার’ সমষ্টিগত ও জটিল রূপান্তরের ফল, তার অনুশীলন ও তার নিয়মের ভিতরে।
এবং এই রূপান্তর কোনো নেতিবাচক ঘটনা নয়: এটি নেতিবাচকতার দমন, বাধার অপসারণ, পূর্বাগ্রহের অবলুপ্তি, পুরোনো মিথ ত্যাগ, অযৌক্তিক বিশ্বাসের পশ্চাৎপসরণ—এবং অভিজ্ঞতা ও যুক্তির প্রতি এক মুক্ত প্রবেশ। এটি আসলে সম্পূর্ণ নতুন এক নিয়ম-ব্যবস্থার প্রয়োগ—তার নিজস্ব বাছাই, বর্জন, সিদ্ধান্ত, সীমাবদ্ধতা, তার নিজস্ব অন্তর্নিহিত যুক্তি, পরিমিতি এবং অচলায়তন নিয়ে—যা উৎপত্তিস্থলকেও পরিবর্তিত করে। এবং এই কার্যপ্রণালীর মধ্যেই বোঝার স্বরূপ বিদ্যমান।
তাই, যখন কেউ জ্ঞানের ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তখন দেখা যায় দুটি প্রধান দিক আছে বিশ্লেষণের। একদিকে, আমাদের দেখাতে হয় কীভাবে, কোন শর্তে এবং কোন কারণে বোঝা তার গঠনমূলক নিয়মগুলোকে পরিবর্তিত করে—একজন মৌলিক “উদ্ভাবক” বা “সত্য-আবিষ্কারক” ধারণার আশ্রয় না নিয়েই। অন্যদিকে, আমাদের দেখাতে হয় যে কীভাবে বোঝার নিয়মগুলির কার্যকারিতা একজন ব্যক্তির মধ্যে নতুন ও অদৃষ্টপূর্ব জ্ঞান উৎপাদন করতে পারে।
এই জায়গাতেই আমার কাজ—অসম্পূর্ণ পদ্ধতিতে এবং অনেক নিম্নমানের পর্যায়ে—মি. চমস্কির প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়: কীভাবে অল্প কিছু নিয়ম বা নির্দিষ্ট উপাদান থেকে সম্পূর্ণ নতুন, কখনোই উৎপন্ন না হওয়া জ্ঞানের সমগ্রতাগুলি ব্যক্তির মাধ্যমে আলোকিত হতে পারে—এই হিসাব প্রদান করা।
এই সমস্যার সমাধানে মি. চমস্কিকে বিষয়ের দ্বিধাকে আবার ব্যাকরণের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রবেশ করাতে হয়। আর আমি যেই ইতিহাস-ক্ষেত্রে কাজ করি, সেখানে এই সমস্যার সমাধান করতে হলে উল্টোটা করতে হয়: ব্যক্তিগত জ্ঞানের খেলায় বোঝার দৃষ্টিভঙ্গি, তার নিয়ম, তার সিস্টেম, তার সমষ্টিগত রূপান্তরগুলিকে প্রবেশ করাতে হয়।
দুটো ক্ষেত্রেই ‘সৃজনশীলতা’র সমস্যা একইভাবে সমাধানযোগ্য নয়; বরং একই ভাষায় এই সমস্যাকে formul করাও যায় না, কারণ সমস্যাটি যেসব ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ভিতরে তোলা হয়, সেগুলির অবস্থানই সম্পূর্ণ আলাদা।
চমস্কি:
আমার মনে হয় আংশিকভাবে আমরা একটু ভিন্ন দিকে কথা বলছি, কারণ আমরা ‘creativity’ শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করছি। আসলে বলা ভালো, আমি ‘creativity’ শব্দটিকে কিছুটা ব্যতিক্রমী অর্থে ব্যবহার করি, আর সেজন্য দায়টা আমার ওপরই বর্তায়, আপনার ওপর নয়। আমি যখন ‘creativity’ শব্দটি ব্যবহার করি, তখন এতে সেই মূল্যবোধের ধারণা যোগ করছি না, যা সাধারণত সৃজনশীলতা বলতে আমরা বুঝি। আপনি যখন বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতা বলেন, আপনি ঠিকই নিউটনের মতো কৃতিত্বের কথা বলছেন। কিন্তু আমি যে প্রসঙ্গে সৃজনশীলতার কথা বলেছি, সেটা একটি স্বাভাবিক মানবিক ক্রিয়া।
আমি এমন ধরনের সৃজনশীলতার কথা বলছি, যা যে-কোনো শিশু দেখায়—যখন সে নতুন পরিস্থিতিকে বুঝতে পারে, ঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারে, সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে, সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলতে পারে, নিজের মতো করে নতুনভাবে ভাবতে পারে ইত্যাদি। আমি মনে করি এগুলিকে সৃজনশীল কাজ বলা ঠিকই হবে—কিন্তু অবশ্যই নিউটনের কাজের সমতুল্য ভেবে নয়।
আসলে এটা খুব সম্ভব যে শিল্প বা বিজ্ঞানের উচ্চস্তরের সৃজনশীলতা—যা সাধারণতার সীমা ছাড়িয়ে যায়—তা এমন মানবিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে, যা হয়তো অধিকাংশ মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় থাকে না, এবং যা প্রতিদিনের জীবনের স্বাভাবিক সৃজনশীলতার অংশ নয়।
এখন আমার বিশ্বাস হলো: বিজ্ঞান এই স্বাভাবিক সৃজনশীলতাকে একটি গবেষণার বিষয় হিসেবে নিজের পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে—হয়তো ভবিষ্যতে তা করতে সক্ষমও হবে। কিন্তু আমি মনে করি না—এবং সন্দেহ নেই আপনি-ও একমত হবেন—যে বিজ্ঞান নিকট ভবিষ্যতে প্রকৃত সৃজনশীলতা, অর্থাৎ মহৎ শিল্পী বা মহৎ বিজ্ঞানীর কৃতিত্বকে আয়ত্ত করার আশা করতে পারে। বিজ্ঞানের পক্ষে এই অনন্য ঘটনাগুলিকে ধারণ করার কোনো বাস্তব সম্ভাবনা নেই। আমি যে সৃজনশীলতার কথা বলছিলাম, তা এই নিম্নস্তরের, প্রতিদিনের মানবিক সৃজনশীলতা।
এখন, আপনি বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে যা বলছেন, তা আমার কাছে সঠিকও এবং অত্যন্ত আলোকপ্রদ—বিশেষত মনোবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান এবং মনের দর্শন নিয়ে ভবিষ্যতে যে ধরনের গবেষণা এগোতে পারে, তার জন্য অত্যন্ত উপযোগী।
আমার মনে হয় গত কয়েক শতকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সময় কিছু বিষয় দমন করা হয়েছে বা পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে।
উদাহরণস্বরূপ, আমি যে নিম্নস্তরের সৃজনশীলতার কথা বলছি, তা দ্যকার্তের (Descartes) লেখাতেও উপস্থিত ছিল। যেমন তিনি যখন বলেন টিয়াপাখি শুধু শোনা কথার নকল করতে পারে, কিন্তু মানুষ পরিস্থিতির উপযোগী নতুন কথা বলতে পারে—এবং যখন তিনি এটিকে সেই বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেন যা পদার্থবিজ্ঞানের সীমা নির্ধারণ করে এবং আমাদের নিয়ে যায় মনের বিজ্ঞানে (আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে)—তখন তিনি আসলে সেই ধরনের সৃজনশীলতার কথাই বলছেন, যেটির কথা আমি বলছি। এবং এই বিষয়ে আপনি যে দিকগুলো তুলে ধরলেন, তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।
কিন্তু এই ধারণাগুলি—এমনকি বাক্যগঠনের সংগঠনসংক্রান্ত ধারণাটিও—স্যার উইলিয়াম জোন্স এবং অন্যান্যের কাজের পর যে বিশাল অগ্রগতি ঘটে, অর্থাৎ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিকাশে, সেই সময় মোটামুটি উপেক্ষিত হয়েছিল।
কিন্তু এখন, আমার মনে হয়, আমরা সেই সময়কে অতিক্রম করতে পারি—যখন এসব বিষয় ভুলে যাওয়া জরুরি ছিল, অথবা এমন ভান করা হয়েছিল যেন এসব ঘটনা কোনও বাস্তব সত্তা নয়, এবং গবেষণার দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের যুগে—এবং আমার দৃষ্টিতে কাঠামোবাদের ভাষাবিজ্ঞানেও—এবং আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানের অনেকাংশে, আসলে মন ও আচরণ নিয়ে অভিজ্ঞতাবাদী ধারার বিস্তৃত অংশেই, এসব সীমাবদ্ধতা পাশ কাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
কিন্তু এখন আমরা সেই সীমাবদ্ধতাগুলি সরাতে পারি এবং ঠিক সেই বিষয়গুলির দিকে ফিরে যেতে পারি—যেগুলো সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিন্তা, তর্ক এবং জল্পনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল—এবং এগুলোকে মানুষের একটি অনেক বিস্তৃত এবং, আমার বিশ্বাস, গভীরতর বিজ্ঞানভিত্তিক বোঝার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।
এই বিজ্ঞান হয়তো উদ্ভাবন, সৃজনশীলতা, স্বাধীনতা, নতুন সত্তা বা নতুন চিন্তাসত্তা ও আচরণ সৃষ্টি—এসবকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারবে না, কিন্তু অন্তত তাদের ভূমিকা আরও সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে পারবে—যেখানে এই নতুন সৃষ্টিগুলি নিয়ম ও বিন্যাসের কোনও ব্যবস্থার ভেতর থেকেই উদ্ভূত হয়।
আমি মনে করি—এই ধারণাগুলির সঙ্গে এখন আমরা কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে পারি।
এল্ডার্স:
আচ্ছা, প্রথমেই কি আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ করতে পারি—আপনারা কি উত্তরগুলো এত লম্বা না করে একটু সংক্ষিপ্ত রাখতে পারেন? [ফুকো হাসেন।]
আপনারা যখন সৃজনশীলতা এবং স্বাধীনতার কথা বলছেন, তখন আমার মনে হয়—যদি কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে—তা এই কারণে যে মি. চমস্কি অল্প কিছু নিয়ম থেকে অসীম সম্ভাবনার প্রয়োগের দিক থেকে শুরু করছেন; আর আপনি, মি. ফুকো, জোর দিচ্ছেন আমাদের ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিয়তিবাদের “জাল”-এর অনিবার্যতার ওপর—যা নতুন ধারণা আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
হয়তো আমরা বিষয়টি পরিষ্কার করতে পারি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ না করে, বরং আমাদের নিজেদের চিন্তাপ্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে।
যখন আপনি একটি নতুন মৌলিক ধারণা খুঁজে পান, মি. ফুকো, তখন কি আপনি মনে করেন—আপনার ব্যক্তিগত সৃজনশীলতার স্তরে এমন কিছু ঘটে যা আপনাকে অনুভব করায় যে আপনি যেন মুক্ত হচ্ছেন; যে কিছু নতুন সৃষ্টি হয়েছে? পরে হয়তো বোঝা যায় যে তা একেবারে নতুন ছিল না। কিন্তু আপনি নিজে কি বিশ্বাস করেন যে আপনার ব্যক্তিত্বের ভেতরে—সৃজনশীলতা ও স্বাধীনতা একসঙ্গে কাজ করে? নাকি আপনি তা মনে করেন না?
ফুকো:
ওহ, জানেন, আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমস্যাটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি না…
এল্ডার্স:
কেন ?
ফুকো:
…এ ধরনের প্রশ্নে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গুরুত্ব ততটা নেই। না, আমি মনে করি যে মি. চমস্কি যা বলেছেন এবং আমি যা দেখানোর চেষ্টা করেছি, তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে বেশ শক্তিশালী মিল রয়েছে। অর্থাৎ, বাস্তবে কেবল সম্ভাব্য সৃষ্টিগুলিই থাকে, সম্ভাব্য উদ্ভাবনই থাকে। ভাষা বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেউ কেবল নতুন কিছু উৎপাদন করতে পারে তখনই, যখন সে এমন কিছু নিয়ম প্রয়োগে আনে, যা সেই উক্তির গ্রহণযোগ্যতা বা ব্যাকরণগততা নির্ধারণ করে, অথবা জ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই উক্তির বৈজ্ঞানিক চরিত্র নির্ধারণ করে।
সুতরাং, আমরা মোটামুটি বলতে পারি যে মি. চমস্কির আগে ভাষাবিদরা মূলত উক্তি নির্মাণের নিয়মগুলোর ওপর জোর দিতেন, আর প্রতিটি নতুন উক্তি বা নতুন উক্তি শোনার মাধ্যমে যে উদ্ভাবন ঘটে, তার ওপরে কম গুরুত্ব দিতেন। আর বিজ্ঞান বা চিন্তার ইতিহাসে আমরা ব্যক্তিগত সৃষ্টির ওপর বেশি জোর দিয়েছি, এবং যে সামষ্টিক, সাধারণ নিয়মগুলো প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এবং এমনকি প্রত্যেক দার্শনিক নতুনত্বের মধ্যে অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়—সেগুলোকে পাশে সরিয়ে, ছায়ায় ফেলে রেখেছিলাম।
এবং সে অর্থে, যখন আমি নিশ্চয়ই ভুলভাবে বিশ্বাস করি যে আমি কিছু নতুন বলছি, তখনও আমি সচেতন থাকি যে আমার বক্তব্যে কিছু নিয়ম কাজ করছে—শুধু ভাষাগত নিয়ম নয়, জ্ঞানতাত্ত্বিক নিয়মও—এবং সেই নিয়মগুলোই সমকালীন জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে।
চমস্কি:
ঠিক আছে, হয়তো আমি আমার নিজের কাঠামোর ভেতর থেকে এই মন্তব্যগুলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাতে পারি—যা হয়তো বিষয়টিকে কিছুটা আলোকিত করবে।
আসুন আবার একটি মানবশিশুর কথা ভাবি, যার মনে এমন এক ধরনের স্কিমা থাকে যা নির্ধারণ করে সে কী ধরনের ভাষা শিখতে পারে। ঠিক আছে। আর তারপর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে খুব দ্রুত ভাষাটি আয়ত্ত করে ফেলে—যে ভাষা এই অভিজ্ঞতারই অংশ, বা যার মধ্যে এই অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত।
এটি একটি স্বাভাবিক কাজ; অর্থাৎ, এটি স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তার কাজ, কিন্তু একই সঙ্গে এটি অত্যন্ত সৃজনশীল কাজ।
যদি কোনও মঙ্গলগ্রহবাসী এই প্রক্রিয়াটি দেখত—অর্থাৎ এক অপরিসীম, জটিল, সূক্ষ্ম জ্ঞানতন্ত্রকে শিশুরা কীভাবে এত সামান্য তথ্যের ভিত্তিতে অর্জন করছে—তাহলে তার কাছে এটিকে এক বিরাট আবিষ্কার ও সৃষ্টির কাজ বলেই মনে হতো। প্রকৃতপক্ষে, আমার মনে হয় সেই কাল্পনিক মঙ্গলবাসী এটি এমনই এক সাফল্য মনে করত, যেমন কোনও পদার্থবিজ্ঞানীকে দেওয়া অল্প তথ্য থেকে একটি পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব উদ্ভাবন করা।
কিন্তু যদি সেই কাল্পনিক মঙ্গলবাসী আরও লক্ষ্য করত যে প্রতিটি স্বাভাবিক মানবশিশু এই সৃজনশীল কাজটি অনায়াসে, একইভাবে এবং কোনও অসুবিধা ছাড়াই সম্পন্ন করে—অন্যদিকে প্রমাণ থেকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে পৌঁছতে প্রতিভাবান মানুষদেরও শতাব্দী ধরে পরিশ্রম করতে হয়—তাহলে যুক্তিবাদী হলে সে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছত যে ভাষাজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে যে জ্ঞানের গঠন দেখা যায়, তা মূলত মানুষের মনের অভ্যন্তরেই নিহিত; আর পদার্থবিজ্ঞানের গঠন এত সরাসরি ভাবে আমাদের মনের ভেতরে রোপিত নয়। আমাদের মন এমনভাবে নির্মিত নয় যে আমরা জগতের ঘটনা দেখলেই তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান সোজা বেরিয়ে আসে, আমরা তা লিখে ফেলি এবং তত্ত্ব তৈরি হয়ে যায়—এভাবে আমাদের মন তৈরি নয়।
তবুও, আমার মনে হয় এখানে একটি সম্ভাব্য সংযোগ রয়েছে, এবং সেটি ব্যাখ্যা করা উপকারী হবে: আমরা আদৌ কীভাবে কোনও ধরনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বানাতে সক্ষম হই? কীভাবে অল্প কয়েকটি প্রমাণ থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞানী, বা প্রতিভাময় ব্যক্তিরা, দীর্ঘ সময় ধরে অন্তত কিছু ক্ষেত্রে কমবেশি গভীর এবং কমবেশি প্রমাণ-সমর্থিত তত্ত্বে পৌঁছে যান?
এটা সত্যিই বিস্ময়কর একটি ব্যাপার।
চমস্কি:
আসলে বিষয়টি এমন যে—যদি এটি সত্য না হতো যে এই বিজ্ঞানীরা, প্রতিভাবান ব্যক্তিরা-সহ, সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের শ্রেণিকে অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে সীমাবদ্ধ করে শুরু করেন, যদি তাঁদের মনের ভিতরেই—অবশ্যই অচেতনভাবে—এমন কোনও নির্দেশনা অন্তর্নিহিত না থাকত যে কোন ধরনের তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে সম্ভব, তাহলে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য থেকে তত্ত্বে পৌঁছনোর যে ‘ইন্ডাক্টিভ’ লাফ, তা একেবারেই অসম্ভব হয়ে যেত। ঠিক যেভাবে—যদি প্রতিটি শিশুর মনে মানবভাষার ধারণাটি এক বিশেষ সংকীর্ণ রূপে অন্তর্নির্মিত না থাকত, তাহলে তথ্য থেকে ভাষাজ্ঞান অর্জনের ইন্ডাক্টিভ লাফটিও অসম্ভব হতো।
সুতরাং, যদিও—ধরা যাক—তথ্য থেকে পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান আহরণ করার প্রক্রিয়া আমাদের মতো জীবের ক্ষেত্রে অনেক বেশি জটিল, অনেক বেশি কঠিন, সময়সাপেক্ষ, এবং যেখানে প্রতিভার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে, তবুও এক অর্থে পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান বা অন্য যে কোনও বিজ্ঞানের তত্ত্ব সৃষ্টি করার সাফল্যটি সাধারণ শিশুর তার ভাষার কাঠামো আবিষ্কারের যে ক্ষমতা, তারই অনুরূপ কিছু উপর দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ, উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজন প্রথম থেকেই সম্ভাব্য তত্ত্বের শ্রেণির উপর একটি সীমাবদ্ধতা—একটি মৌলিক নিষেধাজ্ঞা। যদি আপনি শুরুতেই না জানতেন যে কেবল নির্দিষ্ট কিছু জিনিসই তত্ত্ব হিসেবে সম্ভব, তাহলে কোনও ধরনের ইন্ডাকশনই সম্ভব হতো না। আপনি তথ্য থেকে যেকোনো দিকে, অসীমভাবে যাত্রা করতে পারতেন। আর বিজ্ঞানের যে একমুখী অগ্রগতি ও অভিসৃতি (convergence) রয়েছে, তা-ই দেখায় যে এই প্রাথমিক কাঠামো এবং সীমাবদ্ধতাগুলি বাস্তবেই বিদ্যমান।
যদি আমরা সত্যিই বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির তত্ত্ব উন্নত করতে চাই—বা ওই অর্থে শিল্পসৃষ্টির তত্ত্বও—তাহলে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে ঠিক সেই সমস্ত অবস্থার উপর, যা একদিকে আমাদের সম্ভাব্য জ্ঞানের পরিসরকে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, আবার একই সঙ্গে অল্প তথ্য থেকে বিশদ ও জটিল জ্ঞানতন্ত্র গড়ে তোলার ইন্ডাক্টিভ লাফটিকে সম্ভব করে তোলে। আমার মনে হয়, বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতার একটি তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ, কিংবা সাধারণভাবে জ্ঞানতত্ত্বের যেকোনো প্রশ্নের দিকে এগোনোর পথ, এই দিকেই নিহিত।
এল্ডার্স:
ঠিক আছে, যদি আমরা এই প্রাথমিক সীমাবদ্ধতার বিষয়টিকে—তার সমস্ত সৃজনশীল সম্ভাবনাসহ—ধরি, তাহলে আমার মনে হয় মি. চমস্কির ক্ষেত্রে নিয়ম এবং স্বাধীনতা পরস্পরবিরোধী নয়; বরং একে অপরকে কোনো না কোনোভাবে ধারণ করে বা ইঙ্গিত করে। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে, মি. ফুকো, আমার ঠিক বিপরীত ধারণা হয়। আপনি কেন এটিকে বিপরীতভাবে দেখেন? এটি বিতর্কের সত্যিই একটি মৌলিক প্রশ্ন, এবং আমি আশা করি আমরা এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে পারব।
একই সমস্যাটিকে অন্যভাবে বলতে গেলে: repression বা দমন ছাড়া কি কোনো সার্বজনীন জ্ঞানকে কল্পনা করা যায়?
ফুকো:
মি. চমস্কি যা এখন বললেন, তাতে এমন কিছু আছে যা আমার কাছে সামান্য জটিলতা সৃষ্টি করে; হয়তো আমি ভুলভাবে বুঝেছি।
আমি মনে করি আপনি একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কাঠামোর ভিতরে সীমিত সংখ্যক সম্ভাবনার কথা বলছেন। এটি সত্য—যদি আপনি ইতিহাসের খুব ছোট একটি সময়ের দিকে তাকান। কিন্তু যদি আপনি একটি দীর্ঘ সময়কাল বিবেচনা করেন, আমার মনে হয় লক্ষণীয় বিষয়টি হলো—সম্ভাবনার বিস্তার, বিভেদের মাধ্যমে সম্ভাবনার বৃদ্ধি।
অনেক দিন ধরেই এই ধারণা চালু ছিল যে বিজ্ঞান বা জ্ঞান একটি নির্দিষ্ট রেখা ধরে “অগ্রগতি” করে, “বৃদ্ধি”-র নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং সব ধরনের জ্ঞান একসময় এসে মিলিত হয়। কিন্তু যখন আমরা দেখি যে ইউরোপীয় জ্ঞানব্যবস্থা—যা পরে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকভাবে বিশ্বব্যাপী “সার্বজনীন” জ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল—কীভাবে বিকশিত হয়েছে, তখন কি সত্যিই বলা যায় যে সেখানে “বৃদ্ধি” হয়েছে? আমার নিজের মতে, এটি বরং “রূপান্তর”-এর ব্যাপার।
ধরুন প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাসকে। মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত কতবার এগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে পুনর্লিখিত হয়েছে—কখনো প্রতীকতত্ত্বের ভিত্তিতে, কখনো প্রাকৃতিক ইতিহাস, কখনো তুলনামূলক শারীরস্থান, কখনো বিবর্তনবাদ। প্রতিবার এই পুনর্লিখন জ্ঞানকে পুরোপুরি বদলে দেয়—তার কাজের ধরন, তার অর্থনীতি, তার অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক—সবকিছুতে। এখানে আপনি “অগ্রগতি”-র নীতি পান না; বরং পান বিভেদের নীতি।
আমি বরং বলব যে ইতিহাসের যেকোনো সময়ে কিছু ধরনের জ্ঞানকে একসঙ্গে সম্ভব করার বহু ভিন্ন পথ থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে যে জ্ঞানব্যবস্থা থাকে, তার তুলনায় বিশ্বের তথ্য বা data সবসময় কিছুটা “অতিরিক্ত”—যার ফলে সেই জ্ঞানব্যবস্থাগুলি নিজেদের সীমাবদ্ধতার ভেতর থেকেই অনুভূত হয়, এমনকি তাদের অপূর্ণতার ভেতরেও। এজন্যই আমরা প্রায়ই তাদের সৃজনশীল দিকটি বুঝতে পারি না।
আরেক দিক থেকে দেখলে—ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে—একই অল্প তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, এক ধরনের “অতিরিক্ততা” সৃষ্টি হয়। এখান থেকেই সেই বহুল প্রচলিত ধারণার জন্ম যে বিজ্ঞান-ইতিহাসে “নতুন তথ্যের আবিষ্কারই” পরিবর্তন ঘটায়।
চমস্কি:
আচ্ছা, এখানে আবারও আমি একটু সংক্ষেপ করার চেষ্টা করি। আপনার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ধারণার সঙ্গে আমি একমত—অর্থাৎ, আমার মনে হয় না যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি কেবল নতুন জ্ঞান যোগ হওয়া বা নতুন তত্ত্ব শোষণ করার সাধারণ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বরং আমি মনে করি এর একটি খাঁজখাঁজে, অসম ধরনের গতি আছে—যেমন আপনি বর্ণনা করেছেন—কিছু সমস্যাকে ভুলে যাওয়া, আবার হঠাৎ নতুন তত্ত্বে লাফ দেওয়া।
ফুকো:
এবং একই জ্ঞানকে নতুনভাবে রূপান্তরিত করা।
চমস্কি:
ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা হয়তো এ ব্যাপারে একটি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা অনুমান করতে পারি। আমি এখন যে কথাটি বলব তা খুবই সরলীকৃত—আমি আক্ষরিক অর্থে বলতে চাই না—তবুও সাধারণ রেখায় এটি সঠিক হতে পারে: যেন আমরা, একটি নির্দিষ্ট জৈবিক গঠনবিশিষ্ট মানবসত্তা হিসেবে, আমাদের মাথার ভেতর শুরু থেকেই কিছু সম্ভাব্য বৌদ্ধিক কাঠামো—সম্ভাব্য বিজ্ঞান—নিয়ে জন্মাই। ঠিক?
এখন, সৌভাগ্যবশত যদি বাস্তবতার কোনো অংশ আমাদের মনে থাকা এই কাঠামোগুলির একটির চরিত্রের সাথে মিলে যায়, তবে আমরা একটি বিজ্ঞান পাই। অর্থাৎ, সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের মনের গঠন এবং বাস্তবতার কোনো একটি অংশের গঠন যথেষ্ট মাত্রায় একত্রে মিলে যায়, ফলে আমরা একটি বোধগম্য বিজ্ঞান তৈরি করতে পারি।
এটাই আসলে আমাদের মনে থাকা এই প্রাথমিক সীমাবদ্ধতাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অসাধারণ প্রাচুর্য ও সৃজনশীলতার ভিত্তি। এটি জোর দেওয়া জরুরি—এবং এটি আপনার সীমাবদ্ধতা ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত বক্তব্যের সাথেও যুক্ত—যে এই সীমাবদ্ধতাগুলি না থাকলে আমরা অল্প কিছু তথ্য, অল্প কিছু অভিজ্ঞতা থেকে জটিল, সূক্ষ্মভাবে সংগঠিত জ্ঞানের বিশাল ভান্ডার তৈরি করার সেই সৃজনশীল কাজটি করতে পারতাম না। কারণ যদি সবকিছুই সম্ভব হতো, তবে কিছুই সম্ভব হতো না।
বরং এই কারণেই—আমাদের মনের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য, যার বিস্তারিত আমরা জানি না, কিন্তু যার সাধারণ রূপরেখা আমরা উপলব্ধি করতে শুরু করেছি—আমাদের মন কিছু সম্ভাব্য বোধগম্য কাঠামো উপস্থাপন করে, এবং ইতিহাস, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির প্রবাহে এই কাঠামোগুলি কখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আবার কখনও অস্পষ্ট হয়। আর ঠিক এই কারণেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি আপনার বর্ণনার মতোই এলোমেলো ও খাঁজখাঁজে চরিত্র ধারণ করে।
এর অর্থ এই নয় যে সবকিছু শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের আওতায় আসবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস, আমরা যেসব বিষয় বুঝতে চাই—এবং সম্ভবত যেসব বিষয় আমরা সবচেয়ে বেশি বুঝতে চাই—যেমন মানব প্রকৃতি, একটি ন্যায্য সমাজের প্রকৃতি, অথবা এমন আরও অনেক বিষয়—সেগুলি হয়তো প্রকৃতপক্ষে মানব-সম্ভব বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে পড়ে।
এলডার্স:
আচ্ছা, আমার মনে হয় আমরা আবারও সেই প্রশ্নটির মুখোমুখি হচ্ছি—সীমাবদ্ধতা এবং স্বাধীনতার আন্তঃসম্পর্ক। আপনি কি একমত, মঁসিয়ে ফুকো, মৌলিক সীমাবদ্ধতা ও স্বাধীনতার এই সমন্বয় সম্পর্কে?
ফুকো:
এটা কোনো “সমন্বয়” বা মিশ্রণের বিষয় নয়। সৃজনশীলতা কেবল তখনই সম্ভব যখন আমরা কিছু নিয়মের ব্যবস্থাকে সক্রিয় করি; এটি কোনোভাবে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার মিশ্রণ নয়।
যেখানে সম্ভবত আমি মঁসিয়ে চমস্কির সঙ্গে পুরোপুরি একমত নই, তা হলো—যখন তিনি এই নিয়মিততার ভিত্তিটিকে মানব-মন বা মানব-প্রকৃতির অভ্যন্তরে স্থাপন করেন।
যদি প্রশ্নটি হয় যে মানবমন বাস্তবে এই নিয়মগুলি কার্যকর করে—ঠিক আছে। যদি প্রশ্ন হয় যে ইতিহাসবিদ বা ভাষাবিদ তাদের নিজস্ব বিশ্লেষণে এই নিয়মগুলি পুনরায় চিন্তা করতে পারেন—তাও ঠিক আছে। এবং এটাও গ্রহণযোগ্য যে এই নিয়মগুলি আমাদেরকে বোঝাতে সাহায্য করে মানুষ কী বলছে বা কী ভাবছে।
কিন্তু বলতে চাওয়া যে এই নিয়মিততাগুলি মানবমনের বা মানব-প্রকৃতির অস্তিত্বগত শর্তের সঙ্গে মৌলিকভাবে যুক্ত—এটিকে আমার পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন। আমার মনে হয় সেই অবস্থানে পৌঁছানোর আগে—এবং আমি কেবল “জ্ঞান-ব্যবস্থা” বা understanding-এর কথা বলছি—আমাদের এই নিয়মিততাকে মানব-ব্যবহার বা প্র্যাকটিসের বৃহত্তর ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করতে হবে: যেমন অর্থনীতি, প্রযুক্তি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি—যা জ্ঞানের এই গঠনের শর্ত, মডেল, ক্ষেত্র, আবির্ভাবের স্থান হিসেবে কাজ করতে পারে।
আমি জানতে চাই—বিজ্ঞানকে সম্ভব করে তোলে যে নিয়মিততার ব্যবস্থা, যে বাধ্যবাধকতা, তা কি মানব-মনের বাইরে—সামাজিক রূপে, উৎপাদন-সম্পর্কে, শ্রেণিসংগ্রামে—খুঁজে পাওয়া যায় না?
উদাহরণ হিসাবে, পশ্চিমে একসময় “উন্মাদনা” বা মানসিক ব্যাধি বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের একটি বিষয় হয়ে উঠল—আমার মনে হয় এটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল।
সম্ভবত এখানে চমস্কি ও আমার মধ্যে মূল পার্থক্য হলো—তিনি যখন “বিজ্ঞান” বলেন, তিনি জ্ঞানের আনুষ্ঠানিক সংগঠন বা কাঠামোর কথা ভাবেন। আর আমি যখন বলি “জ্ঞান”, আমি সেই বিচ্ছিন্ন, বহুবিধ বিষয়বস্তুর কথা বলি—যা একটি সমাজের ভেতর ছড়িয়ে আছে, সমাজের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, এবং যা শিক্ষা, তত্ত্ব, অনুশীলন ইত্যাদির ভিত্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।
এল্ডার্স:
কিন্তু জ্ঞানের এই তত্ত্ব তাহলে আপনার “মানুষের মৃত্যু” বা উনিশ-বিশ শতকের মানবতাত্ত্বিক যুগের অবসান—এই থিমের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত?
ফুকো:
কিন্তু এর সঙ্গে তো আমরা যা নিয়ে কথা বলছি তার কোনো সম্পর্কই নেই।
এল্ডার্স:
আমি জানি না, কারণ আমি তো চেষ্টা করছিলাম আপনার কথাগুলোকে আপনার নৃবৈজ্ঞানিক ধারণার সঙ্গে যুক্ত করতে। আপনি তো ইতিমধ্যেই আপনার নিজস্ব সৃষ্টিশীলতা বা স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলতে অস্বীকার করেছেন, তাই না? আমি ভাবছিলাম, এর পেছনে আপনার মনোবৈজ্ঞানিক কারণ কী হতে পারে।
ফুকো:
[প্রতিবাদের সুরে] আপনি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে ভাবতে পারেন, কিন্তু আমি সেটা আটকাতে পারি না।
এল্ডার্স:
আহ, আচ্ছা।
ফুকো:
আমি কিন্তু এ নিয়ে ভাবছি না।
এল্ডার্স:
তাহলে আপনার বোঝাপড়া, জ্ঞান, বিজ্ঞান বিষয়ক ধারণার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে, ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তরে আপনি কেন অস্বীকার করেন—এর বস্তুনিষ্ঠ কারণ কী?
যখন কোনো প্রশ্ন আপনার জন্য কঠিন হয়ে ওঠে, তখন ব্যক্তিগত প্রশ্নকে সমস্যা হিসেবে দেখা—এর আপনার কাছে কী যুক্তি আছে?
ফুকো:
না, আমি কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্নকে সমস্যা বানাচ্ছি না; বরং ব্যক্তিগত প্রশ্নকে সমস্যাহীনতার জায়গায় রাখছি।
একটা খুব সহজ উদাহরণ দিই—যেটা আমি বিশদে বিশ্লেষণ করব না—কিন্তু প্রশ্নটা হলো: কীভাবে সম্ভব হলো যে মানুষ প্রথমবারের মতো, আঠারো শতকের শেষদিকে, পাশ্চাত্য চিন্তার ইতিহাসে এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানের ইতিহাসে, মৃতদেহ কেটে দেখতে শুরু করল—কোথায় আছে রোগের উৎস, কারণ, বা কোন অ্যানাটোমিক সূচের মতো বিন্দু সেই বিশেষ অসুখটির জন্য দায়ী, যা তাদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল?
ভাবতে সহজ মনে হয়। অথচ এই ধারণায় পৌঁছতে পশ্চিমে চার-পাঁচ হাজার বছরের চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস লেগে গেছে—যেখানে আমরা শেষ পর্যন্ত এই মত গ্রহণ করলাম যে রোগের কারণ খুঁজতে মৃতদেহের ক্ষত বা বিচ্যুতি পরীক্ষা করা দরকার।
আপনি যদি এই পরিবর্তনকে বিচার ব্যক্তিত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চান—আমি মনে করি তার কোনো গুরুত্ব নেই।
কিন্তু যদি আপনি দেখতে চান আঠারো শতকের শেষদিকে সমাজে রোগ ও মৃত্যুর স্থান কোথায় ছিল; শিল্পসমাজের জনসংখ্যা চারগুণ বাড়ানোর প্রয়োজন কীভাবে সমাজকে তাড়িত করছিল, যার ফলে সমাজজুড়ে চিকিৎসা-সমীক্ষা হলো, বড় হাসপাতাল তৈরি হলো; যদি খুঁজে দেখেন কীভাবে সেই সময়ে চিকিৎসাজ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিক হলো, এবং অন্যান্য জ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক কীভাবে পুনর্গঠিত হলো—তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন কীভাবে রোগ, হাসপাতালে থাকা অসুস্থ মানুষ, মৃতদেহ, এবং প্যাথলজিক্যাল অ্যানাটমির মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হলো এবং সম্ভব হলো।
এই ধরনের বিশ্লেষণ—আমি বলছি না এটা সম্পূর্ণ নতুন—কিন্তু এটাকে অনেক বেশি অবহেলা করা হয়েছে।
এবং ব্যক্তিগত ঘটনার এখানে প্রায় কোনো ভূমিকা নেই।
এলডার্স:
হ্যাঁ, কিন্তু তবুও আপনারা কীভাবে এই মতের বিরোধিতা করছেন তার একটু বেশি ব্যাখ্যা আমরা পেলে খুবই আকর্ষণীয় হতো।
চমস্কি সাহেব—এবং আমার দিক থেকে বললে, বিতর্কের এই দার্শনিক অংশ নিয়ে এটিই আমার শেষ প্রশ্ন—আপনি কি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারেন, সমাজবিজ্ঞান কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে আপনার ধারণা কী? বিশেষ করে, আচরণবাদ (বিহেভিয়ারিজম) নিয়ে আপনার কঠোর সমালোচনার কথা মাথায় রেখে। আর হয়তো আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন কীভাবে ফুকো এখন এক ধরনের আচরণবাদী পদ্ধতিতে কাজ করছেন। [দু’জন দার্শনিকই হেসে ওঠেন।]
চমস্কি:
আপনার নিষেধাজ্ঞা থেকে খুব বেশি দূরে না সরে, আমি শুধু ফুকো সাহেব যা বলেছেন, তার ব্যাপারে একটা মন্তব্য করতে চাই।
আমার মনে হয় তিনি দারুণভাবে দেখালেন যে আমরা দু’জন যেন পাহাড় খুঁড়ছি দু’দিক থেকে—আপনার সেই প্রথম রূপকের কথাই বলছি। অর্থাৎ, কোনো বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে: প্রথমত, মনের কিছু অন্তর্নিহিত গুণাবলি; দ্বিতীয়ত, সমাজে এবং চিন্তার জগতে যে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত সেই সময়ে বিদ্যমান থাকে। আর আমার দৃষ্টিতে প্রশ্নটা এই নয় যে আমরা কোনটিকে অধ্যয়ন করব—বরং আমরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে বুঝতে পারব তখনই, যখন আমরা জানতে পারব এই দুই উপাদান কী এবং কীভাবে তারা পরস্পরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে একটি নির্দিষ্ট রূপের আবিষ্কারকে সম্ভব করে।
এই প্রসঙ্গে, বিশেষ করে আমার আগ্রহ মনের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলির দিকে; আর আপনার আগ্রহ, যেমন আপনি বললেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তাদের বিন্যাসের দিকে।
ফুকো:
কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে আমাদের এই পার্থক্য চরিত্রগত কোনো বিষয়ের কারণে—কারণ তা হলে তো এলডার্স সাহেব ঠিক হতেন, আর তিনি ঠিক হতে পারেন না।
চমস্কি:
না, আমি একমত, এবং…
ফুকো:
এটি আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের সঙ্গে নয়, বরং আমরা যে জ্ঞান-পরিস্থিতিতে, যে জ্ঞানের অবস্থার মধ্যে কাজ করছি তার সঙ্গে সম্পর্কিত। যে ধরনের ভাষাবিজ্ঞান আপনার পরিচিত ছিল—আর যেটিকে আপনি রূপান্তরিত করতেও সক্ষম হয়েছেন—সেটি ‘সৃষ্টিশীল বক্তা’ বা ‘সৃষ্টিশীল বিষয়ী ব্যক্তি’-র গুরুত্বকে অগ্রাহ্য করেছিল; অপরদিকে, বিজ্ঞান-ইতিহাস, যা আমাদের প্রজন্ম যখন কাজ শুরু করে তখন বিদ্যমান ছিল, ঠিক তার উল্টোভাবে ব্যক্তিগত সৃষ্টিশীলতাকেই মহিমান্বিত করত।
চমস্কি:
হ্যাঁ।
ফুকো:
…এবং সেই সমষ্টিগত নিয়মগুলিকে পাশে সরিয়ে রাখত।
চমস্কি:
হ্যাঁ, হ্যাঁ।
প্রশ্নকারী:
একটা প্রশ্ন করতে পারি?
এলডার্স:
হ্যাঁ, অনুগ্রহ করে বলুন
প্রশ্ন:
আপনাদের আলোচনায় একটু আগে যে বিষয়ে কথা উঠেছিল, তার দিকে ফিরে যাই। আমার জানতে ইচ্ছে করছে, মি. চমস্কি, আপনি যে বলেন মানব-স্বভাবের মধ্যে এক ধরনের প্রাথমিক বা মৌলিক সীমাবদ্ধতার ব্যবস্থা বিদ্যমান—আপনার মতে এই সীমাবদ্ধতাগুলো কতখানি ঐতিহাসিক পরিবর্তনের অধীন? উদাহরণস্বরূপ, আপনি কি মনে করেন যে, ধরা যাক সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এখন পর্যন্ত এগুলোতে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে? সেই ক্ষেত্রে আপনি হয়তো ফুকোর ধারণার সঙ্গে এর কোনো যোগসূত্রও দেখাতে পারতেন?
চমস্কি:
জৈবিক এবং নৃতাত্ত্বিক তথ্যের দিক থেকে বিচার করলে আমি মনে করি যে মানব- বুদ্ধিমত্তার প্রকৃতি সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে তো নয়ই, এমনকি ক্রো-ম্যাগনন মানুষের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিমত্তার যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা আজ রাতে আলোচনা করছি, সেগুলো অনেক প্রাচীন। আপনি যদি পাঁচ হাজার বছর আগের—হয়তো বিশ হাজার বছর আগের—একজন মানুষকে নিয়ে আসেন এবং আজকের সমাজে শিশুর মতো বড় হতে দেন, তবে সে আজকের অন্যদের মতোই সব শিখবে; সে প্রতিভাবান হবে, বা নির্বোধ হবে, বা অন্য কিছু হবে—কিন্তু সে মূলগতভাবে ভিন্ন হবে না।
কিন্তু অবশ্যই, অর্জিত জ্ঞানের স্তর পরিবর্তিত হয়, সামাজিক পরিস্থিতি বদলায়—যে সব পরিস্থিতি মানুষের স্বাধীনভাবে ভাবাকে, কুসংস্কারের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসাকে সম্ভব করে তোলে। আর এই পরিস্থিতিগুলো বদলালে, একই মানব-বুদ্ধিমত্তা নতুন ধরনের সৃষ্টিশীলতার দিকে এগোতে পারে। আসলে, এটি এলডার্স সাহেবের আগের প্রশ্নের সঙ্গেও খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত—যদি এ বিষয়ে আমি একটু বলতে পারি।
ধরা যাক ‘বিহেভিয়ারাল সায়েন্স’—আচরণবিদ্যা—এর কথা, এবং এটিকে এই প্রেক্ষাপটে ভাবুন। আমার কাছে মনে হয় যে আচরণবাদ বা বিহেভিয়ারিজমের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হল এমন একটি ধারণা, যা সত্যিকার অর্থে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গঠনের সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করে। আচরণবাদের মূল ভিত্তি হল একটি অদ্ভুত, আত্ম-ধ্বংসাত্মক অনুমান—আপনি কোনো আকর্ষণীয় তত্ত্ব নির্মাণ করতে পারবেন না।
যদি, উদাহরণস্বরূপ, পদার্থবিদরা এই অনুমান নিয়ে এগোতেন যে আপনাকে শুধু ঘটনাগুলির বাহ্যিক প্রকাশ এবং তাঁদের বিন্যাস ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে, তবে আমরা আজও ব্যাবিলনের পুরনো জ্যোতির্বিজ্ঞানই করতাম। সৌভাগ্যক্রমে পদার্থবিদরা কখনও এই হাস্যকর, অপ্রাসঙ্গিক অনুমানকে গ্রহণ করেননি। আচরণবাদ যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে জন্ম নিয়েছিল, সেই প্রেক্ষাপটেরই বিভিন্ন অদ্ভুত বাস্তবতার সঙ্গে এই সীমাবদ্ধ, অযৌক্তিক ধারণার সম্পর্ক রয়েছে।
শুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, বিহেভিয়ারিজম আসলে একটি ইচ্ছামত আরোপ—একটি জোর করে দেওয়া দাবি—যে মানুষের আচরণের কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তৈরি করা চলবে না; বরং আপনাকে সরাসরি ঘটনাগুলির সঙ্গে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে কাজ করতে হবে, আর কিছু নয়। কিন্তু এই পদ্ধতি অন্য কোনো জ্ঞানক্ষেত্রেই সম্ভব নয়; এবং আমি মনে করি মানব- বুদ্ধিমত্তা বা মানব-আচরণের ক্ষেত্রেও এটি অসম্ভব।
এই অর্থে, আমি মনে করি না যে বিহেভিয়ারিজম কোনো বিজ্ঞান। এখানে আপনি যে উদাহরণটি উল্লেখ করেছেন, এবং যা ফুকোও আলোচনা করেন, সেটিরই এক বাস্তব নমুনা পাওয়া যায়: নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে—উদাহরণস্বরূপ সেই পরিস্থিতি, যাদের মধ্যে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান গঠিত হয়েছিল—কোনো এক কারণে, যেটি এখন আলোচনা করব না, এমন অদ্ভুত কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করা আকর্ষণীয় বা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল, যা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্মাণের ওপর নিষেধাজ্ঞা তৈরি করেছিল। এই অদ্ভুত সীমাবদ্ধতাগুলিই বিহেভিয়ারিজম নামে পরিচিত। আমার বিশ্বাস, তার কার্যকারিতা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। ১৮৮০ সালে হয়তো এর কিছু মূল্য ছিল, কিন্তু আজ তার একমাত্র ভূমিকা হলো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে সংকুচিত করা ও সীমাবদ্ধ করা, এবং সেই কারণে এটিকে সরিয়ে ফেলা উচিত—যেমনভাবে আমরা সেই পদার্থবিদকে সরিয়ে রাখতাম যিনি বলতেন: সাধারণ কোনো ভৌত তত্ত্ব গঠন করা নিষিদ্ধ, কেবল গ্রহগুলির গতিপথ এঁকে আরও নতুন উপবৃত্ত বা এপিসাইকেল যোগ করা যাবে। এ ধরনের কথা ভুলে যেতে হয় এবং পাশে সরিয়ে রাখতে হয়। একইভাবে বিহেভিয়ারিজমের এই অদ্ভুত বিধিনিষেধগুলোকেও সরিয়ে রাখা উচিত; এবং এগুলো আসলে “বিহেভিয়ারাল সায়েন্স” নামটির মধ্যেই গোপনে প্রকাশিত।
আমরা হয়তো একমত হতে পারি, বিস্তৃত অর্থে আচরণ হলো মানব-বিজ্ঞানের (science of man) তথ্যভান্ডার। কিন্তু কোনো বিজ্ঞানকে তার তথ্য দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা মানে হলো পদার্থবিজ্ঞানকে “মিটার-পড়ার বিজ্ঞান” বলে সংজ্ঞায়িত করা। আর যদি কোনো পদার্থবিদ বলেন: হ্যাঁ, আমি মিটার-পড়া নিয়েই কাজ করি, তাহলে আমরা নিশ্চিতই জানব তিনি খুব বেশি দূর এগোতে পারবেন না। তাঁরা হয়তো মিটার-পড়ার তথ্য নিয়ে কথা বলবেন, তাদের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজবেন, কিন্তু কখনোই কোনো ভৌত তত্ত্ব নির্মাণ করতে পারবেন না।
সুতরাং শব্দটিই এখানে রোগের লক্ষণ—এই ক্ষেত্রে, পদ্ধতির সমস্যাকে নামটিই প্রকাশ করে। আমাদের বোঝা উচিত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত, যার মধ্যে এই অদ্ভুত সীমাবদ্ধতাগুলির উদ্ভব হয়েছিল; এবং এগুলি বোঝার পর, আমার মতে, এগুলোকে পরিত্যাগ করা উচিত এবং মানব-বিজ্ঞানকে সেইভাবে এগিয়ে নেওয়া উচিত যেমন অন্য যে কোনো বিজ্ঞানকে—অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে বিহেভিয়ারিজমকে সরিয়ে দিয়ে, এবং আসলে, আমার মতে, পুরো এমপিরিসিস্ট (অভিজ্ঞতাবাদী) ঐতিহ্যকেই, যার মধ্য থেকে এটি জন্ম নিয়েছিল, সরিয়ে দিয়ে।
প্রশ্ন:
তাহলে আপনি আপনার অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যে তত্ত্ব দেন, সেটিকে ফুকোর “গ্রিল” ধারণার সঙ্গে যুক্ত করতে চাইছেন না। কিন্তু এদের মধ্যে তো এক ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে। দেখুন, ফুকো বলেন, কোনো বিশেষ দিকের সৃজনশীলতার উত্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য এক দিকের জ্ঞানকে সরিয়ে দেয় বা অদৃশ্য করে—এই গ্রিল ব্যবস্থার মাধ্যমে। এখন, যদি আপনার সেই সীমাবদ্ধতার ব্যবস্থাটি পরিবর্তনশীল হয়, তাহলে হয়তো দুটো ধারণাই একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।
চমস্কি:
আমি মনে করি, তিনি যে ঘটনাটির কথা বলছেন, তার কারণ ভিন্ন। আবারও বলছি, আমি খুব সরল করে বলছি। আমাদের মনের মধ্যে সম্ভাব্য বিজ্ঞানের সংখ্যা বেশি—অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমরা একাধিক সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক কাঠামো কল্পনা করতে পারি। যখন আমরা এই বুদ্ধিবৃত্তিক নির্মাণগুলোকে পরিবর্তনশীল বাস্তবতার জগতে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করি, তখন আমরা কোনো সঞ্চিত বা ধারাবাহিক বৃদ্ধি দেখি না। বরং দেখি অদ্ভুত ধরনের লাফ—একটা নির্দিষ্ট ঘটনা-ক্ষেত্রে কোনো বিজ্ঞান খুব ভালোভাবে কাজ করে; কিন্তু ঘটনাগুলোর পরিসর একটু বিস্তৃত করলেই দেখি সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেক ধরনের বিজ্ঞান সুন্দরভাবে প্রয়োগযোগ্য, যদিও এতে আগের কিছু ঘটনার ব্যাখ্যা বাদ পড়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, সেটাই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি—এবং এর ফলেই কিছু ক্ষেত্র বাদ পড়ে যায় বা ভুলে যাওয়া হয়।
কিন্তু আমার মতে এর কারণ হলো সেই নীতিমালা বা নীতিগুলির সেট—যা দুর্ভাগ্যবশত আমরা জানি না, আর সেই কারণে আলোচনাটি বেশ বিমূর্ত হয়ে যায়—যা আমাদের বলে দেয়: কোনটি একটি সম্ভাব্য বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামো, কোনটি একটি সম্ভাব্য গভীর-বিজ্ঞান (deep-science), যদি বলতে চান।
এল্ডার্স:
তাহলে এখন আলোচনার দ্বিতীয় অংশে, অর্থাৎ রাজনীতিতে চলে আসি। প্রথমেই আমি ফুকো মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই কেন তিনি রাজনীতিতে এত আগ্রহী, কারণ তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আসলে তিনি রাজনীতিকে দর্শনের চেয়ে অনেক বেশি পছন্দ করেন।
্ফুকো:
আমি কখনওই, যাই হোক, দর্শন নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখিনি। তবে এটাতে কোনো সমস্যা নেই। (হেসে)
আপনার প্রশ্ন হল: আমি রাজনীতিতে এত আগ্রহী কেন? খুব সোজা ভাবে বললে আমি বলব: কেনই বা আমি আগ্রহী হব না? বলতে চাইছি, কী ধরনের অন্ধত্ব, কী ধরনের বধিরতা, কী ধরনের মতাদর্শগত জড়তা আমাকে চেপে ধরলে আমি সেই বিষয়ে আগ্রহী না হয়ে থাকতে পারতাম—যে বিষয়টি আমাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক—অর্থাৎ আমরা যে সমাজে বাস করি, যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভেতরে সেই সমাজের কার্যপ্রণালী স্থাপিত, এবং যে ক্ষমতার ব্যবস্থা আমাদের আচরণের নিয়মিত ধরন, অনুমতি ও নিষেধকে নির্ধারণ করে।
আমাদের জীবনের সারমর্ম গঠিত হয় সেই সমাজের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা, যার ভেতরে আমরা অবস্থান করি।
সুতরাং কেন আমি আগ্রহী—এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি না; বরং প্রশ্নটা উল্টে জিজ্ঞাসা করতে পারি, কেনই বা আমি আগ্রহী হব না?
এল্ডার্স:
আপনি যেন বাধ্যই—এমনটাই কি?
্ফুকো :
হ্যাঁ, অন্তত, এতে কোনো অদ্ভুত ব্যাপার নেই যার জন্য আলাদা প্রশ্ন বা উত্তর প্রয়োজন। রাজনীতিতে আগ্রহী না হওয়াই বরং সমস্যা। সুতরাং আমাকে প্রশ্ন করার বদলে আপনাকে এমন কাউকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে রাজনীতিতে আগ্রহী নয়—তখন আপনার প্রশ্ন যথার্থ হত, আর আপনি পুরো অধিকার নিয়ে বলতে পারতেন, “ধুর, আপনি রাজনীতিতে আগ্রহী নন কেন?” (তাঁরা হাসেন এবং শ্রোতারাও হাসে।)
এল্ডার্স:
ঠিক আছে, হ্যাঁ, সম্ভবত। মিস্টার চমস্কি, আমরা সবাই খুব আগ্রহী জানতে যে আপনার রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলি কী, বিশেষত আপনার সুপরিচিত অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিজম বা আপনার ভাষায় লিবার্টারিয়ান সোশ্যালিজমের সঙ্গে সম্পর্কিত লক্ষ্যগুলো। আপনার লিবার্টারিয়ান সোশ্যালিজমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য কী?
চমস্কি :
আমি আপনার আগের, খুবই আকর্ষণীয় প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা দমন করে, এবার এই প্রশ্নে আসছি।
আমি শুরু করতে চাই এমন একটি বিষয় দিয়ে, যা আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। যদি এটা ঠিক হয়—যেমন আমি মনে করি ঠিকই—যে মানুষের স্বভাবের একটি মৌলিক উপাদান হলো সৃজনশীল কাজের প্রয়োজন, অনুসন্ধানের প্রয়োজন, এমন সৃষ্টির প্রয়োজন যা কোনো জোরজবরদস্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের নির্বিচার সীমাবদ্ধতার বাইরে থাকে—তাহলে তো অবশ্যই বলা যায়, একটি শোভন সমাজ এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবে যেখানে এই মৌলিক মানবিক বৈশিষ্ট্যটির বাস্তবায়নের সুযোগ সর্বোচ্চ মাত্রায় বাড়ানো যায়। এর অর্থ হল যে represssion, oppression, destruction, coercion—এইসব উপাদান যা যে কোনও বিদ্যমান সমাজে থাকে (আমাদের সমাজেও, অতীতের অবশিষ্টাংশ হিসেবে)—সেগুলোকে অতিক্রম করার চেষ্টা করতে হবে।
এখন যেকোনো ধরনের জবরদস্তি বা দমন, অস্তিত্বের কোনো ক্ষেত্রের ওপর স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণ—ধরা যাক মূলধনের ব্যক্তিগত মালিকানা, বা রাষ্ট্রের দ্বারা মানুষের জীবনের কিছু ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ—এসব স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণ কেবল তখনই ন্যায্য হতে পারে যখন তা টিকে থাকার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য, বা কোনো ভয়াবহ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রক্ষার প্রয়োজনের কারণে জরুরি বলে দেখা হয়। এগুলো কখনোই নিজস্বভাবে ন্যায়সিদ্ধ নয়; বরং এগুলোকে অতিক্রম করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত বিলোপ করতে হবে।
আমি মনে করি, অন্তত পশ্চিমের প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত সমাজগুলিতে আমরা এখন এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছি যেখানে অর্থহীন ক্লান্তিকর পরিশ্রম প্রায় পুরোপুরি দূর করা যায়। যে সীমিত অংশটুকু প্রয়োজন, তা জনসংখ্যার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব। আবার কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণ—প্রথমত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, তা বেসরকারি পুঁজিবাদ হোক বা রাষ্ট্রীয় সর্বগ্রাসী ব্যবস্থা হোক কিংবা বিভিন্ন ধরণের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ—এসবই ইতিহাসের ধ্বংসাত্মক স্মারক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এসবই অতীতের অবশিষ্টাংশ, যেগুলোকে উৎখাত ও নির্মূল করতে হবে—সরাসরি অংশগ্রহণমূলক কাঠামোর পক্ষে, যেমন শ্রমিক পরিষদ বা মানুষের স্বেচ্ছায় গঠিত বিভিন্ন মুক্ত সংগঠন, যা তারা নিজেদের সামাজিক অস্তিত্ব ও উৎপাদনশীল পরিশ্রমের জন্য তৈরি করবে।
একটি ফেডারেটেড, বিকেন্দ্রীভূত মুক্ত সংগঠনের ব্যবস্থা—যার ভেতরে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন থাকবে, তেমনই অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান—এই ব্যবস্থাকেই আমি অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিজম বলি। আমার মনে হয় একটি উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর সমাজের জন্য এই ধরনের সামাজিক সংগঠন উপযুক্ত, যেখানে মানুষকে আর যন্ত্রের দণ্ডের মতো বা মেশিনের চাকা হিসেবে ঠেলে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষের প্রতি উৎপাদন প্রক্রিয়ার যান্ত্রিক উপাদান হিসেবে আচরণ করার কোনো সামাজিক প্রয়োজন আর নেই। এটা অতিক্রম করা সম্ভব, এবং আমাদের সেটা অতিক্রম করতেই হবে—একটি স্বাধীনতা ও মুক্ত সংগঠনের সমাজের মাধ্যমে, যেখানে মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনশীল তাগিদ বাস্তবে তার ইচ্ছামতো নিজেকে বিকশিত করতে পারে।
আর আবার, মিস্টার ফুকোর মতো, আমি বুঝতেই পারি না কীভাবে কোনো মানুষ এই প্রশ্নে আগ্রহী না হতে পারে। (ফুকো হাসেন।)
এল্ডার্স:
মিস্টার ফুকো, মিস্টার চমস্কির বক্তব্য শোনার পর আপনি কি মনে করেন যে আমাদের সমাজকে কোনো অর্থেই গণতান্ত্রিক বলা যায়?
ফুকো:
না, আমাদের সমাজকে গণতান্ত্রিক বলে মনে করার মতো সামান্যতম বিশ্বাসও আমার নেই। (হাসেন।)
যদি গণতন্ত্র বলতে বোঝায়—একটি এমন জনসমষ্টির কার্যকর ক্ষমতা-চর্চা, যা শ্রেণিভাগহীন, শ্রেণিবিন্যাসহীন—তাহলে এটা স্পষ্ট যে আমরা গণতন্ত্র থেকে অনেক দূরে। একদম পরিষ্কার যে আমরা এমন এক শাসনব্যবস্থার মধ্যে বাস করছি যা প্রকৃতপক্ষে শ্রেণি-স্বৈরতন্ত্র—একটি শ্রেণির ক্ষমতা, যা নিজেকে প্রতিস্থাপন করে সহিংসতার মাধ্যমে, এমনকি যখন সেই সহিংসতার উপকরণগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক রূপে আসে। সেই অর্থে, আমাদের পক্ষে গণতন্ত্রের কথা ওঠেই না।
ঠিক আছে। আপনি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন আমি রাজনীতিতে আগ্রহী, তখন আমি উত্তর দিতে চাইনি, কারণ আমার কাছে বিষয়টি এতই স্পষ্ট ছিল। কিন্তু হয়তো আপনার প্রশ্নটি ছিল—
আমি কীভাবে রাজনীতিতে আগ্রহী?
আপনি যদি আমাকে এ প্রশ্ন করতেন—এবং এক অর্থে আপনি করেছেন—তাহলে আমি বলতাম যে আমি আমার পথে মিস্টার চমস্কির মতো এতদূর এগোইনি। অর্থাৎ, আমি স্বীকার করি যে আমি আমাদের বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিগত সমাজের জন্য একটি আদর্শ সামাজিক মডেল সংজ্ঞায়িত করতে পারি না, এবং আরো শক্তিশালী কারণে তা প্রস্তাব করতেও পারি না।
অন্যদিকে, আমার কাছে যে কাজটি অত্যন্ত জরুরি এবং অবিলম্বে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, তা হল—সমাজের ভেতরে যেখানেই রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্পর্কগুলি লুকিয়ে থাকে, যেখানেই তারা সামাজিক শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে, দমন বা দমিয়ে রাখে—সেগুলিকে নির্দেশ করা, উন্মুক্ত করে দেখা।
আমি বলতে চাইছি: ইউরোপীয় সমাজে অন্তত প্রচলিত ধারণা হল—ক্ষমতা সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনী, ও রাষ্ট্রযন্ত্রের মতো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে তা প্রয়োগ করা হয়। আমরা জানি এইসব প্রতিষ্ঠান জাতির বা রাষ্ট্রের নামে সিদ্ধান্ত তৈরি করে, সেগুলো বাস্তবায়ন করে এবং যারা মানে না তাদের শাস্তি দেয়। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি রাজনৈতিক ক্ষমতা এমন অনেক প্রতিষ্ঠান মারফতও কাজ করে, যেগুলোকে আমরা মনে করি রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং স্বাধীন—কিন্তু বাস্তবে তারা মোটেও স্বাধীন নয়।
পরিবারের ক্ষেত্রেই আমরা এটি জানি। আবার বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণভাবে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা—যা দেখতে জ্ঞান বিতরণের উপায় বলে মনে হয়—আসলে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণিকে ক্ষমতায় রাখার জন্য তৈরি, এবং অন্য শ্রেণির ক্ষমতার উপায়গুলোকে বাদ দেওয়ার জন্য। জ্ঞান, পূর্বানুমান এবং যত্নের প্রতিষ্ঠানগুলি—যেমন চিকিৎসা ব্যবস্থা—রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সমর্থন করে। মনোরোগবিদ্যার কিছু ক্ষেত্রে এটি এতই স্পষ্ট যে তা প্রায় কেলেঙ্কারির মতো।
আমার কাছে মনে হয়—আমাদের সমাজে প্রকৃত রাজনৈতিক কাজ হচ্ছে সেইসব প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের সমালোচনা করা, যেগুলো নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বলে মনে হয়; এমনভাবে সমালোচনা ও আক্রমণ করা যাতে রাজনৈতিক সহিংসতা—যা দীর্ঘদিন ধরে অদৃশ্যভাবে এদের মাধ্যমে কার্যকর হয়েছে—উন্মোচিত হয়ে যায়, এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়।
এই সমালোচনা ও সংগ্রামকে আমি জরুরি মনে করি বিভিন্ন কারণে। প্রথমত, রাজনৈতিক ক্ষমতা আমাদের ধারণার চেয়েও অনেক গভীরে প্রোথিত; এমন কিছু কেন্দ্র আছে, অদৃশ্য ও অল্প-পরিচিত কিছু সমর্থনের বিন্দু, যেখানে এর প্রকৃত দৃঢ়তা লুকিয়ে থাকে। কেবল বলা যথেষ্ট নয় যে সরকারের পেছনে বা রাষ্ট্রযন্ত্রের পেছনে একটি প্রভাবশালী শ্রেণি রয়েছে; আমাদের খুঁজে বের করতে হবে সেই কার্যস্থলগুলি, সেই রূপগুলি, যেখানে এই আধিপত্য কার্যকর হয়। এবং কারণ এই আধিপত্য শুধু অর্থনৈতিক শোষণের রাজনৈতিক প্রকাশ নয়—এটি সেই শোষণের যন্ত্র, এবং বৃহৎ অংশে সেই শোষণকে সম্ভব করার শর্ত। তাই একটিকে দূর করতে গেলে অন্যটিকে সম্পূর্ণভাবে চিহ্নিত ও উন্মোচিত করতে হবে।
যদি আমরা এই শ্রেণি-শক্তির সমর্থন-বিন্দুগুলিকে চিনতে ব্যর্থ হই, তাহলে এগুলো টিকে থাকবে—এমনকি কোনো আপাত বিপ্লবী পরিবর্তনের পরেও নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।
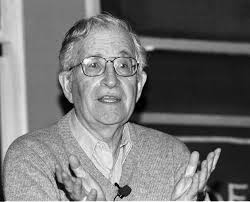
চমস্কি
হ্যাঁ, আমি অবশ্যই এর সঙ্গে একমত—শুধু ভাবনায় নয়, কাজেও। অর্থাৎ দু’টি বৌদ্ধিক কাজ আছে। একটি—এবং যেটি নিয়ে আমি আলোচনা করছিলাম—হলো ভবিষ্যতের একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজের কল্পনা তৈরি করা; অর্থাৎ, মানব-সত্তা বা মানব-প্রকৃতির মানবিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটি মানবতাবাদী সামাজিক তত্ত্ব গড়ে তোলা, যদি সম্ভব হয়। এ এক ধরনের কাজ।
আরেকটি কাজ হলো আমাদের নিজের সমাজে ক্ষমতা, দমন, সন্ত্রাস এবং ধ্বংসের প্রকৃত রূপ স্পষ্টভাবে বোঝা। এটি অবশ্যই আপনার উল্লেখ করা প্রতিষ্ঠানগুলিকেই অন্তর্ভুক্ত করে, এবং পাশাপাশি যেকোনো শিল্পোন্নত সমাজের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান— অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে, বিশেষত আগামী সময়ের ক্ষেত্রে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোকে, যাদের মধ্যে কিছু তো আজ রাতের আলোচনার জায়গা থেকে খুব দূরেই নেই [আইনডহোভেনে ফিলিপস-এর দিকে ইঙ্গিত]।
এই প্রতিষ্ঠানগুলোই দমন, জবরদস্তি এবং স্বৈরাচারী শাসনের মূল কাঠামো—যেগুলো নিজেদের নিরপেক্ষ বলে দাবি করে। তারা বলে: “আমরা তো বাজারতন্ত্রের গণতন্ত্রের অধীন।” কিন্তু সেই কথাটিকেই বুঝতে হবে—এটি হলো একটি বৈষম্যমূলক সমাজে বাজারশক্তির আধিপত্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণের আরেক রূপ।
আমাদের অবশ্যই এই বাস্তবতাগুলোকে বুঝতে হবে—শুধু বুঝলেই চলবে না, তার বিরুদ্ধে লড়াইও করতে হবে। আর বাস্তবে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে যেখানে আমরা সবচেয়ে বেশি শক্তি ও শ্রম দিই, তা অবশ্যই এই ক্ষেত্রেই হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত কথা তুলতে চাই না, কিন্তু আমার নিজের রাজনৈতিক কাজও প্রধানত এই ক্ষেত্রেই—এবং আমি অনুমান করি অন্য সকলের ক্ষেত্রেও তাই।
তবুও, আমি মনে করি পুরোপুরি ভুল হবে যদি আমরা সেই অপেক্ষাকৃত বিমূর্ত এবং দার্শনিক কাজটিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করি—যেটি হলো এমন এক মানব-প্রকৃতির ধারণা গড়ে তোলা যা স্বাধীনতা, মর্যাদা, সৃজনশীলতা এবং মানব-সত্তার অন্যান্য মৌল বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশকে অনুমতি দেয়, এবং তারপর সেই ধারণাটিকে এমন এক সামাজিক কাঠামোর ধারণার সঙ্গে যুক্ত করা যেখানে এই বৈশিষ্ট্যগুলো বাস্তবায়িত হতে পারে, যেখানে অর্থপূর্ণ মানবজীবন সম্ভব হতে পারে।
আসলে, যদি আমরা সামাজিক রূপান্তর বা সামাজিক বিপ্লব নিয়ে ভাবি, তাহলে লক্ষ্যকে বিস্তারিতভাবে আঁকার চেষ্টা করা অবশ্যই হাস্যকর হবে। তবুও, আমরা কোথায় যেতে চাই, সেই বিষয়ে কিছুটা ধারণা থাকা উচিত—এবং একটি তত্ত্ব আমাদের সে ধারণা দিতে পারে।
ফুকো:
হ্যাঁ, কিন্তু তবুও এখানে কি কোনো বিপদ নেই? আপনি বলছেন, একটি নির্দিষ্ট মানব-প্রকৃতি আছে; এবং বাস্তব সমাজ সেই মানব-প্রকৃতিকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিকশিত করার অধিকার ও সম্ভাবনা দেয়নি… আমার মনে হয়, আপনার বক্তব্য মোটামুটি এটাই।
চমস্কি:
হ্যাঁ।
ফুকো:
আর যদি আমরা এটা মেনে নিই, তাহলে কি এই ঝুঁকি নেই যে আমরা যে মানব-প্রকৃতিকে একই সঙ্গে বাস্তব এবং আদর্শ বলে সংজ্ঞায়িত করছি—যা এতদিন চাপা ছিল, দমিত ছিল—আমরা সেটাকেই আমাদের সমাজ, আমাদের সভ্যতা, আমাদের সংস্কৃতির ধার করা ধারণায় ব্যাখ্যা করতে শুরু করব?
আমি একটি উদাহরণ দেব, খুব সরল করে। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুরুতে যে ধরনের সমাজতন্ত্র গড়ে উঠেছিল, তারা সত্যিই মনে করত যে পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ তার বিকাশের পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন করতে পারেনি; যে মানব-প্রকৃতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর তারা কল্পনা করত এক এমন মানব-প্রকৃতি যেটি পূর্ণ মুক্ত।
কিন্তু—কি ছিল সেই স্বপ্নের মডেল? প্রকৃতপক্ষে তা ছিল বুর্জোয়া মডেল।
তারা ভাবত যে একটি বিচ্ছিন্ন, ‘এলিয়েনেটেড’ সমাজ হলো সেটি, যা সবার কল্যাণের নামে, বুর্জোয়া ধরনের যৌনতা, বুর্জোয়া পরিবারের রীতি, বুর্জোয়া নন্দনবোধ—এসবকে কেন্দ্র করে থাকে। আর সত্যিই, সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং নানা জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যা ঘটেছে তা হলো—এক ধরনের সমাজ গড়ে উঠেছে যা উনিশ শতকের বুর্জোয়া সমাজেরই রূপান্তরিত পুনর্গঠন।
বুর্জোয়ার মডেলকে সার্বজনীন করে দেখাই ছিল সোভিয়েত সমাজ গঠনের অন্তর্নিহিত ইউটোপিয়া।
ফলত, আমরা দেখলাম এমন অবস্থায় এসে মানব-প্রকৃতি ঠিক কী, তা বলা খুব কঠিন—এটা আপনিও উপলব্ধি করেছেন।
তাহলে কি এই ঝুঁকি নেই যে আমরা ভুল পথে চালিত হব? মাও সেতুং তো বলেছিলেন—বুর্জোয়া মানব-প্রকৃতি আর প্রলেতারিয় মানব-প্রকৃতি আলাদা; তিনি মনে করতেন দুটো এক নয়।
চমস্কি:
দেখুন, রাজনৈতিক চিন্তা ও বৌদ্ধিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে—অর্থাৎ কোনো মানব-প্রকৃতির ধারণার ভিত্তিতে একটি ন্যায়সঙ্গত ও মুক্ত সমাজের রূপরেখা গড়তে গেলে—আমরা ঠিক সেই একই সমস্যার মুখোমুখি হই যা বাস্তব রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রেও থাকে।
সমস্যাগুলো এত গুরুতর যে কিছু করা জরুরি—তবু আমরা জানি যে যা-ই করি, তা সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে আংশিক বোঝার ভিত্তিতেই করতে হয়; আর এ ক্ষেত্রে মানব-বাস্তবতার ব্যাপারও যুক্ত হয়।
নির্দিষ্ট উদাহরণ দিই। আমার নিজের অনেক কাজ ঘোরে ভিয়েতনাম যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। আমি কিছু শক্তি নাগরিক অবাধ্যতাতেও দিই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অবাধ্যতা এমন একটি পদক্ষেপ, যার ফল সম্পর্কে প্রচুর অনিশ্চয়তা থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ বলতে পারে—এটি সামাজিক শৃঙ্খলাকে এমনভাবে বিপন্ন করে, যাতে ফ্যাসিবাদ উত্থিত হতে পারে; আর সেটা আমেরিকার জন্য, ভিয়েতনামের জন্য, হল্যান্ডের জন্য—সবার জন্য ভয়ানক পরিণাম ডেকে আনবে।
যদি যুক্তরাষ্ট্রের মতো এক মহাশক্তি সত্যিই ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠে, তাহলে বিপদ তো বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। অর্থাৎ এ এক বাস্তব ঝুঁকি।
অন্যদিকে, যদি আমরা কিছুই না করি—তাহলে ইন্দোচীনের সমাজ মার্কিন শক্তির হাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। এই অনিশ্চয়তার মাঝেই আমাদের পদক্ষেপ বেছে নিতে হয়।
ঠিক একইভাবে, বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও—আপনি যেই সংশয়টার কথা বললেন, তা একেবারে ঠিক। আমাদের মানব-প্রকৃতির ধারণা সীমাবদ্ধ; তা সামাজিকভাবে গঠিত, আমাদের নিজস্ব চরিত্রগত দোষ ও বৌদ্ধিক সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতার দ্বারা প্রভাবিত।
তবু একই সময়ে এটা অত্যন্ত জরুরি যে আমরা জানতে পারি আমরা কোন অসম্ভব লক্ষ্যটাকে সামনে রেখে চলছি—কারণ তবেই কিছু সম্ভব লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।
অর্থাৎ আমাদের সাহস করে আংশিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সামাজিক তত্ত্ব গড়তে হবে; এবং একই সঙ্গে খুব খোলা মন নিয়ে মেনে নিতে হবে যে অনেকটা সম্ভাবনা—বরং প্রায় নিশ্চিত—আমরা অনেক দিক থেকে ভুলও হতে পারি।
এল্ডার্স:
হ্যাঁ, সম্ভবত এ কৌশলগত সমস্যাটিকে আর একটু গভীরভাবে দেখা দরকার। আপনি যে “নাগরিক অবাধ্যতা” বলছেন, তা কি আমাদের ভাষায় যাকে “পার্লামেন্ট- বহির্ভূত আন্দোলন” বলা হয়—তারই সমান?
চমস্কি:
না, আমার মনে হয় এটা তার চেয়ে বেশি।
পার্লামেন্ট-বহির্ভূত আন্দোলনে ধরা যাক—আইনসম্মত বড় জনসমাবেশ থাকতে পারে। কিন্তু নাগরিক অবাধ্যতা তার চেয়ে সরু পরিসরের; এটি হলো সেই কাজ, যেখানে রাষ্ট্র যে কাজটিকে “আইন” বলে দাবি করে—যা আমার মতে ভুল দাবি—তাকে সরাসরি অমান্য করা।
এল্ডার্স:
তাহলে, উদাহরণস্বরূপ, হল্যান্ডে যে জনশুমারি হয়, যেখানে সবাইকে ফর্মে সরকারি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়—যদি কেউ ফর্ম না ভরার সিদ্ধান্ত নিত, আপনি কি তাকে নাগরিক অবাধ্যতা বলতেন?
চমস্কি:
ঠিক। এ ব্যাপারে আমি একটু সতর্ক হতে চাই, কারণ—ফুকো যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন তার দিকে ফিরে গেলে—আমরা রাষ্ট্রকে অপরিহার্যভাবে এটা নির্ধারণ করতে দেব না যে কোনটি বৈধ। রাষ্ট্র অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট বৈধতার ধারণাকে কার্যকর করার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু ক্ষমতা কখনোই ন্যায়বিচার বা এমনকি সত্যতার নিশ্চয়তা দেয় না। সুতরাং রাষ্ট্র কোনো কিছুকে ‘সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স’ বলতে পারে, কিন্তু সেই সংজ্ঞা ভুলও হতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্র মনে করে যে ভিয়েতনামে পাঠানো হবে এমন গোলাবারুদের ট্রেন লাইনচ্যুত করা একটি সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স। কিন্তু সেই সংজ্ঞা ভুল, কারণ এটি প্রকৃতপক্ষে একটি বৈধ ও যথার্থ কাজ—রাষ্ট্রের অপরাধমূলক কার্যকলাপ রোধ করতে এমন কাজ করা উচিত। যেমন একটা হত্যাকাণ্ড ঠেকাতে ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করা বৈধ এবং নৈতিক—ঠিক তেমনি।
ধরা যাক, আমার গাড়ি রেড লাইটে থেমে আছে, কিন্তু আমি লাল সিগনাল অমান্য করে গাড়ি চালিয়ে গেলাম যাতে কেউ একটি দলকে গুলি করে হত্যা করতে না পারে—এটি কোনো বেআইনি কাজ নয়; বরং উপযুক্ত এবং নৈতিক কাজ। কোনো সুস্থ বিচারক এটা অপরাধ বলবেন না।
ঠিক সেইভাবে, রাষ্ট্র যেসব কাজকে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স বলে চিহ্নিত করে, তার অনেকগুলোই প্রকৃতপক্ষে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স নয়; বরং সেগুলো বৈধ, প্রয়োজনীয় এবং নৈতিক আচরণ—যদিও রাষ্ট্রের আদেশের বিরোধিতা করা হয়, এবং রাষ্ট্রের সেই আদেশ বৈধ কি না, সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ।
সুতরাং কোনো কিছুকে বেআইনি বলা নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত।
ফুকো:
হ্যাঁ, কিন্তু আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। যখন যুক্তরাষ্ট্রে আপনি কোনো বেআইনি কাজ করেন, তখন আপনি কি সেটিকে ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বা কোনো ‘উচ্চতর বৈধতার’ দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায্যতা দেন? নাকি আপনি যুক্তি দেন যে বর্তমান সময়ে শ্রেণিসংগ্রাম—প্রোলেতারিয়াতের শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রাম—অপরিহার্য, এবং সেই রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার কারণেই কাজটি ন্যায্য?
চমস্কি:
এখানে আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিতে চাই যা মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট এবং সম্ভবত অন্যান্য আদালতও এ ধরনের পরিস্থিতিতে নেয়—অর্থাৎ, বিষয়টিকে যতটা সম্ভব ‘সংকীর্ণ’ ভিত্তিতে বিচার করা। আমার মনে হয়, শেষ পর্যন্ত বহু ক্ষেত্রেই সমাজের বিদ্যমান আইন-সংস্থানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া যথার্থ হতে পারে, যদি তার ফলে সেই সমাজের ক্ষমতা ও দমনযন্ত্রের উৎসে আঘাত করা যায়।
তবে, বিদ্যমান আইনের একটি বড় অংশ মানবিক মূল্যবোধ ধারণ করে—সেগুলো যথেষ্ট সৎ ও মানবিক মূল্যবোধ—এবং সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করলে সেই আইনই অনেক কিছুকে বৈধতা দেয়, যেগুলো রাষ্ট্র আপনাকে করতে নিষেধ করে। আর এই বাস্তবতাকে কাজে লাগানো—আমার মনে হয়—খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
ফুকো:
হ্যাঁ।
চমস্কি:
…আইনের যে ক্ষেত্রগুলো সঠিকভাবে গঠিত হয়েছে, সেগুলোকে কাজে লাগানো গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেইসব ক্ষেত্রের আইনের বিরুদ্ধে সরাসরি পদক্ষেপ নেওয়াও প্রয়োজন হতে পারে, যেগুলো কেবলমাত্র কোনো ক্ষমতাকাঠামোকে বৈধতা দেয়।
ফুকো:
কিন্তু, কিন্তু, আমি… আমি…
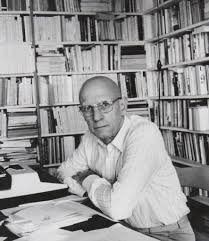
চমস্কি:
আমাকে বলতে দিন—
ফুকো:
আমার প্রশ্নটা ছিল এই: যখন আপনি স্পষ্টভাবে বেআইনি কোনো কাজ করেন—
চমস্কি:
—যেটিকে আমি বেআইনি মনে করি, শুধু রাষ্ট্র নয়—
ফুকো:
না, না, মানে রাষ্ট্র—
চমস্কি:
—যেটাকে রাষ্ট্র বেআইনি ভাবছে—
ফুকো:
—হ্যাঁ, রাষ্ট্র যেটাকে বেআইনি বলে বিবেচনা করে—
চমস্কি:
ঠিক।
ফুকো:
আপনি কি সে কাজটি করেন আদর্শ ন্যায়বোধের কারণে, নাকি শ্রেণিসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার কারণে? আপনি কি কোনো আদর্শ ন্যায়বিচারের ধারণার দিকে তাকান?—আমার প্রশ্ন এটাই।
চমস্কি:
আবার বলছি, রাষ্ট্র যেটাকে বেআইনি বলে, খুবই প্রায়ই আমি সেটাকে বৈধ মনে করি—কারণ আমি রাষ্ট্রের কার্যকলাপকেই অপরাধমূলক মনে করি। তবে সব ক্ষেত্রেই এমন নয়। তাই আমি একটি সরাসরি, স্পষ্ট উদাহরণ দেব এবং শ্রেণিসংগ্রাম থেকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দিকে যাব, যেখানে বিষয়টা আরও পরিষ্কার।
ধরা যাক আন্তর্জাতিক আইন—যা খুবই দুর্বল একটি উপকরণ, কিন্তু তবুও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিকে ধারণ করে। আন্তর্জাতিক আইন বহু দিক থেকেই শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর হাতিয়ার; এটি মূলত রাষ্ট্র ও তাদের প্রতিনিধিদের সৃষ্টি। আন্তর্জাতিক আইন গঠনের সময়ে কৃষক বা সাধারণ জনতার কোনো অংশগ্রহণ ছিল না।
এই বাস্তবতা আন্তর্জাতিক আইনের কাঠামোতে প্রতিফলিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন বর্তমান ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলিকে অত্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে বলপ্রয়োগের অনুমতি দেয়—যা রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাকাঠামোকে রক্ষা করে, কিন্তু রাষ্ট্র-বহির্ভূত বৃহদাংশ মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করে না।
এটা আন্তর্জাতিক আইনের এক মৌলিক ত্রুটি, এবং আমি মনে করি এই দিকটিকে নাকচ করা ন্যায্য—এটি ঠিক রাজাদের ‘দৈবাধিকারের’ মতোই অকার্যকর ও অযৌক্তিক। এটি কেবল শক্তিশালীদের ক্ষমতা বজায় রাখার অস্ত্র।
কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন পুরোপুরি এমন নয়। আসলে আন্তর্জাতিক আইনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে—উদাহরণস্বরূপ নুরেমবার্গ নীতি এবং জাতিসংঘ সনদ—যেগুলো নাগরিককে বাধ্য করে নিজের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও কাজ করতে, এমন কাজ যেগুলোকে রাষ্ট্র মিথ্যাভাবে অপরাধ বলে চিহ্নিত করবে। তবুও সে কাজ বৈধ, কারণ আন্তর্জাতিক আইন বলপ্রয়োগ বা বলের হুমকি নিষিদ্ধ করেছে, কেবলমাত্র খুব সংকীর্ণ কিছু পরিস্থিতি ছাড়া—যার মধ্যে ভিয়েতনাম যুদ্ধ মোটেও পড়ে না।
এর মানে বিশেষত ভিয়েতনাম যুদ্ধের ক্ষেত্রে—যা আমাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন করে—আমেরিকান রাষ্ট্র অপরাধমূলকভাবে আচরণ করছে। আর মানুষদের অপরাধীকে হত্যা বা ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বিরত রাখার অধিকার আছে। আপনি কোনো অপরাধীকে থামাতে চেষ্টা করলে সে যদি আপনার কাজকে ‘বেআইনি’ বলে, তাতে সেই কাজ বেআইনি হয়ে যায় না।
এর সবচেয়ে পরিষ্কার উদাহরণ এখন যুক্তরাষ্ট্রে পেন্টাগন পেপার্স–এর ঘটনা, যা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন।
সংক্ষেপে বললে—আইনি জটিলতা বাদ দিয়েই—ঘটনাটি হলো, রাষ্ট্র তার নিজের অপরাধ প্রকাশকারী মানুষদের বিচারের মুখোমুখি করতে চাইছে। আসলে ঘটনা এতটাই সরল।
এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, এবং এমন বিকৃত বিচারপ্রক্রিয়াকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। আরও বলি, বিদ্যমান আইনের কাঠামোই ব্যাখ্যা করে কেন এটি অ Absurd। কিন্তু ধরুন বিদ্যমান আইন তা ব্যাখ্যা করতে না পারত—তাহলেও আমাদের সেই আইনের বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে হতো।
ফুকো:
তাহলে কি আরও বিশুদ্ধ কোনও ন্যায়বোধের নামে আপনি ন্যায়বিচারের কার্যক্রমকে সমালোচনা করেন?
এখানে আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উপস্থিত হয়। সত্যিই সকল সামাজিক সংগ্রামে “ন্যায়” প্রশ্নটি থাকে। আরও স্পষ্ট করে বললে—শ্রেণিন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই, তার অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, সবসময়ই সামাজিক সংগ্রামের অংশ। বিচারকদের বরখাস্ত করা, আদালত বদলানো, দণ্ডিতদের ক্ষমা করা, কারাগার খুলে দেওয়া—যতক্ষণ না একটু সহিংস রূপ নেয়, ততক্ষণ না পর্যন্ত, প্রতিটি বড় সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে এইগুলো যুক্ত থেকেছে। বর্তমান ফ্রান্সে ন্যায়ব্যবস্থা ও পুলিশ সেইসব লোকেদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু, যাদের আমরা “গঁশিস্ত” বলি।
কিন্তু যদি ন্যায়বিচার সামাজিক সংগ্রামের বিষয় হয়, তাহলে তা ক্ষমতার একটি উপকরণ হিসেবে—এই কারণে; কোনো আশা নিয়ে নয় যে কোনো সমাজে একদিন মানুষকে তাদের যোগ্যের ভিত্তিতে পুরস্কৃত বা ত্রুটির ভিত্তিতে দণ্ডিত করা হবে। “সামাজিক সংগ্রামকে ন্যায়ের দৃষ্টিকোণে” ভাববার বদলে আমাদের উচিত “ন্যায়কে সামাজিক সংগ্রামের দৃষ্টিকোণে” দেখা।
চমস্কি
হ্যাঁ, কিন্তু নিশ্চয়ই আপনি বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা ন্যায়সঙ্গত—অন্য প্রসঙ্গ থেকে একটি ধারণা আনতে চাই—আপনি একটি ন্যায্য যুদ্ধ করছেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি মনে করতেন যে আপনি অন্যায় যুদ্ধ করছেন, তবে এই যুক্তির ধারায় এগোতে পারতেন না।
আমি আপনার কথাটি একটু পুনর্গঠন করতে চাই। আমার কাছে পার্থক্যটি “বৈধতা” ও “আদর্শ ন্যায়”-এর মধ্যে নয়; বরং “বৈধতা” ও “উত্তম ন্যায়”-এর মধ্যে।
আমি একমত—আমরা আদর্শ ন্যায়বিচার বা আদর্শ সমাজ কল্পনা করে তৈরি করার অবস্থানে নেই। আমরা খুব কম জানি, আমরা সীমাবদ্ধ, পক্ষপাতগ্রস্ত, বহু উপায়ে ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু তবুও আমরা এমন এক অবস্থানে আছি—এবং দায়িত্বশীল মানবসত্তা হিসেবে আমাদের সেই অবস্থান গ্রহণ করতে হবে—যেখান থেকে আমরা কল্পনা করতে পারি ও এগোতে পারি একটি উত্তম সমাজের দিকে, একটি উত্তম ন্যায়বিচারব্যবস্থার দিকে।
এই উত্তম ব্যবস্থা অবশ্যই ত্রুটি-বিচ্যুতিসম্পন্ন হবে। কিন্তু যদি এই উত্তম ব্যবস্থাকে বিদ্যমান ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে দেখি, আদর্শ বলে ভুল না করে, তাহলে আমরা বলতে পারি—
বৈধতা ও ন্যায় এক নয়; আবার একেবারে বিচ্ছিন্নও নয়। যেখানে বৈধতা “উত্তম ন্যায়”কে ধারণ করে—অর্থাৎ উত্তম সমাজের দিকে নির্দেশ করে—সেখানে আমাদের উচিত আইন পালন করা, রাষ্ট্রকে আইন মানতে বাধ্য করা, বৃহৎ কর্পোরেশনকে আইন মানতে বাধ্য করা, পুলিশকে আইন মানতে বাধ্য করা—যদি আমাদের সে ক্ষমতা থাকে।
অবশ্য, সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে আইনব্যবস্থা উত্তম ন্যায়কে নয় বরং কেবলমাত্র স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার কৌশলগুলোকে আইনরূপে স্থায়ী করে, সেখানে যুক্তিসঙ্গত মানুষকে সেই আইনকে অগ্রাহ্য ও প্রতিরোধ করা উচিত—অন্তত নীতিগতভাবে, বাস্তবে হয়তো না-ও পারতে পারে।
ফুকো:
আপনার প্রথম বাক্যের উত্তরে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই: আপনি বলেছিলেন, যদি পুলিশবাহিনীর বিরুদ্ধে আপনার লড়াইকে ন্যায়সঙ্গত না ভাবতেন, তবে আপনি তা করতেন না।
আমি আপনাকে স্পিনোজার ভাষায় উত্তর দিতে চাই: প্রলেতারিয়েত শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না কারণ সে যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত মনে করে; বরং প্রলেতারিয়েত যুদ্ধ করে কারণ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সে নিজেই ক্ষমতা নিতে চায়। আর শাসক শ্রেণিকে উৎখাত করার কারণেই সেটিকে সে ন্যায়সঙ্গত মনে করে।
চমস্কি:
হ্যাঁ, আমি এতে একমত নই।
ফুকো:
মানুষ যুদ্ধ করে জয়ের জন্য, ন্যায়ের জন্য নয়।
চমস্কি:
আমি ব্যক্তিগতভাবে এতে একমত নই।
উদাহরণস্বরূপ, আমি যদি নিজেকে এই ব্যাপারে রাজি করাতে পারি যে প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা দখলের ফলে একটি সন্ত্রাসী পুলিশ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে—যেখানে স্বাধীনতা, মর্যাদা ও মানবিক সম্পর্ক ধ্বংস হয়ে যাবে—তাহলে আমি প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা গ্রহণের পক্ষে থাকব না। বাস্তবে, আমি মনে করি, এ ধরনের পরিবর্তন কামনা করার একমাত্র কারণ হলো—ঠিক বা ভুলভাবে—আমরা ভাবি এই ক্ষমতা-স্থানান্তরের ফলে কিছু মৌলিক মানবমূল্য বাস্তবায়িত হবে।
ফুকো:
প্রলেতারিয়েত যখন ক্ষমতা দখল করবে, তখন খুবই সম্ভব যে সে সদ্য-পরাজিত শ্রেণিগুলোর ওপর হিংস্র, স্বৈরাচারী ও রক্তাক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। আমি এতে আপত্তি দেখছি না।
কিন্তু আপনি যদি বলেন, প্রলেতারিয়েত নিজের ওপর রক্তাক্ত, স্বৈরাচারী ও অন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ করবে—তাহলে বলব, সেটি তখনই সম্ভব, যখন প্রকৃত অর্থে প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা নেয়নি; বরং প্রলেতারিয়েতের বাইরে থাকা কোনো শ্রেণি, কিংবা তার ভেতরের কোনো গোষ্ঠী—একটি আমলাতন্ত্র, অথবা ক্ষুদ্র-বুর্জোয়া অংশ—ক্ষমতা দখল করেছে।
চমস্কি:
ঠিক আছে, আমি ঐ বিপ্লব-তত্ত্ব নিয়ে একদমই সন্তুষ্ট নই, ঐতিহাসিক এবং আরও নানা কারণে। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তত্ত্বটি ঠিক—তবুও সে তত্ত্ব এই দাবিই করে যে প্রলেতারিয়েত (শ্রমিক শ্রেণি) ক্ষমতা গ্রহণ করবে এবং তা প্রয়োগ করবে সহিংস, রক্তাক্ত ও অন্যায্য উপায়ে, কারণ বলা হয়—আর আমার মতে যে কথাটি ভুল—এই সহিংসতার মাধ্যমে নাকি ভবিষ্যতে একটি বেশি ন্যায়সঙ্গত সমাজ প্রতিষ্ঠা পাবে; এমন একটি সমাজ যেখানে রাষ্ট্র নিজে থেকেই ক্ষয় হয়ে যাবে, প্রলেতারিয়েত হবে এক “সার্বজনীন শ্রেণি” ইত্যাদি।
যদি এই ভবিষ্যৎ ন্যায়পরায়ণতার যুক্তি না থাকত, তাহলে প্রলেতারিয়েতের রক্তাক্ত স্বৈরতন্ত্রের ধারণাটি স্পষ্টতই অন্যায্য হতো।
এখন, এটা একটা আলাদা প্রশ্ন, কিন্তু আমি এমন এক “সহিংস ও রক্তাক্ত প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র” ধারণা নিয়ে অত্যন্ত সংশয়ী, বিশেষত যখন তা উচ্চারিত হয় কোনো স্বঘোষিত অগ্রদূত (ভ্যানগার্ড) দলের প্রতিনিধিদের মুখে। কারণ আমাদের কাছে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে—এবং আগেই অনুমান করা যেত—যে তারা শেষ পর্যন্ত সমাজের উপর নতুন শাসকগোষ্ঠী হয়ে দাঁড়ায়।
ফুকো:
হ্যাঁ, কিন্তু আমি প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা নিয়েই কথা বলিনি—যা নিজস্বভাবে অন্যায্য এক ক্ষমতা হবে; এতে আপনি ঠিক বলেছেন যে বিষয়টি খুবই সহজ হয়ে যেত। আমি বলতে চেয়েছি যে এমন একটি সময় থাকতে পারে যখন প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা প্রয়োগ মানে হবে সহিংসতা এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ—এক এমন শ্রেণির বিরুদ্ধে, যার উপর তাদের বিজয় বা দখল তখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নয়।
চমস্কি:
দেখুন, আমি একদমই বলছি না যে কোনো অবশ্য মেনে চলার মতো নীতি আছে। উদাহরণ হিসেবে বলি—আমি সম্পূর্ণ অহিংসাবাদী নই। সব কল্পনীয় পরিস্থিতিতে সহিংসতা ভুল—এ কথা আমি বলি না, যদিও সহিংসতার ব্যবহার এক অর্থে অন্যায়।
আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সবসময় তুলনামূলক ন্যায়বিচারের প্রশ্নকে বিবেচনা করতে হয়।
কিন্তু সহিংসতার ব্যবহার এবং কিছু মাত্রার অন্যায় সৃষ্টি—শুধুমাত্র তখনই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে, যখন দাবি করা যায়—এবং সেই দাবির মূল্যায়ন অত্যন্ত সতর্কতা, সন্দেহপ্রবণতা ও গভীর বিবেচনার সঙ্গে করতে হয়—যে এই সহিংসতা প্রয়োগ করা হচ্ছে একটি আরও ন্যায়সঙ্গত ফল আনার উদ্দেশ্যে। যদি এমন ভিত্তি না থাকে, তবে আমার দৃষ্টিতে এটি পুরোপুরি অনৈতিক।
ফুকো:
আমি মনে করি না যে প্রলেতারিয়েত যে লক্ষ্য নিয়ে শ্রেণিসংগ্রাম পরিচালনা করে, তাকে শুধু “বেশি ন্যায়বিচার” বলা যথেষ্ট হবে। প্রলেতারিয়েত যখন বর্তমান শাসকশ্রেণিকে উৎখাত করে এবং নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করে, তখন সে যা অর্জন করতে চায়, তা হলো শ্রেণিশক্তির অবসান—ক্ষমতা নামক এই ব্যবস্থারই বিলুপ্তি।
চমস্কি:
ঠিক আছে, কিন্তু ওটাই তো শেষ পর্যন্ত যুক্তি।
ফুকো:
হ্যাঁ, সেটাই যুক্তি—কিন্তু সেটা ন্যায়বিচার–এর ভাষায় নয়, ক্ষমতা–র ভাষায় বলা হয়।
চমস্কি:
কিন্তু আমি বলছি এটি ন্যায়বিচারের প্রশ্ন; কারণ যে ফল লাভ করা হবে সেটাকে ন্যায়সঙ্গত বলে দাবি করা হয়।
কোনো লেনিনবাদী—বা যাকে খুশি ধরুন—এটা সাহস করে বলবে না: “আমরা, প্রলেতারিয়েত, ক্ষমতা দখল করব, এবং তারপর বাকিদের চুল্লিতে ফেলে দেব।” যদি ক্ষমতা দখলের পরিণতি এমনই হতো, তা হলে অবশ্যই তা গ্রহণযোগ্য হতো না।
ভাবনাটা হলো—যে কারণগুলোর কথা আমি বলেছি তাই আমাকে সংশয়ী করে—যে সহিংস একনায়কতন্ত্রের এক পর্ব, হয়তো রক্তাক্ত সহিংস একনায়কতন্ত্রও, নাকি ন্যায়সঙ্গত কারণ শেষ পর্যন্ত তা শ্রেণি-নিপীড়নের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটাবে—যা মানবজীবনের একটি যথার্থ লক্ষ্য। এই শেষ যুক্তিটাই হল সমগ্র প্রকল্পকে ন্যায্যতা দেওয়ার ভিত্তি। সেটা সত্যি কি না—আরো একটি প্রশ্ন।
ফুকো:
আপনি চাইলে আমি একটু নীৎশে-সুলভ হব। আমার মনে হয় “ন্যায়বিচার” নামক ধারণাটি বিভিন্ন সমাজে তৈরি করা হয়েছে এবং ব্যবহার করা হয়েছে কখনো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার হিসাবে, কখনো আবার সেই ক্ষমতার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে।
কিন্তু যাই হোক, শ্রেণিভিত্তিক সমাজে এই “ন্যায়বিচার” আসলে নিপীড়িত শ্রেণির দাবি এবং সেই দাবির ন্যায্যতা প্রমাণের ভাষা হয়ে ওঠে।
চমস্কি:
এ ব্যাপারে আমি একমত নই।
ফুকো:
এবং একটি শ্রেণিহীন সমাজে, আমি নিশ্চিত নই যে আমরা “ন্যায়বিচার” নামক ধারণাটিই ব্যবহার করব।
চমস্কি:
এখানে আমি পুরোপুরি দ্বিমত করি। আমার মনে হয় কোনো না কোনো ধরনের এক চূড়ান্ত ভিত্তি আছে—আপনি খুব চাপ দিলে আমি বিপদে পড়ব, কারণ তার একটি রূপরেখা আঁকতে পারব না—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা নিহিত আছে মানবের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। সেই ভিত্তিতেই একটি “সত্যিকারের” ন্যায়বিচারের ধারণা দাঁড়িয়ে আছে।
আমার মনে হয় বর্তমান বিচারব্যবস্থাকে কেবলমাত্র শ্রেণি-নিপীড়নের যন্ত্র বলে চিহ্নিত করা তাড়াহুড়ো হয়ে যায়; আমি মনে করি এগুলো শ্রেণি-নিপীড়ন বহন করে, অন্য ধারার নিপীড়নের উপাদানও বহন করে—কিন্তু একই সঙ্গে এগুলো মানবিক ন্যায়বোধ, সৌজন্য, প্রেম, দয়া, সহানুভূতির দিকে গোপনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও বহন করে—যা আমার কাছে বাস্তব।
এবং আমি মনে করি ভবিষ্যতের যেকোনো সমাজেও—যে সমাজ কখনোই নিখুঁত হবে না—এই ধারণাগুলো থাকবে, এবং আশা করা যায় সেগুলো মানবের মৌলিক প্রয়োজন, যেমন সংহতি, সহানুভূতি ইত্যাদির পক্ষে আরও দৃঢ় প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করবে। যদিও সমাজের অসমতা ও নিপীড়নের ছায়া কিছুটা রয়ে যাবে।
তবে আপনি যা বর্ণনা করছেন, তা খুব ভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে খাটে।
উদাহরণ হিসেবে বলি জাতীয় সংঘাত। দুইটি সমাজ পরস্পরকে ধ্বংস করতে চাইছে। এখানে কোনো ন্যায়বিচারের প্রশ্নই ওঠে না। একটাই প্রশ্ন—আপনি কোন পক্ষের? আপনি কি নিজের সমাজকে রক্ষা করবেন এবং অন্যটিকে ধ্বংস করবেন?
এক অর্থে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের খন্দকে যারা একে অপরকে হত্যা করছিল—ঐ সৈনিকদের সামনে এই পরিস্থিতিই ছিল। তারা কিছুতেই লড়ছিল না। তারা কেবল একে অপরকে ধ্বংস করার “অধিকার”-এর জন্য লড়ছিল। সেখানে কোনো ন্যায়বিচারের প্রশ্ন নেই।
আর সেখানে খুব অল্পসংখ্যক যুক্তিসম্মত মানুষ ছিলেন—যেমন কার্ল লিব্নেখ্ট বা বার্ট্রান্ড রাসেল—যারা বলেছিলেন এই হত্যাযজ্ঞের কোনো মানে নেই, এবং তাই তারা জেল খেটেছিলেন।
সেই সময়ে বুদ্ধিমান, sane মানুষ বলতে এদেরই বোঝাত।
এ ধরনের পরিস্থিতিতে—যেখানে ন্যায়বিচারের কোনো প্রশ্নই নেই, শুধু আছে মৃত্যুযুদ্ধের প্রশ্ন—সেখানে মানবিক প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত: যুদ্ধ বন্ধ করো; জয়লাভ করো না; লড়াই থামাও। আর এটা বললেই আপনাকে জেলে ঢোকানো হবে বা হত্যা করা হবে—ঠিক যেমন বহু যুক্তিসম্মত মানুষের হয়েছে।
কিন্তু আমি মনে করি এটা মানবসমাজের সাধারণ পরিস্থিতি নয়। এবং শ্রেণিসংগ্রাম বা সামাজিক বিপ্লবের পরিস্থিতিতে তো নয়ই। সেখানে আপনাকে যুক্তি দিতে হবে—আর যদি দিতে না পারেন, তাহলে সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত।
যুক্তি দিতে হবে যে যে সামাজিক বিপ্লব আপনি চান তা ন্যায়বিচারের লক্ষ্যেই, মানবের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই, কেবলমাত্র কোনো নতুন গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলের জন্য নয়।
ফুকো:
ঠিক আছে, আমি কি উত্তর দিতে পারি?
এল্ডার্স:
অবশ্যই।
ফুকো:
কতক্ষণ? কারণ…
এল্ডার্স:
দুই মিনিট। (ফুকো হাসেন।)
ফুকো:
তাহলে এটা অন্যায়! (সবাই হাসে।)
চমস্কি:
সম্পূর্ণ একমত।
ফুকো:
না, এত কম সময়ে আমি উত্তর দিতে চাই না। আমি শুধু এটুকুই বলব—“মানব প্রকৃতি”-র তাত্ত্বিক আলোচনায় আমাদের কোনো মতবিরোধ হয়নি; আমরা একে অপরকে বুঝেছি।
কিন্তু “মানব প্রকৃতি” এবং রাজনৈতিক সমস্যার মিলনবিন্দুতে পৌঁছাতেই মতভেদ দেখা দিয়েছে। এবং আপনার ভাবনার বিপরীতে, আপনি আমাকে এ বিশ্বাস থেকে সরাতে পারবেন না যে মানব প্রকৃতি, ন্যায়বিচার, মানুষের “সত্যিকারের সত্তা”—এই সব ধারণাই আমাদের সভ্যতার তৈরি, আমাদের জ্ঞানের ধরণ ও দর্শনের উৎপাদন। এবং তাই এগুলো আমাদের শ্রেণিভিত্তিক সমাজেরই অঙ্গ।
এগুলোকে কোনো সেই সংগ্রামের ব্যাখ্যা বা ন্যায্যতা দিতে ব্যবহার করা যায় না—যে সংগ্রামটিই মূলত আমাদের সমাজের মূলে আঘাত করবে।
এর জন্য আমি কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে পাই না। এই তো কথা।
চমস্কি:
বোঝা গেল।
এল্ডার্স:
মঁসিয়ো ফুকো, যদি আপনাকে আমাদের বর্তমান সমাজকে রোগের পরিভাষায় বর্ণনা করতে বলা হয়—কোন ধরনের পাগলামি আপনাকে সবচেয়ে প্রভাবিত করে?
ফুকো:
আমাদের সমসাময়িক সমাজে?
এল্ডার্স:
হ্যাঁ।
ফুকো:
যদি আমাকে বলতে হয় আধুনিক সমাজ কোন রোগে সবচেয়ে আক্রান্ত?
এল্ডার্স:
হ্যাঁ।
ফুকো:
রোগ এবং উন্মাদের সংজ্ঞা, আর উন্মাদের শ্রেণিবিন্যাস—এসবই গড়ে তোলা হয়েছে কিছু মানুষকে সমাজ থেকে বাদ দেওয়ার জন্য। যদি সমাজ নিজেকে উন্মাদ বলে চিহ্নিত করে, তাহলে সে নিজেকেই বাদ দিত।
যারা বলে আধুনিক বিশ্ব উদ্বেগ বা সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত—তারা আসলে খুবই রক্ষণশীল, কারণ এগুলো একধরনের কৌশল যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু মানুষ বা আচরণকে বাইরে রাখা হয়।
তাই আমি মনে করি না যে সমাজকে বৈধভাবে সিজোফ্রেনিক বা প্যারানয়েড বলা যায়, যদি না শব্দগুলোকে অ–মনোবিদ্যাগত অর্থ দেওয়া হয়। কিন্তু যদি আপনি আমাকে চেপে ধরেন, আমি বলব—আমাদের সমাজ একটি রোগে আক্রান্ত, এক অদ্ভুত, বৈপরীত্যপূর্ণ রোগ—যার এখনো নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি।
এবং যার সবচেয়ে অদ্ভুত লক্ষণ হলো—লক্ষণটিই রোগটিকে সৃষ্টি করেছে।
এই তো।
প্রশ্ন:
মি. চমস্কি, আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। আপনার আলোচনায় আপনি “প্রলেতারিয়েত” শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন; কিন্তু উচ্চমাত্রায় উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে “প্রলেতারিয়েত” বলতে আপনি কী বোঝাতে চান? আমি মনে করি, এটি একটি মার্কসবাদী ধারণা, যা বর্তমান সমাজের সঠিক সমাজতাত্ত্বিক অবস্থাকে আর ঠিকমতো নির্দেশ করে না।
চমস্কি:
হ্যাঁ, আমি মনে করি আপনি ঠিক বলেছেন, আর এ কারণেই আমি বারবার দ্বিধা প্রকাশ করছিলাম—কারণ আমি পুরো ধারণাটাই নিয়ে খুব সন্দিহান। “প্রলেতারিয়েত” শব্দটি আজ ব্যবহার করতে চাইলে এর অর্থ নতুন করে নির্ধারণ করতে হবে, বর্তমান সমাজের সঙ্গে মানিয়ে। সত্যি বলতে, আমি শব্দটি বাদই দিতে চাই, কারণ এর সঙ্গে খুব নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অভিঘাত জড়িয়ে আছে। তার বদলে আমি বলতে চাই সমাজে যারা বাস্তব উৎপাদনমূলক কাজ করে—হাতে অথবা মস্তিষ্কে—তাদের কথা। এই মানুষগুলোই তাদের কাজের শর্ত, কাজের উদ্দেশ্য এবং তার ফলাফলের ব্যবহার নির্ধারণ করতে পারা উচিত। আর আমার মানব-প্রকৃতি সংক্রান্ত ধারণা থেকে বলতে হয়, এর মধ্যে প্রায় সকলকেই ধরা যায়। কারণ আমার বিশ্বাস, যে কোনও মানুষ—যদি না তার শারীরিক বা মানসিক কোনো বিকৃতি থাকে—সে শুধু সক্ষম নয়, বরং আগ্রহী উৎপাদন, সৃজনশীল কাজ করতে, যদি তাকে সেই সুযোগ দেওয়া হয়।
আমি কখনও এমন কোনো শিশুকে দেখিনি যে ব্লক দিয়ে কিছু বানাতে চায় না, বা নতুন কিছু শিখতে চায় না, বা পরের কাজটা চেষ্টা করতে চায় না। আর প্রাপ্তবয়স্করা কেন এমন হয় না? কারণ আমার ধারণা, তাদের স্কুল এবং অন্যান্য দমনমূলক প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়, যেখানে তাদের এই স্বাভাবিক প্রবণতাগুলোকে চাপা দেওয়া হয়।
যদি এটা সত্য হয়, তাহলে “প্রলেতারিয়েত”, বা আপনি যাই বলুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে সার্বজনীন হতে পারে—মানে, সেই সব মানুষ, যারা নিজেদের হতে চায়—অর্থাৎ সৃজনশীল, অনুসন্ধিৎসু, কৌতূহলী হতে চায়…
প্রশ্ন:
আমি একটু বাধা দিতে পারি?
চমস্কি:
…যারা উপকারী কাজ করতে চায়, জানেন।
প্রশ্ন:
আপনি যদি এমন একটি শ্রেণিবিভাগ ব্যবহার করেন, যার মার্কসবাদে বিশেষ অর্থ আছে…
চমস্কি:
সেজন্যই বলছি, শব্দটি বাদ দেওয়াই ভালো হয়তো।
প্রশ্ন:
তাহলে আপনি অন্য শব্দ ব্যবহার করলেই তো ভালো হতো, তাই নয়? এই অবস্থায় আমি আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই: আপনার মতে কোন কোন গোষ্ঠী বিপ্লব ঘটাবে?
চমস্কি:
হ্যাঁ, এটা অন্য প্রশ্ন।
প্রশ্ন:
ইতিহাসের বিদ্রুপ হচ্ছে—আজকের দিনে উচ্চবিত্ত পরিবারের তরুণ বুদ্ধিজীবীরাই নিজেদের প্রলেতারিয়েত বলে দাবি করছে, এবং বলছে তাদের প্রলেতারিয়েতদের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। কিন্তু আমি কোথাও শ্রেণিচেতনাসম্পন্ন কোনো প্রলেতারিয়েত দেখি না। এটাই সবচেয়ে বড় দ্বিধা।
চমস্কি:
ঠিক আছে। এখন আপনি খুব সুনির্দিষ্ট এবং যথার্থ প্রশ্ন করছেন।
আমাদের সমাজে সবাই উপকারী উৎপাদনমূলক কাজ করেন না, বা আত্মতৃপ্তিকর কাজ—এটা স্পষ্টতই সত্য নয়। তাছাড়া স্বাধীন অবস্থায় একই কাজ করলেও অনেক ক্ষেত্রে তা উৎপাদনমূলক বা তৃপ্তিদায়ক নাও হতে পারে।
বরং বিশাল সংখ্যক মানুষ এমন সব কাজে নিযুক্ত, যা আদৌ উৎপাদনমূলক নয়। যেমন—
• যারা শোষণকে পরিচালনা করে,
• যারা কৃত্রিম ভোগের প্রয়োজন তৈরি করে,
• যারা ধ্বংস ও দমনের প্রক্রিয়া তৈরি করে,
• অথবা যারা স্থবির শিল্পব্যবস্থায় কোনো স্থানই পায় না।
অনেক মানুষকেই উৎপাদনশীল শ্রমের বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।
আমি মনে করি, বিপ্লব—যদি আপনি সেই শব্দটি ব্যবহার করতে চান—মানুষের পক্ষেই হওয়া উচিত; কিন্তু তা বাস্তবে ঘটাতে পারবে শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষ—তারা হল সেইসব মানুষ, যারা সত্যিই সমাজের উৎপাদনমূলক কাজে যুক্ত।
আমাদের সমাজে এর মধ্যে পড়ে—
• বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমিকরা,
• কারিগর, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী,
• পেশাজীবী মানুষের বৃহৎ অংশ,
• সেবাখাতে যুক্ত বহু মানুষ,
এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে এরা আসলে জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় অংশ, এবং ভবিষ্যতেও তাই হবে।
সুতরাং, ছাত্র-বিপ্লবীরা—যদি আপনি এ নাম দেন—কিছুটা হলেও ঠিক বলছে। আধুনিক উন্নত শিল্পসমাজে প্রশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি নিজেদের কীভাবে চিহ্নিত করে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা কি নিজেদের সমাজের “ব্যবস্থাপক” হিসেবে দেখবে—রাষ্ট্র বা কর্পোরেট ক্ষমতার দাস হিসেবে? নাকি তারা নিজেদের শ্রমজীবী মানুষের অংশ হিসেবে দেখবে, যাদের শ্রম বৌদ্ধিক?
যদি দ্বিতীয়টা হয়, তাহলে তারা একটি প্রগতিমুখী সামাজিক বিপ্লবে ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। আর যদি প্রথমটা হয়, তাহলে তারা নিপীড়ক শ্রেণিরই অংশ।
প্রশ্ন:
ধন্যবাদ।
এল্ডারস:
হ্যাঁ, পরের প্রশ্নটি করুন।
প্রশ্ন:
চমস্কি সাহেব, আপনি বলেছিলেন নতুন সমাজের মডেল তৈরি করার বৌদ্ধিক প্রয়োজনের কথা। আমরা উট্রেখটের ছাত্রদলে যখন এ কাজ করি, তখন বড় সমস্যা হয় মূল্যবোধের সামঞ্জস্য রক্ষা করা নিয়ে। আপনি যে মূল্যগুলির কথা বলেছিলেন—তার একটি ছিল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। এলাকার মানুষ নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করবে।
কিন্তু আমরা এমন সমাজে বাস করছি যেখানে ক্রমশ মনে হচ্ছে অনেক সিদ্ধান্ত বিশ্বব্যাপী স্তরে নিতে হয়। যেমন—সম্পদের ন্যায্য বণ্টন করতে গেলে মনে হয় আরও কেন্দ্রীকরণ দরকার। অর্থাৎ, উচ্চতর স্তরে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই অসঙ্গতিটা আমাদের নতুন মডেল তৈরি করতে খুব ভাবায়। আপনার মত জানতে চাই।
আর একটি ছোট প্রশ্ন—বরং মন্তব্য—আপনার কাছে। আপনার ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী সাহসী অবস্থানের কথা বিবেচনা করলে, আপনি এমন একটি প্রতিষ্ঠান—MIT—এ কীভাবে টিকে আছেন, যেটি এখানে বিশাল যুদ্ধপ্রকৌশল কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত?
চমস্কি:
ঠিক আছে, দ্বিতীয় প্রশ্নটি আগে নেব না—কারণ প্রথমটি ভুলে যেতে পারি—চলুন প্রথম প্রশ্ন থেকেই শুরু করি।
সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমি বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে। একে আমি অচল সত্য হিসেবে দেখি না, কিন্তু আমার ধারণা হলো—যে কোনো কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সাধারণত শক্তিশালী গোষ্ঠীর স্বার্থেই সবচেয়ে দক্ষভাবে কাজ করবে।
বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষমতা এবং স্বাধীন সংগঠন অবশ্যই সমস্যায় পড়বে—আপনি যেমন বললেন এক অঞ্চলে বেশি সম্পদ, অন্য অঞ্চলে কম। কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষের মূল অনুভূতি—সহমর্মিতা, ন্যায়ের বোধ—স্বাধীন পরিবেশে আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারে। তাই এ দিকেই ভরসা রাখতে চাই। আর কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানগুলো সবসময় প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থেই কাজ করবে—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।
এটা হয়ত বিমূর্ত শোনাচ্ছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এটি সত্য।
যেমন, এক গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক, স্বাধীনতাবাদী আমেরিকা পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের অনেক বেশি সাহায্য করতে পারত—একটি কেন্দ্রীভূত শক্তির চেয়ে, যার নীতি চালায় বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি।
আপনার প্রশ্নের অন্য দিক—অনেকে বলেন—উন্নত প্রযুক্তি নাকি অবশ্যম্ভাবীভাবে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দিকে নিয়ে যায়। ম্যাকনামারা থেকে অনেকে যে যুক্তি দেন—আমি কখনও এমন কোনো যুক্তি দেখিনি যা সত্যি এটা প্রমাণ করে।
বরং আধুনিক প্রযুক্তি—তথ্যপ্রযুক্তি, যোগাযোগব্যবস্থা—তথ্য ও বোধ সবাইকে পৌঁছে দিতে পারে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা একদল ব্যবস্থাপকের হাতে সীমাবদ্ধ রাখতে হয় না। প্রযুক্তি মুক্তিকামী হতে পারে—কিন্তু ক্ষমতার বন্টন খারাপ বলে তা দমনের উপকরণ হয়েছে। প্রযুক্তির মধ্যে কেন্দ্রীভবনের কোনো স্বভাবগত বাধ্যবাধকতা নেই—বরং উল্টোটা।
এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন—MIT আমায় কীভাবে সহ্য করে এবং আমি MIT-কে কীভাবে সহ্য করি।
MIT অবশ্যই যুদ্ধ গবেষণার বড় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এর মধ্যে আমেরিকার কিছু গভীর স্বাধীনতাবাদী মূল্যবোধও আছে—যা বিশ্বের জন্য সৌভাগ্য। এগুলো যথেষ্ট গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে আরও বড় বিপর্যয় ঠেকানো সম্ভব হয়েছে—যদিও ভিয়েতনামিদের রক্ষা করতে যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু এই মূল্যবোধের কারণেই এমন একটি প্রতিষ্ঠান যুদ্ধবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত একজন অধ্যাপককে সহ্য করে—বরং অনেক ক্ষেত্রে উৎসাহও দেয়।
এখন আমি MIT-কে কীভাবে সহ্য করি—এটি আরেক প্রশ্ন। অনেকে বলেন, র্যাডিকালদের দমনমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা থাকা উচিত। তাহলে যুক্তি দাঁড়ায়—কার্ল মার্কসের ব্রিটিশ মিউজিয়াম-এ পড়াশোনা করা ভুল ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়াম ছিল সাম্রাজ্যবাদী লুটের কেন্দ্র—সেই সব উপনিবেশ থেকে আনা সম্পদে পূর্ণ।
কিন্তু মার্কস ঠিকই করেছিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসে পড়াশোনা করে। তিনি যে সভ্যতার বিরুদ্ধে লড়ছিলেন, তারই সম্পদ ও উদার মূল্যবোধ ব্যবহার করেছিলেন সেই সভ্যতার বিরুদ্ধে। আমিও একই কথা বলি।
প্রশ্ন:
কিন্তু আপনি কি ভয় পান না যে MIT-তে আপনার উপস্থিতি তাদের বিবেককে পরিষ্কার রাখে?
চমস্কি:
আমি সত্যিই তা দেখি না। আমার মনে হয়, MIT-তে আমার উপস্থিতি সামান্য হলেও—কতটা জানি না—ছাত্রদের সক্রিয়তা বাড়াতে সাহায্য করে, যেসব কাজে MIT একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুক্ত, তার অনেকগুলোর বিরোধিতায়। অন্তত আমি আশা করি এটাই ঘটে।
এলডার্স:
আর কোনও প্রশ্ন?
প্রশ্ন:
আমি আবার কেন্দ্রীয়করণের প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই। আপনি বললেন প্রযুক্তি বিকেন্দ্রীকরণের পরিপন্থী নয়। কিন্তু সমস্যাটি হলো—প্রযুক্তি কি নিজেকে নিজে সমালোচনা করতে পারে? তার প্রভাব, তার বিপদ, ইত্যাদি নিজেই বিচার করতে পারে? আপনি কি মনে করেন না যে প্রযুক্তির সামগ্রিক প্রভাবকে বিশ্লেষণ করার জন্য কোনও কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রয়োজন হতে পারে? আর আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে তা ছোট ছোট প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোর মধ্যে সমন্বিত হবে।
চমস্কি:
আমি পরস্পর-সংযুক্ত স্বাধীন সমিতি বা ফেডারেটেড অ্যাসোসিয়েশন-এর পারস্পরিক যোগাযোগ, সমালোচনা, আলোচনা—এসবের বিরুদ্ধে নই; সে অর্থে কিছুটা কেন্দ্রীয় যোগাযোগ তো থাকবে। কিন্তু আমি যে কেন্দ্রীয়করণের বিরুদ্ধে বলছি, তা হলো ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ।
প্রশ্ন:
কিন্তু অবশ্যই ক্ষমতার প্রয়োজন আছে—যেমন এমন কিছু প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করা, যারা শুধু কর্পোরেট মুনাফার জন্য কাজ করছে।
চমস্কি:
হ্যাঁ, কিন্তু আমার যুক্তি হলো এই—যদি আমাদের সামনে দুইটি বিকল্প থাকে:
১) কেন্দ্রীয় ক্ষমতার ওপর ভরসা করে সঠিক সিদ্ধান্ত আশা করা,
অথবা
২) স্বাধীন, মুক্ত সমিতিগুলোর ওপর ভরসা করা,
আমি দ্বিতীয়টির ওপর ভরসা করব। কারণ আমি মনে করি মুক্ত, বিকেন্দ্রীভূত সমিতি মানবিক, সহানুভূতিশীল প্রবৃত্তিকে সর্বাধিক সুযোগ দেয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কাঠামো সাধারণত মানুষের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিকে—লোভ, আধিপত্য, ক্ষমতা দখল, অন্যকে ধ্বংস করা—এসবকে বাড়িয়ে দেয়। ইতিহাসের নির্দিষ্ট পরিবেশে এই প্রবৃত্তিগুলোই মাথা তোলে।
আমরা এমন সমাজ গড়তে চাই যেখানে এগুলো দমিত হবে, এবং মানুষের সুস্থ প্রবৃত্তিগুলোই প্রধান হয়ে উঠবে।
প্রশ্ন:
আমি আশা করি আপনি ঠিক।
এলডার্স:
আচ্ছা, মহিলাবৃন্দ ও মহোদয়গণ, আমার মনে হয় আজকের বিতর্ক এখানেই শেষ করতে হবে। মি. চমস্কি, মি. ফুকো—দর্শন, তত্ত্ব এবং রাজনীতির এত গভীর প্রশ্ন নিয়ে আপনারা যে আলোচনা করলেন, তার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

