
চিন্ময় গুহ কিংবা পাগল হাওয়ার অশ্বারোহীর মাতাল গদ্য
রাজু আলাউদ্দিন
বহু চর্চিত এই তথ্য সবারই জানা যে বাংলা গদ্যের বয়স কম করে হলেও দুই শ বছরের উপরে। ফোর্ট উইলিয়াম-পূর্ববর্তী গদ্যের নমুনার কথা বিবেচনায় নিলে নিঃসন্দেহে এর ইতিহাস আরও পুরোনো। তবে যত পুরোনোই হোক না কেন, তা যে ফরাসী, ইংরেজী, ইতালীয় বা স্প্যানিশের তুলনায় অস্বচ্ছল, দীন ও নবীন তা সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের কাছে আজ অজানা নয়। কিন্তু বাংলা গদ্যের বিবর্তনকে যদি অনুসরণ করা যায় তাহলে আমাদের বিস্মিত হতে হয় এর আকস্মিক উত্তরণে ও পরিপক্বতায়। অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরে যার স্বচ্ছন্দ্য সূচনা, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের হাতে তারই এক শিল্পিত পরিকপক্কতা বর্ণিল রূপ ধারণ করেছে। অল্প বয়সী গদ্যের ইতিহাসে এ ছিল এক উল্লম্ফন। ঠিক যেমনটা ঘটেছে, কবি ও ভাবুক আলফনসো রেইয়েসের ভাষায়, লাতিন আমেরিকার জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে:
“ইউরোপীয় সভ্যতার ভোজ-উৎসবে দেরিতে যোগ দেওয়ায় আমেরিকাকে তাড়াহুড়া করে লাফ দিয়ে পথ এগুতে হয়েছে,এবং পরিপক্ব হওয়ার সময় না দিয়েই এক প্রকরণ থেকে অন্য প্রকরণে দৌড়াতে হয়েছে। কখনো কখনো এই উলম্ফন দুঃসাহসী এবং নতুন ধরনটিকে দেখলে মনে হবে পুরোপুরি রান্না হওয়ার আগেই সেটিকে চুলা থেকে নামানো হয়েছে। ”
Having arrived late at the banquet of European civilization, America goes leaping over steps along the way, hurrying and racing from one form to another, without giving the preceding form time to mature completely. At times, the leap is bold and the new form looks like food taken from the fire before it is fully cooked. (The Position of America and Other Essays. By Alfonso Reyes. Selected and translated by Harriet de Onís. Foreword by Federico de Onís. (New York: Knopf, 1950. P 89)
লাতিন আমেরিকা নিজের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঠিক যেভাবে ইউরোপিয় মননের সমান্তরাল হয়ে উঠেছিল, বাংলা গদ্য তার সবরকম প্রতিকূলতা উজিয়ে শাখাপ্রশাখায় আজ বিরাট মহীরূহ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের পরে এই গদ্যের—প্রবন্ধে ও কথাসাহিত্যে–নানা দিকে নানা হাতে যে-শৈলীগত নবজন্ম ও বিস্তার ঘটেছে তা বয়সের তুলনায় এক বিস্ময়কর অর্জন। রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসু যেন শৈলশিখর থেকে নিসৃত দুই স্বতন্ত্র ঝর্নাধারা যারা গদ্যকে গরীয়ান করে তুলেছেন।
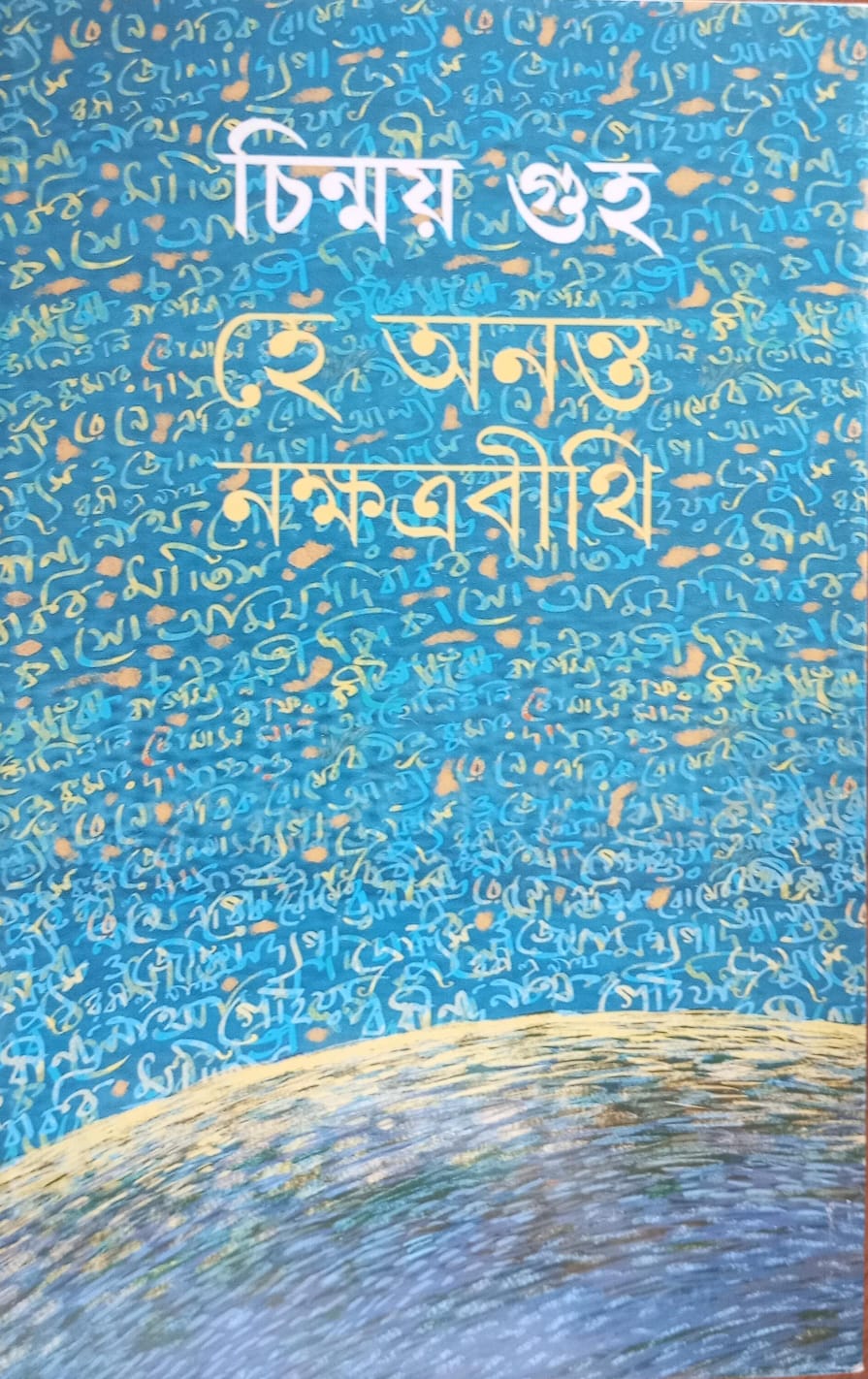
বাংলা গদ্যের ভাষারীতি নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও, প্রবন্ধের শৈলী নিয়ে আলোচনা হয়েছে সে তুলনায় খুবই কম, এ বিষয়ে রচিত গ্রন্থ তারও চেয়ে কম। শৈলী শীর্ষক যে-সব আলোচনাগ্রন্থ রয়েছে, সেগুলোতে মূলত বাক্যরীতি বা বাক্যশৈলীর দিকেই মনোযোগ দেয়া হয়েছে বেশি। যদিও বাক্য ও শব্দকে এড়িয়ে শৈলীর ধারণা অসম্ভব। মূলত শব্দের ব্যবহারেই আলোচকদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থেকেছে। যদিও শব্দ এই শৈলীর একটি উপাদান মাত্র, কিন্তু যে-স্বাতন্ত্র্যবোধ এই শৈলীর জন্মদাতা, চৈতন্যের যে রসায়ন থেকে কল্পনা ও কাব্যবোধের সমন্বয়ে অনন্য এক শৈলীর জন্ম–সেই দিকটিকে কেন্দ্র করে আলোচনাগ্রন্থ খুবই বিরল। যা আছে তা কেবল শব্দ-সংগঠন ও বাক্যরীতির নির্মাণ কৌশলের ব্যবচ্ছেদ মাত্র। একটু তলিয়ে দেখলেই আমরা লক্ষ্য করবো, শৈলীর পেছনে শিল্পীর চিন্তা ও কল্পনার প্রথাবিরোধী নানন্দিক অভিব্যক্তি নিয়ে আলোচনা বাংলা ভাষায় অপ্রতুল। বাক্য ও ভাষারীতি নিয়ে প্রায়শই বিদ্যায়তনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রথাবদ্ধ আলোচনার কারণে উপেক্ষিত থেকে গেছে শৈলীর স্বাতন্ত্র্যে গরীয়ান আমাদের করমেয় লেখকদের শিল্পিত স্বভাবের সবুজ মানচিত্রটি। আমি বলছি না যে শৈলী (Style –এর বাংলা তর্জমা ধরে নিয়ে) বিষয়ে বাংলা ভাষায় একেবারেই কোনো আলোচনা হয়নি। প্রণয়কুমার কুণ্ডু, পবিত্র সরকার, অরবিন্দ পোদ্দার, নবেন্দু সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সৌরভ সিকদার, পরেশচন্দ্র ও অভিজিৎ মজুমদারসহ আরও কেউ কেউ করেছেন। কিন্তু তাঁদের বেশির ভাগেরই আলোচনা মূলত শৈলীগত অনুধাবনের নামে বিদ্যায়তনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষার কলকবজা ও তার নান্দনিক বিন্যাসকে কেন্দ্র করে শাস্ত্রীয় আলোচনা। শিশিরকুমার দাশ, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন বা পবিত্র সরকার ব্যতীত প্রায় সবার আলোচনাই একাডেমিক। ভাষিক সৌন্দর্য ও বৈভবের পেছনে শুধুই যে কলাকৌশল নয়, বরং লেখকের কল্পনা ও কাব্যবোধের দাম্পত্য রসায়ন থেকে ভাষার কলাকৌশলগত প্রয়োগকে অতিক্রম করে বাস্তব ও যুক্তির শৃঙ্খলাকে চুরমার করে অন্য এক অনুভূতির জন্ম দিচ্ছে– সে নিয়ে আলোচনা অতিশয় দুর্লভ। ফলে, শৈলী বা রীতির শীর্ষবিন্দু যারা ছুঁয়েছেন তাঁদের গদ্যের সৌন্দর্য নিয়ে আমরা সশ্রদ্ধ হলেও, তার প্রকৃত মূল্যায়ন থেকে আমরা এখনও অনেক দূরে। তবু কখনো কখনো দুএক জনের প্রবন্ধে যে সেরকম উদ্যোগ আমাদের চোখে পড়েনি, তা নয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যশৈলী নিয়ে শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধের কথা আমাদের মনে পড়বে, মনে পড়বে বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের ছন্দস্পন্দিত গদ্য নিয়ে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের প্রবন্ধ। কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যশৈলী নিয়ে শিশিরকুমার দাশের অনবদ্য আলোচনা। চিন্ময় গুহ’র কোনো কোনো প্রবন্ধেও আছে সেই ক্ষীণ ধারার শীর্ণ আয়োজন। ভাষিক ও ভাবুকতার সম্মিলিত অভিঘাতে আলোচিত লেখকদের যে শৈলীর জন্ম হয়েছে, এইসব আলোচনায় সেই দিকটাতেই তাঁরা মনোযোগ দিয়েছেন নির্ভুলভাবে। এখখুনি, এও স্বীকার করে নেয়া ভালো যে এ ধরনের আলোচনার ঐতিহ্যকে বেশি দূর প্রসারিত করার সুযোগ আমাদের ছিলও না, যেহেতু এর পক্ষে রচনাগত দৃষ্টান্ত অতি অল্প।
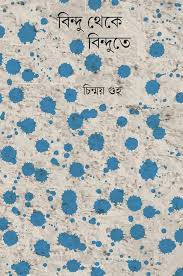
শৈলী ও ব্যক্তিত্ব
কোনো লেখকেরই শৈলীগত বৈশিষ্ট্য এড়িয়ে তার আত্মার স্পন্দন পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় ভিন্ন ধাতুতে গড়ে ওঠা তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বরূপকে বুঝে ওঠাও। কারণ বুফোঁর ভাষায় : Style is the man hismself, গোটা ব্যক্তিত্বেরই প্রতিফলন ওই শৈলী। পশ্চিমের সাহিত্য-আলোচনায় শৈলীগত এই ধারণার প্রাধান্য থাকলেও, বাংলা ভাষায় প্রবন্ধের শৈলীগত অনুধাবন, অনুসন্ধান ও বিচার উল্লেখযোগ্য রকমে গুরুত্ব পায়নি। যা পেয়েছে তা শব্দ ও ভাষিক কলাকৌশলকে আশ্রয় করে আলোচনার নিষ্প্রাণ বিস্তার। পাশাপাশি এই সত্যও আমাদের মনে রাখতে হয় যে পশ্চিমে গদ্যের বয়স ও ঐতিহ্য আমাদের তুলনায় দীর্ঘ হওয়ার কারণেই তার নানামুখী আলোচনা হয়েছে। শৈলী নিয়ে আলোচনার দারিদ্রের পেছনে বাংলা ভাষায় নমুনার স্বল্পতাও একটি বড় কারণ। অমিত রায়কে দিয়ে শেষের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যখন স্টাইল সম্পর্কে এ-কথা বলিয়ে নিচ্ছেন: “ফ্যাশনটা হলো মুখোশ আর স্টাইলটা হলো মুখশ্রী”, তখন বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথ শৈলীর আঙ্গিক নয়, বরং এর আত্মাকেই স্পর্শ করতে চেয়েছেন। আমাদের বেশির ভাগ লেখকের ক্ষেত্রেই মুখোশটাই মূখ্য হয়ে উঠেছে, মুখশ্রীর সন্ধান ও অর্জনের সাধনায় তাই মুষ্টিমেয় লেখকের দেখা পাওয়া যায়। সাহিত্যিক, কিংবা শৈল্পিক বিচারেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখক আছেন, কিন্তু সুক্ষ্ণ বিচারে শৈলীপ্রধান লেখক আমাদের একেবারেই হাতে গোণা।
শৈলীর স্বরূপ
কারোর মতে শৈলী হচ্ছে Mode of linguistic presentation. বাংলা ভাষায় শৈলীগত অনুধাবন ও আলোচনায় এই ধারণার প্রভাবই বেশি। কারো কারো ক্ষেত্রে এটা নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু কোনো কোনো লেখকের ক্ষেত্রে এটা কেবল ভাষিক উপস্থাপনের উপায়ই নয়, তা ভাবনার শৈলীও হয়ে উঠেছে। এমনটা যখন ঘটে তখন সেটা কেবল Mode of linguistic presentation-এ সীমাবদ্ধ থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র, সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, শঙ্খ ঘোষ কিংবা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের ক্ষেত্রে আমরা এর রাজযোটক দেখতে পাবো। আবার ভাষা এবং ভাবুকতার এই মুড নেই, এমন লেখকও আছেন। বিষ্ণু দে’র প্রবন্ধে ভাষিক ও ভাবুকতার শৈলী প্রায় নেই বললেই চলে। প্রায় বৈশিষ্ট্যহীন, শীতল, উত্তাপবিহীন এক গদ্যপ্রবাহ। এই গদ্য আমাদের হিমায়িত স্নায়ুকে দ্রবীভূত করার দিকে মনোযোগ দেয় না। অমিয় চক্রবর্তীর গদ্যও তাই। অন্যদিকে, সুধীন দত্তের গদ্য বাচনিক সর্পিলতা আর ভাষিক ছন্দোময় গতি আর চিন্তার সৌকর্য পাঠকের জন্য কিছুটা দুরধিগম্য হলেও, তাতে সুধীন্দ্রীয় শৈলী এতটাই লক্ষণাক্রান্ত যে পাঠমাত্রই এই গদ্যকে সনাক্ত করতে পারেন অনায়াসে, যদিও বয়ানের সর্পিলতা মনোযোগকে মাঝেমধ্যে কিঞ্চিত পীড়িত করে। এই গদ্য শুধুই ভাষিক উপস্থাপনের স্বাতন্ত্র্যকে অবলম্বন করে নয়, এর সঙ্গে বিজড়িত সুধীন দত্তের ভাবুকতা ও চিন্তার জটিল বুননের স্মারক-স্বভাবও; ভাষা কিংবা বাক্যরীতি এক্ষেত্রে তারই বিশ্বস্ত অনুগামী মাত্র। ভাবুকতা, চিন্তার এই স্বাতন্ত্র্য ও সজীবতা যেখানে নেই ভাষা সেখানে নিছক কঙ্কাল মাত্র, ঠিক যেমনটা বলেছিলেন জীবনানন্দ দাশ অনুভূতিবর্জিত ভাষার স্বরূপ নিয়ে:
মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।”
আমরা এই ‘জ্ঞানের’ পরিবর্তে ‘ভাবুকতার সোনালি সৌরভ’ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতে পারি শৈলীর স্বরূপটি বুঝাবার জন্য। অনুভূতিদেশ থেকে ওই আলো যে-গদ্যে নেই তা নিষ্প্রাণ, স্পন্দনহীন। সুতরাং স্টাইল বা শৈলী বলতে যা বুঝাতে চাইছি বোদল্যের-এর উক্তি দিয়ে তা আরেকটু পরিস্কার করে তোলা যায়: “Always be a poet, even in prose.”। বাংলা ভাষায় এরকম গদ্যের নমুনা নিশ্চিতভাবেই কম যেখানে কবিতার সঙ্গে তার গাটছড়া বাঁধা। তবে অল্প হলেও আছে, যেমন ধরা যাক জীবনানন্দ দাশ-এর এই বাক্যগুলো:
“প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মতো লুকিয়ে থাকে যেন।” (কবিতার কথা, পৃ ৮)
“জীবনের সমস্যা ঘোলা জলের মুশিকাঞ্জলির ভিতর শালিকের মতো স্নান না করে বরং যেন করে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের শাদা রৌদ্রের মতো;–সৌন্দর্য ও নিরাকরণের স্বাদ পায়।” (কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, চতুর্থ সংস্করণ: মাঘ ১৩৮৭, পৃ ৯)
“কিন্তু তবুও সেই সৌন্দর্যের ভিতর গোপন ভাবে বিধৃত রেখা উপরেখার মতো যে জিনিসগুলো মানবী বা ঘাসের সৌন্দর্যের আভার মতো রসগ্রাহীকে প্রথমে ও প্রধান ভাবে মুগ্ধ করে না—কিন্তু পরে বিবেচিত হয়—অবসরে তার বিচারকে তৃপ্ত করে।” (কবিতার কথা, পৃ ৮)
উপরের এই উদাহরণগুলো স্মরণ করার উদ্দেশ্য এটাই যে এই বাক্যগুলো শুধুমাত্র ভাষিক বা বাক্যের রীতিগত কৌশলমাত্র নয়, এদের আত্মা সতত স্পন্দিত ও রঞ্জিত কাব্যবোধের দ্বারা। এই বাক্যগুলো স্ফূর্তি ও প্রাণস্পন্দনে এতই জীবন্ত আর ইন্দ্রিয়ঘন যে পড়ামাত্র আমাদের রক্ত ও স্নায়ুর পালকে মৌসুমী সমুদ্রের সবুজ হাওয়ায় স্ফীত করে তোলে। উপরন্তু, বিভিন্ন উপমা ও চিত্রকল্প কবির অনুভূতির ‘নিহিত পাতাল ছায়া’কে করে তোলে দৃশ্যমান। আর তা স্বভাবত কাব্যস্পর্শী। বাংলা গদ্যে এর ব্যাপক ও সার্থক সূচনা রবীন্দ্রনাথে আর এখনও পর্যন্ত এর শেষ প্রতিনিধি চিন্ময় গুহ।
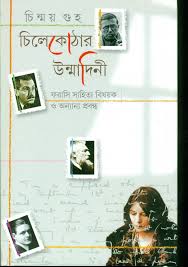
ইংরেজি ভাষায় শৈলীর ধারণায় একাডেমিসিয়ানরা ভাষা ও বাক্যের সৌকর্যের উপর অপেক্ষাকৃত বেশি পক্ষপাত দেখালেও সৃষ্টিশীল লেখক ও দার্শনিকরা ভাবুকতার স্বাতন্ত্র্য ও নান্দনিক দিকটিকে অন্তর্ভুক্ত করতে ভোলেন নি। লর্ড চেস্টারফিল্ড যখন বলেন “Style is the dress of thoughts.” তখন আপাতভাবে কথটা সত্য মনে হলেও, একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারি তিনি কেবল শৈলীগত কঙ্কালের দিকেই ইঙ্গিত করছেন। অর্থাৎ, শৈলী তাঁর কাছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়, বরং অঙ্গের আচ্ছাদন। শৈলী কি শুধুই পোষাক? রবীন্দ্রনাথ যাকে ‘মুখোশ’ বলে পার্থক্যটা চিনিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের তত্ত্বাচার্য কেতাবকুলশিরোমনিদের প্রায় প্রত্যেকেই অনুপম বাচনের রীতিতে ওই পোষাকটিকেই শৈলীর স্মারক বলে অভিহিত করলেন। কিন্তু চেস্টারফিল্ড-এর এই ধারণাকে টমাস ডি কুয়েন্সি মেনে নেননি, তিনি তা খণ্ডন করেছিলেন এই বলে যে “Human body is not the dress or apparel of human spirit;”। শৈলীর ভূমিকা ও স্বরূপ সম্পর্কে কুয়েন্সি আমাদের সজাগ করে দেন এই বলে যে: “Style has two separate functions: first, to brighten the intelligibility of a subject which is obscure to the understanding; secondly, to regenerate the normal power and impressiveness of a subject which has become dormant to the sensibilities. . . . The vice of that appreciation which we English apply to style lies in representing it as a mere ornamental accident of written composition–a trivial embellishment, like the mouldings of furniture, the cornices of ceilings, or the arabesques of tea-urns. On the contrary, it is a product of art the rarest, subtlest, and most intellectual; and, like other products of the fine arts, it is then finest when it is most eminently disinterested–that is, most conspicuously detached from gross palpable uses. Yet, in very many cases, it really has the obvious uses of that gross palpable order; as in the cases just noticed, when it gives light to the understanding, or power to the will, removing obscurities from one set of truths, and into another circulating the life-blood of sensibility.
…style becomes the incarnation of the thoughts. Human body is not the dress or apparel of human spirit;” (Essays on Style, Rhetoric, and Lenguage, Thomas De Quincey, ed. By Fred N. Scott, Allyn and Becon, 1893, P 212- 214)
শৈলী প্রসঙ্গে ডি কুয়েন্সি স্পষ্টতই জোর দিয়েছেন, প্রথমত অবোধ্যকে বোধগম্য করে তোলায়, দ্বিতীয়ত সুপ্ত বিষয়টিকে সংবেদনশীলতার কাছে স্বাভাবিক শক্তি আর আকর্ষণীয়তাসহ জাগিয়ে তোলায়। মোট কথা, ‘সংবেদনশীলতার জীবনসঞ্চারী রক্তপ্রবাহের চলাচলের’ উপরেই রয়েছে তাঁর শৈলীবিষয়ক ধারণার ভরকেন্দ্র। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, হুমায়ূন আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং চিন্ময় গুহ মূলত ডি কুয়েন্সি-কথিত স্বরশৈলীর নয়টি সিম্ফনি, কিন্তু একই রাগের ভিন্ন গায়কীতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাদের প্রত্যেকেই। এঁদের মধ্যে চিন্ময় গুহ একেবারেই ভিন্ন স্বরযোজনায় আলাদা হয়ে আছেন, কিন্তু পূর্বসূরী কেউ কেউ তাঁকে অংশত অনুপ্রাণিত করেছেন নিজস্ব মেজাজ গড়ে তুলতে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যাঁকে গদ্যের সিদ্ধিদাতা গণেশ বলে অভিহিত করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যের পিতৃকুলের আদিপুরুষ।
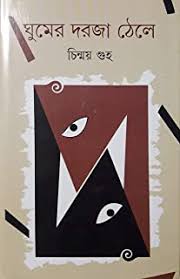
চিন্ময়-তরঙ্গ
রবীন্দ্রনাথের বাঁশরি নাটকে বাঁশরি বলছে: “আগুনের সাপ ফণা ধরেছে–এখনও চেতিয়ে উঠল না তোমার কলম, আমার তো কাল সারারাত্রি ঘুম হল না। এমন লেখা লেখবার শক্তি কেন আমাকে দিলেন না বিধাতা যার অক্ষরে অক্ষরে ফেটে পড়ত রক্তবর্ণ আগুনের ফোয়ারা।” (বাঁশরি – দ্বিতীয় অঙ্ক – প্রথম দৃশ্য, ১৯)
রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত বাক্যের ‘রক্তবর্ণ আগুনের ফোয়ারা’ আমরা চিন্ময় গুহ’র গদ্যের পর্বত বেয়ে নেমে আসতে দেখবো কল্পনামধুর বাকপ্রতিমার সবুজ অরণ্যের তৃষ্ণায়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের কাব্যগুণ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু যা বলেছিলেন তা চিন্ময় গুহর প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক বলে এই মুহূর্তে তলবযোগ্য: “তাঁর গদ্যের গুণ কবিতারই গুণ…যুক্তির বদলে তিনি দেন উপমা, তথ্যের বদলে চিত্রকল্প;…যেখানে বুদ্ধির কাছে প্রমাণ দিতে হবে সেখানে তিনি বেআইনিভাবে আমাদের হৃদয়ের আর্দ্রতা সম্পাদন করেন।” ( বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র-৩, পৃ ২১৭) চিন্ময় গুহর প্রবন্ধে আমরা প্রায় এর অনেকখানি উত্তরাধিকার দেখতে পাবো, কিন্তু এক বিনম্র পুনর্বিন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ থেকে খানিকটা ভিন্ন উপায়ে, ‘বেআইনিভাবে’ কাব্য আর কাল্পনিক আখ্যানের সোনার জলে স্নাত হয়ে ওঠে তাঁর গদ্য। “আমরা তাঁকে দোষ দিতে পারি সাহিত্যে বর্ণসংকরতা ঘটিয়েছেন বলে;”(প্রাগুক্ত, পৃ২১৮)—কিন্তু যদি তেমনটা না ঘটাতেন রবীন্দ্রনাথ, তাহলে গদ্য মুক্তি পেত না প্রথার শৃঙ্খল থেকে। আর এই মুক্তিই অনাগত অসংখ্য মুক্তির জন্য হয়ে ওঠে উদ্দীপক, প্রলুব্ধকর। চিন্ময় গুহ সেই উদ্দীপনার উজ্জ্বল সন্তান।
রবীন্দ্রনাথ নামক প্রপিতামহ তাঁর সেই প্রমিথিউস যিনি চিন্ময় গুহর জন্য রেখে গিয়েছিলেন কল্পনার ললিত আগুন। পিতামহ বুদ্ধদেব বসু তাঁকে দিয়েছেন ভাষার ছন্দোময় বিন্যাসের কুশিকাটা যা দিয়ে চিন্ময় গুহ ভাষার জমিনে ভাবুকতাকে সুরম্য নকশায় রূপান্তরিত করেন। পিতৃপ্রতীম শঙ্খ ঘোষ তাঁকে দিয়েছেন কোমল স্বরের কুহকী মন্ত্র। পিতৃব্য অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁকে প্ররোচিত করেছেন বহুভাষার ব্যঞ্জনে ও পাণ্ডিত্যের পরাগায়নে। তিনি একদিকে ‘অনুভূতিময় কল্পনা’কে তথ্যের ধমনীতে এমনভাবে প্রবাহিত করেন যেন তারা বহুকাল থেকেই পরস্পরের পরমাত্মীয়, যেন শুধু সাক্ষাতের অভাবে উভয়ে নিঃসঙ্গ ও অভিশপ্ত এক নিরস যাপন মেনে নিয়েছিল; কিন্তু চিন্ময় গুহ’র পৌরহিত্যে সূচিত হলো ওই নিঃসঙ্গতার অবসান আর অন্য এক আরম্ভ। উপরোক্ত লেখকরা প্রবন্ধের জগতে কোন মন্ত্রবলে পাঠককে ভিন্ন রুচিতে দীক্ষিত করে তুলেছেন তার হদিস নিলে দেখা যাবে মূলত কাব্যচেতনা ও ভাষিক সুষমার সঙ্গতি সাধনই এর প্রধান কারণ। বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে গিয়ে অলোকরঞ্জন যা বলেছিলেন তা চিন্ময় গুহ সম্পর্কেও এক নির্ভুল নির্দেশিকা হয়ে উঠেছে:
“কবিতার কাছ থেকে ঋণ না নিয়ে গদ্য কখনোই তার স্বাধিকারভূমি খুঁজে পাবে না, এই বিশ্বাস বুদ্ধদেবের মনে উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হয়ে চলেছিল।” (বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা, পৃ ২৭৬)
সম্ভবত চিন্ময় গুহর কাব্যমুখী বিশ্বাসও সমন্বয়ী উৎসর্জনে মুক্তি খুঁজেছিল। প্রচলিত গদ্যের ‘সুরম্য জঞ্জাল’ ও বাচাল ভস্ম থেকে ভাষাকে রক্ষা করার একলব্য-নিষ্ঠায় চিন্ময় ভিন্ন শর ও স্বর যোজনা করে নিয়েছিলেন। চিন্ময় গুর’র রচনার স্বাদ আমরা সরাসরি গ্রহণের আগে কিছু শব্দের বিপরীতার্থক ব্যবহার সম্পর্কে জেনে নেবো যা আমাদের পাঠের জন্য সহায়ক হয়ে উঠতে পারে: যেমন ‘ঘুম’, ‘আয়না’ কিংবা ‘রক্তদীপ’। তাঁর একটি বইয়ের নাম আয়না ভাঙতে ভাঙতে। কিন্তু আসলেই কি ভাঙছেন? বরং উল্টো: তিনি বিশিষ্টজনদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে নির্মাণ করছেন অনঘ লহরীঘন আয়নাগুচ্ছ। আর অন্ধ আয়না? না, এই আয়না অন্ধ কিন্তু সে সবচেয়ে চক্ষুষ্মান; দিব্যদর্শী এই অন্ধ আমাদের হোমার, দক্ষিণের বোরহেস, কিংবা সেই সুদূর কালের তাইরেসিয়াস, ত্রিকালদর্শী এক অন্ধ মুকুর যেখানে তিনটি কালের খিলানগুলো দৃশ্যমান; অন্ধ নয়, এ এক জন্মান্ধ আয়না, অগ্রসর রুচির এক বর্ণময় ভূমন্ডল সোনার আখরে যা আল্পনাময়। এই অন্ধ আয়না আমাদের অন্ধত্ব ঘুচায়। ঘুমের দরজা ঠেলে তিনি কোথায় যাচ্ছেন? যাচ্ছেন এক শষ্পময় জাগরণে, যেখানে শব্দ আর সত্যগুলো ত্রিতাল-ছন্দে নৃত্যরত অনূঢ়া পৃষ্ঠার শুভ্র প্রহরে। আর বিন্দু থেকে বিন্দুতে? সেও এক বিপ্রতীপ বিহার; ব্যক্তি ও বিষয়ের সিন্ধু সেচে তিনি মুক্তা তুলে আনেন, বিন্দু তাই সিন্ধুর প্রতিভূ। অর্থাৎ, শব্দ, ভাব ও অভিব্যক্তির অর্থান্তর ঘটিয়ে তিনি আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস ও ভাবনার কাঠামোকে ধ্বস্ত করে দেন। আর প্রবন্ধ এতো জান্তব, বুনো আবেগে দাউ দাউ শিখায় মাতালের মত এতটা মর্মরিত হয়ে উঠতে পারে, তা না পড়লে বুঝা যাবে না। পাগল হাওয়ার অশ্বারোহী এই ‘মাতাল গদ্য’।
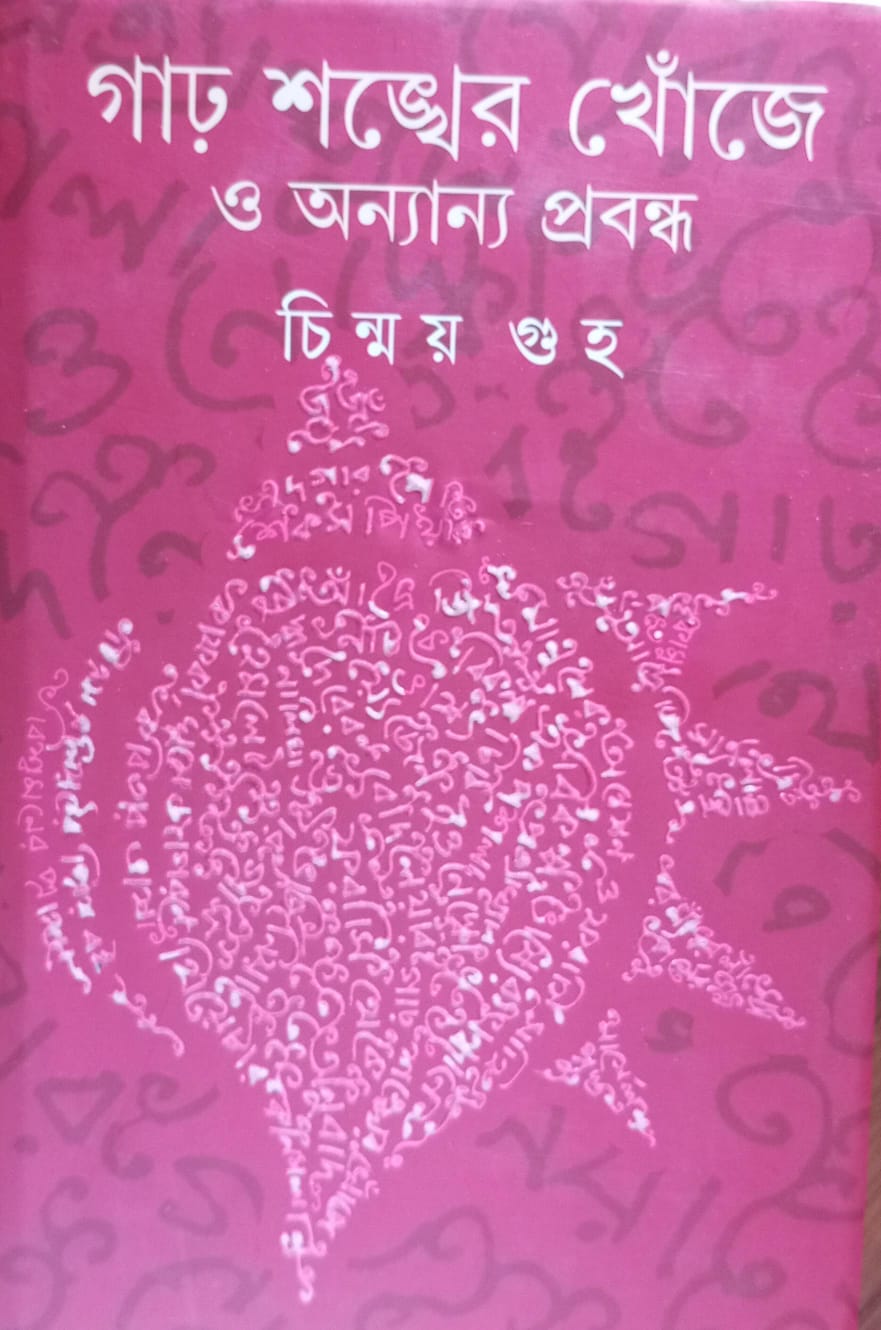
শিশিরকুমার দাশ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে “বারবার একশব্দের বা একধরনের শব্দের ব্যবহারের মধ্যে লেখকের একটি অভিপ্রায় নিহিত থাকা স্বাভাবিক।” (বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা, পৃ ৪১) ‘আয়না’, ‘রক্তদীপ’ ইত্যাদি শব্দ দিয়ে চিন্ময় গুহ তাঁর নিজস্ব অভিব্যক্তি তৈরি করেছেন। এই দুটি শব্দকে তিনি নানাভাবে, নানা অর্থে প্রসারিত করেছেন। কেবল এই দুটিই নয়, একরম আরও শব্দ ছড়িয়ে আছে তাঁর প্রবন্ধপুঞ্জে। এছাড়াও, পূর্বসূরীদের মতো শব্দ ও শব্দবন্ধ উদ্ভাবন চিন্ময় গুহ’র মজ্জাগত বিলাস। আমরা অন্ধ আয়নার কিছু শব্দবন্ধ ও কাব্যশীলিত বাক্যবিথীর মধ্য দিয়ে হেঁটে যাবো:
‘চিন্তারশ্মি’, ‘আলোর শিশির’, ‘শিরাধমনীতে উৎকন্ঠা’, ‘পাণ্ডুর পথরেখা’, ‘মাতালের ধাতুবিভ্রম’, ‘শব্দপ্রজরা’, ‘বোবাস্রোত’, ‘গ্রন্থপ্রদীপগুলি’, ‘অভ্রময় বিস্ফোরণ’, ‘দর্পনদিনে’, ‘মায়াবৃত্ত’, ‘কলঙ্কশীলিত দীধিতি’(এই শব্দযুগল প্রায় অলোকরঞ্জনীয় রসায়নে গড়া)।
“বোদল্যের আর পিকাসো বিস্মিত বিপন্নতায় এই নদীশহরের যোনি চুম্বন করতে চেয়েছিলেন।” (অন্ধ আয়না, পৃ ৩৭)
“আকাশে জ্বলছে এক রঙিন অর্জুন গাছের মতো।” (অন্ধ আয়না, পৃ ৪৩)
“এই দগ্ধ অমানিশায় যে প্রশ্ন আমাদের অসহায় আয়নাগুলো ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে,” (অন্ধ আয়না, পৃ ৬৪)
“আমরা তো কৃষ্ণগহ্বরে ফুটে ওঠা কয়েকটি পীতরক্ত প্রেত শুধু।” (অন্ধ আয়না, পৃ ৬৪)
“অনৈতিকতা শব্দটির টবে নতুন কালো ফুল ফুটেছে। ‘লজ্জা’ শব্দটা পাশের কোনও অজানা বাড়ির ছাদে দড়িতে শুকোচ্ছে। ‘বিবেক’ বলে একটা সেকেলে শব্দ মরা শালিখের মতো পড়ে আছে পেছনের উঠোনে।” (অন্ধ আয়না, পৃ ৭৮)
“এলিয়টের এই বঙ্কিম ভাস্কর্য যেন এক দগ্ধ রাক্ষসের অক্ষিকোটরের মতো।” (অন্ধ আয়না, পৃ ১৪২)
“এত বেদনায় আর্দ্র আকাশখিলান, এত শিশিরভেজা সজলতা আর আর্তি, এত দুঃখনন্দিত সাংগীতিকতা,” (অন্ধ আয়না, পৃ ১৫০)
“তর্ক তাঁর ক্যামেরার রক্ত।” (অন্ধ আয়না, পৃ ১৯৬)
“তাঁর অনুপুঙ্খময় অনুবাদগুলি মূলের মতো কল্পনায় আগুন ধরায়।” (অন্ধ আয়না, পৃ ২১৯)
“হাড়ের নিঃসীম অন্ধকারে কাঁপে। মৃত্যু গৌতমের উপর শুয়ে আছে অসময়ের কুয়াশার মতো।” (অন্ধ আয়না, পৃ ২৪২)
কল্পিত এমন সব বাকপ্রতিমা তিনি তৈরি করেন যা বাস্তব নয়, কিন্তু তার কল্পনাপ্রবণ মন আমাদের খঞ্জ ও মিশকিন বাস্তববোধকে পূর্ণতা দান করে তার কাল্পনিক কথাচিত্র দিয়ে যা আসলে বাস্তবতার উল্টো পিঠে লুকিয়ে থাকা প্রচ্ছন্ন প্রবাল-প্রতিলিপি।
ঘুমের দরজা ঠেলে গ্রন্থে চিন্ময় গুহ’র উদ্ভাবিত শব্দবন্ধ:
‘শব্দের ফিসফিসানি’, ‘একশ ফলা ছুরির মতো’, ‘রক্তবরফের মতো’, ‘মৃত্যু-প্রহেলিকা’, ‘অগ্নিময় আংরাখা’—এনম অসংখ্য শব্দ-যুগল তাঁর গ্রন্থের অলিগলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।
প্রবন্ধের মুণ্ডিত মরু-মস্তকে তিনি বসিয়ে দেন রঙিন উষ্ণীষ, গাম্ভীর্যকে তিনি লুকিয়ে রাখেন গল্পের মুখোশে। এরপর তিনি গল্পময় সবুজ অরণ্য থেকে পাঠককে প্রবন্ধের বিদগ্ধ রাস্তায় তুলে নেন সুমধুর আপ্যায়নে। একটা উদাহরণ নিচে থাকছে:
“প্যারিসে ত্যুইলরি বাগানে লোকজনের ভিড়। বাচ্চারা খেলা করছে। ছোট জলাধারটির ধারে টিনের চেয়ারে বসে এক ভদ্রলোক একটি করে কবিতা পড়ে পাতাগুলো উড়িয়ে দিচ্ছেন হাওয়ায়। কয়েকটি পৃষ্ঠা পায়রা হয়ে উড়ে গেল আকাশে। দু’-একটি পৃষ্ঠা নাচের ভঙ্গিতে জলে নামতে-না-নামতেই কাগজের নৌকো হয়ে ভাসতে লাগলো।” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ৭২)
তাঁর প্রবন্ধের আখ্যানধর্মীতার আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক:
“ঘুমের ভিতর দেখতে পাচ্ছি সুদূর ইতালির লেরিচি উপসাগরে ভেসে আসছে এক অবিশ্বাস্য রূপবান যুবকের শব! ঢেউয়ের মাথায় সাপের মনিতে ফসফরাসের মতো ঝলসে উঠছে তার মুখ। এত রূপ?
গত ৪ অগাস্ট শেলি-র জন্মদিন ছিল। আর সেই দিনই ফরাসি কবি বোদল্যেরের সঙ্গে সমুদ্র-অভিযানে বেরিয়ে ইংরেজ কবি শেলির মৃতদেহকে আবিষ্কার করলাম আমি? অথচ শেলির মৃত্যুর সময় বোদল্যেরের বয়স মাত্র এক। ঘুমের মধ্যে এমন হয়!” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ৯০)
সত্যিই কি হয়? আমাদের স্থূল যুক্তিবোধ একে কখনোই সত্য বলে মেনে নেবে না। কিন্তু নিমগ্ন চেতনায় এর সম্ভাবনা যদি মৃদুমাত্রায়ও থাকে, তবে সংবেদনশীল কোনো প্রাবন্ধিক সেটাকেই অনুভূতির আতশকাঁচের নিচে আয়তাকারে উপস্থাপিত করবেন। চিন্ময় গুহ ঠিক তাই করেছেন। অএতব, স্বপ্নময় নিদ্রায় এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয়, আর তা যদি হয় চিন্ময়-নিদ্রায়!
এই গ্রন্থে ব্লেজ সাঁদ্রারস নিয়ে ১৮ নং যে ভুক্তিটি আছে, সেটা শুরুই করেছেন পুরোপুরি গল্পের ভঙ্গিতে বর্ণনা দিয়ে, পুরো একটি পৃষ্ঠাব্যাপী তাঁর গল্পকে গড়িয়ে যেতে দেখবো আমরা যেখানে অপরূপ বর্ণনায় আবস্যাঁৎ, সুদর্শন দুই যুবতী, সাঁদ্রারস, মার্ক শাগাল, মদিল্লিয়ানি, আপোলিনের, পিকাসোকে দেখতে পাই। প্রবন্ধের শরীরে এভাবে তিনি গল্পের রক্ত ঢুকিয়ে দেন। প্রবন্ধকে তিনি গদ্যের-কেরানির-হাতে-কঙ্কাল-হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন। এই কঙ্কালে যুক্ত করলেন রক্ত, মাংশ, স্তন, নিতম্ব, যোনি; আবেগের স্বর্ণরেণু, যুক্তির কোমল আগুন, আর সর্বোপরি স্তব্ধ পাষাণখণ্ডকে গালাতেয়ার মতো সুন্দর ও জীবন্ত করে তোলেন।
প্রবন্ধের মধ্যে অনায়াসেই তিনি, অকম্পিত আস্থায় বিপরীত মেজাজের শিল্পমাধ্যমকে যুক্ত করে দূষিত করেন, কিন্তু এই দূষণ হয়ে ওঠে নান্দনিক পুনর্বিন্যাসের ভিন্ন এক শুদ্ধতা, আর তাই এই দূষণের ফল হয়ে ওঠে অভিনব, অভাবনীয় ও উপভোগ্য। প্রবন্ধকে তিনি প্রথার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন, তাকে শ্বাস নিতে দেন স্বাধীন এক পরিমণ্ডলে। তার গায়ে চড়িয়ে দেন মিশ্র বুননের জরিদার আলখাল্লা। কিংবা যা হয়ে ওঠে ইয়েটস-কথিত ‘সোনা রুপার আভায় বোনা উত্তরীয়’।
এই গ্রন্থে তিনি কত যে ফরাসি ও ইংরেজ লেখকদের শিরা-উপশিরা উন্মুক্ত করে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে যাদেরকে আগে কখনোই বাংলা ভাষায় দেখিনি। কিন্তু সেই মূল্যায়ন আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা দেখতে চাই তাঁর শৈলীর শৈল-শিখরগুলো।
“শূন্যে কালপুরুষের তারবারি। নীচে স্বেদ, রক্ত, শব্দগুঁড়ো, ভাসমান কাগজের স্তুপ।” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ১)
“ভলতেয়ার ছাড়া কে এত নির্মম শিল্পিত হিংস্রতায় খুলে দিতে পারেন ধর্মীয়, সামাজিক আর রাজনৈতিক ভণ্ডদের ছলছলানো মুখোশমালা?” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ৬)
“‘কাঁদিদ’-এর পৃষ্ঠা বেয়ে চুঁইয়ে পড়া একটি শিশির যেন বিশ্বসংসারকে এক মায়ামুকুরে ধরে রেখেছে।” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ১০)
“তার সুষুম্না বেয়ে নেমে আসে রক্তের লাল মুক্তো।” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ২৭)
“যা সমস্ত অন্তর্লীন স্রোতকে এক রক্তমোহনায় মিলিয়ে দেবে।” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ২৭)
“তাঁর শিরা-উপশিরা সমুদ্রের নীল জলে ভরে যায়।” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ৬৩)
“মানিকতলায় ঘাসের জঙ্গল আর গাছে ঢাকা তার অবহেলিত সমাধিতে কয়েকটা ভেজা পাতা উপুড় হয়ে কাঁদছে। তারা কি জানে তরুলতা এখন রূপকথার দেশের রানি হয়ে গিয়েছে?” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ১০২)
“যা ছিন্ন হতে থাকা মানচিত্রে এক চলমান চিত্রমালার মন্তাজ।” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ১০৬)
“শব্দের শরীর থেকে রক্ত পড়ছে।” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ১০৯)
“সামনে অন্তত রাত ডানা মেলে উড়ছে।” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ১১৫)
“আকাশের তারারা স্ফটিকের মতো গলে গলে পড়ছে সেই পৃষ্ঠার ওপর।” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ১১৫)
“আকাশ থেকে নক্ষত্রের জল পড়ছে। আর তার স্নিগ্ধ চুম্বন ভিজিয়ে দিচ্ছে কবিতার হাড়।” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ১২১)
“পাখির পালকের মতো নরম একটি রক্তিম ঋজু রেখা,” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ১২১)
“তারপর এল নরকের কালো ঢেউ।” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ২০৫)
“শঙ্খরেখাসর্পিল তমিস্রার মধ্যে দাঁড়িয়ে আলোর জন্য হাহাকার।” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ২০৫)
“যেন স্নায়ুতট বেয়ে সমাহিত নদীদের আলো মিশে যাচ্ছে শরীর-মাটির ঢেউয়ে,” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ২৩০)
“মৃত্যুর চুনি-মুখ রক্তের শিকড় খুঁজছে।” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ২৩৯)
“রক্তবিন্দুটি গলা থেকে নেমে এসে একটি ব-দ্বীপ সৃষ্টি করলে।” ( ঘুমের দরজা ঠেলে, পৃ ২৪৬)
উপরোক্ত বাক্যগুলো যেন গদ্যকবিতার কোনো অংশবিশেষ, কিংবা স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ কোন কবিতাই যা সংক্ষিপ্ততা ও বাকসংযমের চূড়ান্ত শিল্পরূপ। উপমা ও চিত্রকল্প, কল্পনা ও সত্য—এই চার বাহুতে পরস্পরকে জড়িয়ে নিয়ে তাঁর বাক্যগুলো আমাদের রুচিকে দেয় ডানার উল্লাস। বিন্দু থেকে বিন্দুতেও তাঁর সেই শব্দ-কল্প-ব্রত অব্যাহত।
বিন্দু থেকে বিন্দুতে গ্রন্থে তাঁর উদ্ভাবিত শব্দবন্ধ ও উদ্ধৃতির অরণ্যে মর্মরধ্বনি শুনতে পাবো:
শব্দবন্ধ: ‘শম্বুক-শঙ্কিত’, ‘বিক্ষতস্নায়ু’, ‘স্নায়ুর খোড়লে’, ‘ক্লিন্ন কঙ্কাল’, ‘মৃগনাভিঘন ভিটে’, ‘প্রযুক্তি-চতুর পৃথিবী’, ‘অনলনিঃশ্বাসী রথ’, ‘রিক্ত কঙ্কাল’, ‘গুঁড়ো গুঁড়ো নৈঃশব্দ্য’, ‘ক্লিন্ন মোমবাতি’, ‘শব্দের নাভিতে’, ‘শষ্পলিপি’, ‘সাহিত্যের বধ্যভূমিতে’,‘ঘুমের রক্তঢেউ’, ‘ফসফরাসদীপ্ত লাইনগুলো’, ‘অশ্রুর অঙ্গার’, ‘অন্তহীন বিতর্কের অগ্নিবলয়ে’, ‘তুরপুন-তীক্ষ্ণ প্রশ্ন’ ইত্যাদি।
নতুন নতুন অভিব্যক্তি তৈরি করা তাঁর প্রধান প্রবণতা, তা সে শব্দবন্ধ, বাক্যাংশ কিংবা গোটা একটি বাক্যের আয়তনেই হোক না কেন। যেমন পাসকাল নিয়ে আলোচনার সূত্রে তিনি মানুষকে নতুন পরিচয়ে তুলে ধরছেন ‘মানুষ নামক শ্বাসরোধকারী গ্রন্থ’ অভিধায়।
স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন-মথিত তাঁর পরাবাস্তব চিত্রকল্প তাঁর প্রবন্ধকে কখনো কখনো কবিতার গোপন দুহিতা করে তোলে।
“যখন গভীর রাতে দুঃস্বপ্নের মধ্যে হঠাৎ আয়নার ভাঙা কাচে আমার শিরা কেটে যায়, রক্ত থামাতে গিয়ে ‘আমি’ নামের একাকী ক্ষতচিহ্নকে খুঁজতে কোন অন্ধকারে তলিয়ে যাই আমি। সুদূর শতভিষা থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত নেমে এসে চুঁইয়ে পড়ে একটি বইয়ের গা বেয়ে। আমি চমকে উঠে দেখি, সেটি পাসকালের অসমাপ্ত নোটস নিয়ে তৈরি বিখ্যাত গ্রন্থ ‘পাঁসে’,” (বিন্দু থেকে বিন্দুতে, পৃ ৫৪)
কাল্পনিক এবং আলংকারিক বয়ানের মাধ্যমে বাস্তবের ইশারাচিত্র তিনি আঁকেন যা মর্ত্য ও অমর্ত্য বোধের সংকেতলিপি হয়ে ওঠে।
“নগ্ন অন্তর্দগ্ধ এক স্তব্ধতা, ঘড়ির শব্দ ছাড়া কিছু নেই, যেন সময়কে কুরে খাচ্ছে অনন্ত ইঁদুর।” (বিন্দু থেকে বিন্দুতে, পৃ ৩১)
“মৃত্যুকাতর ভঙ্গুর মৃৎপাত্র আমরা। জীবনে ফাটল ধরার মুহূর্তে, তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আত্মানুসন্ধানের নতুন এক রক্তদীপময় আয়নার সামনে করোটি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছি।” (বিন্দু থেকে বিন্দুতে, পৃ ৩৩)
“অস্তিত্বের আয়নার ভেতরে প্রদাহ।”(বিন্দু থেকে বিন্দুতে, পৃ ৩৫)
“অন্ধকারের কোন নিঃসীম রেখাবিভঙ্গে স্বাতী নক্ষত্রে হারিয়ে গেলেন।” (বিন্দু থেকে বিন্দুতে, পৃ ৩৫)
“ভাঙা আয়নার গোপন গর্ভে, একা।” (বিন্দু থেকে বিন্দুতে, পৃ ৪৪)
“অক্ষরের ধুলো ছাই হয়ে উড়ছে বিষণ্ণ বাতাসে।” (বিন্দু থেকে বিন্দুতে, পৃ ৬৬)
“তিনি যাদবপুরী হয়েও উচ্চভ্রু যাদব নন।” (বিন্দু থেকে বিন্দুতে, পৃ ২৮৬)
“বৃত্তাকারে এক কেন্দ্রোৎসারিত বোধি-স্রোত:” (বিন্দু থেকে বিন্দুতে, পৃ ২৯৮)
চিন্ময় কাব্যগর্ভ বাক্য তৈরি করেন, কখনো কখনো অন্য লেখক থেকে সমজাতীয়, সমধর্মী পংক্তি আহরণ করে তা গদ্যে আত্মীকৃত করেন, যেমন রবীন্দ্রনাথের, জীবনানন্দের, শঙ্খ ঘোষের। তার ‘শব্দের শরীর এত ভাস্কর্যময়’ যে তা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চক্ষু-শ্রুতি-ইন্দ্রিয়সমূহে আগুন ধরায়।
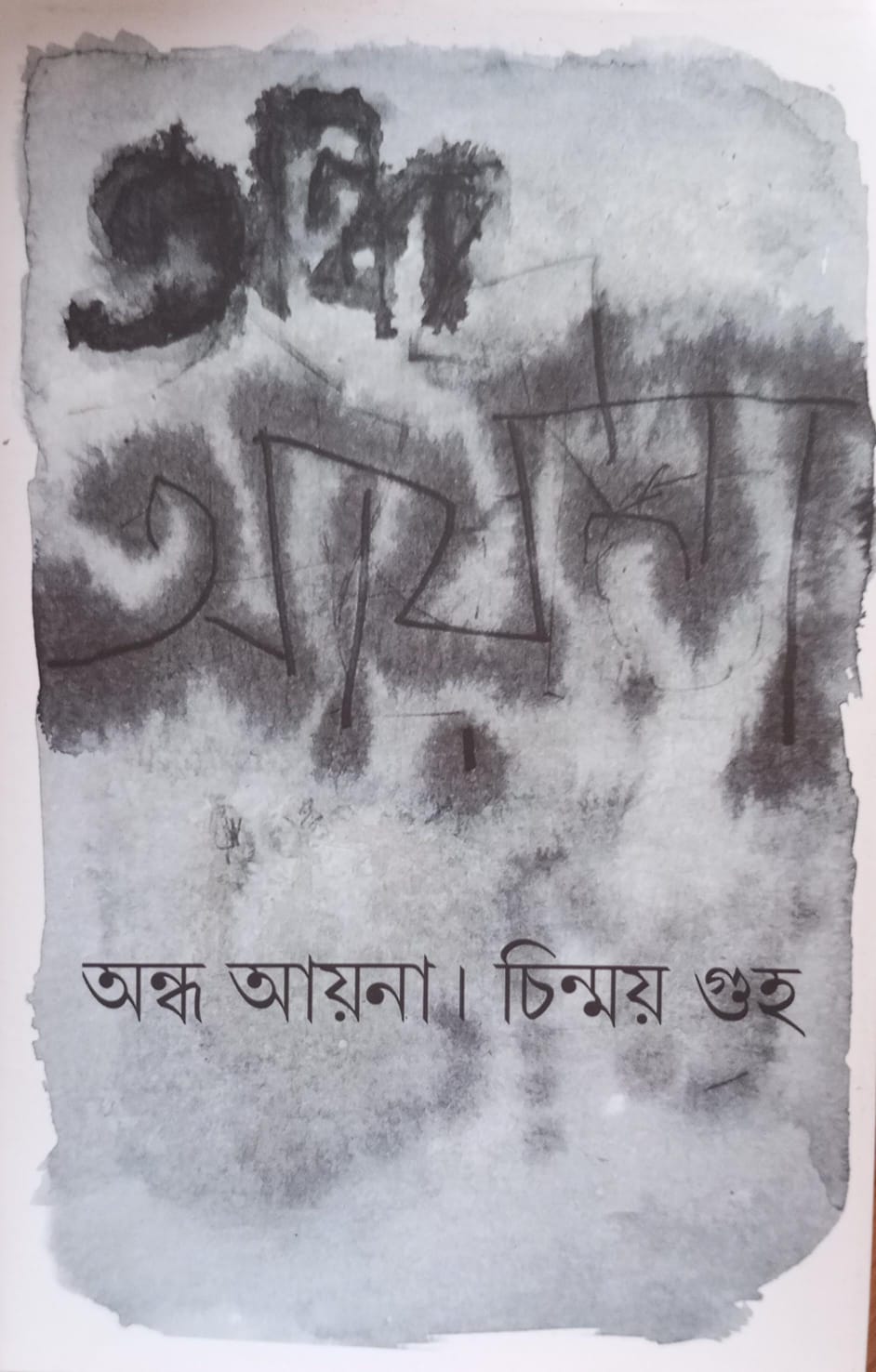
স্প্যানিশ ভাষা ও সাহিত্যে হোর্হে লুইস বোর্হেসের নানাধর্মী অবদান প্রসঙ্গে কার্লোস ফুয়েন্তেস একবার বলেছিলেন: “স্প্যানিশ ভাষার সবগুলো সংকটের (Lacks) সাথেই বোর্হেসকে লড়তে হয়… যে-কারোর ওষ্টাধর পুড়িয়ে দেবার মতো ঠান্ডা গদ্য এই প্রথম আমাদেরকে (লাতিন আমেরিকানদেরকে) গল্প শোনায়… আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন খোপ থেকে বের করে এনে ছুঁড়ে মারে পৃথিবীতে।” ( Borges and his Fiction, Gene H, Bell-Villada, The University of North Carolina Press, 1981, P 37)
চিন্ময় গুহ’র প্রবন্ধের গদ্য প্রসঙ্গে আমরা ফুয়েন্তেসের কথাটা ঠিক উল্টো করে বলবো: বাংলা প্রবন্ধ তোতাপাখির সফল প্রতিনিধিস্বরূপ আমাদের কেরানীকুলের শীতল স্পর্শে এত বেশি ঝিমিয়ে পড়েছিল, এতটাই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল যে, তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য চিন্ময় গুহ’র গদ্যের আগুন ছিল অনিবার্য।
চিন্ময় গুহ এই যে তাঁর প্রবন্ধের শুরুতে প্রায় অবাস্তব বর্ণনা দিয়ে শুরু করেন, কখনো কখনো যা প্রবন্ধের নানা স্তরে, কখনো বা অন্তে গুঁজে দেন তা প্রবন্ধের প্রচলিত ধারণা ও স্বভাবের ঠিক বিপরীত। কিন্তু এই বৈপরীত্যের সঙ্গেই তিনি এক সৃষ্টিশীল বন্ধন তৈরি করেন উল্টো দিক থেকে এসে বাস্তবের বিন্দুতে মিলিত হওয়ার জন্য। এই অবাস্তব সূচনা আসলে কল্পনার এক বাস্তবতা কিন্তু তা আবার একই সঙ্গে আমাদের সর্বজনগ্রাহ্য বাস্তবের মৌল শর্তের কাছে এসে নিজেকে সমর্পন করে। জুডিথ বাটলার তাঁর The force of Fantasy: Feminism, Mepplethorpe, Discursive Excess( 1990) প্রবন্ধে খুব স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন যে “fantasy is not to be equated with what is not real but rather “with what is not yet real, or what belongs to a different version of the real.” ( Columbia History of The American Novel, Emory Elliott, Columbia University Press, 1991,The P 522)
জুডিথ এই কথাগুলো মূলত কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে বললেও, চিন্ময় গুহর প্রবন্ধের রীতি, স্বভাব ও আপাত-অবাস্তব প্রক্ষেপণ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। হ্যারি পটার, জে আর টলকিন-এর লর্ড অব দ্য রিং-এ আমরা যে-ফ্যান্টাসিকে রহস্যময় বাষ্পের মতো মেঘাচ্ছন্ন রূপে দেখতে পাই, চিন্ময় গুহ’র প্রবন্ধে সেই ফ্যান্টাসি আমরা দেখতে পাবো না, কিন্তু যে আবহ দিয়ে তিনি প্রবন্ধ শুরু করেন তা প্রবন্ধের জন্য অবাস্তব, অতএব তা ফ্যান্টাসিরই সহোদর, ফলে যুক্তিতর্ক শাসিত প্রবন্ধের স্বভাবের তা ঘোরতর শক্র। কিন্তু তিনি আশ্চর্য কুশলতায় এই শক্রকে মিত্রে পরিণত করেন। আরও কিছু নজির দেখা যাক তাঁর অন্য এক গ্রন্থ থেকে:
“নামের অক্ষর থেকে স্বর্ণবিন্দু উড়ছে।” ( হে অনন্ত নক্ষত্রবীথি, পৃ ৮)
গদ্য সর্বদাই যুক্তি শাসিত। কিন্তু চিন্ময় গুহ কাব্যবোধকে আশ্চর্য কৌশলে গদ্যে চারিয়ে দিয়েছেন এবং অবাস্তব বা কল্পনাকে তা রূপান্তরিত করে নিচ্ছে কাব্যসত্যে।
“হে অনন্ত নক্ষত্রবীথি, ওপারে উৎকন্ঠা, অসুখ, একাকিত্ব, মৃত্যু, বিশ্বাসঘাতকতা। যন্ত্রণা উপশমের জন্য এক দীর্ঘ নিঃশব্দ আর্তনাদ। যন্ত্রণার খোদাইচিত্র।” (হে অনন্ত নক্ষত্রবীথি, পৃ ১৩)
“তাঁর হাতে এক অন্ধকার আয়না। হে মহাকাশ, মৃত্যু উপত্যকার এক কোণে দাঁড়ানো ওই মহান আলোর পথযাত্রীকে চেনো?” (হে অনন্ত নক্ষত্রবীথি, পৃ ১৯)
“সেই না-পোড়া কাগজের শিখা এই অগ্নিনিশীথে আমাকে দাহন করে।” (হে অনন্ত নক্ষত্রবীথি, পৃ২০)
“যা ইস্পাতের ঢেউয়ের মতো আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।” (হে অনন্ত নক্ষত্রবীথি, পৃ ২১)
“পাখির পালকের মতন নরম তাঁর হাত দুটি বইয়ের ডানা দুটি ছুঁয়ে আছে।” (হে অনন্ত নক্ষত্রবীথি, পৃ ৩৮)
“ওঁর কলম থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত কাগজের ওপর চুঁইয়ে পড়ছে, আর অক্ষরেরা ডানা মেলে উড়ছে সমুদ্রসারসের মতো।
“এই সুরসংযোগ কি অনন্ত আকাশের শিলালিপির গায়ে লেখা ছিল?” ( পৃ৭৬)
“ফরাসি সাহিত্যের সোনার দাঁড় দিয়ে আমায় আকুল দরিয়ায় টেনে নেবে।” (অন্ধ আয়না, পৃ ৩৪)
হৃদয়ের যুক্তি ও কাব্যসত্য দিয়ে তিনি গড়ে তোলেন গদ্যের ভূমি। বাংলা গদ্যকে তিনি পাখির পালকের মতো হাল্কা করে করে নিয়েছিলেন যাতে করে তা হাওয়ায় উড়তে পারে; হুয়ান রামোন হিমেনেসের ভাষায়, গদ্যের শেকড়ে তিনি দিয়েছেন ডানা, আর ডানায় শেকড়।
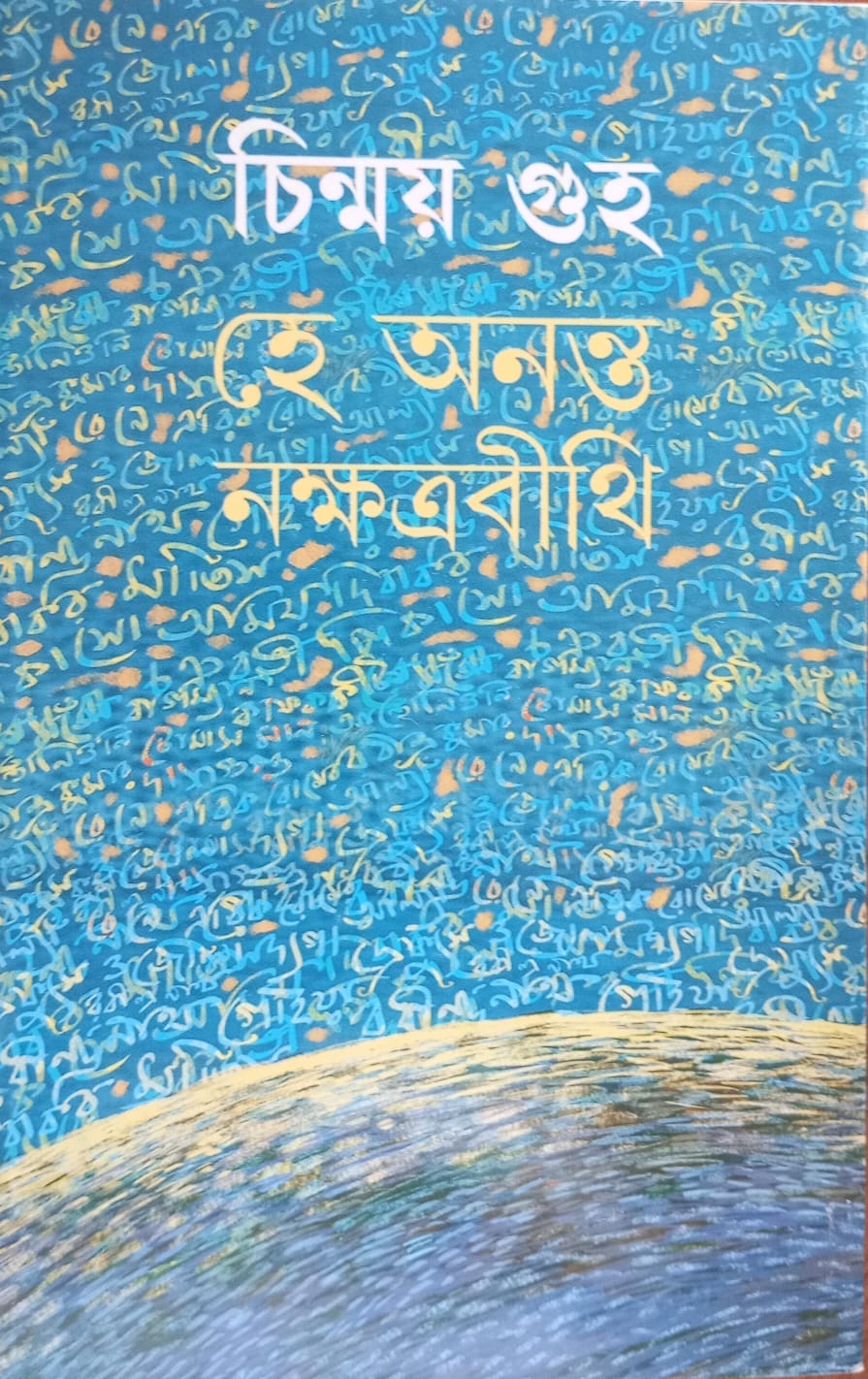
চিন্ময় গুহর মতো এতটা দুঃসাহসের সাথে এবং এতটা আস্থার সাথেও বাংলা প্রবন্ধে কল্পনা ও কাব্যের যৌথ ব্যবহার খুব কম লেখকই করেছেন। বাংলা গদ্যকে কল্পনা ও কাব্যের যুক্ত করপুটে এতো দূর পর্যন্ত অর্পণ—এর আগে এবং পরেও—আর কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ। অসামান্য শৈলী ব্যবহার করে গদ্যকে তিনি কেবল মুক্তিই দেননি, পরবর্তী লেখকদের মধ্যেও সঞ্চার করেছেন নিরীক্ষার হিম্মত। চিন্ময় গুহর গদ্য এমন এক শৈলী-সোপান যা উর্ধায়িত হয়ে ছুঁয়েছে ভাষার অমরাবতীকে।

