
রোদ ও শিশিরের কবিতা : প্রিয় একটি বইয়ের কথা
সন্মাত্রানন্দ
" ক্ষুদ্রাকার এই পুস্তিকাটি ফরাসি ভাষায় লেখা। যদিও আমি ও অন্য অনেকেই পড়েছেন তা ইংরেজি অনুবাদে। বিশ্বজোড়া তার খ্যাতি। আলোচিত হয়েছে পৃথিবীর নানা ভাষায়। বইটির লেখক প্যারিসের কারমেলাইট মনাস্ট্রির একজন লে ব্রাদার। সপ্তদশ শতকে তাঁর জন্ম। পিতৃদত্ত নাম নিকোলাস হারমান। সন্ত-নাম ব্রাদার লরেন্স অফ দ্য রেজারেকশান। আর তাঁর লেখা পুস্তিকাটির নাম—‘দ্য প্র্যাকটিস অফ দ্য প্রেজেন্স অফ গড’। আপনি কী হিসেবে একটি বই পড়বেন, সেটা সম্পূর্ণ আপনার নিজের ব্যাপার। আপনি কোনো একটি বইকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পড়তে পারেন। আবার চাইলে সেই বইকেই আপনি আর্থসামাজিক অবস্থার দলিল হিসেবেও পড়তে পারেন। ব্রাদার লরেন্সের আলোচ্যমান বইটিকে আমি ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পড়িনি। পড়েছি এক অনতিক্রম্য উচ্চতার কাব্যগ্রন্থ হিসেবেই।" নববর্ষ পাঠচক্রে লিখলেন সন্মাত্রানন্দ
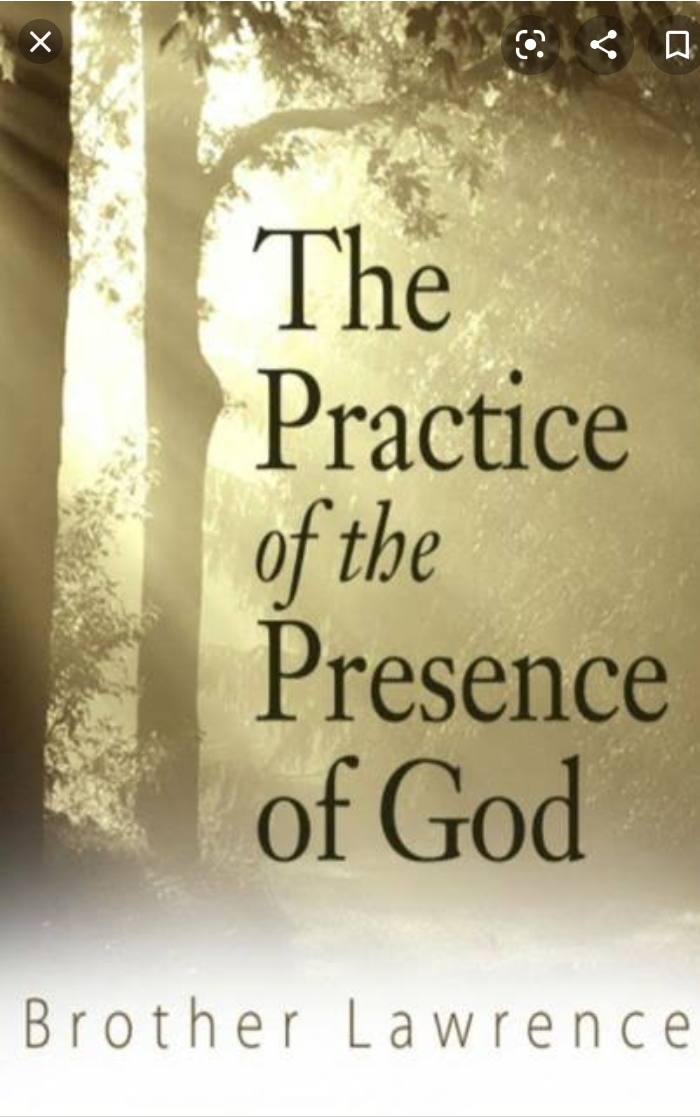
আগম-অপায়ী বছরগুলো স্বাভাবিক নিয়মেই আসে, থাকে, চলে যায়। দিন, মাস, বছর গণনার এই রীতি মানুষের বানানো; বস্তুত সময়ের কোনো পরিচ্ছেদ হয় না। আমরা নিজেদের এবং পরিপার্শ্বের পরিবর্তন অনুভব করি এবং সেই পরিবর্তনকে মাপবার জন্য কতগুলো আপেক্ষিক মাত্রা তৈরি করি। এই জন্যেই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, আজ, কাল, পরশু, এবছর, সেবছরের কল্পনাকে প্রথাসিদ্ধ করে তুলি সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। সময় ব্যাপারটাই যে মানসিক, এবং তার যে কোনো দ্রষ্টানিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ স্বতন্ত্র সত্তা নেই—এই কথাটা এবম্বিধ প্রথার দাসত্ব করতে করতে আমরা ভুলে যাই।
এই ভুলে থাকাকে হাওয়া দিতেই নববর্ষ আসে। ভুল বললাম। বলা উচিত, আমরা নববর্ষ পালন করি। আর সেই পালন করার মুহূর্তে একবার হলেও আমরা কেউ কেউ ফিরে তাকাই নিজের জীবনের দিকে। বা বলা ভালো, নিজের জৈবনিক পরিবর্তনের দিকে। কী ছিলাম, কী হয়েছি, এরপর কী হতে পারি। কী ভেবেছি, কী ভাবছি, এরপর কী ভাবব। আমি আমার চিন্তার বিবর্তনের ইতিহাস জানি। হ্যারিকেন-জ্বলা সন্ধ্যায় বই-খাতা নিয়ে বসা থেকে আজকের ল্যাপটপ খুলে এই লেখাটা লিখতে বসা—জীবনের দুই প্রান্তসীমায় বসে থাকা একটি গ্রাম্য বালক আর একটি প্রৌঢ় নাগরিক মানুষ—এদুয়ের মধ্যে শারীরিক পরিবর্তনটা প্রায় সর্বজনীন, কিন্তু চিন্তার পরিবর্তন এতখানি সর্বজনীন নয়, তার বেশিরভাগটাই ব্যক্তিসাপেক্ষ বা মন্ময়। সেটুকুই আমার নিজস্বতা, অন্যের সঙ্গে সেখানেই আমার পার্থক্য।
চিন্তাস্রোতের এই অবিরাম প্রবাহপথে গতিদায়ী শক্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে যেমন জীবনের অভিজ্ঞতাপুঞ্জ, আশ্চর্য সব মানুষ তেমনই আশ্চর্য কতগুলো বই। হ্যাঁ, বই। কতগুলো তথ্য আহরণ করার জন্য নয়, চিন্তাকে নতুন গতি দান করবার জন্য। এই মনোনদীর স্রোতোপথে আছে তীক্ষ্ণ সব বাঁক, তীব্র সব মোড়, যাকে সম্ভাবিত করে তুলেছিল সেই সব ঘনীভূত ভাবনাকোষ। তেমনই একটি বইয়ের কথা আজ সন্ধ্যায় মনে পড়ছে খুব।
ক্ষুদ্রাকার এই পুস্তিকাটি ফরাসি ভাষায় লেখা। যদিও আমি ও অন্য অনেকেই পড়েছেন তা ইংরেজি অনুবাদে। বিশ্বজোড়া তার খ্যাতি। আলোচিত হয়েছে পৃথিবীর নানা ভাষায়। বইটির লেখক প্যারিসের কারমেলাইট মনাস্ট্রির একজন লে ব্রাদার। সপ্তদশ শতকে তাঁর জন্ম। পিতৃদত্ত নাম নিকোলাস হারমান। সন্ত-নাম ব্রাদার লরেন্স অফ দ্য রেজারেকশান। আর তাঁর লেখা পুস্তিকাটির নাম—‘দ্য প্র্যাকটিস অফ দ্য প্রেজেন্স অফ গড’।
আপনি কী হিসেবে একটি বই পড়বেন, সেটা সম্পূর্ণ আপনার নিজের ব্যাপার। আপনি কোনো একটি বইকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পড়তে পারেন। আবার চাইলে সেই বইকেই আপনি আর্থসামাজিক অবস্থার দলিল হিসেবেও পড়তে পারেন। ব্রাদার লরেন্সের আলোচ্যমান বইটিকে আমি ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পড়িনি। পড়েছি এক অনতিক্রম্য উচ্চতার কাব্যগ্রন্থ হিসেবেই।
বইয়ের কথা আর এই বইয়ের লেখকের কথা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বইটিতে আছে ষোলোটি চিঠি, চারটি আলাপচারিতা, লেখকের জীবনদর্শন-সংক্রান্ত কিছু উক্তিসঞ্চয়ন আর অতি ক্ষুদ্র একটি জীবনী। জীবনীটি কার লেখা জানা যায় না। ব্রাদার লরেন্সের নিজের লেখা নয়, যেকোনো পাঠক তা পড়লেই ষোলো আনা নিশ্চিত হয়ে যাবেন।
নিষ্পত্র একটা গাছ। সাদা বরফ ভেদ করে সেই গাছের কালো কঠিন নিষ্পত্র শাখা আকাশের নিঃসীম নীলের ভিতর একাকী জেগে আছে। গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে আঠারো বছরের একটি ছেলে। একটা পা খোঁড়া। সুইডেনের সৈন্যরা র্যামবারভিলারস শহরে ঢুকে শহর তছনছ করেছিল, হত্যা করেছিল অনেককেই। একটা পা চিরতরে হারিয়েছে ছেলেটি সেই বিপর্যয়ে।
তিরিশ বছর যুদ্ধ চলছে। তিরিশ বছর যুদ্ধ চলা কেমন, আমরা ভারতীয়রা তা জানি না। দেশে ভয়াবহ দারিদ্র্য। মধ্য ইউরোপ চুরমার হয়ে যাচ্ছে। পূর্ব ফ্রান্সের গরীব চাষীর ঘরে জন্ম ছেলেটির। লেখাপড়া বিশেষ কিছুই করতে পারেনি। খেতেই পায় না, তায় লেখাপড়া! রুটি-কাপড়ের জন্য যোগ দিয়েছে সেনাবাহিনীতে। জার্মানদের হাতে ধরা পড়ে গুপ্তচর সন্দেহে অকথ্য অত্যাচার। তারপর গেল পা চিরতরে। বাতিল হয়ে গেছে সে সৈন্যবাহিনী থেকে।
এরই মধ্যে কোনো একদিন ওই নিষ্পত্র গাছটিকে দেখছিল ছেলেটি। অশক্ত শরীর; যে-বয়সে শক্তি ও যৌবনের লাবণ্য প্রকাশিত হয়, সেই বয়সেই তার শরীর ফুরিয়ে এসেছে, উৎসাহ চলে গেছে, আশা নেই, স্বপ্নও নেই কোনো।
খোঁড়া ছেলেটি গাছটাকে দেখছে। তারই মতন মৃতপ্রায়, রুক্ষ, শ্যামলতাহীন। দেখতে দেখতে কী যে হল তার, মনে হল ওই গাছটাই সে নিজে, জীবনের হাতে পরাজিত, অবসিত, অবসন্ন।
এমনই একটা মুহূর্তে অন্য একপ্রকার চিন্তা জেগে উঠল মনে। তার মনে হল, আচ্ছা! গাছটা এখানেই তো শেষ নয়। এরও পর বাতাসের উষ্ণতা বাড়বে, বসন্ত আসবে, বরফ গলে যাবে, নতুন পাতারা চিড়বিড় চিড়বিড় করে জেগে উঠবে গাছটার শরীরে, দেখা দেবে মঞ্জরী, মৌমাছি আর পাখিরা আসবে তার সঙ্গে খেলা করতে। ফুল হবে, ফল হবে। ফুল হবে? ফল হবে? অবিশ্বাস্য যে ব্যাপারটা!
এমন অমিত সম্ভাবনা এইসব শুকনো ডালের ভিতর লুকিয়ে আছে তবে? নিকোলাস ভাবে আর ভাবে। ভাবতে ভাবতে মনে হয়, এই কীটদষ্ট অপক্ষয়িত সৃষ্টির ভিতর কে যেন জেগে আছেন তাঁর লুকোনো ভালোবাসা নিয়ে, যাবতীয় নিরাময় নিয়ে। এমন চিন্ময় কার সৃজন? কে তিনি?
ছাঁটাই হয়ে যাওয়া সৈনিক নিকোলাস একে ওকে ধরে অনেক কষ্টে ফ্রান্সের রাজার কোষাধ্যক্ষ উইলিয়াম দ্য ফুইবার্টের কাছ থেকে একটা অল্প মাইনের চাকরি জোটাতে পারে কোনোমতে। কিন্তু বোকাসোকা, মুখচোরা মানুষ কোনোদিন পৃথিবীর কর্মশালায় চাকরি টেকাতে পারে? আমাদের কবি বলেছেন, ‘পৃথিবীতে নাই কোনো বিশুদ্ধ চাকুরী।’ চাকরি চলে যায় কিছুদিন পরেই।
তারপর কী যেন হয় তার। যুদ্ধের বীভৎসতা সে দেখেছে, দেখেছে কত অর্থহীন এই জীবন। নীরক্ত, পাণ্ডুর মানুষের এই অস্তিত্ব। তবু রাতের পর রাত বীতনিদ্র থেকে তাকে মুখোমুখি হতে হয় সেই প্রশ্নটির। আমার নিজের বলতে কেউ নেই? একান্তই আমার? যে আমার সব চিন্তার সাক্ষী, আমার সব দুঃখের সহমর্মী, আমার সমস্ত ভালোবাসার একমাত্র আধার? আমাকে যে আমার থেকে বেশি করে চেনে?
কেউ নেই?
নেই কেউ?
বোবা রাত্রি উত্তর দেয় না।
খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে ছাব্বিশ বছর বয়সে নিকোলাস এসে পৌঁছান প্যারিসের কারমেলাইট সঙ্ঘে। লেখাপড়া নেই, লাজুক। মুখচোরা, তদুপরি প্রতিবন্ধী। বড়ো বড়ো সাধুদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে হাজার বার কথাই আটকে যায় তাঁর। নাহ্, নিয়মিত সন্ন্যাসী হওয়াও তাঁর হল না।
কী করবেন, ফিরেই যাবেন, ভাবছেন। কে যেন বলল, মনাস্ট্রির রান্নাঘরে রাঁধুনির কাজ ফাঁকা আছে। তাই সই। সৌভাগ্যক্রমে ওই কাজটা পেয়ে গেলেন নিকোলাস।
হাড়ভাঙা খাটুনি সমস্ত দিন। রান্না করা, বাসন মাজা, খাবার পরিবেশন করা… পরিশ্রম, পরিশ্রম আর ক্লান্তি।
তারপর একদিন উনুনে খাবার গরম করতে করতে নিকোলাস শুনতে পেলেন, তাঁর মনের ভেতর কারা দুজন যেন কথা বলছে।
‘প্রিয়, আমার সঙ্গে তো কেউ এখানে কথা বলে না। বলবেই বা কেন? মুখ্যু মানুষ, কিছুই জানি না। কেউ আমাকে কোনোদিন ভালোবাসেনি। তুমি ভালোবাসলে কেন এমন করে?’
—ভালোবাসার কি কোনো কেন কীভাবে হয়, নিকোলাস? তুমি ‘কিছু না’। হয়তো সেজন্যেই আমি তোমাকে ভালোবাসি। ‘কিছু না’ হওয়া সব থেকে কঠিন যে! অথবা তুমি ‘তুমি’ বলেই ভালোবাসি। কেন তা জানি না।
—তবে কি ঈশ্বরেরও আছে অজ্ঞতা? নাকি বোকা নিকোলাসের প্রভুও বোকা? না, না, রাগ কোরো না, প্রিয়তম। কী বলতে কী বলে ফেলি, আমি তো একটা হদ্দ মুখ্যু লোক! আচ্ছা, বেশ, বলো তুমি আমাকে, আমি কেমনভাবে পালটে গেলে তুমি খুশি হও?
—পালটে যাবে? সর্বনাশ! একদম পালটিও না নিকোলাস। তোমাকে একবিন্দুও পালটে দিতে চাই না আমি। তুমি আমাতে পূর্ণ হয়ে আছ। না, না! আমিই তোমাতে পূর্ণ হয়ে আছি।
সব কাজের মধ্যে সর্বক্ষণ নিকোলাস শুনতে পান এই দুজনের বার্তালাপ। আনন্দে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে তাঁর ক্ষয়াটে মুখশ্রী। খঞ্জ মানুষের ভ্রষ্ট অবয়বের ভিতর হতে ফুটে উঠতে থাকে আত্মবিশ্বাস ও শরণাগতির আশ্চর্য আলোক।
বয়স হয়েছে। অসুস্থ তিনি। সঙ্ঘে তাঁকে ডাকা হয় ব্রাদার লরেন্স অফ রেজারেকশন নামে। আশ্চর্য পবিত্র জীবন তাঁর। দুয়েকজন অনুরাগী আসেন তাঁর কাছে। আপাতরুক্ষ চেহারার মানুষটি অপরিশীলিত ভাষায় কথা বলেন। সেসব কথা প্রেমের, মুগ্ধতার, বৈরাগ্যের কথা।
একদিন মৃত্যু এসে তাঁকে নিয়ে যায়। হয়তো সে মৃত্যু নয়, হয়তো সে সেই প্রেমিক, যাঁর সঙ্গে নিকোলাস সারা জীবন কথা বলে এসেছেন। তাঁর ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে পাওয়া যায় কিছু চিঠির খসড়া। ওই চিঠিগুলো, আরও কিছু কথোপকথন আর কিছু উক্তির সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর এক অনুরাগী ছোট্টো একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। দ্য প্র্যাকটিস অফ দ্য প্রেজেন্স অফ গড—ঈশ্বরসান্নিধ্যের সাধনা।
ছোটো ছোটো বাক্য। বড়ো সরল, যেন মাটির কোনো প্রদীপের আলোয় লিখিত। সেই আলোর ইশারার মতই অনুপ্রেরণার অনুভা ছড়িয়ে আছে সেসব কথায়। এক গরীব সাধুর দুটো কথা। কবিতা মাখানো। সেই লাজুক নিকোলাসের সঙ্গে তাঁর অদৃশ্য বন্ধুর কথাযাপন। পৃথিবীর সব শ্রেণির ভাবুকদের মনে উজ্জ্বল নীলমণি হয়ে ওঠে সেই বই অচিরেই।
আমি এমন অনেক কবিতা পড়েছি, যা বেশিরভাগ মানুষ বিবিধ কারণে পড়েননি। কিংবা পড়লেও সেগুলোকে তাঁরা কবিতা হিসেবে পড়েননি। তাঁরা পড়েছেন মুখ্যত সমাজ-স্বীকৃত কবিদের কবিতানামীয় মূল্যবান রচনা। কিন্তু সেসব কবিতাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে কবিতার অনেক টিলাপাহাড়নদী, কবিতার অনেক অপাররৌদ্রশিশির আছে। ব্রাদার লরেন্সের প্র্যাকটিস অফ দ্য প্রেজেন্স অফ গড এমনই পারাপারহীন রোদ ও শিশিরের কবিতা।



লেখাটি প’ড়ে বিশেষ উপকৃত হলাম। প্রচ্ছদটি দেখে মনে হচ্ছে, হয়তো এটি নতুন কোনও অনুবাদ।
অনেক ধন্যবাদ ও নমস্কার নেবেন। ইংরেজি অনুবাদটি নতুন নয়। বইটির অবয়ব শুধু নতুন।
নিকোলাস হারমানের কবিতার মধ্যে হারতে হারতেও প্রবলভাবে জিতে যাওয়া একজন মানুষকে প্রত্যক্ষ করলাম।
আর এই অনুবাদে যিনি আমাদের দেখালেন তাঁর দেখার অন্তর্দৃষ্টিকে অনুভব করলাম।
ধন্যবাদ। প্রীতি-মুগ্ধতা।
আহা!এমন নিভৃতালাপেই কত জীবন কেটে যায়!মুখ ফুটে বলা আর হয়ে ওঠে না!একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হোলো। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই।
আসাধারন লাগলো এই পাঠ প্রতিক্রিয়া । ভাবছি এ ভাবেও প্রতিক্রিয়া শুরু করা যায় ! ঋদ্ধ হলাম।
কাকতালীয় ভাবে ঠিক এই সময়ে পড়ছি নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা। সব বুঝতে পারছি এ কথা বললে খুব ভুল বলা হবে। তবে নতুন ভাবনায় মন আচ্ছাদিত হয়েছে। এটা বুঝতে পারছি। বইটি কভিড সময়ে ডাকে সংগ্রহ করেছি বিদেশে বসে। মুদ্রিত বিদেশী মুল্যের দ্বিগুণেরও বেশী দিয়ে। প্রথমে সামান্য আক্ষেপ ছিল এ নিয়ে। পড়তে পড়তে সে আক্ষেপ দূর হয়ে যাচ্ছে ।