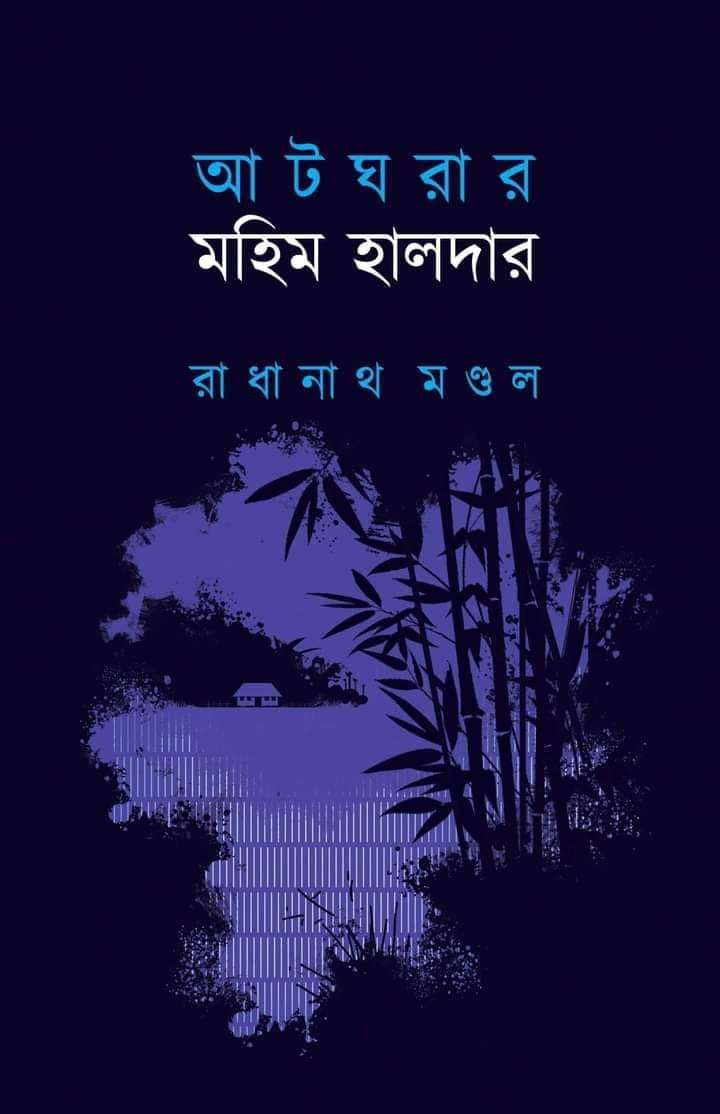
রাধানাথ মণ্ডলের গল্প : মার্জিনে আঁকা আমাদের আপন দেশ
সরোজ দরবার
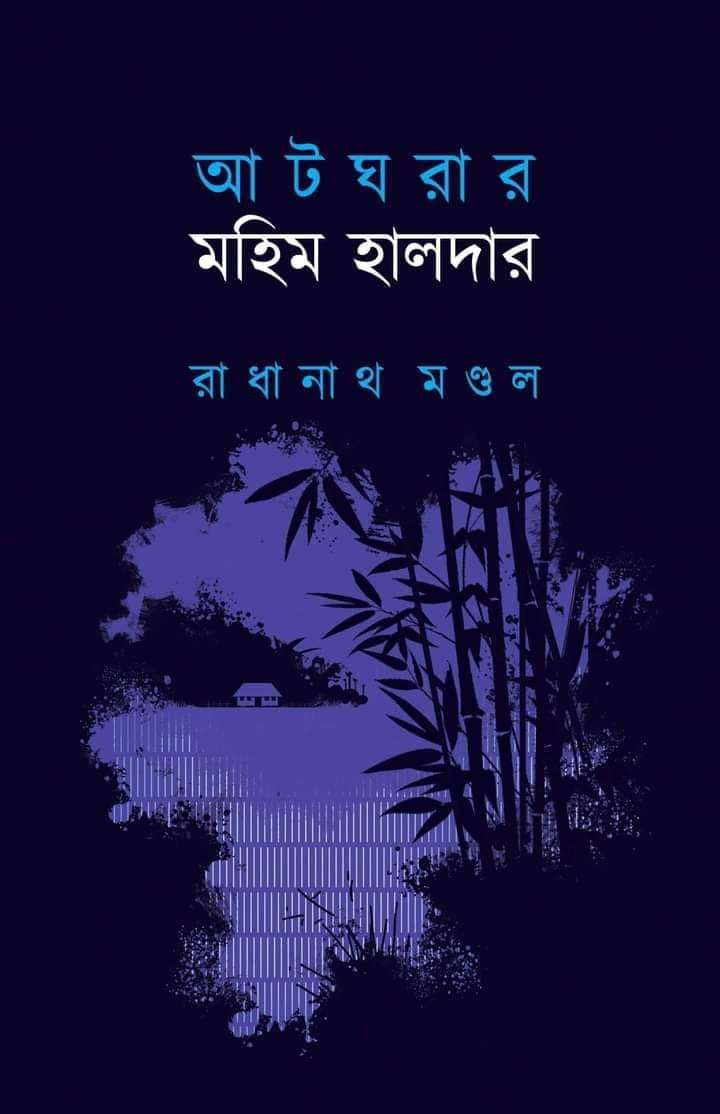
রাধানাথ মণ্ডলের গল্প আমি আগে পড়িনি। আমার মতো হয়তো আরও অনেকেই। কেন পড়া সম্ভব হয়নি, তার নানাবিধ কারণ থাকতে পারে; কিন্তু ঘটনা হল, এই না-পড়া বা দেরি করে পড়া আসলে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা থেকে বহুদিন দূরত্বে থাকা। এমন কিছু পাঠ-অভিজ্ঞতা এসে জমা হয়, যা জীবনকেই ঐশ্বর্য দান করে; বিস্মিত করে; ভাবনার মানচিত্র বদলে দেয়। যেমন, ‘পথের পাঁচালী’ কি ‘অক্ষয় মালবেরী’ পড়া; এই শতকের নতুন দশকে দাঁড়িয়ে রাধানাথ মণ্ডলকে পড়াও তেমনই এক বিস্ময়াবিষ্ট অভিজ্ঞতা। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক অমর মিত্র এক্ষেত্রে আমার এবং আমার মতো অনেকের কাছেই ভগীরথ হয়ে থাকলেন। রাধানাথবাবুর গল্পের এই জাহ্নবীধারা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ ও কৃতিত্ব তাঁরই। আমরা হাতে পেলাম ‘আটঘরার মহিম হালদার’।
মহিম হালদার ছা-পোষা কৃষক পরিবারের ছেলে। গাঁ-ঘরে তার বেড়ে-ওঠা থেকে বিবাহ হয়ে জীবিকা-র সন্ধানে কলকাতায় আসা, জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরনো, যেমন সকলকেই পেরোতে হয়, এভাবেই যেন চলমান চিত্রমালার মতো গল্প থেকে গল্পে মহিম হালদারকে আমরা ক্রমে ক্রমে চিনি। চিনতে থাকি। তাকে ভালোবেসে ফেলি একসময়। তার সহমর্মী হই। একসময় আমরাও মহিম হালদারের সঙ্গে নতুন একখানা গল্পে পথ হাঁটতে থাকি। অর্থাৎ, মহিম হালদার নামে একজন মানুষকে আমরা আবিষ্কার করি এবং তাকে আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর অন্তর্ভুক্ত করে ফেলি। এবার যদি প্রশ্ন করি যে, শুধু এই একজন মহিম হালদারের গল্প বলেই কি রাধানাথ আমাদের এমন আবিষ্ট করে রাখলেন? অবধারিত উত্তর আসবে, মহিমের এইসব গল্পের ভিতরে গল্প আর কোথায় তেমন! বস্তুত, রাধানাথ তো সেই ঘরানার লেখক যিনি গল্পকে একেবারে লুকিয়ে ফেলতে পারেন। গোটা একটা গল্পে তিনি যা যা বলতে চান, আসলে তা তা বলেনই না প্রায়। আর, যা যা বলেন তা অনুষঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাঠকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে গিয়ে পাঠকের মনে নতুন একটা করে গল্পের জন্ম দেয়। সে গল্প একা মহিমের নয়। যিনি পড়ছেন তাঁরও। অর্থাৎ, শুধু মহিমের গল্প এখানে বাজিমাত করে না। এই সব গল্পের ভিতর রাধানাথের গল্প-ও আছে। অবশ্যই আমি লেখক রাধানাথের ব্যক্তি আমির কথা বলছি না। যেভাবে জীবনানন্দ তাঁর কবিতার ‘আমি’ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নেন, সেভাবেই এখানে লেখক রাধানাথকে আমরা স্বতন্ত্র করছি। রাধানাথের গল্প বলতে আমরা বুঝতে চাইছি, রাধানাথের গল্পরচনার এই কল্পটিকে। তা মহিমকে আশ্রয় করেই দানা বেঁধেছে বটে, তবে তা শুধু মহিমের গল্প নয়। রাধানাথের নিজস্ব কিছু লুকোনো তাস থেকে যায় মহিমের এইসব গল্পের ভিতর। বাংলার ইতিহাস আর বাঙালির ইতিহাস প্রায় কাছাকাছি হয়েও যেমন এক নয়, তেমনই মহিমের গল্প আর রাধানাথের গল্প প্রায় একই লিখিত অক্ষর অবলম্বন করে অস্তিত্বশীল হয়ে থাকলেও, একেবারে এক নয়।
কেন এক নয় বলছি? যদি মহিমকে আমরা ব্যক্তি হিসেবে ধরি, তাহলে আমাদের ভাবনা এই পথে চলে যে, এ কি সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তির ধারণা, যা শিল্পবিপ্লবের ফলে জন্ম নেওয়া জাতিরাষ্ট্রের হাত ধরে এল? যার গুণকীর্তন করার জন্য কত না শিল্পকর্মের অবতারণা? সন্দেহ নেই, গল্পগুলিতে আপাতভাবে মহিম-ই সেই ব্যক্তি। সেই-ই গল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বা তার উপর ভর করেই গল্প এগোচ্ছে। অর্থাৎ, নায়ক চরিত্র বা প্রোটাগনিস্ট যদি কাউকে বলতে হয় তবে সে মহিম-ই।
ঠিক এই বিন্দু থেকেই শুরু হয় রাধানাথের গল্প বা তার লুকনো তাসের চাল। যা আমাদের ক্রমাগত জানাতে থাকে, মহিম তো বিভামণ্ডিত একজন প্রোটাগনিস্ট নন, যেভাবে আমরা একজন প্রোটাগনিস্টকে দেখতে অভ্যস্ত। তাহলে? আসলে রাধানাথ চাইছেন অভ্যাসের বদল। রাধানাথ কোনও একজন ব্যক্তির গল্প তো বলছেন না। আবার বলছেন একজন ব্যক্তিরই গল্প, বা বলা যায়, যা যা বলছেন তা একজন ব্যক্তিকে অবলম্বন করেই। এই দ্বিমাত্রিকতায় টেনে এনে রাধানাথ তাঁর পাঠকের কাছে দাবি করছেন অভিনিবেশ। প্রয়োজনীয় হচ্ছে পুনঃপাঠ। এখন, যে কোনও গল্পকারের ক্ষেত্রেই যে এই কৌশল সমভাবে প্রযোজ্য, এমন কথা তো বলাই যায়। একটি চরিত্রের আধারেই তো গল্পকার তার নিজের গল্পটি বলবেন, নিজের সময়ের আখ্যানটিকে বিস্তৃত করবেন; ব্যঞ্জনা জাগিয়ে তুলবেন। তা ঠিক-ই। এখানে মজা হল, রাধানাথ সেখানে একটি চরিত্রকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেন সে প্রোটাগনিস্ট এমনভাবেই তাকে সামনে এনেছেন, এমনকি গল্পগ্রন্থের নাম থেকেও যে আভাস মেলে তা আমাদের পাঠের উপরও একধরনের প্রভাব ফ্যালে। কিন্তু একটি কি দুটি গল্প করে শেষ করেই পাঠক এখানে রাধানাথের পরিকল্পনা অনুধাবন করতে পারেন। বুঝতে পারেন, ব্যক্তিপ্রতিষ্ঠার ছলেই ব্যক্তিকে নস্যাৎ করছেন রাধানাথ, যেন মানচিত্র আঁকার নাম করেই মুছে দিচ্ছেন সবরকমের সীমানা। এইখানে তিনি স্বতন্ত্র হয়ে যান এবং গোটা বইটিকে একটি আলাদা প্রকল্প হিসেবে উপস্থাপিত করেন আমাদের সামনে। এবং, তাই ভীষণ জরুরি হয়ে ওঠে পুনঃপাঠ।
পুনঃপাঠের দরুনই আমরা মহিমকে নতুন করে চিনব। বুঝব, সে এখানে কী বা কে। এবং, এই অনুধাবনে পৌঁছতে আমরা শরণ নেব দেবেশ রায়ের। দেবেশবাবু তাঁর ‘লুপ্ত দেশ, হারানো গল্প’ প্রবন্ধে যখন আমাদের ‘সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ’ আখ্যানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, বা এইরকম আখ্যান চিনতে শেখাচ্ছেন, তখন জানাচ্ছেন, এই ঘরানার কথাকার, যাঁরা সাম্রাজ্যের ভিতর বসেই নিজের স্বদেশকে আবিষ্কার করছেন আর শোনাচ্ছেন সেইসব গোপন গল্প, যার মালিক সাম্রাজ্য কোনোদিন ছিল না, হতেও পারবে না, সেই সকল গল্পকাররা প্রোটাগনিস্ট-অ্যান্টাগোনিস্টের চলতি সমীকরণকে মান্য করছেন না বা করতে পারেন না কারণ, ‘উপনিবেশের প্রজা প্রোটাগনিস্ট হয় না। অথচ তার একটি গল্প আছে। সে-গল্পটি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে উলটোদিকে মাটি খুঁড়ে কোথাও লুকোতে চাইছে’। প্রোটাগনিস্টের বিপ্রতীপ অবস্থানে দাঁড়িয়ে তাঁদের গল্পের এই চরিত্ররা তাই হয়ে উঠছে অপ্রটাগনিস্ট। আমাদের মহিম হালদার-ও তা-ই। সে তো মহামহিম কেউ নয়। যাকে আমরা বলি অকীর্তীত জনসাধারণ, সে তারই একজন। সেই যে ছোটোবেলায় সে একটা গ্লোব কিনতে চাইত, কিন্তু কিছুতেই পেত না। তারপর যেদিন সেটি পেল, সেদিন সে দেখল ও জানল এই সত্যি যে,-
এরপর নিজেদের গাড়ির কাছে ফিরে আসবে মহিম। একসময় গাড়ি ছেড়ে দেবে। আর গোরুর গাড়ির ছইয়ের নিচে আলো-আঁধারের মধ্যে প্রাণপণে গ্লোবটা ঘোরাতে থাকবে সে। দেখবে এখানে তার গ্রাম, বলরামপুর হাইস্কুল, তিন ক্রোশ দীর্ঘ মাঠ, কোনোটাই নেই।
তবু মহিমকে সেখানেই ফিরে যেতে হবে।
এই তো তার সেই জনঅরণ্যে মিলিয়ে যাওয়া অস্তিত্ব। তার গল্পেরাও পলকা। তত্ত্বের ছোঁয়া লাগলে ভেঙে পড়বে যেন; যেন প্রায় লুকোতে চাওয়া কিছু। তা সত্ত্বেও তারও যে কিছু গল্প আছে, এটাই সত্যি। এবং, সেটাই এই বিরাট জনসাধারণের জোরের জায়গা। তাদেরও কিছু গল্প আছে। জীবন আছে। সেইসব গল্পেরা লুকিয়ে লুকিয়ে হলেও বেঁচে থাকে। তাদের মৃত্যু হয় না। এই গল্পগুলো আর মহিমের নয় শুধু, এগুলোই রাধানাথের গল্প।
অপ্রোটাগনিস্টের এই গল্পে তবু বিশেষভাবে খেয়াল করার মতো দেবেশবাবুর বলা ‘উপনিবেশ’ শব্দটা। তিনি এই প্রসঙ্গে উদাহরণ দিয়েছিলেন প্রেমচন্দ ও বিভূতিভূষণের। আমরা রাধানাথের গল্পে যখন সেই একই মাটি খুঁজে পাচ্ছি, তখন অবশ্য আক্ষরিক অর্থে উপনিবেশের কাল নয়। মহিম হালদারের এই সব গল্পেরা গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। অর্থাৎ, লিখিত হয়েছিল, ধরে নিচ্ছি, তারও কিছুটা আগে। এবং গল্পের সময়কাল তো আরও খানিকটা আগেরই, বিশেষত মহিমের শৈশব যে সময় অতিবাহিত হয়েছে, সেই সময়টাকে যদি মাথায় রাখি। অতএব, আমরা বুঝতে পারছি, ঔপনিবেশিক ধারণাটিও এখানে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে, যেমন তা সচরাচর হয়ে থাকে। ভূখণ্ড পেরিয়ে তা যেভাবে সাংস্কৃতিক সীমানায় আধিপত্য বিস্তার করে এবং সেইহেতু শিল্প-সাহিত্যের প্রসব হতে থাকা, প্রাতিষ্ঠানিকতার সেইসব ছল ও চাতুরী নিশ্চিতই রাধানাথের চোখ এড়ায়নি। এই হয়ে-ওঠা সময়কালটা যদি মোটা দাগে দেখা যায় তো দেখব, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এই বাংলায় বিপ্লব ও সেইহেতু সমাজবদলের স্বপ্ন গতপ্রায়। দেশ তো ইতোমধ্যেই দেখে ফেলেছে জরুরি অবস্থা। নীতি আর রাজনীতি কোন পথে চলেছে একটি কিশোর রাষ্ট্র তা বেশ ভালোই বুঝতে পারছে। ঔপনিবেশিকতার নয়া ছদ্মবেশ হয়ে যে গোলোকায়ন আসছে, তার চিহ্নরা ক্রমে ফুটে উঠছে রাষ্ট্রের শরীরে। অর্থাৎ, উপনিবেশ-উত্তর যে ঔপনিবেশিকতা আধিপত্যবাদী বর্গের সূত্র ধরে এই সমাজের শিরদাঁড়ায় বসেই আছে, তা যে ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল শুধু নন, তিনি আসলে সেই কেন্দ্র থেকে সরে যাবার গল্পই লিখছেন আপ্রাণ। অথবা চাইছেন, ব্যক্তির আদলেই ব্যক্তির কেন্দ্র ভেঙে যাক। কেন্দ্র বলে আলাদা করে কিছু যেন না থাকে, বা পরিধিই যেন কেন্দ্র হয়ে ওঠে। যেমনটা আমরা জীবনানন্দের গল্পের ক্ষেত্রে অনুভব করি। বা বিভূতিভূষণের গল্পে। এই মহিম কি অনায়াসে বিভূতিভূষণের কোনও গল্পের চরিত্র হয়ে উঠতে পারত না? আমার ধারণা, পারত। ‘পুইমাঁচা’-কে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে চিহ্নিত করে দেবেশবাবু আমাদের ধরিয়ে দেন সেই জায়গাটা, যেখানে একজন বাবা তার মেয়ের মৃত্যুসংবাদটিও ঠিক করে দিতে পারছেন না। তড়িঘড়ি চলে যাচ্ছেন অন্য প্রসঙ্গে। কী করেই বা দেবেন! কীভাবেই বা বলবেন যে, এক বর্ষা পুঁই বাঁচলেও মেয়ে বাঁচে না। এই বিপর্যয় ব্যক্ত করার মতো তাই ভাষা নেই। ভাষা হয় না।
যেমন সেই দূরত্বকে আমরা আবিষ্কার করি বিভূতিভূষণে, যে দূরত্ব অনতিক্রম্য হয়ে একজন পিতার কাছে তার কন্যার মৃতুসংবাদ অবধি পৌঁছতে দেয় না। হরিহর দেখতে পায় না দুর্গাকে, এমনকি তার চলে যাওয়ার খবরটুকুও জানে না। অথচ গোটা দেশ তখন সংযোগের নতুন দিশা দেখছে। ভিন দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এসে দেশের অলিন্দে পৌঁছতে পারছে, অথচ দেশের লোকের কাছেই দেশ যেন অগম্য হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের দূরত্ব আর মার্কেজের নিঃসঙ্গতা আদপে সমার্থক হয়ে ওঠে এখানে, এই প্রেক্ষিতেই। সেই দূরত্বের ছবিই আমরা আবারও দেখলাম এই করোনা কালে, যদিও তা আলাদা প্রসঙ্গ। আবার নবারুণ ভট্টাচার্য, বিভূতিভূষণের আখ্যানে আমাদের ধরিয়ে দেন, এক ক্রমাগত চলতে থাকা দুর্ভিক্ষের কথা। সে-ও অতি সামান্য সূত্রে যে, মিষ্টান্নের স্বাদ অপু-দুর্গা তো জানেই না। ছোট্ট কথা। কিন্তু কী গভীর বিপর্যয় এর ভিতর লুকিয়ে। মা-বাবার কাছে তা কতবড়ো শাস্তি ও যন্ত্রণার। কিন্তু এই-ই তো দরিদ্র গ্রাম বাংলার চিত্র। এই নিয়েই সে বেঁচে আছে, হয়তো খুশিমনেই বেঁচে আছে। আমরা যদি মহিমের কাছে যাই, দেখব তারও চালে কাক গলছে। দারিদ্রের সমার্থক হয়ে ওঠা গাঁ-গঞ্জের এই কথা। সেখানে যুবক মহিমের বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে। শুধু পুরুষ বলেই সে বাড়তি এই সুবিধাটুকু পাচ্ছে, নইলে তাদের অবস্থা তো এরকম –
চার বস্তা নিয়ে গেলে খোরাকিতে টান পড়বে। আমরা কেউই মায়ের কথা শুনিনি। কারণ, ইউরিয়া কিনতে হবে, দোকানের জিনিস চাই, অনেক টাকার দরকার। ধান বিক্রি হল। কিন্তু মায়ের কথা ফলে গেল কদিন আগে। ধান সিদ্ধ করতে গিয়ে মা দেখল মাত্র দু-বড়ালি ধান পড়ে। এতে বড়োজোর শ্রাবণ মাসের আধাআধি পর্যন্ত যেতে পারে, তারপর ভাদ্র মাস পর্যন্ত কেনা ধানের গোনা ভাত।

অথচ এরকমটা হওয়ার কথা নয়। খোরাকিতে টান লাগার জন্য তো আর উন্নত সার আনেনি বিজ্ঞান। অথচ সেই সার কেনা আর আনুষাঙ্গিক কাজ করতে গিয়েই টান সত্যিই লেগেছে। এই যে কৃষির বদলে যাওয়ার ছবি, কত সন্তর্পণে প্রায় না-বলার মতো করেই তা বলে দেন রাধানাথ। কৃষিব্যবস্থার ভাঙনের সূত্রটি চাইলে আমরা এখান থেকে তুলে নিয়ে খতিয়ে দেখতে পারি। রাধানাথ তার আভাসটুকু দিয়ে রাখেন। তাহলে কৃষক পরিবারের যুবক বেকার সন্তানের স্বপ্ন কোনদিকে বাঁক নেবে, না-
মাঝে মাঝে আমি নানারকম কল্পনা করি। ভাবি বালিশের তলায় চার-পাঁচখানা একশো টাকার নোট রেখে ঘুমোচ্ছি। কিংবা রেডিয়ো খুললেই ভেসে আসছে আমার নিজের গলা— আকাশবাণী কলকাতা, এখন আধুনিক গান শুনবেন গ্রামোফোন রেকর্ডে, শিল্পী শ্রীমতী— মনে হয় আমি এখন কলকাতায় থাকি, চাকরি করি অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে।
এসে পড়ল সেই গ্রাম ছাড়ার গল্প। নতুন করে উচ্ছিন্ন হওয়ার গল্প। বারবার শিকড়ে ফিরতে চাইলেও যে আর কিছুতেই ফিরতে পারবে না, এবং, সেইহেতু এই সেই আর্তনাদ-
এই গ্রাম, এইসব গাছপালা, হাওয়া, মাটি যাদের আশ্রয় দেয় না, তাদের শহরে চলে যাওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে!
এই উচ্ছিন্ন মানুষের জীবন আগামীতে যে কী দুর্বিষহ হয়ে উঠবে বা উঠতে পারে তা তো আমরা আজ দেখছি। পাড়া ভেঙে যাওয়া, আত্মিকতা মুছে যাওয়া জীবনে বিচ্ছিন্নতা কী করে মানবতাকে কোণঠাসা করে দক্ষিণপন্থী আগ্রাসনের রাজপথ খুলে দিতে পারে, পক্ষান্তরে বৃহৎ ধনতন্ত্রকে অর্গলমুক্ত বাজার দিতে পারে, মানুষকে সংখ্যায় বা গুনতিতে কিংবা কাগজের টুকরোয় নামিয়ে আনতে পারে, তা আজ আমরা চাক্ষুষ করছি। আর সেই পুরো সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকল ওই প্রায় আলগোছে বলা এক-কি দু-লাইনে। চালের বাতায় গুঁজে রাখা জরুরি জিনিসের মতো গল্পের ভিতর এভাবেই রাধানাথ রেখে দেন অজস্র ইশারা। মানুষের এই পরিণতি-ই হয়তো ভবিতব্য। যা খণ্ডানো যায় না বা যাবে না। পূর্বনির্ধারণবাদের সপক্ষে যুক্তি খাড়া না করেও বলা যায়, মার্কস যে পৃথিবী বদলের দায় অনুভব করাতে চেয়েছিলেন, মানুষ বড়ো দ্রুততায় দায়মুক্ত হওয়ার তাগিদ অনুভব করেছে বলেই, এই ভবিষ্যৎ এড়ানো গেল না। ধনতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম হয়ে পড়লে, মানুষকে তার ফল ভোগ করতেই হয়। যেমন আমরা করছি। বা কোথাও বসে হয়তো মহিমও আজ করছে।
তবু এইসব মানুষের, এই মহিমেরও তো কিছু গল্প থাকে। তারও তাই শেষমেশ সম্বন্ধ এল। মহিমের বন্ধু গোপীনাথ সে সম্বন্ধ নিয়ে এসে মহিমকে কত করে বোঝাল। তাদের বংশগরিমা দিয়ে দারিদ্র্যকে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু মেয়ের বাবার সামনে তার বাবার যে গায়ে একটা গেঞ্জিও নেই, এই দৃশ্যে মহিমের রাগ হয়, অভিমান হয়। তবুও যে গল্পটা বেঁচে থাকল তা এটুকুই যে,
আমাদের তখন খুবই দুঃসময়। তবু বেশ কয়েকদিন আমাদের কাটল গোবিন্দপুর যাওয়া-আসায়। বাবা গেল দুবার, শঙ্করবাবু আবার একবার এলেন। দেওয়া-থোওয়া নিয়ে কথাবার্তা হল। আমাকে বারবার বলা হল মেয়ে দেখতে যেতে। কিন্তু আমি গেলাম না। আমি শুধু সারা বর্ষাকাল ভেবে ভেবে কাটালাম, আমাদের এই অভাবের সংসারে সেই দুধে-আলতা গায়ের রংকে কোথায় রাখব।
এই বর্ষাকালটার নাগাল পায় না সাম্রাজ্য। এটা মহিমের বা রাধানাথের গল্প যার-ই হোক না কেন, এটা আসলে সেই লুপ্ত দেশের গোপন গল্প। আমরা বলতেই পারি, এ হল সেই ভয়েস ফ্রম দ্য মার্জিন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের বলতে ইচ্ছে করে, এই মার্জিনটাই হল আমার দেশ। রাধানাথ মার্জিনেই আমাদের জন্য আমাদের আপন দেশটাকে এঁকে রেখে গিয়েছেন। প্রেমচন্দের গল্প নিয়ে বলতে গিয়েই দেবেশবাবু লিখছেন, ‘দুই পরিচ্ছেদের মাঝখানে প্রেমচন্দ উপনিবেশের এক মানুষের ভিতরের দেশ উদ্ঘাটিত করে দেন।’ রাধানাথের গল্পের অন্তর্বর্তীতেও আমরা এই দেশের উদঘাটনের সাক্ষী থাকি। তাই তা আমাদের আবিষ্ট করে, অনুসন্ধানী করে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে তা আমাদের শিকড়াভিমুখী করে।
এরপর যখন আমরা মহিমকে কলকাতায় দেখব, নাগরিকতার পরিচিত চোস্ত চক্রান্তের সঙ্গে তার মোলাকাত হবে, আমরা তখন মহিমের বন্ধু হয়েই সেই অনুভূতির অংশীদার হব। এইসব পর্বে এক গল্প শেষই হয় যেন আর-এক গল্পের শুরু হবে বলে। গল্পেরা তো থেমে থাকে না। কেন-না এই জনজীবন তো গতিরুদ্ধ হয় না। সেই প্রবহমনতার একটা নির্দিষ্ট ছন্দ থাকে। রাজনীতি বদলায়, ক্ষমতাসীনের হাত বদলায় কিন্তু সমাজবিন্যাসে প্রতিদিন খুব বেশি যে বদল তাতে আসে, তা নয়। অথবা বদল যা হয়, যতটুকু মিশ্রণ হয় তা-ও বহুবছর ধরে। ঠিক এই কারণেই মহিমের গল্প পড়তে পড়তে বিভূতিভূষণ বা জীবানন্দকে আমাদের খুব মনে পড়তে থাকে। দেবেশ রায় বলেন, ‘বিভূতিভুষণের গল্পে মানুষজন সব হারিয়ে যেতে থাকে, যে যেখানে পৌঁছতে বেরোয়, সে সেখানে পৌঁছয় না। সব গল্পই শেষ হয় আর-এক গল্পের চৌকাঠে।’ অবিকল এই আদলই তো আমরা আবিষ্কার করি মহিমের গল্প থেকে গল্পে পৌঁছনোর পরিকল্পনায়। যেন একই আখ্যান। অথচ এর ভিতরকার এমন অনেক অভিজ্ঞতা আছে যা আজ আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। সময়ের কারণেই মেলে না। গ্রাম সংগঠন, শহরের জনজীবন- দুয়েরই অনেক বদল হয়েছে। তবু মহিমের এই অভিজ্ঞতা বা মহিমের প্রতিনিধিত্বে বলে যাওয়া রাধানাথের এই অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে গুরুত্ববাহী হয়ে ওঠে। কেন-না এই অভিজ্ঞতাই আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে সেতু বেঁধে দেয়। পূর্বজ অভিজ্ঞতার সূত্রে আমাদের যাপনীয় জীবনের জায়মানতাকে নয়া দিশা দেয় বা নতুন অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা স্পষ্ট করে তোলে। বিনির্মাণ সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে বলেই তা পুনর্নির্মাণের পক্ষে সহায়ক হয়ে ওঠে।
অর্থাৎ, মহিমের গল্পে বা সেই গল্প বলতে গিয়ে তার ফাঁকফোকরে, এদিক ওদিক, কথাপ্রসঙ্গে রাধানাথ যে সব নিজস্ব গল্প লুকিয়ে রাখেন, নিজস্ব বয়ান রেখে যান তা আমাদের কাছে দুর্মূল্য হয়ে ওঠে। কেন-না আমরা জানি এই মহিম এক চিরকালের পুরুষ বা চিরকালের মানুষ। আবহমানের পথ ধরে যে হাঁটতে হাঁটছে। মহিম তো বলেই দেয়,আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল মহিম। গায়ের ভিজে পোশাক শুকিয়ে আসছে। একটা আঙুলে জামার কাদা নিয়ে নাকের কাছে তুলে ধরল সে। আঃ! যেদিন প্রথম প্রথম বৃষ্টিপাত হয়েছিল, সেদিন এমনই গন্ধ উঠেছিল মাটি থেকে। মহিম এলোমেলো পায়ে হাঁটতে থাকল! সে জানে না সে কে। সে কি তার বাবা? সে কি জগৎসিংহ? সে কি মহিম হালদার? নাকি সে পৃথিবীর সেই আদিম পুরুষ, যাকে প্রথম নারীটির আকর্ষণে অনন্তকাল ধরে হেঁটে যেতে হয়!
এই হাঁটা হাজার বছরের। এই হাঁটা দু-দণ্ডের অবসর প্রার্থনা করে। মধ্যের যাত্রাপথে ঘনিয়ে ওঠে অভিজ্ঞতা। যার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে মহিমের গল্প বা রাধানাথের গল্পেরা। এ-প্রান্তে থাকি আমরা। অভিজ্ঞতাই রচনা করে সেতু। আমাদের মনে পড়ে জীবনানন্দের কথা, ‘কেন লিখি’ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সেই যে তিনি বলছেন, ‘আজকের দুর্দিনে মানুষের নিঃসহয়তার রূপ কী রকম, কী করে তা কাটিয়ে উঠে জীবনের শুভ অর্থ বোধ করতে পারা যায়, এ-সব বিষয় নিয়ে যে-কোনো প্রবীণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও তার লিপিময় প্রকাশ মূল্যবান জিনিস।’ ব্যক্তির আদলেই ব্যক্তিকে ছাপিয়ে যাওয়ার এই যে অভিজ্ঞতা লিখে গিয়েছেন রাধানাথ মণ্ডল, তা আজ আমাদের কাছে অমনই মূল্যবান এক জিনিস। কেন-না সেইটেই একদিকে আমাদের দেশ, আমাদের স্মৃতি, দাঁড়াবার জায়গা। আমাদের শিকড় ও অভিজ্ঞান। যাকে ছাড়া আমাদের বর্তমান, আমাদের এই অস্তিত্বশীল হয়ে থাকা অর্থহীন এবং দুর্বিষহ। রাধানাথ মহিমকে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে সেই অসহ ভারবহন থেকে আমাদের মুক্তি দেন। আবার, এর ফলেই আমাদের মনন যে জাড্য লাভ করে, তা জীবনের শুভ অর্থের দিকে আমাদের ধাবমান করে। আমাদের অবস্থানকে পুনর্বিবেচনায় প্ররোচিত করে। এইটেই চিরকালের জীবন। আজকে যখন জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের ধারণা মুখ থুবড়ে পড়ছে, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার উত্তরোত্তর চাপে আমরা বিধ্বস্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের দোহাই দিয়ে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিচ্ছিন্নতাকামী চাতুরীতে আমরা যখন নিঃসঙ্গ এবং সর্বার্থেই একা- তখন এই মার্জিনে আঁকা দেশ সম্বল করেই তো আমরা বেঁচে থাকতে চাইছি। হয়তো ঘুরে দাঁড়াতেও চাইছি। এই তীব্র আগ্রাসনের ভিতর এইসব গল্পেরা হয়ে উঠছে আমাদের আয়ুধ।
রাধানাথ মণ্ডলের গল্পেরা তাই গল্প নয়, শেষ পর্যন্ত তা আমাদের অস্তিত্বেরই অংশ হয়ে ওঠে।
-০-

