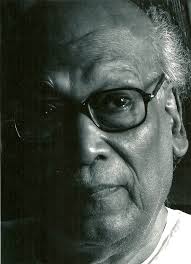
তোমরা কেউ জানোনি যে বহুদিন আগে তোমরা মৃত
যশোধরা রায়চৌধুরী
কবি শঙ্খ ঘোষের ৮৯ তম জন্মদিনে আবহমানের শ্রদ্ধার্ঘ্য
আজ তিনি ৯০-এ পা দিলেন। আমাদের বিবেক ও চেতনার একটি ফলা , ইস্পাতের ও শ্লেষের, ফলক, অচ্ছেদ্য পাথরের ও প্রজ্ঞার। এখনো সৃষ্টিশীল কলম, ক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক। এখনো আমাদের কশাঘাত করতে সক্ষম তাঁর অক্ষরেরা। এই না হলে কি শঙ্খ ঘোষ ?
শিখর থেকে একে একে খসে পড়েছে তারা ।
গহ্বরের দিকে গড়িয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করছে, ‘বলো, কেন
কেন অসময়ে আমাদের এই বিনাশ ?’
জানতে চাইছে শিলায় শিলায় ঝলসে-ওঠা স্বর :
‘আমরা কি তবে সত্য ছিলাম না আমাদের শব্দে ?
আমরা কি স্থির ছিলাম না আমাদের স্পন্দে ?
আমরা কি অনুগত ছিলাম না আমাদের স্বপ্নে ?
তবে কেন, কেন আমাদের এই— ’
পায়ে পায়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন পাহাড়ের কিনারে । বললেন, ‘শোনো
ছোট ছোট সফলতায় অন্ধ
তোমরা সকলেই ছিলে নিজের ভিতরে রুদ্ধ । ’
সকলের দিকে একে একে আঙুল তুলে তিনি বললেন, ‘তুমি ভেবেছিলে
তুমি যতটুকু জানো তার চেয়ে বেশি কোনও জ্ঞান নেই আর
তুমিই পরম আর সমস্ত পূর্ণতা এসে তোমাতেই মেশে ভেবেছিলে
ভেবেছিলে নিমেষেই জিতে নেবে ধনধান্যে অবোধ পৃথিবী
কখন্ও-বা ভুলে গেছ গ্রাসে ভুলেছ সংসারসীমা
আর তুমি
যদিও তোমাকে আমরা আমাদের সকলেরই জানি
লালন করেছ তবু গোপন গোপন অতিগোপন তত-কিছু-গোপনও-না লোল পক্ষপাত
আর আমি, তোমাকে বাঁচাব বলে অতর্কিতে মিথ্যাচারী, বুঝি
তোমরা কেউ জানোনি যে বহুদিন আগে তোমরা মৃত !’
গহ্বরে মিলিয়ে যায় স্বর । স্তব্ধ শ্বাস । তার পর
তিনি ফিরে তাকালেন আমাদের দিকে । বললেন, ‘এবার
আসুন এক শতাব্দী আমরা নীরব হয়ে দাঁড়াই ।
’সে অনেক শতাব্দীর কাজ / শঙ্খ ঘোষ
There is no possibility that any perceptible change will happen within our own lifetime…. Our only true life is in the future. … But how far away that future may be, there is no knowing. It might be a thousand years. At present nothing is possible except to extend the area of sanity little by little.
-George Orwell, 1984
এখনকার শিল্প, সাহিত্য কোথাও যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে মনে হয়, নিজের বাস্তবতা থেকে। না , আলগা স্টেজ গরম করার প্রতিবাদের কথা বলছি না হয়ত। চারদিক থেকে যাবতীয় অন্যায় অবিচারকে তিল তিল আহরণ করে, নিজের ভেতরে তার প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা করে, ঝুঁকি নিয়ে কিছু একটা লিখে বা তৈরি করে ফেলার যে কাজ, তা যে কত কঠিন আর অমিল আজকের দিনে।
কোন আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠছেন শিল্পী সাহিত্যিক, এমন কোন ঘটনাকে গল্পকথা মনে হতে শুরু করেছে, আজকাল জনমানসে তাই বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে রসিকতা, ইয়ার্কিও সেই দিকেই নির্দেশ করে। পাঠক আর বিশ্বাস করেনা যে লেখক কোন সততা বা সিনসিয়ারিটি থেকে রচনা করছেন। আগুন ও আহরণ করতে পারেন না। এই সময়ের এটাই অভিশাপ। এতটাই অবিশ্বাসী সময় আমাদের।
মনে পড়ে ১৯৮৫ সাল। প্রেসিডেন্সি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের শেষাশেষি অথবা সেকেন্ড ইয়ারের শুরু সেটা। কলেজটাই নরম লোহার পাতকে দুমড়ে মুচড়ে আকার আকৃতি দেয়। কলেজের তিন প্লাস দুই ওই পাঁচটা বছর। আমার কাছে অমোঘ, অনিবার্য। বি এ ফার্স্ট ইয়ার থেকে এম এ পড়া অব্দি জীবনের বছরগুলোর যে দৃপ্ততা, তা আমার বাকি জীবনকে গড়ে দিল। দেয় বোধ হয় এভাবেই। আর সেই সময়ের প্রতি মুহূর্ত কীভাবে যেন গানে কবিতায় বইয়ের পাতা ও সিনেমায় এক জমজমাট হয়ে চলা, বেজে ওঠা অর্কেস্ট্রা ছিল।
সেই অর্কেস্ট্রায় প্রায় প্রতিদিন ছিলেন শঙ্খ ঘোষ ও তাঁর কবিতারা।
আমি কে হই — শঙ্খ ঘোষের কবিতা নিয়ে, তাঁর কবিতার ইতিহাসচেতনা নিয়ে কথা বলার? আমার কোন অধিকার, যোগ্যতা এই বিশাল প্রেক্ষিত নিয়ে বিচার করবার? আমি বলি আমার কথা। তুচ্ছ কথা, কিন্তু মিছে কথা নয়। বরং তা থেকেই গড়ে নেওয়া যায় এক অন্য ইতিহাস।
আমাদের কলেজ জীবনের সেই দিনগুলোর ধরতাই ছিল রাজনীতি। এক দিকে এস এফ আই, অন্যদিকে অতিবাম রাজনীতির ছেলেপিলেরা ক্যান্টিন কাঁপাত, পোর্টিকোয় জমায়েত হত। ক্লাসে ক্লাসে ক্যামপেন করত। তো, সেইসব ক্যাম্পের থেকেই আসত ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা, ভোট পেয়ে যারা ইউনিয়ন রুম দখল করত আর তারপর একের পর এক আয়োজন করত নানান প্রতিযোগিতার।
আশ্চর্যের কথা, সেরকমই এক ইউনিয়ন আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম বিষয় হিসেবে পেয়েছিলাম, ‘বাবুমশাই’।
সে ছিল একদিন আমাদের যৌবনে কলকাতা!
বেঁচে ছিলাম ব’লেই সবার কিনেছিলাম মাথা
আর তাছাড়া ভাই
আর তাছাড়া ভাই আমরা সবাই জেনেছিলাম হবে
নতুন সমাজ, চোখের সামনে বিপ্লবে বিপ্লবে
যাবে খোল-নলিচা
যাবে খোল-নলিচা পালটে, বিচার করবে নিচু জনে’
কিন্তু সেদিন খুব কাছে নয় জানেন সেটা মনে
মিত্র বাবুমশয়
প্রত্যেকের মুখে মুখে ফেরা সেই কবিতার সঙ্গে ক্যান্টিনের টেবিল পিটুনির শব্দ। ছন্দের মায়াজালের সঙ্গে সঙ্গে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ইতিহাসচেতনাই। কেননা তখন সময় লালে লাল। আমরা কম্যুনিস্ট কাকে বলে জানছি। কম্যুনিস্ট আদর্শবাদের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের সংঘাত নিয়ে এ কবিতা তার আগে অথবা পরে অনেকেই আবৃত্তি করেছে। কিন্তু মুখে মুখে ফেরা সেই মজাদার ছড়ার ছন্দের সূত্র একবার যার মাথার ভেতর বসে গেছে, তার জীবন হয়ত পুরোটাই একরকম থাকেনি।
এই যে কলেজ ক্যান্টিনে বসে বসে জীবনের কিছু পাঠ নেওয়া, এই যে প্রতিটি রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ, আর এই যে কবিতার মধ্যে দিয়ে তা ঘটা — কেমন এক অব্যর্থ দীক্ষা এটা। শঙ্খ ঘোষের ভাষাতেই বলতে ইচ্ছে করে :
‘আর কলকাতা, কলকাতা খুলে দিল সাম্প্রতিকের দরজা। একদিনে নয়, দিনে দিনে। সেখানেও ছিল বহিয়াগতের ভীরুতা, জানা ছিল না কোনদিকে আছে পথ… প্রেসিডেন্সি কলেজের পিছনবেঞ্চ থেকে সামনের দিকে টান দিয়েছিল যারা, তারা কবি ছিল না কেউ, ছিল কবিতার প্রেমিক। তাদেরই হাতে উপহার পেয়ে পেয়ে একদিন আধুনিক কবিদের পৃথিবীতে পৌঁছে গেছি কখন। ছমছমে এক অজানা গুহার সামনে সেই আমাদের সমবেত মুগ্ধতা – আজও স্পষ্ট মনে পড়ে।’ ( কবিতার মুহূর্ত)
আশ্চর্য, এই কথা কি আমারো নয়? অথবা, আমরা কি নিজেদেরই বার বার করে তৈরি করে নিইনা আমাদের পিতৃসমদের আদলে? হয়ত এভাবেই ঘটে দীক্ষা, চলে প্রজন্মের পর প্রজন্মে চলাচল, মানসধারার।
হ্যাঁ, সেই বইটিকে আবিষ্কারও আমার ক্যান্টিনে বসেই। একদিন এক বন্ধু ক্যান্টিনে নিয়ে এল পাতলা একটা বই। কবিতার মুহূর্ত। এ বই নিয়ে কীভাবেই না কাড়াকাড়ি করেছি আমরা। এই বইতেই পেয়েছি, কবির নিজের লেখা নিজের কবিতার ইতিহাস — যে প্রবন্ধটির নামই ‘কবিতার মুহূর্ত’।
নিভন্ত এই চুল্লীতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে।
…
যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।
যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে।
নিভন্ত এই চুল্লীতে বোন আগুন ফলেছে!
‘যমুনাবতী’-র মত অতি জনপ্রিয় কবিতার লেখার পেছনের ঘটনাকাহিনি, কোন সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংযোগ করে চিন্তার বারুদে আগুন, আর ঘটিয়ে তোলে কবিতার আতশবাজি…তা জানার সুযোগ পেয়েছি। জেনেছি ‘বাবরের প্রার্থনা’-র মত কবিতার প্রেক্ষাপট। আরো কত, কত কবিতা। ‘আরুণি উদ্দালক’, ‘আপাতত শান্তিকল্যাণ’, ‘লজ্জা’, ‘ভিখিরি ছেলের অভিমান’, ‘কলকাতা’। প্রতিটা কবিতা নিজেকে উন্মোচিত করেছে আমার কাছে, এই কবিতার মুহূর্তের হাত ধরে ধরেই। আর কী বিশাল এক ইতিহাসপট রচিত হয়েছে মাথার ভেতরে। কতটাই না বড় হয়ে খুলে গেছে কবিতার আকাশ।
হ্যাঁ, ইতিহাসচেতনার প্রথম পাঠ তো এভাবেই পেতে হয়। সমাজসচেতন, এক তীব্র সময়-সংবেদী কবির প্রতিটি অক্ষরকে হতে হয় সৎ ও দায়বদ্ধ, প্রতিটি অক্ষর থেকে ঝরে পড়ে তাঁর বিশ্বাসের কথা – এই কথাটিও মনের ভেতর মুদ্রিত হয়েছে সেই সময় থেকেই অমোঘভাবে। আর তো কোনমতেই তা থেকে মুক্তি এল না আমার মত সামান্য কবিতালেখকেরও।
নিজেকে যখনই মনে হয়েছে বিচ্ছিন্ন, প্রেসিডেন্সির ক্যান্টিন থেকে শুরু করে, জীবনের যে যে ক্ষেত্রে নিজের ‘অযোগ্যতা’ নিজেই দেখে মুখ লুকিয়ে সরে আসা হয়, তখন তো সাথী হয় ‘কলকাতা’-র মত অমোঘ কবিতাই। ‘বাপজান হে/ কইলকাত্তায় গিয়া দেখি সক্কলেই সব জানে/ আমিই কিছু জানিনা’…
২
তার কিছুদিন পরে এল জার্নাল। হাত থেকে হাতে তারপর নদীর মত প্রবাহিত হয়ে যায় বই। কাড়াকাড়ি করা হয়, পড়া হয়, গদ্য দিয়ে যে কবিতা লেখা যায় জানতে পারি ধীরে ধীরে। এরপর আমরা বড় হয়ে গেলাম। আমরা আমাদের যার যার জীবনে অংশগ্রহণ করলাম। আমি তো আর ফিরে যাইনি পঠনপাঠনের প্রাঙ্গনে, করিনি মেধা ও জ্ঞানের বিশ্ববিদ্যায়তনিক চর্চা। অ্যাকাডেমিশিয়ার থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি আমি। এসেছি অন্য পেশায়।
কিন্তু কবিতা লিখতে লিখতে, কখনো যদি বা সমাজ সচেতন হবার চেষ্টা করে থাকি, তাহলে কি অদৃশ্য এক হাত মাথার উপর অনুভব করিনি সর্বদাই, তাঁরই? তাঁরই দেখান পথে কি যাইনি, শ্লেষের পথ ধরে, নয়া-অর্থনীতির পরবর্তী নব্বই দশকের দিনকালে, সমসময়ের অলিগলি চোরাপথগুলি ঘুরতে, সেগুলি নিয়ে লিখতে! এতটাই, এমনকি, যে, দেশ পত্রিকার দপ্তরে লেখা জমা পড়ার পর, শ্রদ্ধেয় সম্পাদক বলেছিলেন নাকি (অপর এক কবির মুখেই যা আমার বিশ্রুত), এই মেয়েটি শঙ্খ ঘোষকে অনুসরণ করে দেখছি।
এ আমার সম্মান। সেই নব্বই দশকের পর আরো এক দশক কেটে গেছে। ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’, ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ বা ‘এক দশকে সংঘ ভেঙে যায়’-এর মত কথা সবই শঙ্খ ঘোষের লিখিত কবিতার লাইন, কিন্তু আমাদের প্রজন্মের এক-একটি স্লোগানের মত। ‘রাতে ঘুমোবার আগে ভালোবাসবার আগে প্রশ্ন করো কোন্ দল তুমি কোন্ দল’, ‘শবের উপর শামিয়ানা’ — এক একটি মেধাবী খড়্গ, না বোঝার, কুয়াশার আঁধার কেটে ফেলার। মুখে মুখে উচ্চারিত হবার মত সহজ, গভীর, তীব্র, আলো।
তারপর, ভাঙনময় এক দুরূহ সময়ে দাঁড়িয়ে, দু হাজার ছয় থেকে সাত, নতুন এক আলোক উদ্ভাসে চিনেছি সময়চেতনার দিশারী শঙ্খ ঘোষকে। আমার আশৈশবের শোনা আন্দোলন তো একটাই ছিল তার আগে অব্দি। গল্পগাথার, সত্তর দশকের, নকশাল আন্দোলন। সে আন্দোলনের রোমান্স, সে আন্দলনের বিশ্বাসের ধারে মর্চে পড়ে গেছিল, বহুদিন। তিরিশ বছর পশ্চিমবঙ্গ ‘শান্তিকল্যাণ’-এ ছিল। এক মজে যাওয়া, পলিতকেশ বিশ্বাসের, অথবা বিশ্বাসহীন আদর্শ-কপচানোর সময়ের শবের উপর শাসকের শামিয়ানা ছিল হয়ত বা। একটি স্বপ্নদেখানো রঙিন তাজ পরা বিরাট পার্টিতন্ত্র, তাঁদের অভিপ্রায় ভুলেছিলেন, তাঁদের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি। মানুষের থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন, মানুষের রক্ত ঝরেছিল সে সরকারের পুলিশের হাতেই। উন্নয়ন আর শিল্পের সম্ভাবনার বেদীতে কৃষকের বলিদান হতে গিয়েছিল, আর সেই নাটকীয় দৃশ্যগুলো সদ্যজাগরুক দৃশ্য-শ্রাব্য মিডিয়ার উপর ঝরে পড়েছিল প্রবল আঘাতে। আমাদের চোখ ঝলসে গিয়েছিল।
তারপর আবার রক্ত, রণ, আবার প্রবল তোলপাড়, মানুষের ইচ্ছে, চেষ্টা, শক্তি। মানুষের কথা আবার ভাবার যুগসন্ধি। এই সময়টাই তাই — এক অনিবার্য দ্রুততায়, খুলে গেল আমাদের মনের কপাট। একের পর এক সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মুখে মুখে, প্রতি মুহূর্তে প্রশ্নের পাথরে বিদ্ধ হতে লাগলাম আমরা এবং আমাদের প্রায় স্থির বদ্ধ জলার ভেতরে উঠতে শুরু করল তরঙ্গ।
সেই সমসময়ের ইতিহাস আবার রচনা করলেন শঙ্খ ঘোষ। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিবেকী চেতন ও তীক্ষ্ণ ধারের শ্লেষ নেমে আসতে লাগল একের পর এক কবিতায়।
বিনয় কোঙার যখন বাক্যবাণে ঘৃণা ঝরিয়ে দিচ্ছেন, কেউ তাঁর মতাদর্শের বিরুদ্ধতা করলেই তার জীবন ‘নরক করে’ দেবার আশ্বাস দিচ্ছেন, সেই সময়েই শঙ্খ ঘোষের এই লেখাটি সংবাদপত্রের পাতা থেকে আমাদের যৌথ স্মৃতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মজা এই যে, বিনয় চলে গেলেও, যে কোন নেতার অবিনয়ের সঙ্গে এ লেখার শ্লেষাক্ত বাচন কেমন করে জানি মিলে যায়!
আমি তো আমার শপথ রেখেছি
অক্ষরে অক্ষরে
যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন
দিয়েছি নরক করে |
দাপিয়ে বেড়াবে আমাদের দল
অন্যে কবে না কথা
বজ্র কঠিন রাজ্যশাসনে
সেটাই স্বাভাবিকতা |
গুলির জন্য সমস্ত রাত
সমস্ত দিন খোলা
বজ্র কঠিন রাজ্যে এটাই
শান্তি ও শৃঙ্খলা |
যে মরে মরুক, অথবা জীবন
কেটে যাক শোক করে—
আমি আজ জয়ী, সবার জীবন
দিয়েছি নরক করে |
( স-বিনয় নিবেদন)
৩
আমাদের এই সময়টাকে সবদিক দিয়ে সর্বার্থে জড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁরই কথায়, ‘শিকড় দিয়ে আঁকড়ে’ আছেন। বাংলা কবিতায় প্রায় ষাট বছর ধরে তিনি তৈরি করে নিয়েছেন এমন এক পথ, যে-পথে স্বল্প যাত্রী, যে-পথে সামান্য আলো জ্বলে। সমালোচনায় নিয়ে এসেছেন সর্বজনবোধ্য এক জ্ঞানচর্চার দিশা, সংক্রামকভাবে বারবার সাড়া দিয়েছেন সংকট সময়ে।
–শঙ্খ ঘোষ বিষয়ে রেজাউল করিম সুমন
কবির ‘নিঃশব্দের তর্জনী’কে, অনেকে বলেন, ‘নিহিত পাতালছায়া’-র ভূমিকা। নিজের ভেতরে সমসময়কে বিস্তার দেওয়া। এ বড় কঠিন দায়। অথচ কবি যেহেতু ক্রমাগতই এ কাজটি করে চলেন, কবিতায় ও গদ্যে, তাই এ কথা মনে হতেই পারে। ‘কবি ও তার পাঠক’ বলে এ গ্রন্থে একটি প্রবন্ধ আছে। যে লেখায় কবির নিজস্ব বীক্ষণকে আমরা পাচ্ছি। সেখানেই কবি ‘সমসময়’ নামে একটি অংশে লেখেন :
…কাকে বলি সমসময়। আমরা সকলে যে ঠিক একটাই সময়ে বেঁচে আছি, আমাদের সকলের সময় যে একেবারে সমান, এ কথা তত সত্যি নয়।… সময়ের যেন ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি তল তৈরি হয়ে আছে আমাদের ভিন্ন জনের অভিজ্ঞতায়…
শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন সকলেই কি আসলে আলাদা আলাদা সময়ে বাঁচি না আমরা? আলাদা আলাদা বৃত্তে?
তারপরই তিনি বলেন, সমসময়কে তাই ধারণ করা যায়না, করা যায় ঐতিহ্যকে। ঐতিহ্য মানে কিন্তু অতীতমাত্র না, সে স্থাণু নয়। সে বার বার আবিষ্কৃত হয়।
সেখানে কবি নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলে দেন, শিল্পীর/ কবির কাজ হল — দেশনিহিত কালকে দেশোত্তর কালে পৌঁছে দেওয়া। নদীকে সমুদ্রে মিলিয়ে দেওয়া।
বারবার এইসব প্রশ্নে ফিরে ফিরে এসেছেন তাঁর সারাজীবনের কথায়, লেখায়। আমি শুধু আলো পেয়েছি, দিশা পেয়েছি, ঘোর তমসায় যেমন দিশা দেখায় কম্পাস।
সমসময়কে দূরবীক্ষণ নিয়ে দেখার ক্ষমতাটি দিয়ে তিনি আমাদের কম্পাস হয়ে থাকেন। যে সময়ের বাসিন্দা আমরা, যে দেশের বাসিন্দা, সে দেশ ও কালে বেঁচে থাকতে থাকতেই সমসময় পাতিত আকারে পৌঁছে যাচ্ছে তাঁর কবিতার ভেতর দিয়ে পরবর্তী পাঠকের হাতে।
অথবা সমসময়ের পাঠকই, যেন, কবির নিজস্ব আতশ কাঁচের সহায়তায়, দেখতে পাচ্ছেন তাঁর নিজের সময়কে, বিশাল প্রেক্ষাপটে চিরদিনের পৃথিবীর চিরদিনের হিংসা দ্বেষ গ্লানি মারমুখী আক্রমণ প্রেম স্নেহ সবকিছুর সঙ্গে মিলিয়ে। চিনতে পারছেন। লিখছেন তাই আয়ুকে। নিজের ও আমাদের আয়ুকে।
এখানে প্রাসঙ্গিক হবে বলেই তুলে দিচ্ছি কবির এক সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়।
প্র : ‘নিঃশব্দের তর্জনী’তে লিখেছিলেন, ‘এখন ইচ্ছে করে যেমন-তেমন বলতে, খুব আপনভাবে কাঁচা রকমে, খুব ছোটো আর খুব সহজ’! – এখানে ‘সহজ’ বলতে কী বুঝিয়েছিলেন? ‘জলের মতো সহজ হব’ বলেছেন কবিতায়। সেই ‘সহজ’ই বা কী? কবিতার সহজ কি ঠিক ততটা সহজ?
উ : নয় তো। লিখেও তো ছিলাম ‘সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়’। তখন যেটা বলতে চেয়েছিলাম তা হল নানা রকমের চমৎকৃতি থেকে বেরিয়ে আসার কথা। শব্দের ভার, ছবির জৌলুস, ছন্দের দোল – এসব থেকে নিজেকে যথাসম্ভব সরিয়ে নেওয়ার কথা। অন্ধকারে পাশাপাশি চুপচাপ বসে থাকতে পারে দু’জন, মাঝে মাঝে আলতো দু’-একটা কথা বলে ফেলে, সেইরকম। দৈনন্দিন কথাবার্তার চাল, তার শ্বাসপ্রশ্বাস, যথাসম্ভব তার কাছাকাছি থেকে কথা বলা। এসবকেই বলেছিলাম সহজ। কিন্তু তার থেকে যে-অনুভূতিটা পৌঁছয় তাতে হয়তো অনেক জট-জটিলতা থাকতে পারে। আসলে, ভাষার বা কথার নানা রকমের তল তৈরি হতে থাকে তখন। এক দিকে সহজ সীমায় সময়টাকে ধরে রাখতে পারে যে-ভাষা, সে কিন্তু অন্য দিকে আবার গড়িয়ে যেতে পারে অনেক দূরে।
প্র : সময়চিহ্ন ধরবার জন্য এখন অনেকেই সচেতনভাবে নিয়ে আসছেন প্রচুর হিন্দি বুলি আর ইংরেজি গালিগালাজ, টেলি সিরিয়াল, টেলিশো, এফএম রেডিও – এইসব থেকে খুঁজে পাওয়া। ওই ভাষাগুলোর সত্যিকারের স্পন্দ আর চালচলন বড়-একটা জানা থাকে না আমাদের। কেমন করে সচেতন থাকবেন লেখক, শব্দ দিয়ে বা কানে শোনা এইসব বুলি দিয়ে সময়কে ধরবার চেষ্টায়?
উ : খুব বেশি চেষ্টা করে এটা হয় বলে মনে করি না। এ খানিকটা প্রবণতার ব্যাপার। বিশেষ বিশেষ কবির ক্ষমতার ব্যাপার। হিন্দি বা ইংরেজি যেসব বুলি দৈনন্দিনে ঢুকে গেছে – তা টেলিশো থেকেই হোক বা অন্য কোনও সূত্রেই হোক – কবিতার মধ্যে তা তো চলে আসতেই পারে, আসবারই কথা। সমসময়ের সঙ্গে একটা যোগ তো রাখতেই চায় কবিতা। সমস্যা হল, যদি কারও মনে হয় এটা তাকে করতেই হবে, কেননা এই হল একটা আধুনিকোত্তর লক্ষণ, তাহলে একটা জবরদস্তির ব্যাপার ঘটতে পারে লেখায়। কবিতা পড়ে কিন্তু বোঝা যায়, কোনটা স্বভাবত আসে আর কোনটা-বা জোর করে চাপানো। স্বতঃস্ফূর্ত এক জৈব সম্পর্কে যদি জড়ানো থাকে সবটা, তবে সমকালীন বুলি কবিতার একটা শক্তিই হতে পারে।
প্র : আপনি একবার লিখেছিলেন, ‘মারের জবাব মার’। ওই একবারই অবশ্য। আজও কি বিশ্বাস করেন ও কথাটায়? কীভাবে এসেছিল লাইনটা?
উ : কীভাবে এসেছিল তা ঠিক মনে নেই এখন। তবে কথাটার মর্মে এখনও আমার বিশ্বাস নেই, তখনও ছিল না। তবে লিখলাম কেন? প্রথমত, কবিতার সব কথাই কিন্তু রচয়িতার নিজের কথা নয়, নাট্যচরিত্রের কথা যেমন নয় নাট্যকারের কথা। কবিতায় আমার ও তোমার শব্দগুলির দ্যোতনা মুহুর্মুহু পাল্টে যেতে পারে। আর দ্বিতীয় কথাটা হল, গোটা কবিতা থেকে একটা দুটো লাইনকে আলগা করে নিয়ে ভাবলে অনেকসময় একটা গোলমাল হয়ে যায়। ধরো, এই যে কবিতাটা, দু’-লাইন দু’-লাইনে গাঁথা বোধহয় দশ-বারোটা লাইন, যার মধ্যে কয়েকবারই ধুয়োর মতো আসছে ওই ‘মারের জবার মার’, যে-কবিতার নাম ‘স্লোগান’ – তার শেষ দুটো লাইন মনে আছে তো? সেটা ছিল ‘কথাই কেবল মার খায় না, কথার বড়ো ধার/ মারের মধ্যে ছল্কে ওঠে শব্দের সংসার।’ তখন কি কথা দিয়ে বা শব্দ দিয়ে মারের একটা পাল্টা শক্তিই তৈরি হল না? হিংসা-রাজনীতির যে-হাওয়া বইছিল সেই সত্তর দশকের গোড়ায়, ওইসব স্লোগানের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল কত ‘ব্যক্তি’ হয়ে উঠবার সম্ভাবনা, সেই বোধ থেকেই কিন্তু লেখা হয়েছিল ওই কবিতা।
আমাদের পথের প্রান্তে এক ধ্রুবতারার মত, এক ঈশ্বরের মত, এক নৈতিক গন্তব্যের মত দাঁড়িয়ে থাকেন শঙ্খ ঘোষ। অনেক শব্দ দিয়ে ভারাক্রান্ত করেন না, অমোঘ এক সারল্য আর সংক্ষেপিত ভাষা তাঁর কাছে থেকে আসে, দিক-নির্দেশের মত। আমরা সেই আলোয় পথ চলি।
রাজনীতির কবিতা নয়, বিবেকের কবিতা, কোলাহলের কবিতা নয়, নৈঃশব্দ্যের কবিতা, অন্যের নিন্দা নয়, নিজেদের ভেতরকার নিহিত পাতালছায়ার কবিতা লিখতেই বলেন তিনি। যেভাবে, এই কবিতাতেও, আসলে, এক চূড়ান্ত ইতিহাসচেতনার কথাই, আয়ু লেখার কথাই বলেন তিনি।
এত বেশি কথা বলো কেন? চুপ করো
শব্দহীন হও
শষ্পমূলে ঘিরে রাখো আদরের সম্পূর্ণ মর্মর
লেখো আয়ু লেখো আয়ু
ভেঙে পড়ে ঝাউ, বালির উত্থান, ওড়ে ঝড়
তোমার চোখের নিচে আমার চোখের চরাচর
ওঠে জেগে
স্রোতের ভিতরে ঘূর্ণি, ঘূর্ণির ভিতরে স্তব্ধ
আয়ু
লেখো আয়ু লেখো আয়ু
চুপ করো, শব্দহীন হও
( চুপ করো, শব্দহীন হও )


Bah yashodhara
এই সময়ের বাংলা সাহিত্যের সংসারে অভিভাবক স্থানীয় কবি শঙ্খ ঘোষ। তাঁকে নিয়ে কবি জশোধারা রায়চৌধুরীর স্মৃতিচারণা অতি সুখপাঠ্য।
লেখাটা ভালো লাগলো
খুব সুন্দর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও স্মৃতিচারণ।
শব্দব্রহ্মের কাছে শব্দতত্ত্বের রহস্য খুঁজে পেলাম। আপনাকে শ্রদ্ধা, যশোধরা।
খুব ভালো লাগলো
খুব ভালো লাগলো। মুগ্ধ হলাম।
খুব ভালো লাগলো লেখাটি ।
খুব ভালো লাগল।
খুব ভালো লাগল।