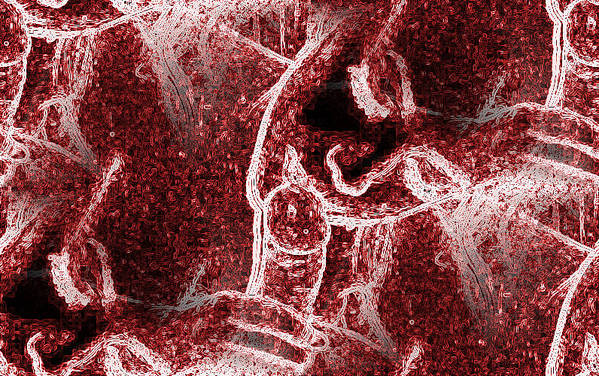
পাবলো’র ডায়েরি – ঈলের নিঃশ্বাসের মর্ম
দ্বিতীয় পর্ব
সম্রাট সরকার
“দ্বিতীয়রহিত” একটা রুদ্ধশ্বাস খোঁজ। এই বিরল শব্দটা আমি দু-বার খুঁজে পাব ভাবিনি। প্রথমবার দেখেছিলাম বাবার কাছে একটা বইয়ে। কবি অমিতেশ মাইতি-র কবিতাসমগ্রের মুখবন্ধে। আরেক কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের লেখা সে মুখবন্ধ। শব্দটা খুব মনে ধরেছিল তখন। আমি যেখানে-সেখানে খুঁজতাম। শব্দটার শুরু ও শেষে দুটি শৈলশিরা আর মধ্যে একটা ছোট্ট উপত্যকা আছে। ‘দ্বি’ ও ‘তী’ বেয়ে প্রথম শৈলশিরার চুড়োয় উঠি। তারপর ‘য়’-এ এক বিশ্রাম। উপত্যকার মত সহজ স্বস্তি, অল্প সময়ের হাঁপছাড়া – নিচু। পরক্ষণেই ‘র’ আর ‘হি’-তে পরবর্তি চড়াই ও পুনরায় ‘ত’ নামক শৈলশিরার সর্বোচ্চে চ’ড়ে বসা। আর কী অদ্ভূত কান্ড সেখানে এক গাছের ডালে বসে আছেন জিম করবেট আর মহাশ্বেতা দেবী। মাথার ওপর শকুনের দল। নিচে উপত্যকায় এক চিতা এগিয়ে চলেছে সদ্য শিকার করা গরুটিকে খেতে। চিতার অসাধারন রূপের বর্ণনায় জিম কোনো এক শব্দ বলেছেন ইংরেজিতে আর তার বাংলা তর্জমায় মহাশ্বেতা তুলে আনছেন “দ্বিতীয়-রহিত”। জিম-এর বাংলা তর্জমায় মহাশ্বেতা লিখছেন –
“…সুন্দরতম এই প্রাণীটির গতিভঙ্গী যে কত লাবণ্যভরা, এর গায়ের রং যে কী চমৎকার, সে বিষয়ে তাঁদের কোনো ধারণাই থাকতে পারে না। এর আকর্ষন শুধু বাইরের চেহারাতেই সীমাবদ্ধ নয় কেননা পাউন্ড বনাম পাউন্ডে ওর বল দ্বিতীয়-রহিত এবং সাহসেও অতুলন”।
– আচ্ছা বাবা, জিম করবেট বাঘ এত ভালোবেসেও কোন মনের জোরে এতগুলো বাঘ মেরে ফেলেছিল?
– বৈপরীত্য!
– সে আবার কেমন বাবা?
– তুমি যে এখনও পড়োনি, পাবলো-
– কী পড়িনি?
– জীবনানন্দ দাশের সেই “অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে”! তুমি যে এখনও দেখোনি অপার আলোর সুক্ষতম গভীরের সেই ব্যপ্ত অন্ধকার! রোদ্দুরের ভেতর অন্ধকার একসাথে হৃদয়ে নিয়ে চলা। ঠিক সেরকম ভালোবাসার অতলে হত্যাসূত্রতা। অবশ্য উল্টোটাও হতে পারে অনেক সময়।
– বৈপরীত্য?
– ঠিক তা নয়, এটা আবার উভোমুখিতা। সে অন্য প্রসঙ্গ। তবে করবেট সাহেবের অফুরন্ত বাঘ-ভালোবাসা এসেছিল হয়তো হত্যাপথ ধরে। নিকেশ ও আধিপত্যের ওপর জয় হয়েছিল ভালোবাসার। তাই কোথাও যেন তাঁর প্রতিটি হত্যাকাহিনীর শেষে আছে জয়ী হওয়ার দুঃখ। তবে পাবলো, সবশেষে কিন্তু এই ভালোবাসাই থেকে গেছে – তার অন্তরে হত্যা কখনো কখনো। তাই যায়। তাই তো জীবনানন্দ কখনো লেখেননি ‘অফুরন্ত তিমিরের অনন্ত রৌদ্রে’।
– তাহলে বাঘেরা কি ভাবতো গুলি খেতে খেতে? “হে করবেট সাহেব, তুমি আমাদের কয়েকজনকে দয়া করে মেরে ফেলো তবে না তোমার মধ্যে আমাদের প্রতি ভালোবাসা গড়ে উঠবে! তোমার ভালোবাসা পাওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য তাই তো তোমার রাইফেলের সামনে আমরা কুড়ি বছর ধরে দাঁড়িয়ে পড়ছি!”
– না পাবলো, বাঘেরা যে ভাবতে পারেনা সবাই জানে। তাই তো তাদের হেরে গিয়ে ক্ষোভ নেই। জীবনানন্দই তো লিখেছেন “সংসারে সমাজে দেশে প্রত্যন্তেও পরাজিত হলে/ ইহাদের মনে হত দীনতা জয়ের চেয়ে বড়ো;/ অথবা বিজয় পরাজয় সব কোনো-এক পলিত চাঁদের/ এপিঠ-ওপিঠ শুধু;- সাধনা মৃত্যুর পরে লোকসফলতা/ দিয়ে দেবে; পৃথিবীতে হেরে গেলে কোনো ক্ষোভ নেই”। পশুদের শুধু বেঁচে থাকার সাধনা। ওইটাই সার্থক আবহমান। ‘পলিত চাঁদ’। এদিকে আমাদের শুধু রকেটের চতুর অভিমুখ। খুনফন্দি। – তাও ভালোবাসা-সমীকৃত। এপিঠ-ওপিঠ।
বাবার কথার প্রতি আমার যে মন নেই বাবা বুঝতে পেরেছে। তাই এটুকু বলেই বাবা কবিতা আওড়াতে শুরু করলো।
“কোনো-যে মানে নেই, এটাই মানে।/ বন্য শূকরী কি নিজেকে জানে?/
বাঁচার চেয়ে বেশি বাঁচে না প্রাণে।… কোনো-যে মানে নেই, এটাই মানে।“
বাবা এত জটিল ক’রে বলছে আমি মাঝে মাঝেই খেই ধরে রাখতে পারছিনা। সুতরাং মন দিয়ে শুনছিনা। ঠাট্টা করছি। আমার মন এখন কাঁকড়ার দিকে। ঠিক যেখানে অনুষ্কা পায়ে কাদা মেখে পার হয়েছিল, মরা-যমুনার ঠিক সেখানে আমি আর বাবা এসেছি কাঁকড়া ধরতে। বাবার কথার মাঝে মাঝে সায় দিচ্ছি। না হ’লে কথা থামিয়ে অন্যদিকে চলে যাবে। এখানে আমার যথেষ্ঠ ভয় করে। বর্ষাকাল এখন। মরা-যমুনায় জল অনেক। ওপর থেকে টুপটাপ পাকা কদমফুল পড়ছে জলে। আর ঝরে পড়ছে বাবলার ফুল। যেদিকেই তাকাই হলুদ রঙ। মাথার ওপরের মেঘ ভর্তি আকাশটা হরেক গাছের ডালপালা নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নিয়েছে। বেশিটা কদমের দখলে। আর আছে আম, বাবলা, জিলিপি। মেঘলা আলো তাই জল অব্দি আসার গরজ দেখায়নি। ডালপালাপাতার ওপর ওপর দিয়ে দায় সেরেছে। অতয়েব জল এখানে কালচে-সবুজ। জলের ওপর অসংখ্য বাবলার হলুদ ফুল পড়ে ভাসছে। এইসব হলুদ বর্ণমালার ভেতর কাঁকড়া দেখতে পাওয়া খুব কঠিন। পাড়ের কাছে একটা দেখেছি বটে তবে হাত দিতে সাহস হচ্ছেনা। কারণ ঠিক ওর সামনে জলের একটু নিচেই হলদে রকেটের মত কি একটা আকাশের দিকে তাক করে আছে। আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরেই আবছা খেয়াল করছিলাম। বাবার মুখে ‘রকেট’ কথাটা শুনে খেয়াল গাঢ় হল। সত্যিইতো জলের ঠিক নিচে ঠিক রকেটের মত লম্বালম্বি কি রয়েছে। বাবা এবার খুব সতর্ক। কাছে যেতে নিষেধ করছে। কাঁকড়া থাক। আগে দেখতে হবে ওটা কি বস্তু। বাবার সন্দেহ জলঢোঁড়া। একটা কাঠি দিয়ে আলতো খোঁচা দিল বাবা ওর মুখে। সামান্য কেঁপে উঠল যেন। আর কিছু না। না ভয় পাওয়া না তেড়ে আসা। খোঁচাটা চুপচাপ হজম করে নিল। উপরন্তু মুখটা ধীরে ধীরে উঠে আসছে জলে উপরের দিকে। গোল-গোল চোখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। দেহটা অবিকল সাপের মত। গায়ের রং বাদামি। পেট হলুদ।
– এটা তো ঈল মাছ! আরে আমরা কুচেমাছ বলি না? ঠিক সাপের মত হয়?
– হ্যাঁ তো!
ওর মাথা ক্রমাগত উঠতে উঠতে এখন পরিষ্কার দেখা যায়। খুব ধীরে সে মাথা তুলে আনল জলের তলের কাছে। তারপর মুখটা আলতো ফাঁক ক’রে জলের ঠিক ওপর থেকে হাওয়া চোয়ালে ভ’রে নিল আর মুখটা ধীরে ধীরে নিচে নামিয়ে নিল। হারিয়ে গেল জলের ধোঁয়াশায়। এই হয়ে চলেছে। ঈল উঠছে, শ্বাস নিচ্ছে মাথাটা একটুও না ঘুরিয়ে জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মিনিট পাঁচেকের অন্তরে এই এক কান্ড। তারপর সেই অন্তর বাড়তে থাকে। ঈলের নিঃশ্বাসের মর্ম বুঝতে বুঝতে আমাদের কথা চুপ হয়ে গেছে। ততক্ষণে কালো মেঘের দল কদম-বাবলার মাথায় জড়ো হয়েছে। প্রায় আলো নেই বললেই হয় ঈলের জলে। ঈলটাও আর উঠছেনা অনেকক্ষণ ধরে। হাওয়া নেওয়ার মাঝের অন্তর লম্বা হতে হতে শুধু অন্তরটাই স্থির হয়েছে। জলের নিচে কি ওর সংসার? আর নিঃশ্বাস নিতে উঠছেনা কেন! তবে কি আজকের মত নিঃশ্বাস নেওয়া হয়ে গেল? নিঃশ্বাসেরও কি ছুটি আছে! শ্বাস নেওয়ার কাজে ছুটি হয়ে গেলে ঘুম ছাড়া আর কি কাজ! বাবা এখন একটা কবিতা বলছে –
– “সর্বদা মানুষ তার সন্তান ও রমণীর সাথে/ সম্পূর্ণ সক্রিয় গোল নিসর্গের মত স্বল্পতায়/ জীবনকে ভেঙে গ’ড়ে জীবন বানাতে গিয়ে – তবু – / ব্রহ্মা’র হাঁচির শব্দে কেঁপে উঠে – কোটি বৎসরের/ পুরোনো ঘুমের থেকে পুনরায় ডুবে যায় ঘুমের ভিতরে।“
– “ব্রহ্মা’র হাঁচি” কি বাবা?
– ওই যে আমি কাঠি দিয়ে ওকে খোঁচা দিলাম! ও একটু শিহরিত হল!
– ওরও কি তোমার মত রমনী আর সন্তান আছে?
– যদি ধ’রেই নি আছে জলের অতলে আটকায় কে।
– “সম্পূর্ণ সক্রিয় গোল নিসর্গের মত স্বল্পতায়” মানে কি?
– আসল কথা হল “স্বল্পতা”। স্বল্পতা-র একটা সামঞ্জস্য মত ধারণা পেতে গোল নিসর্গের কথা। সেই নিসর্গ, যা প্রকৃত নিসর্গের উপস্থিতিময় বিবিধ উপাদানে পূর্ণ। গাছপালা, আকাশ, মাটি, জল অথবা তোমার কল্পনায় নিসর্গের যা কিছু উপাদান – তুমি পাহাড় সমুদ্র, অরণ্য – যা তোমার কল্পনায় আসে তাই দিয়ে পরিপূর্ণ নিটোল নিসর্গ। পরিপূর্ণ নিটোল তাই “গোল নিসর্গ”। সেই নিসর্গের যাবতীয় উপাদান, প্রেক্ষিত যেহেতু উপস্থিতিময় তাই “সক্রিয়”।
– কিন্তু বাবা, স্বল্পতার কল্পনায় নিসর্গের ধারণা কেন?
– উপমা হিসেবে নিসর্গের সমগ্রতাটুকু জীবনানন্দ আগেও ব্যবহার করেছেন। আসলে পাবলো, আমরা তো জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে ভালো মন্দ বুঝতে বুঝতে নিজেদের শোধরাতে শোধরাতে চলি। প্রতিটি শোধন ও তার প্রেক্ষিত ওই রকম নিসর্গের মতই উপস্থিতিময় ও শেষে পূর্ণতার দিকে ঢলে পড়ে। তবু এই সুবিশাল সময়কালের নিরিখে আমাদের মানুষের এক একটি জীবন ও তার শোধন কত ক্ষুদ্র, তাই না! তাই এই স্বল্পতার কথা। তবে এই “স্বল্পতা”-র মধ্যে একরকমের করুণা বিজড়িত শ্লেষ আছে। সেই শ্লেষ হল আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অর্জিত প্রচুর ব্যর্থতার প্রতি। বয়সের সঙ্গে ঠিক অনুভব করতে পারবে। কারণ আমাদের আয়োজন বিপুল। নিসর্গের উপাদানের মত। অথবা নিঃশ্বাস-প্রঃশ্বাসের মতই। খাদ নেই তবু সে আয়োজন থিতিয়ে পড়বেই। তারপর ছুটি। হয়তো অযূত কোটি বছরের জন্য ঘুম তারপর।
খুব বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের আর বাড়ি ফেরার উপায় নেই। অতয়েব আমি আর বাবা ভিজছি। দুজনেই কদমগাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে।
– বাবা, আমিও কি জীবনকে ভেঙে গ’ড়ে জীবন বানাতে বানাতে বুড়ো হয়ে ঘুমিয়ে পড়ব?
– তাছাড়া আর কি! জীবনানন্দ-ই তো লিখে গেছেন-
“অনেক অ্যামিবা, কীট, উঁচু সরীসৃপ/ এখুনি তো খেলে গেছে কাদার ভিতরে/ শেষ মানুষের হাড় এক-ঘুম দিয়ে/ আবার ঘুমায়ে আছে কোটি বৎসরে।”

