
ডেভিড লিঞ্চ এবং উইম ওয়েন্ডারস্– নির্জ্ঞানের দৃশ্যকাব্যকৃতি
সন্দীপন দাশগুপ্ত
সিনেমা তার জন্মলগ্ন থেকেই বাস্তবতার প্রতিফলন এবং তার বিকৃতি, এই দুই বিপরীত প্রবণতার দ্বন্দ্বে গড়ে উঠেছে। একদিকে লুমিয়ের ভাইদের ট্রেন-প্রবেশের দৃশ্য দর্শককে বাস্তবতার দৃশ্যত চমকে অভ্যস্ত করেছিল, অন্যদিকে মেলিয়েসের Le Voyage dans la Lune দেখিয়ে দিয়েছিল যে সিনেমা আসলে স্বপ্ন দেখার যন্ত্র, কল্পনার ক্যানভাস। এই দুই দিক — বাস্তব ও পরাবাস্তব — ২০ শতকের সিনেমাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এক দার্শনিক দোলাচলে। ইতালির নব্যবাস্তববাদ থেকে শুরু করে ফরাসি নিউ ওয়েভ, তারপর আমেরিকান নিউ সিনেমা, সব জায়গায়ই দেখা গেছে মানুষের অভিজ্ঞতা আর অচেতনের সংঘাত। কিন্তু বিশ শতকের শেষার্ধে, যখন প্রযুক্তি, মনস্তত্ত্ব এবং রাজনীতি সবই বদলে যাচ্ছে, তখন পরাবাস্তবতার ভাষা নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে ফেলেন দুই পরিচালক — ডেভিড লিঞ্চ এবং উইম ওয়েন্ডারস।
ডেভিড লিঞ্চের চলচ্চিত্রে পরাবাস্তবতা শুধুমাত্র চিত্রভাষা নয়, এটি একধরনের অস্তিত্ববাদী কোলাহল — যেখানে প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ছায়া জীবন্ত, অথচ মানসিকভাবে অসংলগ্ন। তাঁর সিনেমা কখনও আমাদের বাস্তবতার গভীরে নামিয়ে দেয়, আবার কখনও বাস্তবতার পৃষ্ঠে এক অনন্ত বিভ্রমের বুদবুদের মতো আমাদের ভাসিয়ে রাখে। Eraserhead-এর শিল্পায়িত দুঃস্বপ্ন থেকে Mulholland Drive-এর বিভ্রান্ত সাইকোলজিকাল গহ্বর পর্যন্ত, লিঞ্চের জগত আসলে আমাদের অচেতনের সিনেমা — যেখানে ভয়ের, ইচ্ছার, এবং পাপের সমস্ত প্রতীক সঙ্গীত ও নিঃশব্দতার মাঝখানে নাচে।
অন্যদিকে উইম ওয়েন্ডারসের সিনেমা একদম বিপরীত ভুবন। তিনি পরাবাস্তবতা সৃষ্টি করেন না দুঃস্বপ্ন দিয়ে, বরং শূন্যতা দিয়ে। তাঁর চরিত্ররা ঘুরে বেড়ায় এক শহর থেকে আরেক শহরে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে, নিজেদের খুঁজে ফেরে সময়ের ভেতর দিয়ে। Alice in the Cities বা Paris, Texas-এর নায়করা মূলত নিজেদের অতীতের ধ্বংসাবশেষে ফিরে গিয়ে মানবিক অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। ওয়েন্ডারসের সিনেমায় আকাশে উড়ে বেড়ানো দেবদূত, বা একাকী ফটোগ্রাফারের ফ্রেমবন্দী সময়, এই সবই পরাবাস্তব নয় — বরং বাস্তবতার মর্মে থাকা আধ্যাত্মিক শূন্যতার দৃশ্যায়ন।
এই দুই পরিচালক একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ২০ শতকের শেষ তিন দশক ও ২১ শতকের সূচনাকে নতুন এক সিনেমাটিক দর্শনে বদলে দেন। যেখানে ডেভিড লিঞ্চ আমাদের অচেতন, বিকৃত, যৌন ও হিংসাত্মক মনের আয়না দেখান, সেখানে উইম ওয়েন্ডারস আমাদের চেতন, স্মৃতি ও সময়ের মধ্য দিয়ে আত্মার নিঃসঙ্গ অভিযাত্রা দেখান। তাদের সিনেমা যেন দেহ ও আত্মার দুই বিপরীত ব্যাখ্যা, তবু একই প্রশ্নের উত্তর খোঁজে — মানুষ কে, সে কোথা থেকে এসেছে, এবং তার বাস্তবতা আসলে কতটা সত্য।
লিঞ্চ ও ওয়েন্ডারসের এই সংলাপকে বোঝার জন্য আমাদের ফিরে তাকাতে হয় ইউরোপীয় শিল্পতত্ত্ব ও আমেরিকান সংস্কৃতির দ্বন্দ্বের দিকে। ইউরোপে যেখানে ফ্রয়েড, সার্ত্র, কাফকা এবং বার্গম্যান মানুষের মনোজগতের অন্ধকারকে বিশ্লেষণ করেছেন, আমেরিকায় সেখানে পুঁজিবাদ, মিডিয়া, এবং সাবার্বান জীবনের ভেতর থেকে উঠে এসেছে বিকৃত বাস্তবতার নতুন চিত্র। লিঞ্চ এই আমেরিকান মনস্তত্ত্বকে রূপ দেন সিনেমার পরাবাস্তব ভাষায় — যেন উপশহরের শান্ত মুখোশের পেছনে ফেটে যাচ্ছে দুঃস্বপ্নের অন্তঃসলিলা। আর ওয়েন্ডারস ইউরোপীয় মানসিকতার ঐতিহ্য মেনে সময়, স্মৃতি ও স্থানকে চলচ্চিত্রের আত্মা বানান — যেন পরাবাস্তবতা তাঁর কাছে স্বপ্ন নয়, বরং বাস্তবতার গভীরে দেখা অন্তর্দৃষ্টি।
এই দুই নির্মাতা একে অপরের বিপরীতে দাঁড়ালেও, তাঁদের মধ্যেই ২০ শতকের সিনেমার সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নগুলো প্রতিধ্বনিত হয় — কীভাবে আমরা দেখি, কীভাবে স্মরণ করি, এবং কীভাবে মরতে শিখি। তাঁদের সিনেমা দেখায় যে পরাবাস্তবতা কোনো বিমূর্ত শিল্প নয়; এটি বাস্তবেরই এক বিস্তৃত আয়না, যেখানে প্রতিটি চিত্র, শব্দ ও নীরবতা আমাদের ভেতরের মানসিক প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে ওঠে।
এই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশ করা যায় — ডেভিড লিঞ্চের ভয় ও সৌন্দর্যের ভূগোল, যেখানে শহর, অন্ধকার, যৌনতা, এবং মৃত্যু এক হয়ে গড়ে তোলে এমন এক সিনেমাটিক ধর্মগ্রন্থ, যা আধুনিক মানুষের চেতনার অন্তর্গত ভূতদের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

ডেভিড লিঞ্চ — ভয়, স্বপ্ন, যৌনতা এবং মৃত্যুর অচেতন ভূগোল
ডেভিড লিঞ্চের সিনেমা দেখা মানে এক শহর থেকে আরেক শহরে নয়, বরং এক স্বপ্ন থেকে আরেক দুঃস্বপ্নে প্রবেশ করা। তাঁর প্রতিটি ফ্রেম, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি নীরবতা এমনভাবে নির্মিত যে দর্শক ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে এক অচেতন গোলকধাঁধায়, যেখানে বাস্তবতার প্রতিটি নিয়ম গলে যায় এবং মানবমন তার গোপন ভয় ও কামনার প্রতিফলন দেখতে পায়। লিঞ্চের সিনেমা একধরনের দার্শনিক পরীক্ষাগার, যেখানে তিনি যৌনতা, হিংসা, অপরাধ, প্রেম, এবং মৃত্যুকে একই বৃত্তে আবদ্ধ করে দেন, যেন মানবজীবনের গভীরতম সত্যটি কেবল বিভ্রান্তির মধ্য দিয়েই ধরা যায়।
তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র Eraserhead (১৯৭৭) আজও পরাবাস্তবতার ইতিহাসে এক বিপ্লব। এখানে এক শিল্পায়িত শহরে বাস করে হেনরি — এক নিঃশব্দ মানুষ, যার সন্তান জন্ম নেয় এক বিকৃত, ভিনগ্রহীয় দেহে। শহরের প্রতিটি মেশিন, প্রতিটি পায়রার ডানা, প্রতিটি চুলের সোঁদা গন্ধ যেন ভয়ের এবং যন্ত্রণার এক সিম্ফনি। লিঞ্চের সাদা-কালো চিত্রভাষা, গম্ভীর শিল্পশব্দ, এবং মুখবিহীন মানুষজন যেন মিলে তৈরি করে এক অন্তর্গত দুঃস্বপ্ন, যেখানে মানবতা প্রযুক্তির যন্ত্রে আটকে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ফ্রয়েডের ভাষায় বললে, Eraserhead হল অচেতনের সিনেমা — দমিত যৌনতা, পিতৃত্বের ভয়, এবং জীবনের অস্তিত্বগত বীভৎসতা এখানে মিলে যায় এক যান্ত্রিক বিষণ্নতায়।

এর পরের কাজ Blue Velvet (১৯৮৬) সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে বহুল আলোচিত ছবি। একটি ছোট্ট আমেরিকান শহর, সবুজ ঘাস, উজ্জ্বল আকাশ, এবং হঠাৎ মাটির নিচে পাওয়া এক কাটা মানব-কান — এখান থেকেই শুরু হয় এক ভৌতিক যাত্রা। ছবির মূল চরিত্র জেফ্রি বোম্যান এক নারী, ডরোথি ভ্যালেন্স-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এক গোপন জগতের মধ্যে, যেখানে যৌনতা এবং হিংসা এক হয়ে যায়, যেখানে “good” ও “evil”-এর সীমানা মুছে যায়। Blue Velvet-এ লিঞ্চ দেখান আমেরিকান স্বপ্নের অন্তর্গত পচন — উপশহরের নির্ভেজাল জীবনের নীচে কেমন এক দমিত ইচ্ছা, ভয়, এবং বিকৃতি পুষে রেখেছে সমাজ। ডেনিস হপারের চরিত্র ফ্র্যাঙ্ক বুথ, যার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে অক্সিজেন মাস্ক আর বিকৃত হাসি, সে যেন এক দানব নয়, বরং মানবমনের সেই অংশ যা আমরা অস্বীকার করি কিন্তু যা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে।
লিঞ্চের Twin Peaks (১৯৯০–৯২) টেলিভিশনে নতুন বিপ্লব ঘটায়। লরা পামারের মৃত্যু এখানে কেবল এক রহস্য নয়, বরং এক সভ্যতার মৃত্যু। ছোট্ট শহরের উজ্জ্বল কফিশপ, নরম সঙ্গীত, এবং “Who killed Laura Palmer?” প্রশ্নটি এক সময় পরিণত হয় “What killed America?” প্রশ্নে। লিঞ্চ এখানেও ভয় ও রোমান্সের মধ্যে যে গোপন সূক্ষ্ম ভারসাম্য তৈরি করেন, তা টেলিভিশন ভাষার গণ্ডি ভেঙে দেয়।
এরপর আসে Lost Highway (১৯৯৭) এবং Mulholland Drive (২০০১) — যেখানে লিঞ্চের পরাবাস্তবতা একেবারে চূড়ান্ত রূপে পৌঁছায়। Lost Highway এক অন্তহীন ঘূর্ণি, যেখানে মানুষ নিজের অপরাধ, পরিচয়, এবং সময়কে হারিয়ে ফেলে। একজন স্যাক্সোফোনবাদক এক খুনের পর নিজেকে দেখতে পায় অন্য এক যুবকের শরীরে — যেন বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে কোনও দেয়ালই নেই। ছবির গঠন, সাউন্ড ডিজাইন, এবং অদ্ভুত আলোর খেলা এক ধরনের অন্তর্মুখী বিভ্রান্তি তৈরি করে, যা পরে Mulholland Drive-এ আরও নিখুঁত হয়।
Mulholland Drive নিঃসন্দেহে লিঞ্চের মাস্টারপিস। এই ছবিতে এক তরুণ অভিনেত্রী বেটি এলমস লস অ্যাঞ্জেলেসে আসে, স্বপ্ন দেখে হলিউড জয় করার। কিন্তু হঠাৎ সে জড়িয়ে পড়ে এক রহস্যময় নারীর জীবনে, যার স্মৃতি হারিয়ে গেছে। এই দুই নারী, তাদের সম্পর্ক, তাদের যৌন আকর্ষণ, ঈর্ষা, এবং পরবর্তীতে বিকৃত হিংসা — সব মিলিয়ে গড়ে ওঠে এক এমন জটিল কাহিনি, যেখানে বাস্তব আর স্বপ্ন, প্রেম আর অপরাধ একে অপরের প্রতিবিম্ব। “Silencio!” — ছবির ক্লাবে উচ্চারিত এই শব্দটি যেন পুরো লিঞ্চীয় মহাবিশ্বের প্রতীক, যেখানে শব্দ, দৃশ্য, আর আবেগ একে অপরকে প্রতারণা করে।
এর পরের Inland Empire (২০০৬) লিঞ্চের সবচেয়ে র্যাডিকাল কাজ। এখানে তিনি ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করে তৈরি করেন তিন ঘণ্টার এক মানসিক দুঃস্বপ্ন, যেখানে একজন অভিনেত্রীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে পরিচয়ের ক্রমাগত ভাঙন। দর্শক হারিয়ে যায় সময় ও বাস্তবতার ঘূর্ণিপাকে, এবং সিনেমা পরিণত হয় এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায়।
লিঞ্চের সিনেমায় যৌনতা সবসময় একধরনের সহিংসতা, ভয়, এবং মুক্তির সংমিশ্রণ। তাঁর নারী চরিত্ররা — ডরোথি, লরা, বেটি বা নিকি — সবাই কোনও না কোনওভাবে শিকার ও সৃষ্টিকর্তা উভয়ই। তাদের দেহ রাজনীতি, পুরুষের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে বন্দি হলেও, তারা শেষ পর্যন্ত দুঃস্বপ্নকে নিজস্ব শক্তিতে উলটে দেয়। এইভাবে লিঞ্চের পরাবাস্তবতা নারী ও পুরুষ, কামনা ও ভয়, আলো ও অন্ধকার — এই সবকিছুর পারস্পরিক টানাপোড়েনে তৈরি হয়।
ডেভিড লিঞ্চ নিজে একবার বলেছিলেন, “The deeper you go into the dream, the closer you get to reality.” অর্থাৎ তাঁর কাছে স্বপ্ন মানে পালানো নয়, বরং গভীরভাবে প্রবেশ করা। তাঁর ছবিগুলি তাই শুধু ভয়ের সিনেমা নয়, বরং মানবমনের গভীরে প্রবেশের সিনেমা। লিঞ্চ আমাদের শেখান যে বাস্তবতা কোনো কঠিন বস্তু নয়, এটি তরল, রূপান্তরশীল, এবং আমাদের অচেতনের মতোই অনির্দিষ্ট।
তাঁর শিল্পতত্ত্বের এই ধারাটি ইউরোপীয় পরাবাস্তবতার থেকে আলাদা — সেখানে লিঞ্চ কোনো তত্ত্বপ্রধান শিল্পী নন, বরং এক “American mystic”, যিনি সাবার্বান জীবনের নিস্তরঙ্গ শান্তির ভেতরে লুকিয়ে থাকা নৈরাজ্যকে দৃশ্যমান করেন।

উইম ওয়েন্ডারস — সময়, স্মৃতি, আকাশ ও একাকিত্বের সিনেমা
উইম ওয়েন্ডারসের সিনেমায় প্রবেশ করা মানে পৃথিবীর নিঃশব্দ প্রান্তে পা রাখা — যেখানে শহরের কোলাহল, আধুনিকতার রণধ্বনি, কিংবা মানুষের লোভ কিছুই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং যেখানে সবচেয়ে বেশি শোনা যায় একাকিত্বের শব্দ, সময়ের মৃদু প্রবাহ, আর অজানার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার নরম আর্তি। ওয়েন্ডারসের সিনেমা একধরনের আধ্যাত্মিক যাত্রা, যেখানে পরাবাস্তবতা আসে না বিভ্রম বা বিকৃতির মাধ্যমে, বরং স্মৃতি, অনুপস্থিতি এবং দূরত্বের নীরবতায়।
জার্মান নিউ সিনেমার অংশ হিসেবে তাঁর উত্থান ঘটে সত্তরের দশকে, এমন এক সময় যখন যুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপ নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে, আর সিনেমা খুঁজছে নতুন ভাষা, নতুন দৃষ্টি। Alice in the Cities (১৯৭৪) সেই ভাষার প্রথম নিদর্শন। এক ফটোগ্রাফার, যিনি আমেরিকা থেকে জার্মানিতে ফিরতে চায়, কিন্তু পথে এক ছোট্ট মেয়ের দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর কাঁধে। এই সহজ কাহিনির ভেতরেই ওয়েন্ডারস এমনভাবে সময়কে স্থির করে দেন যে প্রতিটি যাত্রা হয়ে ওঠে আত্ম-আবিষ্কারের পথ। ক্যামেরা কখনও থামে না, কিন্তু কোথাও গিয়েও পৌঁছয় না — যেন যাত্রাই গন্তব্য।

এরপর Kings of the Road (১৯৭৬) এবং The American Friend (১৯৭৭) তাঁর সিনেমার দিকচিহ্নকে আরও স্পষ্ট করে। Kings of the Road-এ দুই পুরুষের নির্জন ভ্রমণ, ধ্বংস হয়ে যাওয়া সিনেমা হলগুলির পাশে ঘুরে বেড়ানো, একদিকে জার্মান সংস্কৃতির মৃত্যু, অন্যদিকে বন্ধুত্ব ও নিঃসঙ্গতার গভীর সুর তোলে। ওয়েন্ডারস এখানে ক্যামেরাকে ব্যবহার করেন যেন সে এক সহযাত্রী — স্থির পর্যবেক্ষক নয়, বরং যাত্রাপথের সঙ্গী। The American Friend তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক সাফল্য, যেখানে প্যাট্রিসিয়া হাইস্মিথের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হয় নৈতিক দ্বন্দ্বের এক রহস্যময় কাহিনি। ডেনিস হপার ও ব্রুনো গানৎসের অভিনয়ে এই চলচ্চিত্রে শহুরে বিষণ্নতা ও অপরাধের ছায়া মিলেমিশে যায়, তৈরি করে এক ধূসর বাস্তবতা।

কিন্তু তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র আসে ১৯৮৪ সালে — Paris, Texas। এটি কেবল ওয়েন্ডারসের নয়, বিশ্ব সিনেমার ইতিহাসে অন্যতম আবেগময় ও অন্তর্মুখী চলচ্চিত্র। এক ব্যক্তি ট্র্যাভিস, যিনি বহু বছর পর মরুভূমি থেকে ফিরে আসে, খোঁজে তার হারানো স্ত্রী ও পুত্রকে। ছবিটি শুরু হয় আমেরিকার ধূসর মরুভূমিতে, যেখানে ট্র্যাভিসের নীরব হাঁটা যেন মানুষের অনন্ত নিঃসঙ্গতার প্রতীক। সময় এখানে কেটে যায় না, বরং জমে থাকে আলো, ধুলা, আর সঙ্গীতের মধ্যে। রাই কুডারের স্লাইড গিটারের সুর যেন ট্র্যাভিসের ভেতরের নীরব আর্তি। শেষে যখন সে এক মেয়ে, তার হারানো স্ত্রী, তার সামনে দাঁড়ায় এক কাচের ঘরে, তখন ওয়েন্ডারস দেখান আধুনিক সভ্যতার আবেগহীন কাঠামোর ভেতরেও কীভাবে মানুষ এখনও ভালোবাসার ভাষা খোঁজে। “I knew that I couldn’t make you stay,” — ট্র্যাভিসের সংলাপটি পরিণত হয় ২০ শতকের একাকিত্বের মন্ত্রে।
এর পরের ছবি Wings of Desire (১৯৮৭) হল তাঁর পরাবাস্তব বাস্তবতার চূড়ান্ত নিদর্শন। এখানে বার্লিন শহরজুড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে অদৃশ্য দেবদূতরা, যারা মানুষের চিন্তা শুনতে পায়, কিন্তু স্পর্শ করতে পারে না। তারা একের পর এক মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, একাকিত্ব অনুভব করে, কিন্তু হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এই দেবদূতরা আসলে সময়ের প্রতীক — ইতিহাসের সাক্ষী। যখন দেবদূত ড্যামিয়েল অবশেষে নেমে আসে মানবজগতে, সে রক্তমাংসের জীবনে প্রবেশ করে, ভালোবাসা শেখে, ব্যথা অনুভব করে, তখন ওয়েন্ডারস আসলে দেখান পরাবাস্তবতার সবচেয়ে মানবিক রূপ — বাস্তবতার জন্য আকুলতা। বার্লিনের কালো-সাদা ও রঙিন ফ্রেমের দ্বন্দ্ব, হ্যান্ডহেল্ড ক্যামেরার মৃদু দোলা, আর পিটার ফক-এর আত্ম-উপহাসময় উপস্থিতি এই সিনেমাকে পরিণত করে জীবনের ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সংলাপে।

নব্বইয়ের দশকে তাঁর Until the End of the World (১৯৯১) এবং Lisbon Story (১৯৯৪)-এ এই ধারা আরও প্রসারিত হয়। এখানে প্রযুক্তি ও স্মৃতি একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়। এক চলচ্চিত্রকার ও এক সাউন্ড রেকর্ডিস্ট ঘুরে বেড়ায় লিসবনের অলিগলি, খোঁজে ‘শব্দের আত্মা’। এই ছবিগুলিতে ওয়েন্ডারসের পরাবাস্তবতা এসেছে আধুনিকতার বিভ্রান্তি থেকে — যেখানে মানুষ তার নিজের তৈরি প্রযুক্তির মধ্যে হারিয়ে ফেলছে স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা।
পরবর্তী সময়ে The Salt of the Earth (২০১৪) এবং Perfect Days (২০২৩)-এ ওয়েন্ডারস এক আধ্যাত্মিক বাস্তবতায় পৌঁছান। Perfect Days-এর নিঃশব্দ পরিচ্ছন্নকর্মী হিরায়ামা, যে প্রতিদিন একই রুটিনে টোকিওর টয়লেট পরিষ্কার করে, তার দিনযাপন, তার শান্ত দৃষ্টি, তার গান শোনা, গাছের দিকে তাকানো — এইসব সাধারণ মুহূর্তে ওয়েন্ডারস এমন এক গভীর মানবিক পরাবাস্তবতা সৃষ্টি করেন, যেখানে জীবন নিজেই এক শিল্পকর্ম। এই ছবিতে সময় যেন স্থির হয়ে যায়, কিন্তু সেই স্থিরতায় আমরা শুনতে পাই জীবনের গোপন সঙ্গীত।
ওয়েন্ডারসের সিনেমায় মৃত্যুচেতনা খুবই সূক্ষ্ম, কিন্তু সর্বব্যাপী। তাঁর চরিত্ররা মরে না, বরং বিলীন হয়ে যায় সময়ের প্রবাহে। তাঁদের যাত্রা শেষ হয় না, শুধু দিক পরিবর্তন করে। তাই তাঁর সিনেমা একদিকে কবিতার মতো, অন্যদিকে দর্শনের মতো। বাস্তবতা ও পরাবাস্তবতার মধ্যে তিনি তৈরি করেন এমন এক সিনেমাটিক সেতু, যেখানে দর্শক নিজেকে খুঁজে পায়, হারায়, আবার ফিরে পায় — যেমন ট্র্যাভিস ফিরে পায় নিজের আত্মাকে মরুভূমির নিঃসঙ্গ আলোয়।
এইভাবে উইম ওয়েন্ডারসের পরাবাস্তবতা ডেভিড লিঞ্চের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা মাত্রা নেয়। লিঞ্চ যেখানে ভয় ও দমনের অচেতন জগতে প্রবেশ করেন, ওয়েন্ডারস সেখানে শূন্যতা ও নীরবতার মধ্যে জীবনের সারবস্তু খুঁজে পান। দুই নির্মাতা দুই মহাদেশের সন্তান, তবু তাঁদের সিনেমার কেন্দ্রে একই প্রশ্ন প্রতিধ্বনিত — সময়ের অর্থ কী, স্মৃতির ওজন কত, এবং মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব কোথায় মিলিয়ে যায়।
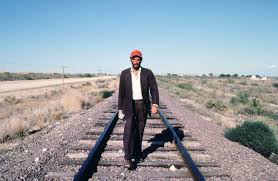
ডেভিড লিঞ্চ ও উইম ওয়েন্ডারস — পরাবাস্তবতা, সময় ও মৃত্যুচেতনার দ্বৈত সেতুবন্ধ
ডেভিড লিঞ্চ ও উইম ওয়েন্ডারস — দুইজনই এমন চলচ্চিত্রকার যাঁদের সিনেমা আধুনিক বাস্তবতার সীমানা অতিক্রম করে অচেতন, স্মৃতি, নীরবতা ও সময়ের অঞ্চলে প্রবেশ করে। কিন্তু তাঁদের যাত্রার পথ এক নয়। লিঞ্চ যেখানে বাস্তবতার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা ভয়, বিকার, দমন ও যৌন-অস্থিরতাকে উন্মুক্ত করেন, ওয়েন্ডারস সেখানে সময়ের কোমল আলোয় মানবিক একাকিত্বের নকশা আঁকেন। একে বলা যায়, লিঞ্চের পরাবাস্তবতা হল অন্তর্দ্বন্দ্বের চিৎকার, আর ওয়েন্ডারসের পরাবাস্তবতা হল নীরবতার দীর্ঘশ্বাস।
লিঞ্চের চলচ্চিত্রে শহর ও ঘর, আলো ও অন্ধকার, পরিচিত ও অচেনা — সবকিছুই দ্বিমুখী। তাঁর দৃষ্টি চিরকাল সন্দেহে পূর্ণ। Blue Velvet-এর সুন্দর উপনগরী হঠাৎ খুলে দেয় পচে যাওয়া মৃতদেহের গর্ত; Twin Peaks-এর শান্ত শহর আসলে এক যৌথ দুঃস্বপ্ন; Mulholland Drive-এর প্রেম আসলে এক হত্যার স্মৃতি। এই দ্বৈততার ভেতরেই লিঞ্চ গড়ে তোলেন তাঁর পরাবাস্তব জগৎ, যা প্রতিনিয়ত দর্শকের বোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তিনি বিশ্বাস করেন, বাস্তবতা এক নয় — বরং একাধিক স্তরের সত্তা, যেখানে সত্য ও স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও ভয় একসাথে বাস করে।
অন্যদিকে, ওয়েন্ডারসের সিনেমা একই দ্বৈততাকে অন্যরকম কোমলতায় ধরে। তাঁর Wings of Desire-এ দেবদূতরা মানুষের চিন্তা শোনে, কিন্তু ছুঁতে পারে না — এই দূরত্বই বাস্তবতার গভীর রূপক। লিঞ্চের দৃষ্টিতে ‘স্পর্শ’ বিপজ্জনক, কামনাবিদ্ধ, অন্ধকারে ভরা; ওয়েন্ডারসের দৃষ্টিতে সেটি পবিত্র, সময়ের আলিঙ্গনের মতো। লিঞ্চ যেখানে মানবমনকে খুলে ফেলেন অস্ত্রোপচারের মতো, ওয়েন্ডারস সেখানে তাকে ধীরে ধীরে শুনে বোঝার চেষ্টা করেন।
দু’জনেরই চলচ্চিত্র সময়ের বিপরীতে চলে। লিঞ্চ সময়কে ভেঙে দেন — Lost Highway বা Inland Empire-এ সময় যেন বারবার নিজেকে খেয়ে ফেলে, গঠন ও বিন্যাস হারায়। চরিত্ররা যেন নিজের ভবিষ্যৎ ও অতীতের মধ্যে হারিয়ে যায়। ওয়েন্ডারস কিন্তু সময়কে প্রসারিত করেন — এক অনন্ত টান তৈরি করেন। Paris, Texas-এর মরুভূমি বা Perfect Days-এর টোকিও শহর যেন একই সময়ের ভিতরে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে ধরে রাখে। লিঞ্চ সময়কে দুঃস্বপ্নের গোলকধাঁধা বানান, ওয়েন্ডারস সময়কে ধ্যানের প্রান্তর করে তোলেন।
তবু এক জায়গায় তাঁরা মিলিত — মৃত্যু ও অনুপস্থিতির অনুভবে। লিঞ্চের জগতে মৃত্যু মানে মনের ধ্বংস, পরিচয়ের বিলোপ; ওয়েন্ডারসের জগতে মৃত্যু মানে সময়ের শান্ত গ্রহণ। The Straight Story-এর বৃদ্ধ আলভিন যেভাবে এক লনমোয়ারে চড়ে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যায়, সেই ধীর যাত্রায় মৃত্যু এক কোমল রূপ নেয় — যেন জীবনের পরিণত সুর। অন্যদিকে Eraserhead বা Twin Peaks: Fire Walk With Me-এ মৃত্যু ভয়ঙ্কর, বিকৃত, ধ্বংসাত্মক — কিন্তু তবুও সেখানে আধ্যাত্মিকতা আছে, এক অন্ধকার মন্দিরের মতো।
দু’জনের সিনেমায় পরাবাস্তবতা তাই কখনও কেবল শৈল্পিক কৌশল নয় — এটি অস্তিত্বের অনুসন্ধান। লিঞ্চ বলেন, “We live inside a dream.” ওয়েন্ডারস বলেন, “We live inside time.” দু’জনই মানবজীবনের সীমা পরীক্ষা করেন — একজন স্বপ্নের অন্ধকার দিয়ে, অন্যজন সময়ের আলো দিয়ে।
লিঞ্চের ক্যামেরা চলে ঘূর্ণির মতো — অস্থির, চঞ্চল, অন্ধকারে ডুবে থাকা। ওয়েন্ডারসের ক্যামেরা হাঁটে — ধীরে, ধীরে, নিঃশব্দে। কিন্তু দু’জনেই বিশ্বাস করেন, ক্যামেরা মানুষের আত্মার আয়না। লিঞ্চের ফ্রেমে আয়না ভেঙে যায়, তাতে রক্ত ঝরে। ওয়েন্ডারসের ফ্রেমে আয়না শুধু আলো প্রতিফলিত করে, তাতে ছায়া পড়ে।
তাঁদের দর্শনও একে অপরের বিপরীতে দাঁড়ায়। লিঞ্চের চলচ্চিত্র অস্তিত্ববাদী আতঙ্কে ভরা; তাঁর চরিত্ররা জানে না তারা কে, কোথা থেকে এসেছে, বা তাদের ভেতরের অন্ধকার কোথা পর্যন্ত সত্য। ওয়েন্ডারসের চরিত্ররা জানে তারা পথিক — তারা খুঁজে চলে অর্থহীন এক জীবনের সৌন্দর্য। তাই লিঞ্চের সিনেমা শেষ হয় বিভ্রান্তিতে, ওয়েন্ডারসের সিনেমা শেষ হয় প্রশান্তিতে।
কিন্তু এই দুই বিপরীত দৃষ্টি এক জায়গায় এসে মিলিত হয় — মানুষ ও বিশ্বের সম্পর্ক নিয়ে গভীর আধ্যাত্মিক ভাবনায়। লিঞ্চ মনে করেন, জগৎ এক রহস্যময় সত্তা, যাকে বোঝা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়। ওয়েন্ডারস মনে করেন, জগৎ এক আলোকিত নীরবতা, যেখানে প্রতিটি মুহূর্তেই অর্থ লুকিয়ে আছে।
এদের দুজনের সিনেমা পরাবাস্তবতার দুই প্রান্ত — ভয় ও শান্তি, অন্ধকার ও আলো, বিকার ও প্রার্থনা। লিঞ্চ আমাদের টেনে নেয় স্বপ্নের অন্ধকারে; ওয়েন্ডারস আমাদের বসিয়ে রাখে সময়ের জানালার ধারে। একজনে দেখান মানুষের ভয়াবহতা, অন্যজনে তার কোমলতা।
তবু শেষ পর্যন্ত, দুইজনই প্রমাণ করে দেন — পরাবাস্তবতা মানে কল্পনা নয়, বরং বাস্তবতারই এক গভীর রূপ, যা দেখা যায় কেবল তখনই, যখন আমরা চোখ বন্ধ করি।

পরাবাস্তবতা, সময় ও মৃত্যুচেতনা।
ডেভিড লিঞ্চ ও উইম ওয়েন্ডারস—দুই প্রান্তের দুই চলচ্চিত্রকার, কিন্তু দুজনেরই সিনেমা আমাদের বাস্তবতার ভিতর থেকে এক অদৃশ্য সত্যকে টেনে তোলে, যে সত্য আমরা সাধারণত দেখতে পাই না, কিন্তু অনুভব করি গভীরে। তাঁদের সিনেমায় পরাবাস্তবতা কেবল এক নান্দনিক ঘূর্ণি নয়; এটি মানুষের চেতনার সীমানায় দাঁড়িয়ে এক সঙ্কেত—যে আমরা যা দেখি, তা আসলে অসম্পূর্ণ, আর আমাদের অভিজ্ঞতা সময় ও মৃত্যুর সঙ্গে এক অনন্ত সংলাপে যুক্ত। এই সংলাপই তাঁদের শিল্পকে করে তোলে দার্শনিক।
লিঞ্চের কাছে পরাবাস্তবতা হল এক ভয়ের অঞ্চল, যেখানে মানবমন নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে আতঙ্কিত হয়। তাঁর চরিত্ররা যেন নিজেদের স্বপ্নের মধ্যে বন্দি। Eraserhead-এর মিউটেটেড শিশু, Lost Highway-এর ভাঙা পরিচয়, Mulholland Drive-এর প্রতারিত প্রেম—সবই আমাদের মনের ভয় ও দমনের প্রতীক। লিঞ্চ এই ভয়ের ভাষাকে সিনেমার ভাষা বানিয়েছেন—আলো, শব্দ, শব্দহীনতা, হঠাৎ বদলে যাওয়া দৃশ্য, ভাঙা সময়—all মিলে তিনি এক অন্তর্গত মনস্তত্ত্ব নির্মাণ করেন। তাঁর সিনেমা স্বপ্নের মতো, যেখানে দৃশ্যের চেয়ে বেশি সত্য লুকিয়ে থাকে তার অস্বস্তিতে।
অন্যদিকে উইম ওয়েন্ডারসের পরাবাস্তবতা হল এক দীর্ঘ নীরব যাত্রা—এক আধ্যাত্মিক বাস্তবতা, যেখানে মানুষ নিজেকে বুঝতে শেখে সময়ের ভিতর দিয়ে। Paris, Texas-এ ট্র্যাভিস মরুভূমি পেরিয়ে ফিরে আসে নিজের ছেলেকে খুঁজে, কিন্তু যা খুঁজে পায় তা হল নিজের নিঃসঙ্গতা। Wings of Desire-এ দেবদূতরা মানুষের দুঃখ শুনতে শুনতে অবশেষে মানবিক হতে চায়। ওয়েন্ডারসের ছবিতে মৃত্যু ভয় নয়, বরং এক স্বাভাবিক মিলন—মানুষ ও সময়ের সম্পর্কের পরিণতি। তাঁর প্রতিটি ক্যামেরা-মুভমেন্ট যেন এক ধ্যান; প্রতিটি মুখের ক্লোজ-আপ এক প্রার্থনা।
তবু এই দুই জগৎ—লিঞ্চের অন্ধকার ও ওয়েন্ডারসের আলো—আসলে একে অপরের পরিপূরক। লিঞ্চ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে জীবনের গভীরে ভয় আছে, এবং এই ভয়ই আমাদের অস্তিত্বকে বাস্তব করে তোলে। ওয়েন্ডারস বলেন, ভয়কে অতিক্রম করেই আমরা অর্থ খুঁজে পাই। লিঞ্চের মৃত্যু হল পতন, ওয়েন্ডারসের মৃত্যু হল গমন; একজন দেখান কেমন করে মানবমন নিজেকে ছিঁড়ে ফেলে, অন্যজন দেখান কেমন করে সময়ের ভিতর দিয়ে আমরা নিজেকে মেলাই।
দু’জনের সিনেমাতেই সময় স্থির নয়। লিঞ্চের সময় ভাঙা—দুস্বপ্নের মতো বিক্ষিপ্ত ও বৃত্তাকার। দর্শক জানে না কোথায় শুরু, কোথায় শেষ। ওয়েন্ডারসের সময় ধীর—এক দীর্ঘ শ্বাসের মতো। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই সময়ের গঠনই চরিত্র হয়ে ওঠে। এই সময়চেতনা তাঁদের সিনেমাকে এক মহাজাগতিক মাত্রা দেয়—যেখানে ব্যক্তি আর সমাজ, বাস্তব আর কল্পনা, সব মিশে যায় এক অজানা পরিসরে।
এই দুই পরিচালকের চলচ্চিত্রকে যদি একসাথে দেখা যায়, দেখা যাবে তাঁরা আসলে একই প্রশ্নের দুই উত্তর খুঁজেছেন—মানুষ কেন বাঁচে, এবং মৃত্যু মানে কী। লিঞ্চ এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন অচেতন ও বিকারের ভেতরে, যেখানে জীবন ভাঙা আয়নায় প্রতিফলিত হয়। ওয়েন্ডারস খোঁজেন সেই উত্তর সময়ের অবসরে, যখন মানুষ বুঝতে শেখে যে বেঁচে থাকা মানে দেখা, শোনা, অনুভব করা।
তাঁদের মধ্যে আরও একটি সূক্ষ্ম মিল আছে—দু’জনেই প্রযুক্তি ও নগরসভ্যতার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া মানবতার খোঁজ করেন। লিঞ্চের শহর এক দুঃস্বপ্ন; বৈদ্যুতিক তারের গুঞ্জন, মেশিনের শব্দ, কৃত্রিম আলোর ঝলক—সবকিছু মিলিয়ে এক যান্ত্রিক দুঃসহতা। ওয়েন্ডারসের শহর এক ধ্যানস্থ পরিসর—ক্যামেরা হেঁটে চলে খালি রাস্তায়, যেন মানবতা হারানো কোনও নীরব শহর খুঁজে বেড়াচ্ছে। এইভাবে দু’জনেই সিনেমাকে ব্যবহার করেছেন সভ্যতার আত্মপরিচয় নিয়ে চিন্তার উপকরণ হিসেবে।
পরাবাস্তবতা তাঁদের কাছে তাই শুধুমাত্র স্বপ্নের উপস্থাপন নয়, বরং বাস্তবতার অতিক্রমণ। লিঞ্চ বলেন, বাস্তবতার অন্তর্গত স্তর আছে, যেখান থেকে আমাদের ভয় এবং ইচ্ছা জন্ম নেয়। ওয়েন্ডারস বলেন, বাস্তবতা হল সময়ের প্রবাহ, আর মানুষ সেই সময়ের ভিতর দিয়ে নিজেকে চিনে। তাঁদের এই ভাবনা সিনেমাকে এক দার্শনিক উচ্চতায় নিয়ে যায়—যেখানে দৃশ্য কেবল গল্প নয়, বরং এক ধ্যান।
শেষ পর্যন্ত, তাঁদের সিনেমা মৃত্যুচেতনা নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। লিঞ্চের মৃত্যুচেতনা হল আতঙ্ক ও ধ্বংসের প্রতীক—অচেতনের শেষসীমা। ওয়েন্ডারসের মৃত্যুচেতনা হল সময়ের মৃদু আত্মসমর্পণ—এক ধরণের আধ্যাত্মিক মুক্তি। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই মৃত্যু এক রূপান্তর, যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় জীবনের ভঙ্গুরতা।
এই কারণে ডেভিড লিঞ্চ ও উইম ওয়েন্ডারস আধুনিক চলচ্চিত্রের দুই মেরু হয়ে উঠেছেন। তাঁরা বাস্তবতা থেকে পালিয়ে যান না; বরং বাস্তবতার গভীরে নেমে গিয়ে তার ভিতরে থাকা অদ্ভুত, অপরূপ, ভয়ানক ও পবিত্র সত্যটিকে উন্মোচন করেন। তাঁদের সিনেমা এক ধরনের ‘চেতনার স্থাপত্য’, যেখানে ফ্রেম, শব্দ, ছায়া ও সময় মিলে তৈরি হয় এমন এক জগৎ, যা আমাদের নিজের মনের প্রতিফলন।
লিঞ্চের দুঃস্বপ্ন ও ওয়েন্ডারসের নীরবতা—দুইই শেষ পর্যন্ত একই উদ্দেশ্যে কাজ করে: মানুষকে তার সীমা দেখানো। তাঁরা শেখান, আমরা যতই বাস্তবকে আঁকড়ে ধরতে চাই, তার অন্তরালে সবসময়ই এক স্বপ্ন আছে; এবং সেই স্বপ্নের ভেতরেই আমরা মৃত্যুর আভাস পাই।
তাঁদের চলচ্চিত্র তাই শুধু পরাবাস্তব নয়, বরং গভীরভাবে মানবতাবাদী। লিঞ্চের বিকৃত মুখোশের নিচে যেমন এক গভীর ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে, ওয়েন্ডারসের নিঃসঙ্গতার মধ্যেও তেমনি আছে স্নেহের উষ্ণতা। এই দ্বৈততাই তাঁদের সিনেমাকে জীবন্ত রাখে—যেমন জীবন নিজে, তেমনি জটিল, তেমনি সুন্দর।
সম্ভবত এই কারণেই আজও লিঞ্চ ও ওয়েন্ডারসের সিনেমা আমাদের তাড়া করে—কারণ তারা শুধু গল্প বলে না, তারা আমাদের চিনতে শেখায়। তারা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বাস্তবতা ও পরাবাস্তবতা, সময় ও মৃত্যু—সব এক সূত্রে বাঁধা। আমরা যে পৃথিবীতে বেঁচে আছি, সেটি হয়তো একটি দীর্ঘ স্বপ্ন, বা হয়তো এক অনন্ত নীরবতা।
আর এই দ্বন্দ্বের মাঝেই, লিঞ্চ ও ওয়েন্ডারস আমাদের শেখান—সিনেমা কেবল এক দৃশ্যশিল্প নয়, এটি এক আত্মার অভিজ্ঞতা।

