‘তর্কের উজ্জ্বল রৌদ্র’ এবং অলোকরঞ্জনের চিন্তার ঈশ্বর
: হিন্দোল ভট্টাচার্য
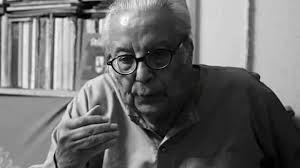
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পূর্ণ ভাবে আস্তিক ছিলেন। অস্তিত্ববাদের নিরীশ্বর-চেতনা তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কিন্তু এই আস্তিক্যবোধের স্বরূপ সন্ধান করতে না পারলে সম্ভবত, তাঁর কবিতাকে স্পর্শ করাও যাবে না। এই আস্তিক্যবোধ কি ঈশ্বরের প্রতি একধরনের প্রশ্নহীন আনুগত্য, না অন্ধ সমর্পণ? এখানে প্রশ্ন আসতেই পারে, আস্তিক্যের মধ্যেই একপ্রকার অন্ধ সমর্পণের কথা বলা নেই? না কি আস্তিক্যবাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে একপ্রকার সংশয়হীন বিশ্বাসের শিকড়? যদি না সংশয়হীন বিশ্বাসের জায়গায় কেউ উপনীত হয়, তাহলে কি আস্তিক্যবোধকে আশ্রয় করে কেউ নিজের চিন্তাচেতনার জগতের উন্মেষ ঘটাতে পারে? এখানে এসে মনে হয় একপ্রকার দ্বন্দ্বই তৈরি হয়। অলোকরঞ্জনের আস্তিক্যবোধে যে ঈশ্বর থাকেন, তা এতটাই সর্বব্যাপী, যে তার মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকেন গ্বালিব, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, সক্রেটিস, বুদ্ধ এবং কার্ল মার্ক্স-ও। কীভাবে আমি বলছি ঈশ্বর প্রসঙ্গে কার্ল মার্ক্সের কথা? এ কথা শুনলে তো ঘোড়াও হাসবে। কিন্তু, আমার মনে হয়, জগতের মঙ্গলবোধের যে ধারণা থেকে ঈশ্বরের সৃষ্টি, সেই ধারণা থেকেই বুদ্ধ বা মার্ক্স অবধারিত ভাবে তাঁর কবিতার, প্রবন্ধের ও ভাবনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হত। বিশেষ করে যৌবন বাউল এবং প্রথম পর্যায়ের কবিতার আত্মানুসন্ধানী বিশ্বাসের যে জগতের চিত্র বাংলা কবিতার কাছে পাথেয় হয়েছিল স্বাভাবিক ভাবেই, কবি স্বয়ং সেই বিশ্বসন্ধানী বিশ্ববীক্ষার রাস্তা থেকে বেরিয়ে প্রবেশ করেন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সন্ধিপর্যায়-সদৃশ পরিবর্তন আমরা লক্ষ করেছি আগেও ইউরোপীয় কবিতায়। ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে সৌন্দর্য, অস্তিত্ব ও আস্তিক্যবোধের ধারণার ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে গেল। অনেকটা এমনই পরিবর্তন ঘটেছিল প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপের কবিতায়, চিত্রকলায়, উপন্যাসে, গল্পে এবং দার্শনিক চিন্তাধারায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের লেখালেখিতেও সময়ের অস্থিরতায় প্রভাব পড়েছিল লেখালেখিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ের ঠান্ডা যুদ্ধের ইউরোপে তো এই পরিবর্তন রীতিমতো লক্ষণীয়।
অলোকরঞ্জনের কবিতায় গিলোটিনে আলপনার পরবর্তী পর্যায় থেকেই যে পরিবর্তন দেখা দিল, তা তাঁর নিজেরই ভাষায় দুর্বৃত্তায়নের (ভুবনায়নের) বিরোধী একটা সাংস্কৃতিক লড়াই। লঘু ছন্দ কীভাবে শাসন করতে পারে চিন্তাকে, তার উদাহরণ আমরা পেয়েছি তাঁর কবিতা থেকেই। পেয়েছি ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও আশাবাদের সময়চেতনা। ব্যক্তিগত জীবনের ভাঙাচোরার মধ্যে দাঁড়িয়ে, মৃত্যুকে নিবিড় ভাবে লক্ষ করতে করতে তিনি কামড়ে ধরছেন সময়কে। তাঁর কবিতায় ঢুকে পরছে উদ্বাস্তু সমস্যা। মানুষ যে ক্রমশ তার শিকড়চ্যুত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, তা তিনি এক সচেতন কবি হিসেবেই দেখছেন। গোটা পৃথিবীটা যখন হয়ে উঠছে শরণার্থী মানুষের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে চাওয়ার রাস্তা, সেখানে তিনি দেখছেন, মানুষ ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে তার মর্যাদা। নিজের আত্মার কাছে মানুষ নিজেই হয়ে উঠছে পরবাসী। কিছুটা পরজীবীও। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান কোথায়, তা তিনি জানেন না। এক চোরা অথচ স্পষ্ট রাজনৈতিক ভাষ্য উঠে আসছে তাঁর কবিতার মধ্যে। আবার পাশাপাশি, সেই রাজনৈতিক ভাষ্যেও থাকছে মৃত্যুচেতনার সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা। দুটিই তাঁর কবিতায় পাশাপাশি চলছে। যেমন থিও অ্যাঞ্জিওপোলসের বর্ডার ট্রিলজির ছবিগুলিতে মৃত্যু, দুঃখ, প্রেম, উদ্বাস্তু রাজনীতির মূল শিকড় থাকে পাশাপাশিই। অলোকরঞ্জনের গিলোটিনা আলপনার পরবর্তী পর্যায়ের কবিতায় এবং জীবনের শেষ দিকের কবিতাগুলির মধ্যে এই বহুস্বরের খোঁজ পাওয়া যায়। চরম অস্থিরতা এবং বিপন্ন অস্তিত্বের খোঁজ তো আমরা পাইই। কিন্তু পাশে, এটাও বুঝতে পারি, ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও অলোকদার চোখ খুঁজে চলেছে সুন্দরকে।
তবে তো একটা তর্ক আছে নিশ্চয়। কিন্তু এ তর্কটি কেমন? সে কি মুখোমুখি যুদ্ধ? সে কি নেতিকে মেনে নিয়ে অস্তির সঙ্গে যুদ্ধ না কি অস্তিকে মেনে নিয়ে নেতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব? এখানেই মনে হয় অলোকরঞ্জন আলাদা। তিনি তাঁর কবিতাতেই বলছেন, ভালোবেসে আগে মেনে নেওয়ার কথা। তর্ক পরে। কারণ তিনি এই তর্কের পরিণতিতে ধ্বংসস্তূপ চান না। তিনি চান যাতে তর্কে ঝরে উজ্জ্বল রৌদ্র, ঝরে মানবিকতা। তিনি অস্তিকে মেনে নিচ্ছেন, আর তার পরে তার সঙ্গে তর্কে নামছেন। এই তর্ক কিন্তু সংলাপ। এই তর্ক হল ডায়ালগ, কথাবার্তা। সব মিলিয়ে উঠে আসছে এক সন্দর্ভ ( ডিসকোর্স)। পরস্পর বিরোধী ভাবনাগুলো যেখানে একে অপরের সঙ্গে সংলাপে অবতীর্ণ হয়, এ কথা মেনে নিয়ে যে ‘ভালোবেসে’ মেনে নিতে হবে অস্তিকে। তার পর তার সঙ্গে তর্কে নামতে হবে। ভালোবেসে মেনে নেওয়াকে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন বেশি। কিন্তু তাই বলে, সেই মেনে নেওয়াকে প্রশ্নহীন ভেবে নিচ্ছেন না। অবশ্যই কূটতার্কিকরা বা একমাত্রিক তার্কিকরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন, বলবেন, এ তো ঠিক বাইনারি হল না। বাইনারিতে তো মহাজগতের কোনওকিছুই নেই। সত্য-এর বিপরীত তো মিথ্যা নয়। অ-সত্য। এখানে অ-সত্য বলা মানেই, সত্যকে একপ্রকার ভালোবেসে মেনে নেওয়াও। সত্য এবং অসত্যের যে তর্ক, তাতে নেতির অন্ধকার নেই, অস্তির উজ্জ্বল রৌদ্র আছে। অলোকরঞ্জনের এই বাইনারি বা ‘পক্ষ-বিপক্ষ’-হীন দার্শনিক অবস্থান তাঁকে আলাদা করে রেখেছে সকলের সঙ্গেই, এমনকি আধুনিকতাবাদীদের থেকেও। এই জায়গাতেই তিনি আধুনিকতাকে ছাড়িয়ে চলেছেন অধুনান্তিক দার্শনিকতার দিকে, যদিও তার মূল ভিত্তি অস্তি।
তবে কি তাঁর ঈশ্বরচেতনা রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচেতনার মতো নয় একেবারেই? রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক ব্রহ্মের দর্শন দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হলেও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর মেজাজে বরং একপ্রকার শচীশের মতো প্রতিমুহূর্তে সংশয়ের সঙ্গে বিশ্বাসের টানাপোড়েন চলত বলেই আমার পাঠক হিসেবে মনে হয়। যৌবনবাউলেও রয়েছে সেই টানাপোড়েন, আবার নিষিদ্ধ কোজাগরীতে সেই টানাপোড়েনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক গভীর তীক্ষ্ণ শাক্ত-অনুসন্ধান। যেন বা মনে হয়, প্রকৃতির রুদ্ররূপ অলোকরঞ্জনের কাব্যাদর্শের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। হপকিন্সের বা হুইটম্যানের অথবা তলস্তয়ের ভাবাদর্শের সঙ্গে কোনওমতেই এখানে অলোকরঞ্জনের ভাবাদর্শের সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর আস্তিক্যবোধ, তাঁর অন্যান্য ভাবনার মতোই প্রশ্নহীন আনুগত্য বা সন্দেহজনক সমর্পণ নয়। দু বছর আগে আমারই নেওয়া এক সাক্ষাৎকারের অংশ তুলে দিচ্ছি আবার-
প্রশ্ন- ‘প্রতিবার তরী কান্নায় শুরু হয়/ কান্নায় ডোবে জলে/ হাসিমুখে তবু কেন হে বিশ্বময়/ তোমার তরণী চলে?’ – বারবার মনে হয় আপনার আস্তিক্যবোধ প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই এক ভিন্ন পথের পথিক। যেখানে ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত অভিমান কান্না রাগ আবার ভালোবাসাও কত সহজে বলা হয়ে যায়…একে কি কথোপকথন বলা যায়?
অলোকরঞ্জন-আমি তো ঈশ্বরে বিশ্বাসকে কবিতার একটা জঙ্গম উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করি – একটা নির্মিতি হিসেবে ব্যবহার করি। তাতে প্রমাণ হবে না কিন্তু যে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। তুমি অগ্রজ হিসেবে আমার ওপর একটা বিশ্বাস রাখো। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে তোমার সঙ্গে আমার একটা চিন্ময় মতান্তর হতে পারবে না। সেই জায়গাতে আমি এসে গিয়েছি আসলে কুয়েত যুদ্ধের পর। আমি অনেক শরণার্থী কবিদের সঙ্গে বসবাস করেছি। এখনও করি। তাদের দেখে প্রশ্ন হয় তাহলে কি ঈশ্বর আছেন? থাকলে, কোথায় তিনি? এত অবিচার! তুমি লক্ষ্য করো এই যা ঘটছে এখন সারা জগৎ জুড়ে – এই দক্ষিণপন্থার উদগ্র উল্লাস এবং কত অকারণ মৃত্যু। এরপরে আমি ঈশ্বরকে গিয়ে, ধূপ না জ্বালিয়ে, যদি তাঁকে চ্যালেঞ্জ করি।
মরমীয়া ভাব তাঁর মধ্যে আজীবনের সম্পদ হিসেবে থাকলেও, তিনি বারবার সেই বাউল সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন অস্বীকারের চেতনাকে। যেন আজীবন ধরে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর এক প্রকার কথোপকথন চলেছে। এ প্রসঙ্গে রক্তাক্ত ঝরোখা এবং এবার চলো বিপ্রতীপে গ্রন্থদুটির কথা বলা যায়। ধুনুরি দিয়েছে টংকার বা আয়না যখন নিঃশ্বাস নেয়,- এই কাব্যগ্রন্থদুটিতে মনে হয় তাঁর সেই অটল বিশ্বাসে চিড় ধরেছে। সে কি খুঁজে পেল ঈশ্বরকণা এবং নিরীশ্বর পাখিদের উপাসনালয়ে কাব্যগ্রন্থদুটিতে তাঁর এক নতুন কাব্য ও আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসায় আমরা পেয়ে যাচ্ছি বলে মনে হয়। তবে, এরই মাঝে, গ্যেটের ‘ডিভান’ অনুবাদ করতে গিয়ে মরমিয়া-সুফি- দরবেশ এবং বাউলদের লোকায়ত ধারণাকে তিনি পুনরাবিষ্কার করেন। শুনে এলাম সত্যপীরের হাটে অলোকরঞ্জন এই চেতনাকেই আবার নতুন করে লেখেন।
অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক চেতনার প্রেক্ষিত থেকে বিচার করলেও, অলোকরঞ্জনের আধ্যাত্মিক চেতনা আরও সূক্ষ্ম এবং জটিলতর যে হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রিয়জনের মৃত্যু, ভুবনায়নের দুর্বৃত্তায়ন, একের পর এক মধ্যপ্রাচ্যের এবং পূর্ব ইউরোপের যুদ্ধ, শরণার্থী সমস্যা, সব মিলিয়ে অলোকরঞ্জন যত সময় এগিয়েছে, তত বেশি করে আধ্যাত্মিকতা এবং বিশ্বাসের মধ্যবর্তী এক সূক্ষ্ম অবস্থানে চলে গেছেন, যা, তাঁর বিশ্বাসকে সান্দ্র করে তুলেছে।
কিন্তু তিনি যে ঈশ্বরবিশ্বাস থেকে সরে এসেছেন, এমনটা নয়। কারণ তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস মহাজাগতিক। জাগতিক অসঙ্গতিগুলি সেই আধ্যাত্মিক মহত্বের ভিত টলিয়ে দেয়নি। একইসঙ্গে আধুনিক ও সনাতনের আলোকবর্তিকা হাতে তিনি অন্ধকারের মধ্যে নিজেই হয়ে উঠেছেন এক আলোকশিখা। আর, কে না জানে, প্রদীপ নিভে গেলেও, বাতির মোম ফুরিয়ে এলেও, সেই আলো, যা জ্বালিয়ে দিয়েছেন কেউ, তার মৃত্যু নেই। সে অনন্তকালের পথযাত্রী।


সমৃদ্ধ হলাম ❤
অনবদ্য। খুব ভাল লাগল পড়ে, জেনে
সুস্থ তর্কের পরিসর হারিয়েই যাচ্ছে… বিরোধের সঙ্গে একপ্রকার সখ্য না গড়ে উঠলে যে তার বিরোধিতা করাও যায়না, তা’ ভুলতে বসেছি আমরা। এই ধরণের ভাবনার আদানপ্রদন আমাদের শেখাবে নতুন করে।
অত্যন্ত মননশীল লেখা। অলোকরন্জনের মন ভালো ধরেছেন আপনি। তর্কের বা অলোকরন্জনের ভাষায় চিন্ময় মতান্তর আজকাল হয়না। বরং কুৎসা আর গালিগালাজ ই হয়।
কবি অলোকরঞ্জনের উপর মনন ঋদ্ধ আলোচনায় সমৃদ্ধ হলাম
আমার মন সাড়া দিল
সুন্দর আলোচনা
অলোকদা চ’লে গেলেন ব’লে নয়, অনেক আগে থেকেই তো আমাদের কথাবার্তার অন্তত ৩০ শতাংশ উনিই দখল ক’রে নিতেন। তোমাদের মধ্যে নিভৃতে কী আলোচনা হত, সে তো জানি না; ধ’রে নিচ্ছি সেই সব ভাবনাসূত্রের কিছু-কিছু এখানে জায়গা ক’রে নিয়েছে। তোমার বিচার যথাযথ, কারণ অলোকদার বিশ্বাসের জগৎ নিয়ে প্রশ্ন তোলার জায়গা নেই। তিনি কিসের ওপর ভরসা রাখতেন, তা, অন্তত,যাঁরা ততটা প্রগতিশীল নন, তাঁরা জানেন। প্রশ্ন হল ― সে-বিশ্বাস ধাক্কা খেয়েছিল কি না?এর উত্তর সহজ ― অবশ্যই, প্রবল রকমের ধাক্কা খেয়েছিল।
আমি ভাবি অন্য কথা, যা হয়তো অন্য কথাও নয়। অলোকরঞ্জন গোড়া থেকেই দু’রকম লেখা লিখছেন, একদিকে ‘তুলসীতলা’, অন্যদিকে ‘বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে’। রবীন্দ্রনাথেও এই দুই রকমের লেখা আছে। একটা কথা মাঝে-মাঝে শুনি; রবীন্দ্রনাথ না কি মধ্য বয়সে পৌঁছে তাঁর ধর্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে শুরু করেন। এগুলি তর্কের বিষয় নয় ব’লে হারজিতও নেই ; কিন্তু প্রশ্নগুলি রয়ে যায়। আমার ধারণা রবীন্দ্রনাথেও ভিন্ন দু’টি অভিমুখ ছিল এবং তা চল্লিশ বছর বয়স পৌঁছনোর আগেই দেখা যায়। ‘তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়’ ৩৯ বছর বয়সের রচনা । কী ক’রে এমনটি সম্ভব হল? খুঁজতে-খুঁজতে প্রভাতবাবুর ছোট্ট বইটাতে ১৩০৬-০৯/১৯০০ ( কবির বয়স ৩৯) এই এন্ট্রি পেয়েছিলাম।
‘কুষ্ঠিয়ার ব্যবসা লইয়া অত্যন্ত বিব্রত, ঋণদার বাড়িতেছে । অবশেষে তারকনাথ পালিত হইতে টাকা ধার করিয়া সর্বঋণ মুক্ত হন। মিঃ পালিতের ঋণ শোধ হয় ১৯১৭ সনে আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়া প্রাপ্ত অর্থ হইতে।’
ভাবো একবার! দাদার বন্ধুর কাছ থেকে নেওয়া ঋণের বোঝা ১৭ বছর ধ’রে বয়ে বেড়ালেন রবি ঠাকুর এবং অবশেষে পরিশোধ করলেন এমন এক ঋণদাতাকে যাঁর ওই টাকার প্রয়োজনই ছিল না। এটাই তো ধর্মবিশ্বাস! আর আমি কি করলাম? ‘তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়’ প’ড়ে আমি লিখে দিলাম সম্পূর্ণ ভুল কথা। ভুলে গেলাম যে, সংশয় /দ্বিধা/ দ্রোহ এসব বিশ্বাস থেকেই আসছে। আমার মনে হয় বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের জগৎ নিয়ে আলোচনা করার সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক আমরা ভুলে যাই, ভুলে যাই যে, বিশ্বাস আর অবিশ্বাস পরস্পরের পরিপূরক, এ ওকে সাপোর্ট করছে।
আলাদা কথা বলেছেন ঋত্বিক ঘটক মহাশয়। তিনি বলেছেন, ভাল সবসময়ে দুর্বল আর মন্দ সবসময়ে প্রভূত শক্তিশালী। গ্রেট মাদার গডেস অন্তর থেকে চান যে তাঁর সন্তানেরা সুখেশান্তিতে থাক, কিন্তু তিনি অসহায় । সাহেবরা যাকে হিউমান ট্র্যাজেডি বলেন, এটা সেই বস্তু ।
শুভেচ্ছা
ইতি ৫.৮.২৭
বিনীত গৌতম
এই বিষয়টি নিয়ে আরও ভাবছি। কথা হোক।
বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যে একটা ‘ভিসকাস’ অবস্থায় রয়েছি আমরা সকলেই।
চরম বিশ্বাসীরা সম্ভবত থেমে গেছেন।
অলোকরঞ্জনের কবিতায় বিশ্বাস- অবিশ্বাসের মধ্যযবর্তী যে অঞ্চলটি এখানে উন্মোচিত হল, তা আগে তাঁর সম্পর্কে কারও আলোচনায় পড়িনি। অলোকরঞ্জনের মতো কবি তো বারবারইনিজেকে পেরিয়ে যাবেন। কখনও বাইরে থেকে নিজেকে দেখবেন। এই প্রবন্ধে স্পষ্ট কবির কাব্যিক নিয়তিই ছিল নিজের বিশ্বাসের bull’s eye-তে সংশয়ের তীর নিক্ষেপ।
ভালো লেখা ।
যতবার পড়ি আপনাকে নতুন নতুন ভাবে সমৃদ্ধ হই। আসলে চিন্তার অচেনা গলি পথ গুলো খুলে যায় মনে হয় যেখানে একা পৌঁছান কিছুটা কষ্টসাধ্য ছিল।