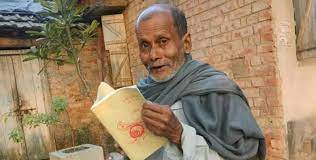
মহাকবিতার কাপালিক
বেবী সাউ
“আমি ভেবেছি আমাকে ঘরের দেওয়ালে বিভিন্নভাবে
স্থাপন করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করব।” ( চিন্তন/ শম্ভু রক্ষিত)
প্রকৃত কবি বলতে আমাদের কাছে হয়তো এক রূপকথার মতো ভাবনা কাজ করে। কিন্তু বাস্তবের দিকে তাকিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেই কবির দেখা পাই না। যিনি তাঁর কাব্যভাষাতেই শুধু না, জীবনচর্যাতেও কবি। আমাদের কাছে হয়তো জীবনচর্যা বলতেও ঠিক কী বলতে চাওয়া হয়, তা পরিষ্কার নয়। কারণ কবিজীবন তো ঠিক নিয়ম করে কবিতা পড়তে যাওয়া, সেজেগুজে সাংস্কৃতিক হলমার্ক কাঁধে চাপিয়ে সংস্কৃতি করা নয়। তার জন্য এক বিশেষ প্রজাতির উদ্ভব চিরকাল হয়, যাঁরা কাব্যজীবন অপেক্ষা কবির বাহ্যিক জীবনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন্ন। বস্তুত কবির জীবন এই সাংস্কৃতিক কুরুক্ষেত্রের যে ঝাঁ চকচকে আড়ম্বরের জীবন, তা নয়। তাঁর জীবন সবকিছুকে গ্রহণ করে আমোদপ্রমোদ স্তুতি ও ক্ষমতায় মেতে ওঠার জীবন নয়। তাই যদি হতে হয়, তবে তো সিনেমা আর্টিস্ট হলেই হয়, অথবা কোনও বিশেষ প্রশাসনিক পদে চাকরি নিলেও হয়। কেন সবকিছু ছেড়ে তিনি অক্ষরের কাছে হাজির হন? আমার মনে পড়ছে এক বিশেষ ঘটনার কথা। এক বিশেষ কবি, তিনি সারাদিন কাটিয়ে দিচ্ছেন কীভাবে কোথায় কবিতাপাঠ করা যায়, তাকে কেন কেউ ডাকল না, কাকে কোথায় ডাকা হবে, কার সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে এ নিয়ে। তো তিনি পড়ছেন কখন, ভাবছেন কখন, লিখছেন কখন? আশ্চর্যের বিষয়, তিনিই বললেন, আমাকে চার পাঁচটি কবিতা দিতে হবে। বর্ষামঙ্গলের উপর। তো, লিখে ফেলি, কেমন? লেখা হয়ে গেল। ছাপা হয়ে গেল। লাইক হাজার হাজার। মন্তব্য লক্ষ লক্ষ। পরের দিন মানুষ ভুলে গেল সে কবিতা। আমি বুঝলাম্, কবি অনেকপ্রকারের। প্রশ্ন আসে, এঁরা তো ভাল জনসংযোগ অফিসার হতে পারতেন, কিংবা হতে পারতেন ভাল আই এ এস, বা ভাল বিজনেসম্যান। কেন এঁরা কবি হতে গেলেন? হ্যাঁ, হতে গেলেন শব্দটি ব্যবহার করলাম, কারণ এঁরা কবি হয়েছেন। এঁরা কবি হয়ে জন্ম নেননি।
আমার এক অগ্রজ কবিবন্ধুকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন, কবি অনেকটা বাঘের মতো। একা থাকে। দাঁত মাজে না। চান কম করে। তিনি বলেছিলেন, কবিকে ছাঁচের মধ্যে ফেলতে যাস না। আজ দেখলি চান করে না। তো কাল দেখলি ঝরনার তলায় লিরিল সাবানের বিজ্ঞাপন হয়ে গেছে। আবার পরের দিন দেখলি জল দেখলেই আতঙ্ক। মোদ্দা কথাটি ছিল, কবিকে ছাঁচের মধ্যে ফেললে সেই ছাঁচটাই বিপন্ন হতে বাধ্য। প্রকৃত কবি আসলে এমন একধরনের বৈচিত্র তৈরি করেন নিজেকে নিয়েই, তাঁর কাব্যভাষা এবং জীবনচর্যা দিয়ে, যে তাঁর সম্পর্কে সম্ভ্রম চলে আসে, তাঁকে এক বিপজ্জনক আগুনের শিখা মনে হয়। ‘না’ শব্দটি খুব ভীষণভাবেই প্রযোজ্য হয়ে যায় তাঁর সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি পড়া একটি লেখার একটি অংশ তুলে না ধরলে অন্যায় হবে। “সবে চায়ে চুমুক দিয়েছে সে। আমি বলি, খুব নিচু গলায় সন্তর্পণে তাকে বলি – “এখন তো সরকার অনেক কবি শিল্পী আর গায়কদের একটা মাসিক ভাতা সাম্মানিক অনুদান হিসেবে দেয়, তা তুমি তো সঙ্গত কারণেই তা পেতে পারো। তুমি কি সরকারের কাছে একটা আবেদন করবে? আমি জানি আমার কোনও বন্ধু তা করেছেন। আর হয়তো তিনি তা পেয়েও যাবেন। আর তিনি পেলে তুমি তো অবশ্যই পাবে। তোমাকে শুধু একটা আবেদন করতে হবে। আর আমি সে আবেদন নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেব।”
প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, আমি এই সরকারের কেউ নই। কী ভাবে এসব পথে যাতায়াত করতে হয়, তাও জানা নেই আমার। কিন্তু ওই সময় কোনো দৈববলে প্রভূত এক ক্ষমতাবান কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল আমার। কথাপ্রসঙ্গে শম্ভুর কথা তাকে সামান্য বলেও রেখেছি। সেই ভরসায় আমি আজ কথা বলছি শম্ভুর সঙ্গে। কিন্তু আমার কথা শেষ হবার আগেই খুব সোজাসুজি শম্ভু বলল – “না, করব না।” (দূরের বন্ধু, দীপক রায়)
এই অস্বীকারের ক্ষমতাই একজনকে কবিকে স্বতন্ত্র ভাবনার অধিকারী করে তোলে। প্লেটোর কাছ থেকে আমরা তো শিখেছিলাম কবি সমস্ত ক্ষমতাকাঠামোর বাইরে থাকেন। কিন্তু তার উল্টোটাই যেন আমাদের চোখে পড়ে। শম্ভু রক্ষিত তাঁর আজীবনের কাব্যকৃতি, কবিতাযাপন এবং জীবনচর্যাতে ক্ষমতাকাঠামোর বৃত্তের বাইরে, চেনা ছকের বাইরে ভাষা এবং ভাবনার মধ্যে এমন এক ধূসর অঞ্চল গড়ে তুললেন, যার ভিতরে ঢুকে পড়াটাই পাঠকের কাছে এক অভিযাত্রা । শম্ভু রক্ষিতের কবিতায় এই অস্বীকারের জীবনচর্যা ছাপ ফেলেছিল তো বটেই। বরং বলা যায়, শম্ভু রক্ষিতের কাব্যসাধনার অঙ্গ ছিল এই জীবনচর্যা। জীবন এবং কাব্যকে এক সুতোয় বেঁধে ফেলা খুব সহজ কাজ নয়। খুব কম কবিই করতে পারেন। কারণ জীবন কোথাও কোথাও অনেক জায়গাতেই আমাদের তথাকথিত সামাজিক ভারসাম্য দাবি করে। কিন্তু শিল্প দাবি করে সেই ভারসাম্যকে ছুঁড়ে ফেলতে।
“যারা আমাকে ডিগডিগে
আমার রুহকে যুদ্ধের হিরো
আমার ঈশ্বরকে অনিষ্টজনক
আমার কবিতাকে
চাকচিক্যময় আভিজাত্য বা বিক্ষিপ্ত প্রলাপ মনে করেআহ ভাইরে
তারা বাণিজ্যের অযথার্থ ক্ষমতা দিয়ে
তাদের নাক মুখ কান দখল করে
এই শক্তিশালী প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের
অস্তিত্ব রক্ষা করুকযারা বালি ফুঁড়ে
আমাকে বাল্যপাঠ শেখাচ্ছে
আহ ভাইরে
তারা মেকি সুন্দরের মিথ্যে সীমারেখা প্রত্যাখ্যান করে
অন্তত্ব একটা ছোটখাটো দেবদূতের সন্ধান করুকঅকেজো জ্যুকবক্সে স্থির ডিস্ক
জীবনের আর ভাঙা ইঁটের
অশুভ যুদ্ধপরা যন্ত্রনায় আন্তর্জাতিক কোরাস
আহ ভাইরেকবরখানা আর টাউনশিপের সুড়ঙ্গের মধ্যে গুঞ্জন করা
আস্তাবলের ধূর্ত পিটপিটে মায়া
মধ্যে মধ্যে ফ্যাঁকড়া
আহ ভাইরেকাঁধে অগ্নিবর্ণের ক্যামেরা
হাতে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট ট্রানজিস্টর
অন্য সম্রাটের দায় যাতে মেটে
মাংস ভেদ করে সচল ফ্রেস্কোর মত
এইসব রেডিয়ো-টিভি-অ্যাকটিভ যুবশক্তি
মুক্তিবাদ এবং জাঁকজমক খুঁড়ে নৈশস্তব্ধতা
আহ ভাইরে
(মুক্তিবাদ, শম্ভু রক্ষিত)
এই কবিতাটি সম্পূর্ণ তুলে দেওয়ার কারণ কবিতাটিকে খণ্ড করে কিছু বলার ক্ষমতা আমার অন্তত নেই। মুক্তিবাদ কবিতাটির মধ্যে কবি শম্ভু রক্ষিতের আশ্চর্য কাব্যকৃতির একটা উদাহরণ পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে ন্যাকা ন্যাকা আঁকাবাঁকা ভাসাভাসা লিরিকাল কবিতার বিপরীতে বাংলা কবিতার আশ্চর্য শক্তিকে কী অবলীলায় কবি শম্ভু রক্ষিত ধারণ করেছিলেন তাঁর কবিতায়। এই শক্তির মধ্যে কি সম্পূর্ণই ছিল অমৃত? বিষ কি ছিল না? বিষ তো অবশ্যই ছিল। আর ছিল একটি ঝুঁকিহীন বাকপ্রতিমা। এই ঝুঁকিহীন প্রকাশভঙ্গির জন্য দরকার হয় একজন কবির নিজের অস্তিত্ব এবং ভাবনাচিন্তার জগতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। তাঁকে নিয়ে যে অজস্ব মিথ, তার কোনটাই আমার পরিচিত নয়, কারণ আমি ব্যক্তিগত ভাবে বাংলা কবিতার ভূগোল থেকেই অনেক দূরে থাকি। কিন্তু বাংলা কবিতার থেকে যেহেতু দূরে থাকি না, তাই শম্ভু রক্ষিতের কবিতা আমার কাছে চিরকালই মনে হত দেশ-কাল-সীমাহীন। তাঁর বয়স বুঝতে পারতাম না। তাঁর প্রিয় ধ্বনির জন্য কান্না কাব্যগ্রন্থটি পড়ার পরে কখনও মনে হয়নি এই গ্রন্থটি সাতের দশকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত। মনে হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থটি এখন প্রকাশিত। একজন কবিই পারেন সময়কে এভাবে নিজের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলতে। তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে পাঠক যেন তাঁকে তাঁর সময়ের কষ্ঠিপাথরে শুধুই বিচার করতে না পারেন। কবি শম্ভু রক্ষিত চিরকাল তাঁর কাব্যভাষার স্বাতন্ত্রের মাধ্যমে সময়ের এই প্রাচীরকে অতিক্রম করে যেতেন। হয়তো এখনও এমন অনেক কবিতাই রয়েছে, যেগুলি ঠিক এ সময়ে আবিষ্কার করাও হয়নি। হয়তো সেই কবিতাগুলি আবিষ্কৃত হবে বা সঠিক ভাবে সেই কবিতাগুলির পাঠ সম্ভব আজ থেকে আরও একশো বছর পরে। কবি শম্ভু রক্ষিতকে চিরকাল বাংলা কবিতার অভিজাত কবিসমাজ একটু হালকা নজরে দেখে এল সম্ভবত তিনি প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ ছিলেন বলে এবং তাঁর কাব্যিক স্পর্ধায় তিনি অনন্য ছিলেন বলেই। কারণ আগুন নিয়ে খুব কেউ খেলা করতে চায় না। তাতে হাত পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। কে আর যেচে নিজের হাত পোড়াতে চায় এই অবেলায়? তার চেয়ে সুখে শান্তিতে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়তে থাকাই ভাল। ঠিক এই জায়গাতেই মৌচাকে ঢিল মারেন শম্ভু রক্ষিত। তিনি ছিলেন বাংলা কবিতার এক অস্বস্তিজনক আউটসাইডার। আউটসাইডার হয়েও, অস্বস্তির কাঁটা হয়েও, তিনি কিন্তু নিজেকে আলাদা, সংগোপনে রেখে দেননি। ফলে, বাংলা কবিতার যে আবহমান ধারা তা শম্ভু রক্ষিতকে গিলতেও পারেনি, ওগরাতেও পারেনি।
“আমার অস্তিত্বের কেন একটা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য আছে-আমি জানি না
আমার তুষারশুভ্র হাত আমাকে এগিয়ে দিয়ে
নিজেকে ফুটকি রঙের সাহায্যে প্রকাশ করে
আমি থাকি তার যন্ত্রপাতির ও তার রত্নভরা শরীরের টূকরো টাকরার মাঝে
নির্দিষ্ট আমি, অদ্বিতীয় শান্ত, মানুষকে বোঝাই দর্শনীয়ভাবে উর্ধ্বে যেতে ও
নীলরঙের সন্ধ্যায় ছদ্মবেশে ঘুরি এক জাজ্জ্বল্যমান মুহূর্তকে প্রতিষ্ঠা
করার জন্যে আমার ঘৃষ্ট স্বরঃ আমি নগরের কোথা থেকে আসছি?
আমাকে কি ঈশ্বরের নিঃসঙ্গতার উপায়সমূহ উপহার দেওয়া যায়?”
( সাক্ষ্য, শম্ভু রক্ষিত)
ভাষার পাশাপাশি শম্ভু রক্ষিতের ব্যক্তিগত দর্শনের কথাও বলতে হবে। আসলে এই ব্যক্তিগত দর্শনবোধ ছাড়া শম্ভু রক্ষিতের কবিতা আলোচনা করাই যায় না। এই যে তিনি লিখলেন ‘আমার তুষারশুভ্র হাত আমাকে এগিয়ে দিয়ে/ নিজেকে ফুটকি রঙের সাহায্যে প্রকাশ করে’, এখানেই কবি শম্ভু রক্ষিতের আজীবনের জীবনদর্শন যেন লুকিয়ে আছে। মৃত্যুর সময়েও যে কবি একাকী থেকে যান, মৃত্যুর পরেও যে কবি এক প্রকৃত কবির মতোই চিরকালের মতো শেষযাত্রায় চলে যান, তিনি আজীবন সাধনা করে গেছেন বৃহৎকে, মহাকাশকে ভাষার মধ্যে দিয়ে ধরতে। এই বৃহতের সাধনাই কবি শম্ভু রক্ষিতকে অন্যান্য হাংরি প্রজন্মের কবিদের চেয়ে পৃথক করে রাখে। কারণ তাঁর কবিতায় চিৎকার কম, আত্মানুসন্ধান অনেক বেশি। যেন বোঝা যায়, তাঁর এই একাকী যাপনের উদাসীন স্পর্ধার ভিতরে রয়েছে আসলে পার্থব সফল জীবনের প্রতি এক চরম নিস্পৃহতা। এই যে লিখলেন কবি, ‘ আমাকে কি ঈশ্বরের নিঃসঙ্গতার উপায়সমূহ উপহার দেওয়্যা যায়?’ , এই লাইনটির মধ্যেই কি লুকিয়ে নেই কবি শম্ভু রক্ষিতের জীবনের সাধনা? জীবনের এই নিভৃত সংলাপই তাঁকে করে তুলেছে তাঁর নিজস্ব পারসোনা বা ব্যক্তিত্বের লেখক। সব কবি এই ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন না। হতে পারেন না। আজীবন কবিতা লিখেও এই ব্যক্তিত্ব তাঁর বা তাঁদের কাছে অধরা থাকে, কারণ তাঁদের যেটি থাকে না, তা হল, কবিতার মাধ্যমে জীবনের প্রতি, সময়ের প্রতি এই আত্মানুসন্ধানের আকুতি।
‘প্রিয় ধ্বনির জন্য কান্না’ বাংলা কবিতার জগতে এক চিরকালীন বিস্ময়। কারণ এই কাব্যগ্রন্থ বাংলা কবিতাকে সেই নিশ্চেতনার কাছে নিয়ে যায়, যার সাধনা এক সময়ে জীবনানন্দ করেছেন। সেই নিশ্চেতনার জগতের মধ্যে এক খ্যাপাটে সাধক হয়ে আজীবন থেকে যাওয়ার ক্ষমতা থাকে যিনি প্রকৃত সাধক, তাঁরই। কারণ, কবিতা এবং নিশ্চেতনার ইশারা এমন ভাবেই তাঁকে ঘিরে থাকে, যে, তাঁর পক্ষে সেই জগতের আলো কিংবা ধূসর অঞ্চল থেকে বেরোন সম্ভব হয় না। আসলে, প্রত্যেক কবিই হলেন সেই অভিমন্যুর মতো। জেনে বুঝেও প্রবেশ করেন চক্রব্যুহে। প্রবেশ না করলে তো তিনি স্পর্শই করতে পারবেন না বাক্য ও মনের অতীত সেই ভাবনার স্তরকে। কবি শম্ভু রক্ষিতের এই জীবনচর্যার পাশাপাশি আরও একধরনের সক্ষমতার জায়গাটি হল, জীবনচর্যাকে, জীবনদর্শনকে, ভাবনার সর্বোচ্চ সীমাকে তিনি ভাষার বুননে বেঁধে দিতেন। ফলে, তাঁর প্রতিটি কবিতাই হয়ে উঠত মহাকাব্যিক।
জীবনানন্দ যে মহাকাব্যিক মহাকবিতার কথা বলে এসেছেন তাঁর কবিতার কথা-য়, শম্ভু রক্ষিত আপাতত, সেই মহাকবিতার সাধনার শেষ পথিক।


ভাল লেখা, বেবী। শিরোনামে চমকে উঠলাম, সত্যিই তাই।