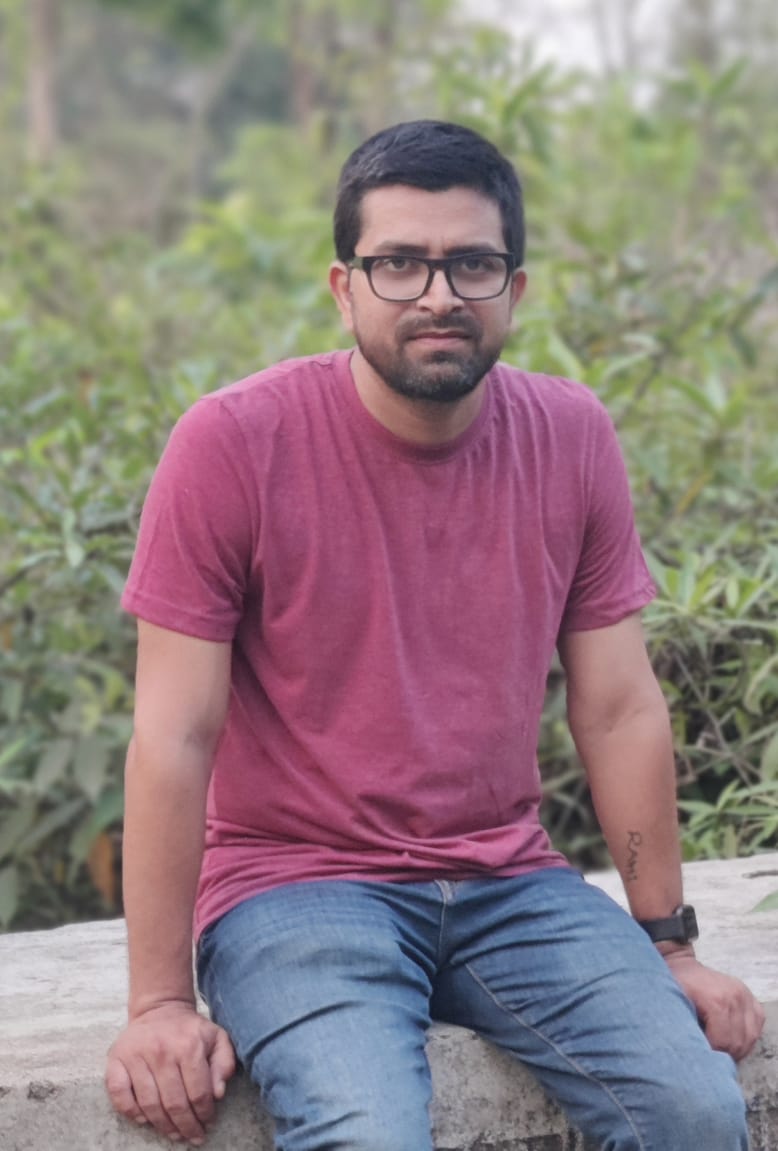
……হিসাব মেলাতে মন মোর নহে রাজি
রাহী ডুমরচীর
আমি কাবুলিওয়ালাকে চিনতাম। কিন্তু তখন রবীন্দ্রনাথকে চিনতাম না। স্কুলের বইয়ের বাইরে মিনিকেও অনেকটা নিজের মতোই মনে হয়েছিল। তার মনে জেগে থাকা প্রশ্নগুলোকেও নিজের বলে মনে হত। তার কাবুলিওয়ালার প্রতি ভয় এবং পরে তার সাথে বন্ধুত্ব করাটাও যেন আমাদের জীবনের একটা অংশ হয়ে উঠেছিল। আমাদের পাহাড়ি গ্রামে কোনো কাবুলিওয়ালা আসেনি, তবে তাকে দেখার ও তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা অবশ্যই জন্মে নিয়েছিল। পরে কোনো একদিন স্কুলের একজন মাস্টারমশায় জানান, ১৫ আগস্ট ও ২৬ জানুয়ারিতে যে জাতীয় সঙ্গীত আমরা গাই, সেটাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। তিনি এটাও বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ খুব দূরেরও নয়, বরং ওনার বাড়ি আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিম বাংলায়। আমার গ্রাম থেকে বাংলার সীমান্ত ছিল মাত্র কুড়ি-পঁচিশ কিলোমিটার। আমাদের গ্রামের আশে-পাশে কিছু বাঙালিরাও থাকতেন। কোনো প্রয়োজনে বা অসুখ হলে গ্রামবাসীরা বাংলার দিকেই ছুটত। তিনি বাংলার লোক, এটা জেনে ছোটবেলা-তেই ওনাকে খুব আপন মনে হয়েছিল।
প্রাথমিক শিক্ষার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাকে আমার পাহাড়ি গ্রামের বাইরে একটা বোর্ডিং স্কুলে পড়তে যেতে হয়। সেখানে হিন্দি ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে পড়ানো হত। বাংলাভাষা শিখতে গিয়ে প্রথম-প্রথমই আমাদের পড়তে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে’ কবিতাটি। এত কঠিন শব্দ, তার ওপর জন্মের সার্থকতা নিয়ে শিশু মনে এত গভীর জ্ঞান না থাকার ফলে, কবিতাটি আমার খুব কঠিন মনে হয়েছিল। আমার কিশোরমন তখনই বুঝতে পেরেছিল, রবীন্দ্রনাথ ভালো গল্প লেখেন কিন্তু তাঁর কবিতা খুবই কঠিন হয়। স্কুলে অনুষ্ঠিত কুইজ প্রতিযোগিতার কারণে আমরা আরও জানতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘গীতাঞ্জলি’ বইটির জন্য সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। এবং এটি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় পুরস্কার। পরে যখন আমি ‘বিশ্বভারতী’–তে পড়াশোনার জন্য ভর্তি হই শান্তিনিকেতনে সেই নোবেল পুরস্কারটি নিজের চোখে দেখেছিলাম এবং দুর্ভাগ্যবশত যখন সেটি চুরি হয়, তখন আমি ছাত্র হিসেবে সেখানেই পড়তাম। স্কুলে থাকা কালীন একদিন আমি স্কুলের লাইব্রেরি থেকে ‘গীতাঞ্জলি’ তুলে এনেছিলাম, সেই গানগুলো আবার আমার কিশোর বিশ্বাসকে আরও একবার দৃঢ় করেছিল যে রবীন্দ্রনাথ সত্যি একজন কঠিন কবি।
পরে শান্তিনিকেতন থেকে স্নাতক করার সময় তাঁর কবিতা, গান পড়ার এবং শোনার সুযোগ পাই। এখানে উল্লেখ করা জরুরী যে, যখন আমি শান্তিনিকেতনে পৌঁছাই, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে শোনা, একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। সেই পাঠ আমার জন্য রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি এক নতুন দ্বার খুলে দিয়েছিল। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন তাঁর উপন্যাস পড়ার এবং তাঁর নাটক দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। ধীরে-ধীরে তাঁর গানগুলো আমার ‘ভেতরে-বাইরে’ প্রতিধ্বনিত হতে আরম্ভ করলো। তাঁর গানের কথাগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার ঠোঁটে ভেসে আসত, ‘মাঝে মাঝে তবে দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না’। বলা যায় আমার জীবনে শান্তিনিকেতন, ভালোবাসা এবং রবীন্দ্রনাথ তিনটেই ধীরে-ধীরে রূপ নিতে শুরু করে এবং আমি এই ‘জাদু’ থেকে কখনোই বেরোতে পারিনি।
শান্তিনিকেতন ছিল কবির ‘বিশ্ব-নীড়’-এর স্বপ্নের বাস্তব প্রতীক। যদিও পরে আমি নিমাই সাধন বসুর ‘ভগ্ন নীড় শান্তিনিকেতন’ও পড়েছিলাম, কিন্তু শান্তিনিকেতনের হাওয়ায় সেই মনীষীর উপস্থিতি সহজে অনুভব করতে পারতাম। শান্তিনিকেতনের বাতাসে গন্ধের মতো থাকা, লাল মাটির নিচে স্রোতের মতো প্রবাহিত রবীন্দ্রনাথের বিচারগুলি কখনোই বিলীন হয়নি। কখনও পুরনো হতে পারে না। এটা সত্যি যে, কোপাই নদীর মতোই তার প্রবাহও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আমি সান্তাল (সাঁওতাল) অধ্যুষিত একটি পাহাড়ি গ্রাম থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম। এই কারণেই দিন-দিন দুর্বল হয়ে পড়া কোপাই নদী এবং শান্তিনিকেতনে সান্তালদের চোখে না পড়ার মতো উপস্থিতি আমাকে দুঃখিত করত। রামকিঙ্কর বেইজের তৈরি সান্তাল দম্পতির মূর্তিটি সবাই দেখতে পেতেন, দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসে প্রশংসা করতেন, কিন্তু অদ্ভুতভাবে নিজের চোখের সামনে উপস্থিত সান্তাল লোকজন দেখতে পেতেন না তারা । যেখানে তারা বছরের পর বছর বসবাস করে আসছিল, সেখানেই তারা এখন প্রান্তিক হয়ে যাচ্ছিল ধীরেধীরে। নিজের লাল মাটির দেশেই লালমাটি বাসীরা হয়ে উঠেছিল গুরুত্বহীন।অপাংক্তেয়। আম্রকুঞ্জে পাতা কুড়োতে সহজেই দেখতে পেতাম ওদের বা দিন-দিন সোনাঝুরির হাটে প্রদর্শনীতে পরিণত হতেও দেখছিলাম। এটা ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য খুবই বেদনাদায়ক ছিল।
বুঝতে পেরে ছিলাম, যে শান্তিনিকেতনের স্বপ্ন কবি দেখেছিলেন এখন সেই শান্তিনিকেতন নয়। তাসত্ত্বেও এটাও ভেতর থেকে অনুভব করেছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ও তাঁর সাহিত্য আপনাকে মানুষ হিসেবে মহৎ হতে অনুপ্রাণিত করে। জাতি-রাষ্ট্রের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে, জাতি-ধর্মের বাধা প্রত্যাখ্যান করে, মানুষকে বিশ্বমানব হতে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর কাছে জাতি মানে এই দেশের মানুষ (লোকজন), তাই তিনি জাতীয় সংগীতে তাদের প্রশংসা করেছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে একটি জাতি কেবল মানুষের উন্নতির সঙ্গেই উন্নতি করতে পারে। তাই ওনার কাছে মানুষ হওয়ার অর্থ ছিল ‘ঘরে’ এবং ‘বাইরে’ উভয়ের জন্যই উপযুক্ত হওয়া ।
শেষে শুধু আরেকটি কথা, শান্তিনিকেতন থেকে যাওয়ার সময় আশ্চর্য ভাবে প্রথম বার বোলপুর স্টেশনে ওই লেখাটার ওপরে চোখ পড়েছিল। এখন যখনই কিছু দিন থাকার পর কোথাও আমাকে যেতে হয়, সেই স্টেশনের গায়ে লেখা তাঁর কাব্যপংক্তিগুলি আমার চারপাশে বাজতে শুরু করে দেয়-
“আমার যাবার সময় হল আমায় কেন রাখিস ধরে।
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে বাঁধিস নে আর মায়াডোরে॥
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি, ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি–
নাম ধরে আর ডাকিস নে ভাই, যেতে হবে ত্বরা করে ॥”
রাহী ডুমরচীর:জন্ম ২৪ এপ্রিল ১৯৮৬। ডুমারচির গ্রাম, সাঁওতাল পরগনা জেলায় ঝাড়খণ্ডে। তিনি মূলত হিন্দি ভাষায় লেখেন। আদিবাসী দর্শনে তাঁর গভীর বিশ্বাস। বাংলা ভাষায় এটি তাঁর প্রথম লেখা।

