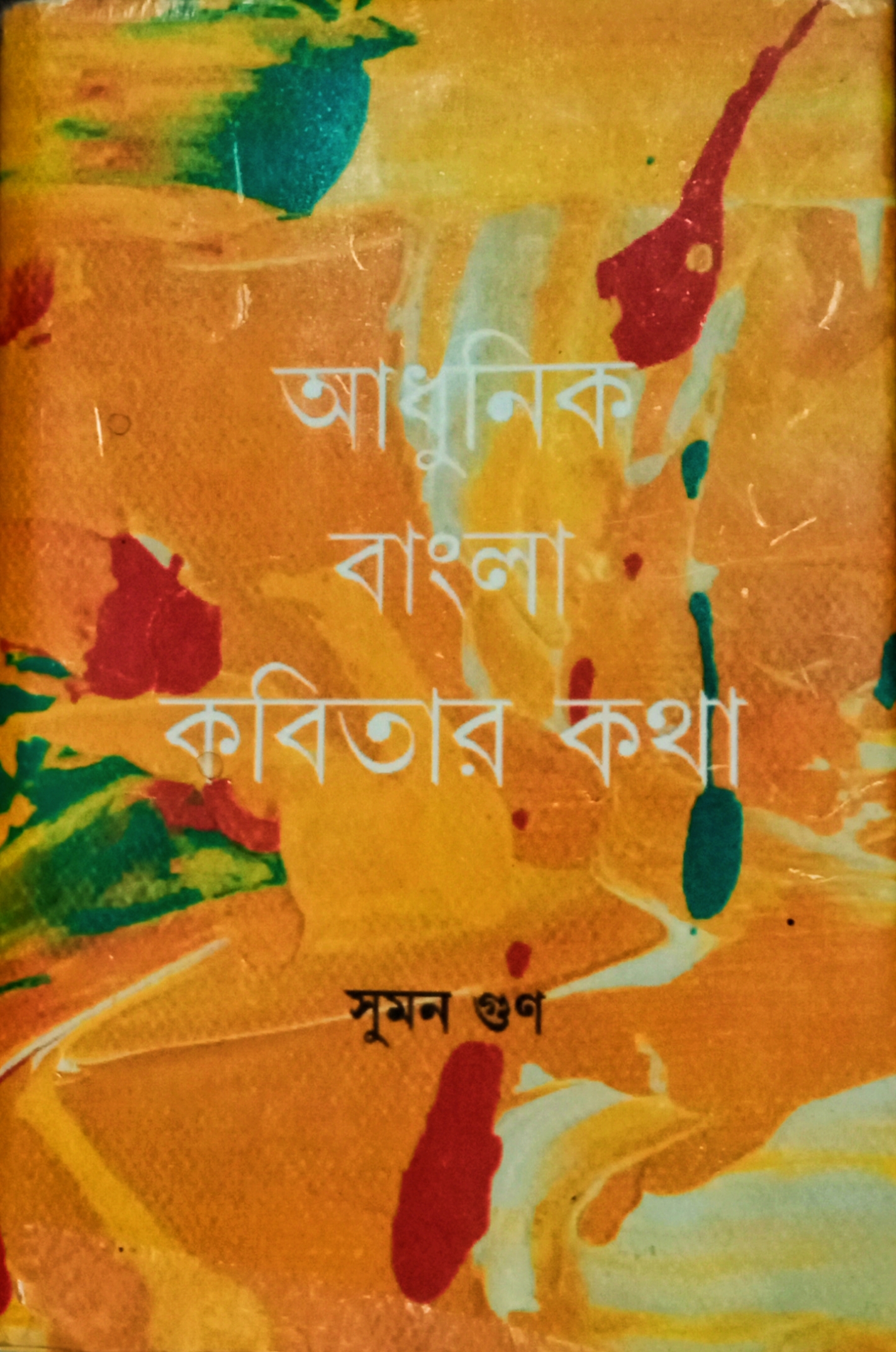
আধুনিক বাংলা কবিতার কথা
সব্যসাচী মজুমদার
আধুনিক বাংলা কবিতার কথা: সুমন গুণ: প্রচ্ছদ-আবীর মুখোপাধ্যায়:দাম-৪৭৫টাকা: গাঙচিল
বাংলা প্রবন্ধ চর্চার ক্ষেত্রে একটি অভিযোগ বেশ বৈধ হয়ে গেছে,বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ খুব বেশি ও গভীরে চর্চিত নয়। অবশ্যই এ অভিযোগের বিরুদ্ধে আমরা অনায়াসে এমন কিছু উদাহরণ সহজে উপস্থাপন করতে পারি,যাতে নস্যাৎ করতে সময় লাগে না আরোপিত অভিযোগটিকে। কিন্তু,একথাও সত্য, সাহিত্য আলোচনার প্রেক্ষিতে যদি ভাবি,সহৃদয় পাঠকের পরিশুদ্ধিময় হৃদয়বত্তা কতটা ক্রিয়াশীল হয়েছে, আবহমানের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রেক্ষিতে-সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠে যায়।
বঙ্কিম পরবর্তী প্রহরে যখন রবীন্দ্রনাথ হৃদয়বত্তার আধিক্যে গদ্য চর্চায় অবতীর্ণ,বুদ্ধদেব বসু কিন্তু মল্লিনাথের মতো অর্থে প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁকে স্বীকার করতে চাইছেন না।
কেন এই অস্বীকরণ!বু.ব.কে অনুসরণ করলেই তারও একটা যুক্তি পাওয়া যায়। প্রবন্ধ রচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ গীতিকবির অনুভবকেই অধিক প্রাধান্য দিয়ে বসছেন।অথচ প্রবন্ধ দাবি করে যুক্তি -প্রতিযুক্তি ও বিনির্মীত যুক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্বমূলক অবস্থান।হয়তো বু.ব. রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ভঙ্গিমায় খুঁজে পেয়েছিলেন,এমন কিছু চিহ্ন,যার মধ্যে ব্যক্তির ধারণাই প্রাধান্য পেয়েছে,যুক্তি নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠতে পারেনি।
এই সূত্র ধরে যদি আমরা বাংলা ভাষার প্রবন্ধ সাহিত্যে অভিনিবেশ করি, অবশ্যই এটুকু দাবি করতেই পারি,বাংলা প্রবন্ধের প্রধানতঃ দুটো ধারা।একটা মন্ময় আরেকটি তন্ময়।এমনকি স্বয়ং বু.ব.ও কী তাঁর প্রবন্ধ রচনা কর্মে মন্ময়তার উপস্থিতিকে অস্বীকার করতে পারেন!
এবার এই প্রসঙ্গের পাশাপাশি যদি আরেকটি প্রসঙ্গের উপস্থাপনা রাখি, খুব বেশি অসঙ্গত বোধ হয় হবে না। সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে তন্ময় মেধার প্রাবল্য কী বোধ মোক্ষণে ঈষৎ বাধার সৃষ্টি করে না!মন্ময় রসগ্রাহীতা ও সহৃদয়হৃদয়বত্তার আধিক্য যে প্রবন্ধকে আরও সপ্রতিভ ও অভিনব করে তোলে এ কথা কী স্বয়ং বু.ব.,আবু সৈয়দ আইয়ুব, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত,বিষ্ণু দে, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়,শঙ্খ ঘোষ, জয় গোস্বামীর প্রবন্ধগুলি প্রমাণ করে দেয় না!
এই রমনীয় প্রবন্ধই বাংলা চিন্তা চর্চার অধিক জুড়ে আছে এবং এই অভিনবত্ব হয়তো বাংলা ভাষারই অর্জন।তা নইলে কেন উত্তর সত্তর দশকে,যখন আরবান ভাবনা বিশদ হচ্ছে বাংলায়,বুদ্ধদেব সুচিত রসময় অথচ পিনদ্ধ, সুখপাঠ্য অথচ অন্তর্ঘাতময় প্রবন্ধ রচনার ধারাটি আরও শৌর্য হয়ে কেন ফিরে আসবে!সুমন গুণ প্রণীত ‘আধুনিক বাংলা কবিতার কথা’ বইটিকে যদি এই আলোচনার প্রসঙ্গে নিয়ে আসি,এই আলোচকের বক্তব্য উদাহরণ পায়।
রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসুর পারস্পরিক কাব্যিক সম্পর্ককে সূচনায় রেখে গ্রন্থটি বিবিধ প্রসঙ্গে মীমাংসা ভাবতে প্রচেষ্টা করেছে।’কবিতা সংকলনের কুহক ‘থেকে এসেছে সমর সেন থেকে,আল মাহমুদ প্রসঙ্গ।প্রবেশ করেছেন চল্লিশের কবিতায়,আলোকে নির্জন অন্তরীপ ছুঁয়ে পৌঁছে গিয়েছেন শঙ্খের ক্ষতচিহ্নে।মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কবিতার অস্ত্র এবং উদাসীনতা যেমন রচিত হয়েছে,তেমনই জয় গোস্বামীর কবিতাগুলির গহন মনস্তত্ত্বের অপহরণের শাশ্বত ক্ষমতাকেও তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক।রণজিত দাশের নশ্বরতা কিংবা সুধীর দত্তের মৌলিকতার প্রান্ত স্পর্শ করে সমকালীন কবিতার নারী চেতনার গহীনেও প্রবেশ নিয়েছেন শ্রীগুণ।বলা যায়,আক্ষরিক অর্থেই বাংলা কবিতা যে প্রবাহ অনুসারে স্বতঃবিনির্মাণের দিকে এগিয়ে নিজেকে ‘আধুনিক’ করে তুলছে সবসময়,সেই প্রবাহেরই এক রম্য বিবরণ আলোচ্যমান গ্রন্থ।
দৈগন্তিক এক বিস্তার
‘কবির গদ্য ‘ সবসময়ই আলাদা করে রাখা হয়। কেন হয়?এর জন্য কি কবিরাই দায়ি? এরকম বিভিন্ন প্রশ্ন উঁকি দিলেও এ কথা স্বীকার করে নিতে দ্বিধা হয় না যে,কবির গদ্য অনেক বেশি অন্তর্ঘাতময় শব্দ সঞ্চারে সক্ষম,স্বল্পবাক কিছুটা ব্যঞ্জনা ও রহস্যের আবডালের ছায়ায় এসেই তত্ত্বনেপদী থাকতে পছন্দ করে।তত্ত্ব যে থাকে না,তা নয়, কিন্তু,কবির আত্মসম্পাদিত শব্দ সঞ্চার তাকে প্রশম করে দেয়।
সাধারণভাবে ‘কবি ‘ হিসেবে পরিচিত মানুষের প্রবন্ধে এই চিহ্ন গুলির উপস্থিতি কিন্তু অস্বীকার করা যায় না।তাই সুমন গুণ প্রণীত আলোচ্যমান বইটির গদ্য ভঙ্গিমাকে আগে লক্ষ করার প্রয়োজন বলে বোধ করছি। একটি পরিক্রমার আভাস পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করি।
উত্তর রৈবিক যুগে প্রাবন্ধিক হিসেবে নিঃসন্দেহে সর্বাতিশায়ি প্রভাব বিস্তার করেছেন বুদ্ধদেব বসু। এই গ্রন্থেও বুদ্ধদেব প্রসঙ্গ একাধিকবার এসেছে তাই,বু.ব.র গদ্য ভঙ্গিমাকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করলেই সুমন গুণের গদ্য বিন্যাসের প্রকৃত অবয়ব ও বিনির্মাণ বোঝা যাবে।
‘কবি রবীন্দ্রনাথ ‘গ্রন্থের ‘দেবতা ও বধূ ‘ শীর্ষক তৃতীয় প্রস্তাবে বু.ব.লিখছেন,
“কিন্তু রবীন্দ্রনাথ,আর যা-ই হোন, দার্শনিক কবি নন; তাঁকে জানতে হ’লে প্রত্যক্ষ কোনো গুহ্য তত্ত্বে দীক্ষিত হতে হয় না; তাঁর আবেদন প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক ব’লে অতি সহজে তিনি আমাদের জয় করে নেন। তাঁর সঙ্গে পাঠকের কোনো বিশ্বাসগত ব্যবধান নেই;আপনি নাস্তিক বা সংশয়বাদী বা ইশ্বরবিশ্বাসী যা-ই হোন না, তাঁর কবিতায় আপনার আমন্ত্রণ সমানভাবে অবধারিত।”(পৃঃ ৬১)
এই মন্তব্য পাঠ অন্তে আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে বু.ব.র বক্তব্য বিষয়ে। অন্ততঃ বুদ্ধদেব তাঁর প্রবন্ধগুলির প্রকৌশলের ভেতর যুক্তির একরৈখিক দার্ঢ্য প্রকাশ করতেন যে, তাঁকে বিশ্বাস করে নেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না।বুদ্ধদেবের এহেন মর্মগ্রাসী স্বভাব সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত;তত্রাচ আপনাকে লক্ষ করতেই হবে শ্রীগুণের প্রবন্ধেও সেই স্বাধর্ম্য।
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীগুণ লিখছেন,
“আমাদের ভাষায় আরো অনেকেই সময়ের স্পর্শ কবিতায় সাফল্যের সঙ্গে ধরে দিতে পেরেছেন।এই ধরনের লেখার একটা সাধারণ বিপদ আছে।বিষয়ের দাম এখানে অনেক বেশি।তাই,অনেক সময়,কী বলা হচ্ছে সেটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে কীভাবে বলা হচ্ছে তার দিকে খেয়াল থাকে না।সেটা কিছুটা পর্যন্ত মেনেও নেওয়া যায়।কারণ শেষ পর্যন্ত আমাদের বেঁচে থাকা , সবাইকে নিয়ে ভালভাবে এই গ্রহমুহূর্ত সম্মিলিত উদযাপনের চেয়ে মহত্তর প্রসঙ্গ আর কী হতে পারে! কিন্তু তবুও, কোনোভাবে,প্রসঙ্গের চেয়ে প্রসঙ্গান্তরের দিকেই যে আমাদের ঝোঁক বেশি,সেটা তো আমাদের শিল্পচর্চার ইতিহাসে বারবারই প্রমাণিত হয়েছে।(পৃঃ ১০১: চল্লিশের সচেতন প্রত্যাহার ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
স্বভাব ধর্ম নির্মাণ করতে গিয়ে শ্রীগুণ একই পথ অনুসরণ করলেন। দৈগন্তিক স্পর্শ রাখলেন পূর্বজের যত্নে। শিল্পচর্চার ইতিহাসের একটি বৃত্তান্তকে সহসাই এমনভাবে উপস্থাপন করলেন যে,বিহ্বল পাঠ তখন বক্তব্যের সঙ্গে বিরোধ রাখতেই অক্ষম।একই সঙ্গে অনুরোধ করব,’গ্রহমুহুর্ত’ শব্দটির দিকে মনোযোগ রাখতে।এরই সঙ্গে দুটো শব্দ যুক্ত হয়েছে ‘সম্মিলিত’ও ‘উদযাপন’শব্দদুটো।এই ‘সম্মিলিত উদযাপন’ প্রসঙ্গে অব্যবহিত সময়ে আসা গেলেও ‘গ্রহমুহুর্ত’কে অবলম্বন করে অবশ্যই পরবর্তী প্রসঙ্গে যাওয়া যেতে পারে।
কবির গদ্য
কবিতা সবসময়ই একটি বহুগামী পন্থা অবলম্বন করে। বিভিন্ন ভাবে তার স্বভাবকে দেখাও যেতে পারে।তবে,একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বভাব হলো সংহতি। এবং সেটি নির্ভর করে কবির নিজস্ব সংহতির ওপর।একটা মাত্র শব্দকে বহুবর্ণীল অর্থের দ্যোতনা দেওয়ার জন্য অতি সাধারণ কারণেই শব্দকে পিনদ্ধ,অমোঘ ও সুচিমুখ করে তোলার ক্ষমতা তৈরি করতে হয় কবির অন্যতম শর্ত হিসেবে।
এবার এই কবি যদি গদ্য লেখেন, বাংলা ভাষায় এহেন উদাহরণ প্রচুর,সঙ্গত স্বভাবেই গদ্যেও আসে কুহক,ইঙ্গিত ও অলঙ্ঘনীয় শব্দের সঞ্চার।শ্রীগুণের এই গ্রন্থ সে উদাহরণ সঞ্চয় করেছে যথেষ্টই। তারমধ্যে থেকে দুই একটির নমুনা পেশ করলে রসিকের আনন্দ বৃদ্ধি পাবে বলেই বিশ্বাসবাসি।
‘রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসু: ধ্রুপদী সঙ্গ ‘শীর্ষক প্রস্তাবে সুমন বাবু লিখছেন,
“প্রায় সেই সময়ই ,এক ‘শীতের সকালে ‘কোনো- একজন ‘আত্মীয়’র কাছ থেকে তিনি অর্জন করলেন ‘চয়নিকা’।”
আবার একই রচনায় বুদ্ধদেবের ‘ছিন্নপত্র’-এ পহেলা সংস্পর্শের প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক লিখছেন,
“কৌশোরেই ‘ছিন্নপত্র’ও আয়ত্বে আসে বুদ্ধদেবের।”
পাঠক লক্ষ করুন,’অর্জন’ ও ‘আয়ত্ব’ শব্দদুটির ব্যবহারেই লেখক বুঝিয়ে দিচ্ছেন বই দু’টি পড়তে পারার সুযোগ তৈরি হয়েছিল দু’রকমভাবে।অতিকথনকে ছেঁটে ফেলে শব্দকে অভিধা অর্থেই প্রয়োগ করে অর্থান্তর ঘটালেন।একই সঙ্গে ‘করলেন’ ও ‘আসে’ ক্রিয়াদ্বয়ের প্রয়োগ। প্রথমটির মধ্যে উপহার পাওয়ার মধ্যেও প্রাপকের একটি কৌশলগত কৃতিত্ব স্বীকার করে রহস্য নির্মাণ করা হচ্ছে। অপরপক্ষে দ্বিতীয় ক্রিয়াটি একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ফুটিয়ে তোলে।যেন আসারই ছিল।অথচ এই আয়াসে যান্ত্রিক কৌশিক তো দৃষ্ট নয়ই বরং কাব্যের নান্দনিক প্রতিষ্ঠা করছে।এহেন উদাহরণ গ্রন্থে বিশেষভাবে অবিরল।জয় গোস্বামীর কবিতা সম্পর্কে আমাদের জানাতে গিয়ে লিখছেন সুমন,
“জয় গোস্বামী নানা সময়ে ছোটো কবিতা লিখেছেন। তাঁর যে- ধরনের কবিতায় স্মরনীয় হয়ে ওঠার ঝোঁক থাকে,সেই ঘরানায় এমনকি দু’লাইনের কবিতাও মন দিয়ে লিখেছেন তিনি। অনেক আগে থেকেই।ভাষায় লাবণ্য আর ঔদ্ধত্যের যে -অতুলনীয় মিশেল থাকে তাঁর কবিতায়,তার জোরে যে -কোনও কথাই অবধারিত মনে হয়।সে-কথার ভেতরে কখনও সম্ভাবনার সাতমহল, কখনও ত্বরিত কিছু অনুপান।”(জয় গোস্বামীর ‘নিশ্চিহ্ন’:গহন অপহরণের কবিতা)
অত্যন্ত সুখপাঠ্য গদ্যে অযথা সমাসবদ্ধ, নবগঠিত বা অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করার ঝোঁক দেখা যায় না। কিঞ্চিৎ মখমলি ভঙ্গিতে বরং এক একটা ইমেজ গড়ে দেন প্রবন্ধের চলনকে অসন্তুষ্ট না করেই।যেমন,’সম্ভাবনার সাতমহল’, কখনও ‘ত্বরিত কিছু অনুপান ‘।
প্রবন্ধের যুক্তি ও বৈদগ্ধের মধ্যেই চিন্তার অবকাশ তৈরি করার জন্যই যেন কাব্যিক স্পেস নির্মাণ করেন লেখক।এখানেই কবি লুকিয়ে থাকতে পারেন না।
তত্ত্বের ইতিকথা
সুমন গুণ মন্ময় পদ্ধতি ব্যবহার করতেই অধিক আগ্রহী।রসপ্রস্থানের পথে পাঠককে নিয়ে যেতে চান।প্রাজ্ঞের অভিজ্ঞ পাঠ অভিজ্ঞতা এ টেক্সটে প্রধান হয়ে ওঠে। কবিতার প্রাথমিক পাঠকের পক্ষেও আলোচিত কবিদের কাব্যের কুটাভাষ সহজেই বোধগম্য হয়ে যেতে পারে।যেমন , ‘মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কবিতা: সশস্ত্র সন্ন্যাস ‘-এ লিখছেন,
“রূপকের অনায়াস আর তীর্যক ব্যবহারে মণিভূষণের দক্ষতার সেরা নজির এই কবিতা।পেশল,রুক্ষ আর নৈর্ব্যেক্তিক ধরনটি গোটা কবিতায় সফলভাবে রক্ষা করেছেন তিনি।’কোনো কবিসম্মেলনে’র চেয়েও অনেক সংহতভাবে।এই কবিতাটিও এতো অবিচ্ছিন্ন আর টানটান যে কোনও একটা অংশ তুলে এর জোর বোঝানো অসম্ভব।তবু কয়েকটা লাইন তুলে এই ধরনের লেখায় মণিভূষণের তুখোর দাপট টের পাওয়া যেতে পারে:
খিদেয় নেতিয়ে-পড়া কনিষ্ঠ কঙ্কালগুলো দলা পাকিয়ে
ঘুমিয়ে পড়েছে। বিরক্ত বয়স্করা ঝিমুচ্ছে।মধ্যরাত্রির এই পচনশীল
নৈঃশব্দ্যের দিকে,নিবন্ত উনুনের পাশে গরমমশলার সুদূর গন্ধের মধ্যে
হে অন্ধ অধিরাজ, আপনাকে বসিয়ে রাখবো;মনে রাখবেন, পরিবেশনের
ভার আপনাদের উপর;জানি, অসমবণ্টনে আপনার কত শ্রান্তি!তবু,
মেটের টুকরোগুলো বাচ্চারাই যেন পায়।
গন্ধের ‘সুদূর’ বিশেষণটির বহুতল সম্ভাবনা খেয়াল না করে পার হওয়া যাবে না।শেষ লাইনটিতে এসে কথার গমক যেভাবে হঠাৎ বেঁকে গেল,তাও আমাদের সচকিত করে তোলে।”(পৃঃ ১৬৪-৬৫)
পাঠকের চোখ এড়ায় না যে তত্ত্বের ইঙ্গিতে প্রবেশ করেও লেখক শব্দ সংস্থানের ওপর দৃষ্টিপাত করে পাঠকের চিন্তার অবকাশ তৈরি করে দিলেন। তবে সে অবকাশ কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রয়েছে লেখকেরই।’সুদূর’-এর তাৎপর্য গন্ধের ওপর এসে পড়লেই যে নাটকীয় শীর্ষারোহনকে পাওয়া যায়, তাকে পূর্বেই কিন্তু কিন্তু চিহ্নিত করে রেখেছেন আলোচক ‘তীর্যক’ শব্দের ব্যবহার করে।
বস্তুত এ গ্রন্থে পাঠককে পরিসর দিয়েছেন শ্রীগুণ।তবে ঠিক ততটাই পরিসর দিয়েছেন,যতটা তিনি ইচ্ছা করেন।অন্তরালে বহমান সর্বজ্ঞ ও সর্বাতিশায়ি লেখক।
এখন প্রশ্ন আসতে পারে,এই নিয়ন্তা নৈয়ায়িক সাহিত্য আলোচনার কোন প্রেক্ষিতটিকে ব্যবহার করলেন?অর্থাৎ, কোন কৌণিক দৃষ্টিতে তাঁর এই দর্শন স্ফূর্তি পেয়েছে! গ্রন্থের একাধিক স্থানে আমাদের চোখে পড়ছে Elaine Showalter,এমিলি ব্রন্টি বা,
“Juxtaposition -এর সচেতন ব্যবহার ইমেজিস্ট কবিতা আন্দোলনের একটা মৌলিক উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, এলিয়টের সেই সুখ্যাত ‘objective correlative ‘ খোঁজার তাগিদ আসলে এই উদ্যোগেরই ফসল।’আকাশ-পাতাল’-এর বৈষম্য দেখার মধ্যেও সেই প্রবণতা ভেতরে ভেতরে কাজ করছে। আর এই বিপুল মহাজাগতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝখানে,খালি গায়ে,বিমূঢ় বিস্ময়চিহ্নের মতো কবি জেগে থাকেন।”(রণজিৎ দাশের কবিতা:নশ্বর ও রহস্যময়; পৃঃ ১৭৭)-এর মতো উল্লেখ থাকলেও লেখক অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিতার যেসব নমুনা তুলে ধরলেন,তার তাঁর দৃষ্টি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমবণ্টনের বোধকেই নির্ভর করেছে,তা বলাই বাহুল্য।যেমন মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখছেন সুমন,
“আমরা যখন লেখালিখি শুরু করি মল্লিকা তখন বাংলা কবিতায় চেনা নাম।নারীবাদ তখন তাঁর কবিতাকে অন্যভাবে স্পর্শ করলেও তেমনভাবে নিয়ে নেয়নি। তাঁর প্রথম দিকের কবিতার কৌণিক মন্দ্রতা ক্রমশঃ সরল হয়ে এল তাঁর পরবর্তী বইগুলিতে।সুগম হয়ে উঠল তাঁর কবিতা, চারপাশের সময়কে কবিতায় ধরতে চাইলেন তিনি,ফুলন দেবী থেকে আক্রান্ত স্কুলবালিকা,তহমিনা থেকে মেধা পাটেকর, গুজরাট কিংবা আমেরিকা তাঁর কবিতার অবধারিত বিষয় হয়ে উঠতে লাগলো।”(‘নারীবাদ ‘ও নারীকণ্ঠের বাংলা কবিতা; পৃঃ ২০৩)
মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতার এই মুক্তিই যেন অভিপ্রায় ছিল লেখকের।যেন এই বহবর্ণময় বিভা তাঁকে স্বস্তি দিয়েছে। এবং সুমন স্বস্তি পেয়েছেন কখন?
“অসমাপ্ত ন্যাড়া ছাদে
বাবা,মা’কে তারা চেনাচ্ছেন।(কস্তুরী সেন)
ছাদ যে -অর্থে অসমাপ্ত,তা টের পেয়ে আমরা বিমূঢ় হয়ে পড়ি । মনে পড়ে বেটি ফ্রিডেনের কথা।’ফ্রম দ্য ফেমিনিস্ট মিস্টিক ‘প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন সেই মায়ের কথা,যিনি বিছানা গোছান, দোকানের ফর্দ তৈরি করেন,রুটি বানান,রাতে স্বামীর পাশে শো।আর গোপনে, ভয়ে ভয়ে, নিজেকে প্রশ্ন করেন:’এটাই কি সব?’এটাই যে সব নয়,সেই আনন্দময় জ্ঞাপনটিও নারীচেতনাবাদের ফসল।সেই মায়েদের কথা বলা,যাঁকে তাঁর স্বামী বিকেলের অসমাপ্ত ছাদে নক্ষত্রলোকের ঠিকানা চেনান।”(ঐ: পৃঃ)
একটি তত্ত্বকোষের বিস্ফোরণান্ত স্তিমিত গতি যখন প্রলম্বিত হচ্ছে, বিনির্মীত হচ্ছে, এবং প্রসারিত হচ্ছে বিবিধ সম্ভাবনার দিকে, বিশেষ মেঘ আর শস্যের লড়াইয়ের দিকে,সুমন গুণের পাঠ নিষ্ণাত হতে চাইছে সেখানেই।যেন,
“Artistic work under socialism is marked by the growing role of the subjective element, talent and world view of the writer but also by the growing importance of the objective aspect ,i.e., reflection of the gigantic changes taking place in life, The more politically -minded the artist is and the broader his view of reality, the more actively he probes into new areas of life and the more audacious he is in raising unresolved questions, the greater his chance of discovering the truth indipendently and of being objective and truthful in his work.(artistic truth and dialectics of creative work:Vassily Novikov: page:81-82)
চিন্তাকেই মান্যতা দিতে চাইছেন শ্রীসুমন গুণ। কবিতা যখনই এবং যেখানেই বহুমাত্রাকে অবলম্বন করেছে,সুমন বাবুর কৌতুহলের আয়ত্বে এসেছে। সমাজতন্ত্রের আওতায় যে মুক্তির সংস্পর্শে যেতে পারে কবিতা,তাকেই রমণীয়তায় চিহ্নিত করেছেন সমগ্র গ্রন্থে শ্রীগুণ। এইবার আরেকবার স্মরণ করতে বলব প্রথম অংশে মৎ উল্লিখিত ‘সম্মিলিত’ আর ‘উদযাপন’ শব্দ দু’টিকে।সুমন গুণের আলোচনা অবস্থান করতে চেয়েছে মানবসমাজের এই সম্ভাব্য অন্বিষ্টে।
আধুনিক বাংলা কবিতার কথা
কবিতার মতোই পাঠকেরও এবং পাঠরীতিরও বহুমাত্রিক অবস্থান থাকে। অন্ততঃ দুটো প্রধান শ্রেণির পাঠক তো খুব সহজেই সাব্যস্ত হয়ে থাকেন— তত্ত্ব- নিষ্ণাত ও তত্ত্ব -নিরপেক্ষ পাঠক।এই দুই শ্রেণিকেই তৃপ্ত করতে সক্ষম প্রাবন্ধিকের পাঠরীতির পরিবহন। পূর্ববর্তী প্রহরেই বলতে চেষ্টা করা গেছে লেখকের শব্দ -ব্যবহারের স্বাতন্ত্র।এই উভবিধ মিথোষ্ক্রিয়া গ্রন্থটিকে বস্তুতই পাঠভোগ্য কেবল নয় মননের অভিভাবক করে তুলেছে। উত্তর রৈবিক যুগের কবিতার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক এবং সেই বিবর্তনের হোতা স্বরূপেরা স্পষ্ট করে নির্দিষ্টিকৃত ও যথাযোগ্যতায় আলোচিতও হয়েছেন।
এ অভিযোগ অংশত মিথ্যে নয় যে,উত্তর জীবনানন্দ পর্বের বাংলা কবিতার যুগ বিভাগ ও যুগবৈশিষ্ট্য সুচিহ্নিত আকারে আলোচিত নয়।এই গ্রন্থ সে অভাব পূরণ করল বলেই বিশ্বাসবাসি।
লেখাটি ভালো লাগলে, আবহমানের জন্য আপনার ইচ্ছেমতো অবদান রাখতে পারেন
এই কিউ আর কোড স্ক্যান করে ফোন পে-র মাধ্যমে।
এই অবদান একেবারেই বাধ্যতামূলক নয়।
স্ক্যান করার জন্য কিউ আর কোড–


