প্রসঙ্গ ধর্মরক্ষা ও একটি বই
:: সরোজ দরবার
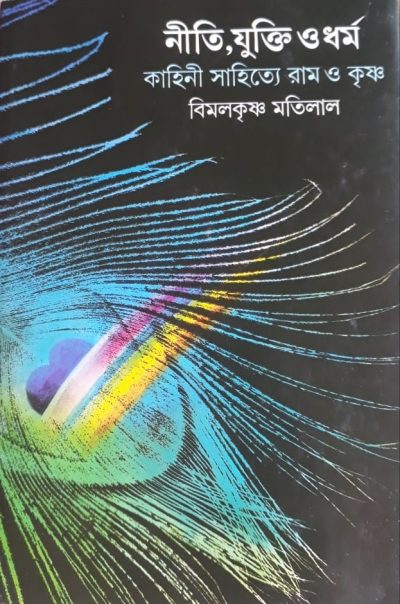
মানুষের জন্য ত্যাগস্বীকারের যে মহতী শিক্ষা, তা আমাদের দিয়ে থাকে ধর্মই। তরুণ মার্কস এমনটা মনে করতেন, গভীর বিশ্বাসের সঙ্গেই। ধর্ম নিয়ে তাঁর ধারণাকে সেই বহুশ্রুত আফিমের সঙ্গে তুলনার একটি লাইনে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার ঐতিহাসিক ভুল আর যেই করুন না কেন, মার্কস স্বয়ং ভাগ্যিস মার্কসবাদী ছিলেন না। এবং, সোভিয়েট মডেলের ছাঁচে ফেলা মার্কসবাদী তো আদৌ নন। ফলে মার্কসের ধর্ম-সংক্রান্ত প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা ও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর একটা পরম্পরা ও বিবর্তন আছে। তরুণ মার্কস মনে করতেন, একজন মানুষ তখনই সর্বাপেক্ষা সুখী হতে পারেন, যখন তিনি সর্বাধিক মানুষকে সুখী করতে পারেন। বস্তুত, পেশা নির্বাচন নিয়েই ছিল তাঁর এই সিদ্ধান্ত। তাঁর ধারণা ছিল, এমন পেশাই নির্বাচন করা উচিত, যেখানে মানবতার মঙ্গলসাধন হয়। আর এই মানবতার কারণে ত্যাগস্বীকারের যে মহান শিক্ষা, তা ধর্মই মানুষকে শিখিয়ে দেয়।
এই ত্যাগস্বীকারের কথা আর-একটু এগিয়ে নিয়ে গেলে আমরা দেখব, সম্প্রতি যে ‘ঘরহারা’ রামচন্দ্রের মাথায় ছাদ তুলে দিতে বহুজন এককাট্টা হয়েছেন, সেই নরচন্দ্রমা স্বয়ং বহুজনহিতায় বহু বহু ত্যাগস্বীকার করেছেন। অভিষেক মুহূর্তে রাজ্যত্যাগ করেছেন। অথচ অমন বীর, চাইলে যুদ্ধ তো করতেই পারতেন। হারিয়েও দিতে পারতেন তাঁর বিরোধীদের। ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ তো বিরল নয়। গোটা মহাভারত তো তা-ই নিয়েই। কিন্তু যুদ্ধ করে রাজ্যভোগ করতে চাননি রামচন্দ্র। তারপর বনবাসকালে, ভাই ভরত রাজ্যে ফেরার আহ্বান নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। নরচন্দ্রমা সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। আরও পরে যুদ্ধ করে রাবণকে হারিয়েছেন, কিন্তু লঙ্কাদখল করেননি। সে-রাজপাট ত্যাগ করেছেন। প্রতি পদেই এই ত্যাগ স্বীকার করেছেন রামচন্দ্র। আমাদের এখানে মনে পড়বে, রবীন্দ্রনাথ কেন তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে ‘আত্মনিগ্রহ’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ‘নিজের সমুদয় সহজ প্রবৃত্তিকে শাস্ত্রমতে কঠিন শাসন করিয়া সমাজরক্ষার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। আমাদের স্থিতিপ্রধান সভ্যতায় পদে পদে যে ত্যাগ ক্ষমা ও আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন হয়, রামের চরিত্রে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়া রামায়ণ হিন্দুসমাজের মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে।’ – বলছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং, তাঁর মত- রামচন্দ্র যে ‘লোকপূজ্যতা’ অর্জন করেছিলেন, তার কারণ হল, ‘গার্হস্থ্যপ্রধান হিন্দু সমাজের যত-কিছু ধর্ম’, সেই সবকিছুরই অবতার হিসেবে রামচন্দ্রকে গড়ে তুলেছিলেন আদিকবি। এখানেও সেই ধর্ম। এবং ত্যাগস্বীকার।
এহেন রামচন্দ্র এইভাবে মন্দিরকে শিখণ্ডি করে ক্ষমতাদখলের রাজনীতিতে সায় দিতেন কি-না, সে-প্রসঙ্গ থাক। বরং এই বিন্দু থেকেই আমরা ঢুকে পড়ি শ্রদ্ধেয় বিমলকৃষ্ণ মতিলালের লেখায়। এ-কথা আমাদের জানা যে, রিলিজিয়ন শব্দটি ধর্মের ব্যাপকার্থ ধারণে সক্ষম নয়। সংকীর্ণভাবে তা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কথাই বলে। তাই-ই ধর্মের এক বা একমাত্র অর্থ নয়। কারণ, যে অর্থে রামচন্দ্র রাজধর্ম পালন করেন, বা রবীন্দ্রনাথ যাকে বলছেন ‘সমাজের যত ধর্ম’, তা রিলিজিয়ন নয়। তা প্রকৃত প্রস্তাবে নৈতিকতা। খেয়াল করলে দেখব, তরুণ মার্কস সেই নৈতিকতার কথাই বলছিলেন। নৈতিকতাই ত্যাগস্বীকারের প্রসঙ্গ আনছে, যা শিখিয়ে দিচ্ছে ধর্ম। অর্থাৎ, ধর্ম, নীতি ও যুক্তি একেবারে পাশাপাশি হাত ধরে চলেছে। এদের তিনজনের কারও থেকে কেউ আলাদা হলেই অর্থ খণ্ডিত হয়ে পড়ছে। বকবেশী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরের প্রসঙ্গ টেনে বিমলকৃষ্ণ বলেন, ‘যুক্তির দ্বারা গ্রাহ্য মহত্ত্বর নীতির অনুমোদিত কর্মকে এখানে ধর্ম বলা হয়েছে যাতে ধর্মের অর্থাৎ নৈতিকতার কল্যাণময়তা ও পরার্থপরতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।’
এখন, এইভাবে ধর্মের যে ধারণা আমরা পাই, তা মাঝেমধ্যেই ধূলিসাৎ হয়ে যায় যখন রামায়ণ বা মহাভারতের কিছু ঘটনাবলির দিকে তাকানো যায়। অর্থাৎ, যখন দেখি যুদ্ধিষ্ঠির যেভাবে দ্রোণকে বধের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন, বা, নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র যেভাবে বালীকে বধ করছেন এবং তার জন্য প্রায় অসার যুক্তি সাজাচ্ছেন, বা শম্বুক হত্যা করছেন যেভাবে, তা যে ধর্মের সীমানায় পড়ে না, তা সহজবোধ্য। কিন্তু আমরা আগেই জেনেছি রামচন্দ্র কীভাবে ধর্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর। আর, কুরুক্ষেত্র তো ধর্মযুদ্ধই। তাহলে? বিমলকৃষ্ণের যে-বই নিয়ে এই বিনীত আলোচনা-প্রয়াস, সেই ‘নীতি, যুক্তি ধর্ম – কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ’ পুনর্বার পাঠ প্রয়োজনীয় ঠিক এই কারণেই, এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানেই। নীতি ও যুক্তির জট ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে আমাদের ধর্মের প্রকৃত অর্থের কাছে পৌঁছে দেয় এই বই। অবলম্বন হিসেবে এখানে তুলে নেওয়া হয়েছে ভারতীয় সভ্যতার দুই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রাম ও কৃষ্ণকে; অবশ্যই ঈশ্বর হিসেবে নয়। ফলত, মহাকাব্যে তাঁদের নীতি ও যুক্তির দন্দ্বগুলি অতিক্রম করতে করতে গেলে আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে সত্যিকার চোখ খোলে।
বালীবধের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সীতাকে ত্যাগের ঘটনাও আমরা জানি। এবং এও জানি যে, এই রামচন্দ্র যা কিছু করছেন, তা ধর্ম ও সত্যরক্ষায়। কিন্তু যখন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ্মণকে হত্যার প্রসঙ্গ এল, তখন কিন্তু তিনি অন্যরকম করে ভাবতে শুরু করলেন। মন্ত্রণালয়ে আচমকা কেউ ঢুকে পড়লে, তার শাস্তি হবে মৃত্যু। এই ছিল নির্দেশ। প্রহরী ছিলেন লক্ষ্মণ। হেনকালে হাজির হলেন স্বয়ং দুর্বাশা। তা দুর্বাশাকে লক্ষ্মণ কিছুতেই কিছু বোঝাতে পারলেন না, বাধ্য হয়ে তাঁকে ভিতরে ঢুকতে হল। এখন, প্রতিজ্ঞা রাখতে গেলে, লক্ষ্মণকে তো হত্যা করতে হয়। যে-রাম শম্বুক হত্যা করেন এবং যে যুক্তিতে করেন, সেই রাম এখানে লক্ষ্মণকে হত্যাই করতে পারতেন; সেটাই যেন স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তিনি একটু আলাদা পথ নিলেন। এবার তাঁর মনে হল, প্রিয়জনকে ত্যাগ করাই হত্যার সমান। অনুরূপ কাজ তো কৃষ্ণও করেছেন। অর্জুনকে ধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যুদ্ধের জন্য চাঙা করেছেন তিনি। সেই কৃষ্ণই তো দ্রোণবধের যুক্তি হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন এই যুক্তিকে যে, অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করার পরিকল্পনা তো দ্রোণেরই ছিল। কাজেই ঘটনাক্রমে যখন অর্জুনকে প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করার সময় এল, তখন তিনি অর্জুনকে নিবৃত্ত করলেন। বললেন, গুরুজনকে কটুকথা বললেই তা হত্যার শামিল হবে।
এই দুটি গল্পকে পাশাপাশি রেখেই আমাদের খানিকটা ধাঁধা লাগে। এবং, প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে নীতি, যুক্তি ও ধর্ম কখন কীভাবে হাত ধরে চলেছে? এর উত্তর এই বইয়ের দেওয়া হয় এরকম ভাবে, ‘সর্বজনীনতা-রূপ গুণটি ‘ভালত্ব’-রূপ গুণের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রায় ওতপ্রোতভাবে। কাজেই কোন বিশেষ কর্ম যদি তার ‘ভালত্ব’ রূপ গুণটি হারায় তবে তার সর্বজনীনতাও লোপ পায়।’ ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে এমন কাজ যদি করা হয়, যা তার ভালত্ব গুণ হারিয়েছে, তবে তা ওই ভালত্বহীন ধর্ম। এবার এটুকু আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, যে, ধর্ম ধারণাটি কেন বহুরূপী। নীতি, নিয়ম ও যুক্তি পদে পদে তাকে বেঁধে রেখেছে নানা প্রেক্ষিত থেকে। সে-অরণ্যে পথ পাওয়া সহজ নয়। ‘মহাজনো যেন গতঃ সে পন্থাঃ’ – এখানে ‘মহাজন’ শব্দটির অর্থের আর-এক রূপ বুঝিয়ে দেন তিনি। বহুজন। অর্থাৎ, অরণ্যে বহুজন বহুদিনের পরীক্ষায় যে-পথ বেছে নিয়েছেন, তা ভুল হতে পারে না। এই বহুজন মেজরেটেরিয়ানের কথা বলে না। বলে, সেই উপায়ের কথা যার সঙ্গে বহুজন জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ, বহুলোকের হিতাকাঙ্ক্ষাও জড়িয়ে। বহুজনহিতায়। বহুজনসুখায়। তাহলে, ধর্ম হল গিয়ে সেই উপায় বা পথ যা কিনা আমাদের বহুজনের হিতসাধনে সহায়তা করে। হায় তরুণ মার্কস! কেন যে আমরা তাঁর ধর্মভাবনাকে আফিমে মেশানো এক লাইনের উদ্ধৃতির সঙ্গে সমীকৃত করে ফেললাম!
এখন, বহুজনের হিতসাধনই যদি ধর্ম হবে, তবে, ধর্মযুদ্ধে এত অধর্ম কেন? বিমলকৃষ্ণ আমাদের স্পষ্ট করে দেন যে, এই ধর্মযুদ্ধ কখনও জাস্টওয়ার নয়। অর্থাৎ, একদিকে ন্যায়, অন্যদিকে অন্যায়। ন্যায়যুদ্ধ অন্যায়কে ধ্বংস করবে। ‘এরকম ধারণাকে সত্য বলে ধরে নিয়ে তথাকথিত ন্যায় বা ধর্মের পক্ষে অবিচারে নরহত্যা ধর্মসম্মত বা রিজিয়নসম্মত – এসব যুক্তি যাঁরা দেন তাঁরাও ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা মনের অজ্ঞাতসারে ধর্ম ও ন্যায়কে, রিলিজন ও মরালিটিকে মিশিয়ে একীভূত অর্থাৎ কনফ্লেট করেন। এই অবৈধ একীভবনের ফলে যুদ্ধকামীদেরর যুক্তিগুলিও যেন জোরাল হয়ে ওঠে’ – মত বিমলকৃষ্ণের। তাঁর তাই অভিমত, এক্ষেত্রে ধর্মকে নিয়মবন্ধন হিসেবে ভাবা আবশ্যক। “ধর্মশাস্ত্রে নানা নিয়মবন্ধনকে ‘ধর্ম’ বলা হয়ে থাকে।” এই যুদ্ধের ক্ষেত্রেও কিছু নিয়মবন্ধন ছিল। তা কি ভাঙা হয়নি? হয়েছে। যিনি ভেঙেছেন, তিনি আবার পালটা নিয়মভঙ্গে প্রাণ দিয়েছেন, যেমন দ্রোণ। তাহলে, এত গল্প বলার সার্থকতা কোথায়? আমাদের সমস্ত শিক্ষাই তো গল্পে গল্পে। কাহিনিতে-আখ্যানে। এই আখ্যান আমাদের এ-কথাই শিখিয়ে দিয়ে যে, এই নিয়মবন্ধ তথা ধর্মরক্ষার ধর্ম যাঁরা ভাঙেন, তাঁরা যত বড় মানুষই হোন না কেন যুগে যুগে সমালোচিত ও নিন্দিত। এই অর্থে যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, রামচন্দ্র কেউই সমালোচনার ঊর্ধে নন। আর, ‘নৈতিকতা মূলত মানবতাকেন্দ্রিক।’
এখন, আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রভাবনায় এই নিয়মবন্ধনকে যদি সংবিধান বলি, বোধহয় ভুল হবে না। কারণ, বহুজনহিতায় ও বহুজনসুখায় যে-পথ তা এই নিয়মবন্ধেই উপলব্ধ এবং পরীক্ষিতও। সেই সংবিধানকে যদি কেউ ভাঙতে উদ্যত হন, এক্ষেত্রে তাঁকেও কি আমরা ধর্মচ্যুত বলব না! নীতি, যুক্তি ও ধর্মের সূত্রে এই আলোচনা এগোতে থাকলেই সম্ভবত আমরা ধর্ম নামক ধারণাটির সবথেকে গ্রহণীয় সঠিক অর্থের কাছাকাছি থাকতে পারব। এই বই পড়তে-পড়তে সেই জানলাটিই খুলে যায়।
যে বইয়ের সূত্রে এই লেখা –
নীতি, যুক্তি ও ধর্ম
কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ
বিমলকৃষ্ণ মতিলাল
প্রকাশক –আনন্দ
প্রথম প্রকাশ – বৈশাখ ১৩৯৫

