
চিন্তার চিহ্নমালা ১৭
সন্মাত্রানন্দ
বাগ্ভঙ্গিমা মানে আপনি যেভাবে কথা বলেন। অবিকল সেটাই যে আপনি লিখতে পারেন, তা হয়তো নয়। তবু আপনার লিখনের সঙ্গে কথনের কোথাও একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। আপনার নিজস্ব কণ্ঠস্বর আপনার লিখিত বয়ানের পেছন থেকে নাটকের প্রম্পটারের মতো কথা জুগিয়ে চলেই। আপনি সেই প্রম্পটারের সব পরামর্শ মানেন না। খানিক রাখেন, খানিক বাতিল করে দেন। তবু আপনার লিখিত বয়ানের পেছনে লুকিয়ে থাকে আপনার কথনশৈলী, আপনার ব্যক্তিত্ব বা আরও পরিষ্কার করে বললে আপনারই চিন্তন বিশ্ব। লেখকের পেছনে লুকিয়ে থাকা ওই প্রম্পটারকেই আমরা লেখকের স্বতন্ত্র ভাষারীতি বলে ভুল করছি না তো?
লেখকের ভাষা, নাকি লেখার ভাষা?
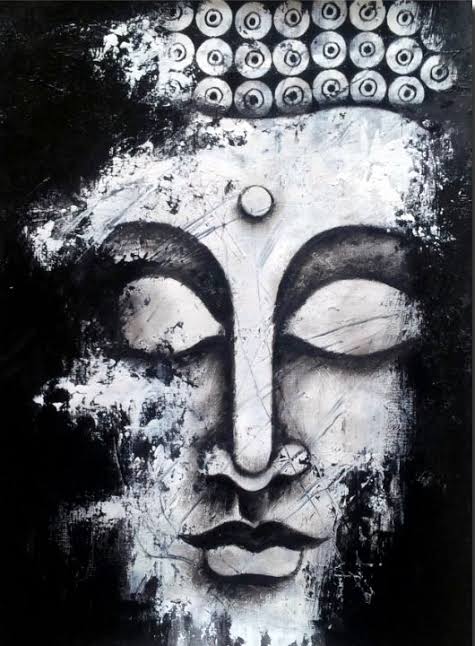
প্রথম লিখতে শুরু করা যেকোনো লেখককেই তাঁর পূর্বজ লেখকেরা এই বলে সাবধান করে দেন, দেখো, তোমার লেখায় যেন আমাদের ভাষার ছাপ না থাকে। সাহিত্যে অনুকৃতির মূল্য নেই। অন্যান্য শিল্পমাধ্যম সম্পর্কেও হয়তো একই কথা খাটে, কিন্তু আমার পক্ষে সেসব নিয়ে কথা বলা ঠিক না, যেহেতু সাহিত্য ছাড়া শিল্পের অন্যান্য শাখায় আমার অভিজ্ঞতা কিছুমাত্র নেই। একজন সামান্য সাহিত্যকর্মী হিসেবে এটুকু আমাকে অন্তত জানতে হয়েছে যে, কোনো লেখকের ভাষারীতি যথাসম্ভব প্রাতিস্বিক হওয়াই জরুরি, পূর্বজ কথাকারদের ভাষারীতির প্রভাব যথাসম্ভব অতিক্রম করাই কাঙ্ক্ষিত, অন্তত সেটাই সাহিত্য-সম্পর্কিত সকলের আন্তরিক দাবি ও অনুদেশ। অন্যদিকে সাহিত্যের মুগ্ধ পাঠকদের ভাবোচ্ছ্বাসে অনেক সময় এমন শংসাবাক্য লেখকেরা পেয়ে থাকেন: আপনার লেখার ভাষা পড়লে আমার সতীনাথ ভাদুড়িকে মনে পড়ে। লেখক ভেবে পান না, এই শংসাবাক্য নিয়ে তিনি কোথায় রাখবেন। পাঠক অবশ্য তাঁর ভালোলাগাটুকুই এখানে সরল মনে জ্ঞাপন করেছেন, হয়তো শ্রেষ্ঠ যেকোনো লেখাই ওই পাঠকের কাছে ‘সতীনাথ ভাদুড়ি’। অর্থাৎ ওই নামটাই হয়তো ওই পাঠকের কাছে রচনানৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু এতে বিড়ম্বিত বোধ করেন লেখক। তাঁর মনে হয় তবে কি তিনি নিজস্ব ভাষারীতি নির্মাণ করতে পারেননি? এখনও তাঁর ভাষায় ভর করে আছে তাঁর প্রিয় কথাকারের ভাষারীতি? সম্প্রতি এক প্রবীণ প্রতিষ্ঠিত কথাকারকেও লাজুক লাজুক মুখে ‘না, না’ করে উঠতে আমি দেখেছি, যখন তিনি তাঁর কোনো পাঠকের দ্বারা তুলিত হচ্ছিলেন বিভূতিভূষণের সঙ্গে। পরে দেখলাম, তিনি তাঁর লিখিত বয়ানে কেন তাঁর ভাষারীতি বিভূতিভূষণের ভাষারীতি নয়, তা নিয়ে বেশ একটি নাতিদীর্ঘ সওয়াল জবাব পেশ করেছেন।
সত্যি কথা বলতে কী, এ নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবার আছে বলে আমি মনে করি না। একজন লেখকের ব্যক্তিত্ব যদি প্রবল না হয়, তিনি যদি কাগজ-কলমে হাত ছোঁয়ানোর আগে নিজস্ব ভুবনের সন্ধান না পেয়ে থাকেন, অন্য সব প্রিয় কথাকারদের লেখা পড়বার পরেও তাঁর নিজের জীবনযাপন ও যাপন-উদ্ভূত অভিজ্ঞতার কাছে সরে আসার দাপট যদি তাঁর না থাকে, তাহলে তাঁর কলম ধরাই উচিত নয় বলে আমি মনে করি। আর ওগুলো যদি তাঁর থাকে, অর্থাৎ প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বানুভব এবং নিজ অভিজ্ঞতার কাছে ফিরে আসার দাপট যদি তাঁর থাকে, তবে প্রাথমিকভাবে পূর্বজ লেখকদের ভাষাগত প্রভাব তাঁর লেখায় কিছু কিছু থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজস্ব ভাষারীতি গনগনে আঁচে স্যাঁকা লোহা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা স্ফুলিঙ্গের মতো নির্ঘাত ফুটে উঠবেই।
কিন্তু এ রচনায় আমার চিন্তা-উদ্রেককারী বিষয় ঠিক সেটা নয়। তাহলে কী? সেটাই এবার বলছি।
এ পর্যন্ত যা লিখেছি, যদি আরেকবার সাবধানে পড়ে দেখেন, তাহলে বুঝবেন, এই সবকিছুর মধ্যেই একটা অপ্রমাণিত প্রতিজ্ঞা বা আনপ্রুভড অ্যাজামশন আছে। সেটা হচ্ছে, প্রত্যেক লেখকের যেন একটা একটা করে ভাষারীতি আছে।
হ্যাঁ, এমনই মনে করা হয়। মনে করা হয়, প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব ভাষারীতি আছে আর সেজন্যই তরুণ লেখককে বলা হয়, তিনি যেন অন্য কারও ভাষারীতির অনুকরণ না করেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আমরা একটু বেশি কিছু ধরে নিইনি তো? যাকে আমরা ‘কোনো লেখকের বিশিষ্ট ভাষারীতি’ বলে চিহ্নিত করতে চাইছি, তা আসলে ওই লেখকের বাগ্ভঙ্গিমা মাত্র নয় তো?
বাগ্ভঙ্গিমা মানে আপনি যেভাবে কথা বলেন। অবিকল সেটাই যে আপনি লিখতে পারেন, তা হয়তো নয়। তবু আপনার লিখনের সঙ্গে কথনের কোথাও একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। আপনার নিজস্ব কণ্ঠস্বর আপনার লিখিত বয়ানের পেছন থেকে নাটকের প্রম্পটারের মতো কথা জুগিয়ে চলেই। আপনি সেই প্রম্পটারের সব পরামর্শ মানেন না। খানিক রাখেন, খানিক বাতিল করে দেন। তবু আপনার লিখিত বয়ানের পেছনে লুকিয়ে থাকে আপনার কথনশৈলী, আপনার ব্যক্তিত্ব বা আরও পরিষ্কার করে বললে আপনারই চিন্তন বিশ্ব। লেখকের পেছনে লুকিয়ে থাকা ওই প্রম্পটারকেই আমরা লেখকের স্বতন্ত্র ভাষারীতি বলে ভুল করছি না তো?
কেননা, ভাষারীতি মানে শুধু ওই প্রম্পটার নয়। ব্যক্তিত্ব, কথনশৈলী, চিন্তন-সাম্রাজ্যটুকুই নয়। ভাষারীতি হল এক বিশিষ্ট শব্দরাজ্য, যা একজন লেখকের দীর্ঘদিনের সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। শুধু সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়েই নয়, প্রতিদিনের কথোপকথন থেকে, আড্ডা থেকে, তর্কবিতর্ক থেকে, জীবনের অনন্ত ক্রিয়াবিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে ওই শব্দভাণ্ডার গঠিত হয় এবং প্রাসঙ্গিক স্থলে প্রযুক্ত হয়।
এই ‘প্রাসঙ্গিক স্থলে প্রযুক্ত হয়’ কথাটা এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের সঙ্গে জগতের ক্রিয়াবিক্রিয়া, সংঘর্ষ, মিথস্ক্রিয়া সব মানুষের ক্ষেত্রেই চলতে থাকে এবং তার ফলস্বরূপ প্রত্যেক মানুষই একেকটি শব্দভাণ্ডার নিজের মগজে বহন করে নিয়ে চলছেন। সে তিনি লেখক হোন বা না হোন, প্রত্যেক মানুষেরই আছে নিজস্ব অর্জিত শব্দভাণ্ডার। কিন্তু একজন লেখকের ক্ষেত্রে বিশেষ এই, তাঁকে ওই শব্দভাণ্ডার তাঁর রচয়মান প্রসঙ্গে যথাযথ প্রয়োগ করতে হয়। সহজ করে বললে, একজন লেখককে একটি লেখায় সেই সব শব্দই বেছে নিতে হয়, যা দিয়ে তিনি ওই লেখাটির বিষয়বস্তুর যথাযথ অ্যামবিয়েন্স বা আবহ তৈরি করতে পারেন।
ধরুন, কলকাতা থেকে অনেক দূরে জামতাড়ায় কিংবা শালবনীর আরণ্যক পরিবেশে যে মানুষেরা রয়েছেন, আমি তাঁদের নিয়ে কিছু লিখতে চাই। তাহলে সেখানকার অভিজ্ঞতা আমার থাকা চাই। ফাঁকিবাজি করলে চলে না। তাছাড়া সেখানকার পরিবেশ, মানুষজনের প্রতি আমার ভালোবাসা থাকা চাই। অর্থাৎ বর্ণিতব্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ থাকা খুবই জরুরি। এই অভিজ্ঞতা আর অনুরাগ যদি আমার থাকে, তাহলে জামতাড়া বা শালবনীতে বহমান জীবনের ভাষা এমনিতেই আমার কলমে এসে ভর করবে। কিন্তু তা না করে, যদি আমি কলকাতার ভাষারীতি অবলম্বন করে কৃত্রিমভাবে জামতাড়া বা শালবনীর কথা লিখি, তাহলে তা কোনোমতেই ওই বিশিষ্ট বিষয়বস্তুর আবহ তৈরি করতে পারবে না, পাঠকের মনেও তা জাগাতে পারবে না কোনো কাঙ্ক্ষিত ঘোর। মোটের ওপর সেই লেখাকে আমি অন্তত যথেষ্ট সৎ লেখা বলতে পারব না।
অর্থাৎ জামতাড়া বা শালবনী-জীবনের আছে একটি নিজস্ব ভাষা, যে ভাষাতেই একমাত্র এতদ্বিষয়ক সাহিত্য রচনা সম্ভব।
এই পর্যন্ত লিখে একটা কূট প্রশ্ন করা যাক। ধরা যাক, কোনো উপন্যাসে টোকিয়ো শহরের কাহিনি বর্ণিত হচ্ছে। এবার সেক্ষেত্রে লেখক কোন ভাষায় লিখবেন? জাপানি ভাষায়?
না, সে সংশয় অমূলক। লেখক বাংলা ভাষায় উপন্যাস লিখতে বসেছেন এমন যদি হয়, তাহলে টোকিয়ো শহর-কেন্দ্রিক তার আখ্যানটিও তিনি বাংলাভাষাতেই লিখবেন। কিন্তু সে কি হতে পারে একান্তই আটপৌরে বাংলা—যেমন বাংলায় আমি এই লেখাটি এখন লিখছি? আমি তা মনে করি না। আমি মনে করি, সেই বাংলাভাষার মধ্যেও এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করতে হবে যা জাপানের জীবন, সমাজ, প্রকৃতি-সংশ্লিষ্ট। যেসব শব্দ বর্ণিতব্য জাপ-জীবনের আবহ তৈরি করতে পারে। এবং এই শব্দগুলোর ব্যবহার কৃত্রিমভাবে করলে চলবে না, এই শব্দ ব্যবহার স্বতঃস্ফূর্ত হবে, যদি আমি বর্ণিতব্য বিষয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকি, যদি তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে থাকি পূর্বাহ্নেই।
এই প্রশ্নটাকেই ঘুরিয়ে অনেকে করে থাকেন ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাসের প্রসঙ্গে। ধরা যাক, পাল-যুগের ইতিহাসকে আধার করে আমি একটা উপন্যাস লিখতে চাই। কাল—সম্রাট নয়পালের শাসনকাল। স্থান—মগধ। তাহলে ওই স্থানে এবং ওই কালে মানুষ কোন ভাষায় কথা বলতেন? নিশ্চয়ই বাংলায় নয়। তাঁরা কথা বলতেন মাগধীতে বা অর্ধমাগধীতে। এখন আমি যে উপন্যাস লিখছি, তা তো আমি আর অর্ধমাগধীতে লিখব না, বাংলায় লিখব। বর্ণিতব্য আখ্যানের পাত্রপাত্রীর ভাষা তো এক্ষেত্রে বাংলা ভাষার আওতার বাইরে। সুতরাং, অন্তত এই ক্ষেত্রে যেমন খুশি বাংলায় আমি লিখতে পারি, এমনকি একুশ শতকের কলকাত্তাইয়া বাংলাতেও লিখতে পারি—এই কথা ভেবে এক শ্রেণির লেখক খুব আমোদ পান।
তা পানগে। প্রত্যেকেরই নিজের খুশিমতো চিন্তা করার অধিকার আছে, কাজ করার অধিকার আছে, আমোদ-আহ্লাদ করবারও অধিকার আছে। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে আমি নিজে যখন ভাবতে বসি, তখন এই যেমন-খুশি-লেখো-র তত্ত্বে আমার মন কিছুতেই সায় দেয় না। আমাকে যদি পালযুগের মগধের কোনো আখ্যান লিখতে হয়, তবে সেই সময়কার ইতিহাস, সমাজব্যবস্থা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলা, ধর্মচিন্তা সম্পর্কে সানুরাগ অধ্যয়ন করতে হবে। সেই নিমজ্জিত অধ্যয়ন হতে হবে দীর্ঘকালীন এবং সুগভীর। এতটাই গভীর, যাতে আমি মানসিকভাবে দীর্ঘকাল সেই কালের ঘটনা, রূপাবলী ও চরিত্রাবলীর সঙ্গে বসবাস করতে পারি, মনে মনে সেযুগের পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারি। এটা প্রায় ধ্যানের মতই। হ্যাঁ, ধ্যানের মতই। আর তা যদি আমি পারি, তাহলে সেযুগের কথা লিখতে বসলে স্বতঃস্ফুর্তভাবেই এমন একটা বাংলা আমার কলমে উঠে আসবে, যা ওই বিষয়ের ওপর সুচিন্তিত সুবিচার করতে পারে। সে কখনই আজকের কলকাতার বাংলা নয়, সে হচ্ছে ওই বিষয়ানুগ বাংলা।
মনে রাখতে হবে, চলচ্চিত্রকারের হাতে গ্রে স্কেল, সেপিয়া টোন, সাদা-কালো প্রভৃতি অনেক উপায় আছে, যা দিয়ে তিনি যে অতীতের কোনো কাহিনি নির্মাণ করছেন, তা বুঝিয়ে দিতে পারেন দর্শককে। লেখকের হাতে ওসব কিচ্ছু নেই। তাঁর হাতে আছে শুধু ভাষা। সেই ভাষা দিয়েই তাঁকে অতীত-কালের বিশেষ আবহ নির্মাণ করতে হয়।
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসের সাফল্যের কারণ, তাঁর উপন্যাসের ওই ভাষা। ওই ভাষাতেই ঠিকঠাক ওই সময়টা দেখা যায়। একই শরদিন্দুবাবু ব্যোমকেশ-কাহিনি লিখেছেন, আবার ইতিহাসনির্ভর আখ্যানও লিখেছেন। তাঁর ব্যোমকেশের গল্পগুলোর ভাষা কি তাঁর ইতিহাসাশ্রিত আখ্যানের ভাষার সঙ্গে এক? মোটেই না। দুটোই সাধুভাষা হলেও, তারা এক নয়। ইতিহাস-নির্ভর আখ্যানের ভাষা অনেক অনেক বেশি ইতিহাসগন্ধী। আবার শরদিন্দুবাবুর ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’, ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’, ‘চুয়াচন্দন’ কিংবা ‘বাঘের বাচ্চা’- এদের সকলের ভাষা সাধু বাংলা হলেও এবং প্রত্যেকটিই ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস বা গল্প হলেও এদের প্রত্যেকটির ভাষারীতি আলাদা আলাদা। ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ আলাউদ্দিন খিলজির সময়কার কাহিনি। ওই লেখায় বোরকা, ডালিম, খাসা, মুলুক, উজবুক, চুটকি, শরাব, খুবসুরৎ, বিবি, মুসাফিরখানা প্রভৃতি বহু আরবি শব্দ উঠে এসেছে। ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ সম্রাট নয়পাল ও অতীশ দীপংকরের সময়নির্ভর কাহিনি। সেখানে বৌদ্ধ যুগের বহু শব্দ, যেমন—বংগাল, বরাঢ়ী, মুদ্গগিরি, বিহার, ভল্ল, কপিত্থ, পরিষৎ ইত্যাদি এসে ঢুকেছে। ‘চুয়াচন্দন’ গল্প শ্রীচৈতন্য ও কানা রঘুনাথের সময়নির্ভর। সেখানে ষোড়শ শতকোপযোগী তৎসম, তৎভব, দেশি, বিদেশি সব রকম শব্দেরই মেলা বসেছে। কাঁচুলি, রজ্জু, নিপাতনে সিদ্ধ, হরিচরণস্রুত, বাজিকর, আঁচড়া-কামড়ি, ডিঙ্গা, চুয়া, রাঙাপাড়, বাতাসা, শাস্ত্রীয়, হুড়াহুড়ি, হুমকি, বজরা, তঙ্কা, ফরমাশী, হয়রানি প্রভৃতি সব শ্রেণির শব্দ। আবার ‘বাঘের বাচ্চা’ শিবাজী-কেন্দ্রিক। সেখানে মারাঠা জাতির প্রাণপ্রাচুর্যের উপযোগী জোরদার শব্দ, আরবি শব্দ, হিন্দুস্থানী শব্দ দিব্বি এসেছে। হল্লা, চোলিমে ছিপাউঁ কৈসে যোবনা মোরি, দাদো, মজলিস, কিংখাপ, হো শিব্বা, ওস্তাদ, ফাগ, চাঁদি, চালাক, সাঁজোয়া—এমন অনেক।
তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? ইতিহাসাশ্রয়ী গল্প বা উপন্যাসের ভাষা সাধুই হোক আর চলিতই হোক, তার শব্দ সমূহ নির্বাচিত হচ্ছে বর্ণিতব্য বিষয় অনুযায়ী; যে-সময়কে আশ্রয় করে ওই কাহিনি নির্মিত, সেই সময়োপযোগী এক বিশেষ ধরনের ভাষা ওই কাহিনিকে সার্থকভাবে রূপ দিতে পারে, অন্য ধরনের ভাষায় তার রূপ তেমন খোলে না।
এখন যদি আরেকটি কূট প্রশ্ন তোলা যায়? ধরা যাক, ক-বাবু ও খ-বাবু—দুজন লেখক। দুজনেই হয়তো পাল যুগকে আশ্রয় করে উপন্যাস লিখছেন। সেক্ষেত্রে দুজনের লেখার ভাষা কি তবে এক হবে, যেহেতু উভয়েই একই কালের ইতিহাসকে আশ্রয় করেছেন? না, তা হয় না। হয় না, তার কারণ, ক-বাবু ও খ-বাবু দুজনে একই মানসিক পদ্ধতিতে, একই গভীরতা সহকারে পালযুগের ইতিহাসের ওপর মনঃসংযোগ করতে পারেন না। দুজনের মনের গঠন আলাদা, দুজনের ব্যক্তিত্ব, কথনশৈলী, চিন্তন-সাম্রাজ্য আলাদা। অর্থাৎ এই লেখার শুরুতে যে ‘প্রম্পটার’-এর কথা বলেছিলাম, সেই কথাই আবার আসে। ক-বাবুর লেখার পেছনে যে-প্রম্পটারটি দাঁড়িয়ে আছে আর খ-বাবুর লেখার পেছনে যে-প্রম্পটারটি আছে, ওই দুজন প্রম্পটার এক নয় বলেই একই কাল আশ্রয় করে ক-বাবু ও খ-বাবু দুজনে দুটো উপন্যাস লিখলেও, ওই দুয়ের ভাষারীতি এক হয় না। কিন্তু উভয় ভাষারীতিই পাল-সাম্রাজ্যের কালোপযোগী নির্মাণ হতে হবে, যদি দুজনের উপন্যাসকেই সার্থক হতে হয়।
কিন্তু এর মানে এই নয় যে, ক-বাবু ও খ-বাবু দুটি বিশিষ্ট ভাষারীতির অধিকারী। ভাষারীতিটি আসছে বর্ণিতব্য বিষয় থেকে। দুটি লেখায় ভাষার তফাৎ হচ্ছে ওঁদের দুজনের মনঃসংযোগের সামর্থ্য, রুচি, ব্যক্তিত্ব, কথনশৈলী, চিন্তন-সাম্রাজ্যের পার্থক্যের জন্য। ক এবং খ যদি দুই ভিন্ন সময়ের লেখক হন, তবে দুজনের পার্থিব অস্তিত্বের কালিক ব্যবধানও একই বিষয় নিয়ে দুজনের লেখার ভাষায় প্রভেদ আনতে পারে। কিন্তু লেখকের ব্যক্তিত্ব, কথনশৈলী, চিন্তন-সাম্রাজ্য, পার্থিব অস্তিত্বের কালিক মাত্রা প্রভৃতি আর যাই হোক, উপন্যাস বা গল্পের ভাষারীতি নয়। ভাষারীতির বিজ্ঞান আলাদা। তার উৎস লেখার বিষয়। তার উৎস লেখকের ব্যক্তিস্বরূপ নয় বলেই আমি মনে করি।
প্রতিটি উপন্যাস, গল্প বা আখ্যানেই একজন গল্পকথক থাকেন। সেই গল্পকথক একটি চরিত্রের রূপ ধরে আসতে পারেন, অথবা নাও পারেন। যাকে আমরা বলি লেখকের বয়ান। আর ওই আখ্যানে অন্য যে সব চরিত্র থাকেন, তাঁরা যখন কথা বলছেন, তখন তাঁদের কথোপকথন থেকে গড়ে ওঠে সংলাপ। এখন চরিত্রগুলির এই সংলাপের ভাষা আর গল্পকথকের ভাষা এক হতে পারে কী করে? লেখক যে ভাষায় গল্প লিখছেন, যদি সেই একই ভাষায় গল্পের চরিত্রগুলোর সংলাপও রচিত হয়, তাহলে উক্তিচিহ্নের ব্যবহার ছাড়া ওদের আলাদা করা যাবে না। সেটা হয়ে উঠবে ওই রচনার একটা বড়ো রকমের দুর্বলতা। এই দুর্বলতার বিপরীতে সবল সাহিত্যকৃতি কেমন হতে পারে, তার একটা ছোটো অনায়াসলব্ধ উদাহরণ দিই—
বেতসী বিরক্তিভরে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—আ গেল! অত হাসছিস কেন?
‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ থেকে নেওয়া এই বাক্যটিতে কোনটা কাহিনি-কথকের ভাষা আর কোনটা বেতসী নামের চরিত্রটির ভাষা বুঝতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। কাহিনি-কথকের ভাষা সাধু ক্রিয়াপদ ও সাধু সর্বনাম-খচিত। তাহাকে, ঠেলিয়া, দিয়া, বলিল। আর বেতসীর মুখের কথা চলিত ভাষায় লেখা এবং তারই চরিত্রের অনুরূপ স্বভাবতরল। আ, হাসছিস। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক সমগ্রে এখানে উক্তি চিহ্ন ছিল। আমি ইচ্ছে করেই সেই উক্তি চিহ্ন তুলে দিলাম। তুলে দিলাম শুধু এটাই দেখানোর জন্য যে, কাহিনি-কথকের ভাষা ও চরিত্রের মুখের সংলাপের ভাষা—এই দুই যদি সচেতনভাবে আলাদা করে লেখা হয়, তাহলে এই উক্তি চিহ্ন বসানোটা একটা বাহুল্য ছাড়া কিছুই নয়।
তারপর ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মুখের ভাষা। যথাসম্ভব সেগুলো আলাদা হওয়াই উচিত। রাজাও যে ভাষায় কথা বলছে, রাণীও যদি সেই ভাষাতেই কথা বলে, কিংকর-কিংকরী-দৌবারিক, শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সক্কলেই যদি সেই একই ভাষায় কথা বলে, তাহলেই তো মুশকিল! কেননা তা বাস্তবানুগ নয়। দুটি মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি, অভিজ্ঞতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থান সবই যেখানে আলাদা আলাদা, সেখানে উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই সেই এক কাহিনিকথকের ভাষাতেই পাতার পর পাতা কথা বলে বলে কথার তাজমহল গড়ে চললে কোনোমতেই তা বাস্তবসম্মত হয় না। আমি এখানে একখুনি খুব বড়ো বড়ো কিংবদন্তী লেখকের নাম বলতে পারি, যাঁদের লেখার এই গোলমালটা লাইন তুলে তুলে আমি দেখাতে পারি। কিন্তু তা আমি করব না। কী দরকার? তাঁরা সব আইকনিক ফিগার, আর তাই তাঁদের লেখা থেকে এই গোলমালটা উদাহরণ হিসেবে দেখালে অনেক মানুষ রে-রে করে উঠবেন। তাতে আমার উদ্দেশ্য পণ্ড হবে ।
আমাদের দেশ ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে কিন্তু এই গোলমাল, এই মুশকিল ছিল না। চরিত্ররা নিজ নিজ সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী তাঁদের পক্ষে যে-ভাষায় কথা বলা স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্মত, সেই ভাষাতেই কথা বলে উঠতেন। অজস্র উদাহরণ আছে। তার মধ্য থেকে নজির হিসেবে একটি সুপরিচিত উদাহরণই দিই—
গৌতমী।। অজ্জ, কিংপি বত্তুকামম্হি। ণ মে বঅণাবসরো অত্থি।…
শকুন্তলা।। কিং ণু ক্খু অজ্জউত্তো ভণাদি?
রাজা।। কিমিদমুপন্যস্তম্?
শকুন্তলা।। পাবও ক্খু বঅণোবণ্ণাসো।
শার্ঙ্গরবঃ।। কথমিদং নাম? ভবন্ত এব সুতরাং লোকবৃত্তান্তনিষ্ণাতাঃ। … (অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, ৫ম অঙ্ক)
এখন এখানে গৌতমী ও শকুন্তলা প্রাকৃত ভাষায় কথা বলছেন। কিন্তু রাজা ও শার্ঙ্গরব সংস্কৃত ভাষায় কথা বলছেন। শকুন্তলা ও গৌতমীর মতো মেয়েরাই যে এই নাটকে প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেন, তাই নয়। প্রতিহারী কিংবা বিদূষক, যাঁরা কিনা পুরুষ, তাঁরাও কিন্তু প্রাকৃতে কথা বলেন, সংস্কৃতে নয়। প্রতিহারী প্রাকৃত ভাষায় কথা বললেও অপর রাজকর্মচারী কঞ্চুকী সংস্কৃতে কথা বলেন, কারণ তিনি উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ।
চরিত্রগুলির সামাজিক অবস্থান ও প্রকৃতিভেদে ভাষাভেদ করা হয়েছে।
কেউ যদি বলেন, এ হল নাটক। এ তো উপন্যাস নয়। উপন্যাস অনেক আধুনিক ব্যাপার। কাজেই নাটকে চরিত্রভেদে ভাষাভেদ করা হলেও উপন্যাসে ও তেমন জরুরি কিছু ব্যাপার নয়। এই আপত্তির উত্তরে বলা যায়, উপন্যাস সাহিত্যের আধুনিকতম অভিব্যক্তি বলেই তা তার পূর্ববর্তী সমস্ত সাহিত্য-অভিব্যক্তিকে আত্মসাৎ করেছে। কবিতা, নিবন্ধ, কথা, আখ্যান, নাটক, মহাকাব্য—এই সব কিছুকেই উপন্যাস আত্তীকৃত করে থাকে। উপন্যাসে চরিত্রসমূহের ভিতর যে সংলাপ রচিত হয়, তার ধরন অবশ্যই নাট্যিক উপাদানে সমৃদ্ধ এবং সেই কারণেই সেই সংলাপে চরিত্রভেদে ভাষাভেদ থাকা জরুরি।
আরেকধরনের আপত্তি উঠতে পারে। কেউ বলতে পারেন, কালিদাস প্রভৃতি নাট্যকার সমাজে শ্রেণি-বৈষম্যকে জিইয়ে রাখতে চেয়েছিলেন বলেই নারী ও নিম্নপদাধিকারী রাজকর্মচারীদের মুখে প্রাকৃত ভাষা বসিয়েছেন আর উচ্চ বর্ণের পুরুষ বা উচ্চপদাধিকারীদের মুখে সংস্কৃত ভাষা বসিয়েছেন। এমন ভাষাবৈষম্য আসলে তাঁদের শ্রেণি-বৈষম্যের পক্ষপাতপুষ্ট মনের ফলাফল।
এর উত্তরে আমি প্রথমেই বলব, কালিদাস, শেকসপীয়র বা তারও পূর্ববর্তী সোফোক্লিস প্রভৃতিদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে দেখা হয়নি! এবং নাট্যিক উপাদান ছাড়া তাঁদের চিন্তাভাবনার মানচিত্র আমার কাছে অপরিজ্ঞাত হওয়ায় তাঁরা শ্রেণি-বৈষম্যে বিশ্বাস করতেন কি করতেন না, আমি জানতে পারিনি। বা সেই বিশ্বাস কতটা বদ্ধমূল ছিল, আমাদের পক্ষে তা নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব নয়। তার পরেও তর্কের খাতিরে না হয় মেনেই নিলাম, ওই প্রাচীন নাট্যকারেরা শ্রেণি-বৈষম্যে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এখন একটি সরল প্রশ্ন করব। ধরা যাক, আপনি একজন ঔপন্যাসিক এবং আপনি সমাজের এই শ্রেণি-বৈষম্যকে ঘৃণা করেন। আপনি স্বপ্ন দেখেন একদিন শোষণমুক্ত শ্রেণিহীন সমাজ তৈরি হবে। এবার আপনি চোখ তুলে একবার চারিপাশে তাকান। আপনার চারিপাশে কি আপনি শ্রেণিহীন সমাজ দেখতে পাচ্ছেন? পাচ্ছেন না। চারিপাশেই অমানবিক নিষ্ঠুরতা, শ্রেণি-উপশ্রেণিতে উপন্যস্ত এক ভয়ানক সমাজের ছবিই আপনি দেখছেন। তাহলে একজন দায়িত্ববান লেখক হিসেবে আপনার উচিত হবে এই ভয়ানক ছবিকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুপুঙ্খ তুলে ধরা। যাতে মানুষ এ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং এর সমাধানের পথ খোঁজে। যাতে শুরু হয় শ্রেণি-সংগ্রাম, যার অন্তিম ফল হয়তো শ্রেণিহীন সমাজ। অসুখকে চিহ্নিত করতে না পারলে ওষুধের খোঁজ পড়ে না। কাজেই শ্রেণি-বৈষম্যে ভরপুর এই সমাজের ছবি যদি আপনাকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে আঁকতে হয়, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন আর্থসামাজিক অবস্থানে অবস্থিত চরিত্রগুলির মুখে যে সংলাপ বসাবেন, সেগুলো সেই সেই শ্রেণির মানুষের উপযুক্ত মুখের ভাষা ছাড়া অন্য কিছু কীভাবে হবে?
কিন্তু আশ্চর্য এই, আমাদের রেনেসাঁ-দীক্ষিত অনেক মহান ঔপন্যাসিকও এই সহজ কথাটা সব সময় ধরতে পারেননি। তাঁদের উপন্যাসে সব চরিত্র একই ভাষায় কথা বলে। এবং উপন্যাসের কথক-ঠাকুরটিও সেই একই ভাষায় কথা বলেন। লেখার বিষয় ও মুড পালটে গেলে যে লেখার ভাষাও পালটে যায়, এই কথা দুঃখজনকভাবে অনেক গদ্যকারই বুঝতে চাননি। আজও বোঝেন না অনেকে। অথচ আশ্চর্য এই, পরিশীলিত বাংলা গদ্যের যিনি আদি রূপকার, সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে এ ব্যাপারটা জলের মতো স্পষ্ট ছিল। নীচের নমুনাগুলো দেখলেই বোঝা যায়, প্রসঙ্গভেদে তিনি কেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাষারীতি প্রয়োগ করেছেন—
মায়াসঞ্চারের ভাষা:
কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে… এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, বৎস! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে… সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতিরোধ করিতেছে। (শকুন্তলা)
হাসিঠাট্টা-ফচকিমির ভাষা:
বিদ্যাধর চিরঞ্জীবকে বলিল, বাবু! তোমার হাতটা দাও, নাড়ীর গতি কিরূপ দেখিব। চিরঞ্জীব যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া বলিলেন, এই আমার হাত তুমি কানটি বাড়াইয়া দাও। (ভ্রান্তিবিলাস)
প্রণয়কোমলতার ভাষা:
রাজা, দেখিয়া শুনিয়া, প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই সেই কণ্বতনয়া শকুন্তলা! মহর্ষি অতি অবিবেচক; এমন শরীরে কেমন করিয়া বল্কল পরাইয়াছেন। (শকুন্তলা)
বর্ণনার ভাষা:
ক) মানবীর বর্ণনা—
শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার সম্পূর্ণ আবির্ভাব; বাহুযুগল কোমল বিটপের বিচিত্র শোভায় বিভূষিত; আর, নব যৌবন, বিকশিত কুসুমরাশির ন্যায়, সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। (শকুন্তলা, প্রথম পরিচ্ছেদ)
খ) প্রকৃতির বর্ণনা—
লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে। (সীতার বনবাস, প্রথম পরিচ্ছেদ, আলেখ্য দর্শন)
শ্লেষ বিদ্রূপের অর্থাৎ খিল্লি করার ভাষা:
এই কয় প্রশ্নের উত্তর পাইলেই, বিদ্যারত্ন ও কপিরত্ন, উভয় খুড় মহাশয়ের সঙ্গে, নানা রঙ্গে, হুড়হুড়ি ও গুঁতোগুঁতি আরম্ভ করিব। প্রশ্নের উত্তর পাইলে, হাঙ্গাম ও ফেসাৎ উপস্থিত করিবেক, এমন স্থলে উত্তর না দেওয়াই ভাল, এই ভাবিয়া, চালাকি করিয়া, লেজ গুটাইয়া, বসিয়া থাকিলে আমি ছাড়িব না। (ব্রজবিলাস)
এইসব পর্যবেক্ষণ থেকে এবার আমরা এই সিদ্ধান্তই টানতে পারি যে, বস্তুত ‘লেখকের ভাষা’ বলে কিছু নেই। যা আছে, তা হল বর্ণিতব্য বিষয়ের ভাষা, বর্ণিত চরিত্রদের ভাষা। প্রতিটি বিষয় যেন এক একটা বিষাক্ত মাকড়সা, যা লেখকের সংবেদনশীল, অনুরক্ত মনকে সরু সরু তীক্ষ্ণ নলাকার পা দিয়ে আক্রমণ করে। হুল বিঁধিয়ে সেই নালিকাপথে বর্ণিতব্য বিষয় তার বিষ ঢেলে দেয় লেখকের মনের মধ্যে। আক্রান্ত লেখক সেই ভয়ানক নীল বিষে আবিষ্ট হয়ে কিছু কথা উচ্চারণ করে চলেন। সেগুলোই হয়ে ওঠে ওই লেখার ভাষা। সে ভাষা কিন্তু আসলে ওই বর্ণিতব্য বিষয়ের ভাষা। লেখকের নয়।
তাহলে ‘লেখকের ভাষা’র ধারণা এসেছে কেন? এসেছে, কেননা পরিসংখ্যানের বিচারে সাহিত্যসংসারে, বিশেষত বাংলা সাহিত্যে একগামী লেখকের সংখ্যা বেশি। একগামী লেখক হলেন তিনিই, যিনি দিনের পর দিন, হয়তো সারা জীবন একই বিষয় নিয়ে লিখে যান। একটির পর একটি বই। আর বহুগামী লেখক হলেন সেই লেখক, যিনি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যান; তাঁর রচনাগুলো বিচিত্র বিষয়মুখী হয়ে থাকে। কিন্তু বহুগামী লেখকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। লেখকের একগামিতার বহুবিধ কারণ থাকতে পারে, তার মধ্যে প্রধান তিনটি কারণ—
ক) লেখকের বহুমুখী প্রতিভার অভাব। প্রতিভা বহুমুখী না হওয়ায় আগ্রহ বহু বিষয়ে থাকে না। এক বিষয় নিয়েই সারা জীবন লিখে চলেন। অথবা;
খ) লেখক বিষয়বিশেষে আসক্ত। এতটাই আসক্ত যে তাঁর প্রিয় বিষয়ের বাইরে চোখ তুলে তাকানোর ক্ষমতাও হারিয়ে গেছে। কম্ফর্ট জোনের মধ্যে লিখতে লিখতে কখন যে নিজেই নিজের কণ্ঠস্বর নকল করে চলেছেন, আর বুঝতে পারেন না। অথবা;
গ) লেখক বিষয়-বিশেষের প্রতি দায়বদ্ধ। এই লেখক আদর্শবান লেখক। তাঁর সেই আদর্শটিই তাঁর একমাত্র বিষয়, তাঁর একমাত্র দায়। এই আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠার কারণে দিনের পর দিন, হয়তো সারা জীবন ওই বিষয় বা ওই প্রসঙ্গের ধারেপাশেই তাঁর সব লেখা আবর্তিত হতে থাকে।
যে কারণেই হোক, এই একগামী লেখকের লেখার মধ্য দিয়ে একই বিষয় বারংবার অভিব্যক্ত হতে থাকে। যেহেতু বিষয় এক, তাই প্রায় একইরকম ভাষারীতিতে তা লিখিত হতে থাকে। এর ফলে একগামী ‘লেখকের একটা বিশিষ্ট ভাষারীতি’ আছে, এমন ইল্যুশন তৈরি হয়। এবং বাংলা সাহিত্যে এই একগামী লেখকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায়, অমুক লেখকের ভাষা, তমুক লেখকের ভাষা, একেকজন লেখকের একেক প্রকার ভাষারীতির ধারণা চালু হয়ে গেছে। প্রকৃতার্থে লেখকের কোনো ভাষা নেই। যা আছে, তা আসলে বিশেষ কোনো লেখার ভাষা, বিষয়ের ভাষা। লেখক বিষয় পরিবর্তন না করায় ওকেই লেখকের ভাষা বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

