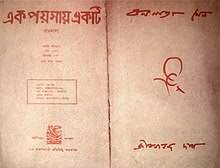
জীবনানন্দ ক্রোড়পত্র– সব্যসাচী মজুমদার
একটা কবিতা পাঠ : আট বছর আগের একদিন
১.
জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ ব্যতিত এতটা আলোচনা সম্ভবত কোনও বাঙালি কবি সম্পর্কে হয়নি — বোধহয় এই কথাটি আমরা স্বীকার করতে দ্বিধা করব না। তবু, এই সময়ে, এই আলোচনায় অংশ নিয়ে মনে হচ্ছে যেন জীবনানন্দ সম্পর্কে সব কথা বলা হয়ে গেছে, অথবা এ তাবৎ কিছুই বলা হয়নি। অসম্ভব পিচ্ছিল এবং বহুস্তরিক জীবনানন্দ কবিতায় সিদ্ধান্তকে এতটাই বহুদূরে রেখেছেন, যাতে মনে হয়, তাঁর কবিতা অতটাই স্বচ্ছ এবং শুদ্ধ হয়ে উঠতে পেরেছে যে, নির্দিষ্ট কোনও আবিষ্কারে বা চিন্তায় তাঁর কবিতাকে স্পর্শ সম্ভব নয়। অনেকটা সেই চিন দেশীয় উপকথার ড্রাগন ওয়ারিয়রের জন্য ধার্য ম্যাজিক স্ক্রোলটির মতো। মন্ত্রহীন, ক্রিয়া পদ্ধতি শূন্য একটি স্বচ্ছ ক্ষেত্র। যে ক্ষেত্রে লেখা নেই,আঁকা নেই কিছু। কেবল তার দিকে তাকালে দর্শক তাঁর মুখখানিই দেখতে পান। কেবল নিজের মুখখানিই…
মনে হয়, জীবনানন্দের কবিতার স্বভাব এরকমই। একমাত্রিক বা দ্বি-মাত্রিক কোনও ধারণায় দেখতে গেলে তার ক্রম বিবর্তনের রূপটিকে সন্ধান অসম্ভব। অবিরত বিনির্মাণপ্রার্থী অক্ষরবিন্যাসগুলি নতুন নতুন পাঠে এক একটি স্তরের উন্মোচনকে স্পর্শ করে। আবার উন্মোচিত পাঠটিও পূণর্পাঠের সময় একই পাঠকের বিবর্তিত মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে নতুনতর স্পর্শ দিতে পারে। বলা ভাল, জীবনানন্দের কবিতা অন্তত এই পাঠকের কাছে একটি ‘ অবিশ্বাসের বাস্তব ‘। আমরা সম্ভবত বুদ্ধদেব বসুর কাছেই জীবনানন্দ পাঠের কারণে সবচেয়ে বেশি ঋণী। বুদ্ধদেব বাবুই সম্ভবত সর্বপ্রথম জীবনানন্দের কবিতার এই স্বভাবটিকে অনুমান করতে পেরেছিলেন। একারণেই হয়তো ‘ কবিতা ‘ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে লিখছেন,
” বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আসনটি ঠিক কোথায় সে – বিষয়ে এখনই মনস্থির করা সম্ভব নয়, তার কোনও প্রয়োজনও নেই এই মুহূর্তে; এই কাজের দায়িত্ব আমরা তুলে দিতে পারি আমাদের ঈর্ষাভাজন সেই সব নাবালকদের হাতে, যারা আজ প্রথমবার জীবনানন্দের স্বাদুতাময় আলো – অন্ধকারে অবগাহন করছে। “( কবিতা : বর্ষ ১৯ , সংখ্যা ২)
বুদ্ধদেব বাবুর এই মন্তব্যের শেষটুকু ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। বুদ্ধদেব নির্ভর করতে চেয়েছেন প্রতিটি সম্ভাব্য নতুন পাঠের ওপর। এমন এক একটি পাঠ যা ( ‘নাবালক’ শব্দটি লক্ষনীয়) পূর্বনির্ধারিত ধারণাশূন্য। যে পাঠ কবিতার সঙ্গে ব্যাক্তিমুদ্রাদোষকে মিলিয়ে নিতে পারে।
ঠিক এই ভরসাতে বক্ষ্যমাণ আলোচনায়, জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন উপলক্ষে ‘আবহমান’-এর আয়োজনে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও পরিচিত কবিতা ‘ আট বছর আগের একদিন ‘ পাঠের চেষ্টা করলাম। বুদ্ধদেব বসু থেকে ক্লিন্টন বি সিলি পর্যন্ত একাধিক বিদগ্ধ পাঠের পরেও এই চেষ্টা নিঃসন্দেহে নিজেরই মুদ্রাদোষকে নির্ণয়ের চেষ্টা।
তবে, শুরুতেই একটি তথ্য নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। রচনাটি ‘ কবিতা ‘ পত্রিকাতে চৈত্র ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।
‘ আট বছর আগের একদিন ‘ কবিতাটির বিষয়বস্তু ভীষণ স্পষ্ট। একজন মানুষ আত্মহত্যা করেছে। এমন অবস্থায় আত্মহত্যা করেছে, যে সময় তার জীবন সামাজিকভাবে পরিপূর্ণ। বস্তুত গৃহ, শিশু, বধু সম্পন্ন সে তথাকথিতভাবে ‘ সফল ‘ গৃহস্থ। তবে, কিসের প্ররোচনায় সে আত্ম হননের পথ বেছে নিল ! এই প্রশ্নের সম্মুখীন কবি একটি ঘটনাকে তার অন্তর্গত নির্মাণের মাধ্যমে দেখতে চেয়েছেন। এবং অনিশ্চিত ভাবনাস্রোতের বশীভূত হয়ে কখনও আত্মহত্যাকে, আত্মহত্যার অধিকারকে সমর্থন করেছেন। কখনও দূরে সরে গেছেন সেই চিন্তা, পরিস্থিতি থেকে। কাল ও ব্যাক্তি মানুষের পরস্পর দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে দেখতে চেয়েছেন মানুষের আত্মহত্যা ও আত্মহত্যার কারণগুলির পারম্পর্যকে। হয়তো নিজেও অনিশ্চিত ছিলেন ‘ আত্মহত্যা ‘ সম্পর্কে । এবং শেষতক একটি আপাত বিরোধী স্বরেও পুঁতে দিয়েছেন অনিশ্চিতির আভাস। এ প্রসঙ্গে যথা সময়ে আসা যাবে।
আপাতত ‘ আত্মহত্যা’ শব্দটিকে ভাবা যাক। জীবনের পরিস্থিতি মানুষকে প্ররোচিত করে তার তথাকথিত পরিণত মৃত্যুর কিংবা অসুখ জনিত মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে নিজের মাধ্যমে মৃত্যু সুনিশ্চিত করতে। মোটামুটিভাবে একেই, এই প্রবণতাকে ‘আত্মহত্যা’ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আবার পরিস্থিতি প্রতিকুল হলেই নয় আনুকুল্যও আত্মহত্যার জন্য মানুষকে প্ররোচিত করে। সে তার বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেয় এ বিষয়ে। যদিও সমাজের গঠনের আদি পর্ব থেকে জীবনের পক্ষে, বেঁচে থাকার পক্ষে এত নানাবিধ উচ্চারণ রয়েছে, যে, এই আত্ম হননের সিদ্ধান্ত এই সময়ের একজন মানুষকে গ্রহণ করতে হয় বিপুল বিরোধীতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এখন, যদি অধিকারের প্রশ্ন ওঠে, তবে, এ বিষয়ে আমরা এখানে কী একমত হতে পারি না, যে, আত্মহত্যা মানুষের একটি সমাজ প্রদত্ত স্বাভাবিক স্বভাব । এবং এই অধিকার রয়েছে সবারই। সকলেই বেছে নেবেন না সেই পথ। কিন্তু, যিনি বেছে নেবেন, তাকে, তার অধিকারকে অস্বীকার করা বোধহয় যায় না। সে যদি সমস্ত দায়িত্ব বোধ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায় ; সে যদি জায়মান উচ্চাবচতার সঙ্গে মিলিয়ে থাকতে না চায়, তবে তার অধিকারকে শাস্তিযোগ্য করে তোলা যায় না কখনও। নিবৃত্ত করার চেষ্টা অবশ্যই জারি রাখা যায়।
মনে রাখতে হবে , সমাজবদ্ধ হওয়ার পর সমাজের প্রতিটা মানুষই আসলে পুঁজির উপাদান এবং উৎস। ফলে পুঁজি, সামাজিক পুঁজি অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই চায় না তার আনুমানিক বৃদ্ধি কোনওভাবেই ব্যহত হোক। আত্মহত্যা সেই ব্যাঘাতের কাজটা করে। এই আত্মহত্যাকে এই কারণেই বিরোধীর ভূমিকায় রাখাটা মোটেই আপত্তিকর নয়। আবার আত্মহত্যার অধিকারকেও নয়। দুটোরই সমান তাৎপর্য আছে বলেই মনে হয়।
এখন, ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতায় এই একজন মানুষের একগাছা দড়ি হাতে অশ্বত্থের গাছে ঝুলে পড়াটাকে জীবনানন্দ অর্থাৎ তাঁর সময়ের প্রতিনিধিস্বরূপ মনস্তত্ত্ব কিভাবে দেখতে চাইছে— এভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে বিষয়টিকে। কবিতার শুরু হয়, একজন মানুষের মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়ার সংবাদের মাধ্যমে। অতঃপর আসে আত্মহননের কালীক বিবরণ। লোকটি নিজেকে মেরেছে।কখন মেরেছে ? যখন ফাল্গুন। মানুষের যৌবন উদযাপনের সময় যখন। সেই ফাল্গুনে যখন পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে গেছে অর্থাৎ ষষ্ঠী আসছে, অর্থাৎ ষষ্ঠী ঠাকুরের দিন আসছে, লোকটির আত্মহত্যার সাধ জাগে। তবে, পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাকেই এখানে প্রধান করে দেখতে চাইছি না। লক্ষ করতে চাইছি মধ্যবর্তী বিনির্মাণের সময়টিকে। যেখানে চাঁদ ডুবে গেছে অথচ সলকও আসেনি। একটা অবস্থান ভেঙে অন্ধকার অথবা আলো আরেকটি অবস্থান নিতে চলেছে, এই চলমানতার অন্ধকার লোকটির আত্মহননের সিদ্ধান্তে প্রেক্ষাপট রচনা করল। এবং তার তাৎপর্য তৈরি করল যে মুহূর্ত, তা কিন্তু চাঁদ ডোবার পরেই এসেছিল, সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তী প্রহর হিসেবে নয়। অর্থাৎ, চাঁদ ডুবে যাওয়াটাই এখানে অধিক অভিপ্রেত হয়ে উঠল। ফাল্গুনের উপস্থিতি কিংবা ষষ্ঠীর দিনের চাইতেও অধিক অভিপ্রেত।
কেন চাঁদ ? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে কবিতার মধ্যে অগ্রসর হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বারবার চাঁদ ডুবে যাওয়ার প্রসঙ্গ আসছে। মনে হয় চাঁদ বা সূর্যের উপস্থিতহীন একটি নিরপেক্ষ প্ররোচনাহীন সময়কে ধরতে চাইলেন কবি। জীবন অলোহীন মুহূর্তে কি চায়— দেখার জন্য! কেউ সেখানে বেছে নিচ্ছে আত্মহনন, কেউ বেঁচে থাকার অধিকার অর্জন করতে চাইছে। নাকি চাঁদ ভোগবাদী সমাজের প্রতীক। যার অনুপস্থিতিতে মানুষের হতাশা আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেয় ! — আত্মহত্যা বিরোধী অবস্থান থেকে আমরা এভাবেও দেখতে পারি। তাহলে, অবশ্য প্রশ্ন জন্মায়। কেননা সেই অন্ধকারেও উচ্চ শ্রেণির খাদক প্যাঁচা শিকার ধরতে চাইছে কেন ? সেটাও কী ভোগ নয় ?
এর পরেই কবি লোকটির সামাজিক জীবনের বর্ণনা দিতে উৎসুক হয়েছেন। এবং বর্ণনানুযায়ী লোকটির সামাজিক সাফল্য অর্জিত। তবুও কেন, এই বৈপরীত্য নির্মাণ করল সে ? ফাল্গুন – ষষ্ঠীর মাঝখানে কেমন অন্ধকার কিংবা ‘ভূত’ তাকে প্ররোচিত করল যে, সে, তার মৃত্যুকে সঁপে দিল মর্গের উদাসীনতার ভেতর ! — এই প্রশ্নের মুখোমুখি কবি ও পাঠক। তার অতীত তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলে সে কেমন অতীত? ব্যক্তির অতীত নাকি সমষ্টির অতীত? যুদ্ধের ইতিহাস নাকি প্রবঞ্চনার চিহ্ন ? এই আত্মহত্যার ইতিহাস প্রবঞ্চকের না প্রবঞ্চনার ? নানাবিধ প্রশ্ন নিয়েই পাঠক এরপর জানতে পারেন, কবিও সংশয়িত এই বিপন্ন মৃত্যু, এই লাঞ্ছিত সমাপতন লোকটির অভিপ্রায় ছিল কিনা ! কেবল তিনি দেখতে পাচ্ছেন অবস্থাকে এবং তার বিবরণ দিচ্ছেন। অন্তর্তদন্ত শেষে বলছেন,
“কোনোদিন জাগিবে না আর
জাগিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর-’
এই কথা বলেছিল তারে
চাঁদ ডুবে চলে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।”
জেগে থাকার, এই জায়মানতা তো আক্ষরিক অর্থেই কোনও সুস্থির দশা নয়। অনবরত সে বিবিধ উচ্চাবচতায় মানুষের নিরাপত্তাকে, তার অস্তিত্বকে আক্রমণ করে চলেছে। আর সেই আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যোগ্যতম হয়ে ওঠাটাই সম্ভবত জীবন। অবশ্য মনে হয়, এই উচ্চাবচতা রয়েছে বলেই, অসুখের আনন্দ রয়েছে বলেই জীবন মোহ তৈরি করে। মানুষ তীব্রভাবে বেঁচে থাকতে ভালোবাসে। বলাই বাহুল্য সেপিয়েন্সের সারভাইভাল ইতিহাস ও ইচ্ছে বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ কৌতুহলের। এবং এও অনুমান করা যাচ্ছে যে, এই পৃথিবী আবহাওয়া বদল করার আগেই মানুষ তার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপনিবেশ খুঁজে নিতে পারবে এই ক্রমবিস্তারী মহাবিশ্বে। ফলত এ কথা বলা অনেকটাই সহজ হয়ে যাচ্ছে যে, এই আত্মহনন প্রবণতা মানুষের সামাজিকভাবে অর্জিত স্বভাব। সমাজের বিবিধ তুলনামূলকতা তাকে আত্মহত্যায় ন্যস্ত করে। লোকটি এই তূলনামুলকতার তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে আর জায়মান থাকতে রাজি নয় বলেই কি তার এই সিদ্ধান্ত ! এমন সন্দেহের পরেই আমরা পাই বাইবেল কথিত উটের গল্পটির আভাস। ‘নিস্তব্ধতা’ ( প্রতিক্রিয়াহীনতা ?) , আদৌ কী ‘নিস্তব্ধতা’ বলে আমরা যা বুঝি, তার অস্তিত্ব সম্ভব ? ধরে নেওয়া যেতে পারে, ‘ নিস্তব্ধতা ‘ মানে এমন একটি ক্রিয়া যার প্রতিক্রিয়া কর্তার( লোকটির বা লোকগুলির )কাছে নেই ? সেই নিস্তব্ধতা এসে ধীরে ধীরে লোকটিকে বাইবেল কথিত উটের মতন তার ঘরের বাইরে বের করে নিজে ঘর দখল করতে করতে লোকটিকে বলেছিল না বেঁচে থাকার নির্ভারতার কথা। কখন বলেছিল, না ‘ অদ্ভুত আঁধারে ‘ । কেমন অদ্ভুত ? না, যখন অন্ধকার আলোর দিকে যাচ্ছে, তেমন অদ্ভুত।
২
আচ্ছা, এটা কী ঠিক আত্মহত্যা ? নাকি অসহ্য বোধ হওয়া যাপনকে পুনর্বিন্যস্ত করে নেওয়া। মানুষের মৃত্যুও তো এই অনন্ত প্রসারিত স্পন্দনেরই অংশ। সেও তো আরেক বিন্যাস।
এরপর কবি এ কবিতায় কিছু বৈপরীত্য নির্মাণ করছেন। মৃতপ্রায় ব্যাঙের ডাক, মশারির চারিদিকে মশার ঝাঁকের উড়াল কবির কাছে জীবনের দুর্দমনীয় উদ্ভাসের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু , ‘অনুরাগ’ আর ‘ভালোবেসে’ শব্দ দুটিকে এখানে ব্যবহার করে জীবনানন্দ বস্তুত একপ্রকার নিশ্চিত করতে চাইলেন এই জীবনের আবহমানকে। এখানে একটি সন্দেহ জাগে, একটি ব্যাঙ বা একটি মশা কী ততটা অনুরক্ত বা প্রেম বোঝে, যতটা বোঝা সম্ভব মানুষের পক্ষে ! নাকি তারা তাদের বেঁচে থাকা, বেঁচে থাকাটুকুকেই সাব্যস্ত করতে অধিক উদগ্রীব ?—”জন্ম দিতে হয়…জন্ম দিতে হয় বলে !” এই জান্তব বেঁচে থাকাগুলি কী আদৌ মানুষের আত্মহননের বিরুদ্ধে যুক্তি নির্মাণ করতে পারে? ‘ রক্ত পুঁজ’ থেকে মাছির রোদের দিকে উড়ে যাওয়াকে তাঁর মনে হয়েছে তুমুল জীবনের দিকে যাওয়া। কিন্তু মাছির প্রেক্ষিতে কী তাই ! মাছি তো আসলে জীবনের এক উপাদান থেকে আরেক উপাদানের ভেতর যাচ্ছে মাত্র। রক্ত পুঁজ তার খাদ্য। শিশুর হাতে ফড়িঙের কেঁপে ওঠাও আসলে জীবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা — এই আবহে কেন লোকটি একগাছা দড়ি হাতে অশ্বত্থের কাছে গেল এই প্রশ্নে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন কবি। কোন গাছে দড়ি বেঁধে ঝুলেছিল লোকটি ? অশ্বত্থ গাছে। যে অশ্বত্থ বোধি লাভের মিথ বহন করে। সেই মিথেই দড়ি বেঁধে ঝুলল লোকটি। সেও কী আরেক বুদ্ধ হয়ে উঠল ?মানুষটির সব ছিল আপাতদৃষ্টিতে। সে হেমন্তের বিকেল আর সুপক্ক যবের গন্ধে আকুল হয়েছিল। তারপরও সে বোধি অর্জন করে যে, মৃত্যুই মানুষের ইহ-শোক লাঘব করে। নির্বাণ দেয়। অথচ প্রাণি জগতে কী বিপুল জীবনের প্রতিপালন চলছে! তার মধ্যেও একটি মানুষ আত্মহত্যার অধিকার পালন করে।
কখন পালন করে ? না,
“চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে ”
ঠিক যে সময়ে ,
” থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে
বলে নি কি: ‘বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে?
চমৎকার!—
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার।’ ”
চাঁদের আলো যখন নিভে গিয়ে অন্ধকারই প্রধান হয়ে ওঠে, সে সময় ফুটে ওঠে এক দৃষ্টি আলো। যে আলোতে অন্ধ পেঁচা ও, গতপ্রায় আয়ুর পেঁচাও শিকারে উদগ্রীব হয়। বেঁচে থাকতে হয় বলে এই বেঁচে থাকাগুলো সহসা আলাদা হয়ে যায় লোকটির সিদ্ধান্তে। সে তার পরিতৃপ্ত জীবন, সে তার প্রণয়পূর্ণ জীবনে দারিদ্রের সঙ্গেও লড়াই করেনি । তাই কী জীবনানন্দ তাকে উদ্বন্ধনে ন্যস্ত করলেন ! বলতে চাইলেন — যে জীবন যাপনগুলি প্রতিকুলতার দ্বন্দ্বে মগ্ন হয় না, তারা পরিপূর্ণতার ভেতর থেকেই ধীরে বেঁচে থাকার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে !
বিশ্বায়নোত্তর পৃথিবীর কথা যদি ভাবি, যদি ভাবি প্রাচুর্যময় নিরাপত্তার ক্রমবিকাশের কথা তবে, তার সঙ্গে এরকম একটা তথ্য পাই,
“The overall suicide rate decreased from 18.0 in 1928 to 11.2 in 2007.”( Wikipedia )অর্থাৎ তথাকথিত ‘ভোগবাদ’ যে মানুষকে অতি প্রাচুর্যের অভিঘাতে মানুষকে আত্মহত্যা প্রবণ করে তুলছে, এরকম প্রচলিত ধারণাটি সন্দেহযোগ্য। আবার এও জানতে পারছি যে,
“In 2022, a record high 49,500 people died by suicide. The 2022 rate was the highest level since 1941, at 14.3 per 100,000 persons. This rate was surpassed in 2023, when it increased to over 14.7 per 100,000 persons. In 2022, the male suicide rate was approximately four times that of females”( Wikipedia)
লকডাউন এবং পরবর্তী পৃথিবীর নতুন অর্থনৈতিক বিন্যাস তৈরি হওয়ার সময় মানিয়ে নিতে না পেরে অথবা সর্বস্বান্ত হয়ে কত যে মানুষ আত্মহত্যা করেছিলেন, আমাদের স্মৃতিতে তা মলীন হবে না হয়তো।
দ্বিতীয় রামেসিসের চিঠিতে জানা যায় দুই-তিন শতাব্দী পূর্বে দুই যুবকের আত্মহত্যার কথা। সেই প্রথম আত্মহননের নথি সম্ভবত। তার আগে বা তার পরে কত রকম ভাবে যে, কত কারণেই যে কত মানুষ নিজেদের আয়ু প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, তার নথি কে রাখে ? অতএব এ কথা আমরা জোর দিয়ে কখনই বলতে পারি না ভোগবাদী জীবন, প্রাচুর্যের আয়োজনই আত্মহত্যার প্রবণতা তৈরি করে সমাজে। জীবনানন্দও বলতে চাননি। তিনি কেবল ওই ‘বিপন্ন বিস্ময়’টিকে বুঝতে চেয়েছেন। যা আমাদের উপুর্যপরি ক্লান্ত করে। যে ক্লান্তি লাঘবে আমরা বেছে নিই আত্মহত্যা। তবে কী জীবনই আসলে এক ‘ বিপন্ন বিস্ময় ‘ ! তার ত্রুটি, না পারা, সাফল্য, অর্জন, দাস্য – লাস্য – ঈর্ষা – ক্রোধময় উচ্চাবচতা নিজেই বিপন্ন এবং বিনির্মাণের তাড়নে বিস্মিত ! তবে কী জীবনানন্দ থামতে বললেন ! প্রয়োজনাতিরিক্ত বেঁচে থাকাটাকে প্রশ্ন করলেন — ‘ আজও চমৎকার! ‘ তারপর বোঝাতে চাইলেন ‘জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার ‘ উজার করে যেতে হয় একদিন, একটি নির্দিষ্ট সময়, যখন তার প্রয়োজন ফুরোয়। অযথা চন্দ্রদোষে আকুল হয়ে বেঁচে থাকতে চাওয়াটা ‘ আজও চমৎকার! ‘ যেমন এই লোকটি বেছে নিয়েছিল পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে যাওয়ার পরের আঁধার !
৩
এ কবিতা এ সময়ে পড়তে চাওয়ার আর কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নেই। বুদ্ধদেব বসুর এই মন্তব্যটিকে
” আপাতত, আমাদের পক্ষে, এই কথাই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরনীয় যে ‘যুগের সঞ্চিত পণ্যে’র ‘অগ্নিপরিধির’ মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি ‘দেবদারু গাছে কিন্নরকণ্ঠ’ শুনেছিলেন, তিনি এই উদভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণ স্বরূপ ” অনুমান করে নিতে। বস্তুত জীবনানন্দ আসন্ন ও সমকালীন অর্থনৈতিক পৃথিবীর ভেতর চিন্তা করেছিলেন তার বিবিধ, বহুগামী জায়মানতা সম্পর্কে। উনিশশো উনত্রিশ থেকে তৈরি হওয়া গ্রেট ডিপ্রেশনের স্মৃতি তাঁর ভেতর জাগরুক। হয়তো কিছুটা নিষ্কৃতির অপেক্ষায় আত্মহত্যার বোধিকে অর্জন করতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন আত্মহত্যা অস্ত্র হতে পারে। হয়ে যেতে পারে মধুর। এ কবিতার ভেতর সম্ভবত রয়েছে কুট জীবনের শৈলীর বিবিধ পক্ষ বিস্তার। তবে, বুদ্ধদেব বসু জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার শূন্য করে দিয়ে চলে যাওয়ার মধ্যে ‘ মৃত্যু পার হয়ে ‘…
জীবনের জয়ধ্বনি’ শুনেছিলেন — এই শ্রবণকে কিছুটা সন্দেহ হয়। যদি তথাকথিত ধারণা থেকে দেখি তাহলেও জীবন তার ভাঁড়ারকে ‘শূন্য’ করে দিচ্ছে। তার ভেতর থেকে জীবন আরেকটি আধারে প্রতিপন্ন হচ্ছে। ফলে বিগত আধারের কিন্তু, জীবনের কিন্তু, মৃত্যুই ঘটল। অন্যদিক থেকে বলা যায়, এই অনন্ত প্রসারণশীল মহাবিশ্বে মৃত্যু বলে তো কিছু হয় না। সবটাই স্পন্দনের এক একটা রূপের উদযাপন। আত্মহত্যাও। এই দিক থেকে যদি কবিতাটিকে ভাবি, তবে, দেখতে পাব, জীবনানন্দ একবারও আত্মহত্যার বিপক্ষে কথা বলেননি। বরং একটি বৈপরীত্য নির্মাণ করে পাঠকের ওপর অর্পণ করেছেন ধারণার ভার। আর অন্তিমে শিকার করার সেই উপুর্যপরি জীবন-বাসনাকে বলেছেন ‘ আজও চমৎকার!’ আর এক সময়ে জীবনের ভাণ্ডার শূন্য করে চলে যেতে হয় — এই সংবাদটুকু দিয়ে রেখেছেন মাত্র।
এ কবিতা আমাদের জনজীবনের বহুস্তরিক বিন্যাস।

