![গান্ধী <br /> [মূলগ্রন্থ : ভিখু পারেখ কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত ‘গান্ধী: অ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাক্শন্’] <br /> তৃতীয় পর্ব <br /> গৌতম বসু গান্ধী <br /> [মূলগ্রন্থ : ভিখু পারেখ কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত ‘গান্ধী: অ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাক্শন্’] <br /> তৃতীয় পর্ব <br /> গৌতম বসু](https://abahaman.com/abahaman/wp-content/uploads/2021/03/download-2.jpg)
গান্ধী
[মূলগ্রন্থ : ভিখু পারেখ কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত ‘গান্ধী: অ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাক্শন্’]
তৃতীয় পর্ব
গৌতম বসু
বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের বহুত্ববাদকে অস্বীকার করে জোর করে 'ওয়ান নেশন'-এর একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে কিছু রাজনৈতিক শক্তি। আমরা কিছুই করতে পারি না, শুধুমাত্র একটা বিপরীতমুখী সংস্কৃতির যুদ্ধ করে যাওয়া ছাড়া। মহাত্মা গান্ধীর ভাবনা এবং জীবন নিয়ে তাই এই ধারাবাহিকের সূচনা। ভিখু পারেখের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'গান্ধী, এ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন' যার অনুপ্রেরণা। সেই গ্রন্থ থেকেই অনুসৃজন করলেন কবি গৌতম বসু। আজ এই ধারাবাহিকের তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হল।
প্রথম পর্ব পড়তে ক্লিক করুন—-> প্রথম পর্ব
দ্বিতীয় পর্ব পড়তে ক্লিক করুন —-> দ্বিতীয় পর্ব
[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ধর্মীয় ভাবনা
মহাজাতিক চেতনা

গান্ধী, গভীরতম অর্থে, এক ধার্মিক ব্যক্তি ও চিন্তক ছিলেন। হিন্দুধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও জৈনধর্মের প্রগাঢ় প্রভাব তাঁর মধ্যে লক্ষ করা গেলেও, এদের কোনোটির দ্বারাই সীমায়িত না হয়ে, তাঁর নিজস্ব ধর্মভাবনা স্বতন্ত্র গোত্রের হয়ে উঠেছিল। স্বভাবতই, ঈশ্বরবিশ্বাস ছিল তাঁর ধর্মচিন্তার ভিত্তিপ্রস্তর। কিন্তু,‘ঈশ্বর’ শব্দটিতে যেহেতু এক ব্যক্তির অথবা পরমপুরুষের অনুষঙ্গ স্পষ্ট, সেহেতু তিনি ‘অবিনাশী নীতি’, ‘সর্বোত্তম চেতনা’, ‘সর্বোচ্চ ধী’,‘মহাজাগতিক শক্তি’ বা ‘মহাজাগতিক চেতনা’ প্রভৃতি বিকল্প শব্দের ব্যবহার বেশি পছন্দ করতেন। পরিণত বয়সে তিনি ব্যবহার করতেন ‘সত্য’ শব্দটি, মনে করতেন, এটিই ঈশ্বরের গুণের একমাত্র সঠিক ও তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের বিধি অনুসরণ ক’রে তিনি সদাপরিবর্তনশীল বিশ্বসংসারে একমাত্র অপরিবর্তনীয় সত্তা, যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধ’রে রেখেছে, ‘সত্য’ ব’লে তাকে অবিহিত করতে চেয়েছেন। বহুদিন পর্যন্ত তিনি ব’লে এসেছেন, ‘ঈশ্বর সত্য’, যার অর্থ দু’রকম; এক, সত্য, ঈশ্বরের অগণিত গুণের একটি গুণ, এবং, দুই, যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে, ঈশ্বর, সত্য-পূর্ববর্তী এক ধারণা। ১৯২৬-এ, প্রস্তাবটি ঘুরিয়ে নিয়ে তিনি বলেন, ‘সত্যই ঈশ্বর’। এটিকে তিনি নিজের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক আবিষ্কার ব’লে মনে করতেন, চিন্তাসূত্রটিকে তাঁর বহু বছরব্যাপী চিন্তাভাবনার নির্যাস রূপে গণ্য করতেন। তাঁর বিবেচনায়, একাধিক নিরিখে নতুন প্রস্তাবটি পুরানোটির চেয়ে উন্নত। প্রথমত, এর দ্বারা মনুষ্যকেন্দ্রিকতা-কে (অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিজ়ম্)এড়িয়ে-চলা সম্ভব এবং এ-ধারণাও অন্তর্নিহিত থাকছে যে, সত্য ঈশ্বরের পূর্বগামী, সত্যকে ঈশ্বরের নাম ধ’রে ডাকলে তাতে নতুন কোনো অর্থসংযোজন করা হচ্ছে না। একজন সৎ নিরীশ্বরবাদীও যেহেতু নিজের মতো ক’রে মহাবিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটন চাইছেন, সন্ধান ক’রে চলেছেন সত্যের, সেহেতু এই নতুন সূত্রনির্মাণ তাঁর এবং ঈশ্বরবিশ্বাসীর মধ্যে মতবিনিময়ের একটা সাধারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারছে। গান্ধী অনেক নিরীশ্বরবাদীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন যাঁদের মধ্যে তিনি গভীর আধ্যাত্মিক চেতনা, এমন-কি, মরমিয়া ভাবও লক্ষ করেছেন এবং তাঁদেরও আধ্যাত্মিক আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত ক’রে নিতে চাইতেন(তথ্যসূত্র নির্দেশ: ‘দ্য মরাল অ্যান্ড পলিটিকাল রাইটিংস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’ / সম্পাদনা: রাঘবন আয়ার)।
গান্ধীর বিচারে, সত্য অথবা মহাজাগতিক চেতনা, সমস্ত গুণাবলীর ঊর্ধ্বে অবস্থিত, তাকে, এমন-কি, নৈতিকতা দিয়েও হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। তিনি লিখছেন, ‘প্রাথমিক স্তরে, ঈশ্বরকে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব … শুদ্ধতম সদিচ্ছা নিয়ে, ঈশ্বরের উপর যা-যা গুণাবলীই আমরা আরোপ করি না কেন, সেগুলি সবই আমাদের দিক থেকে সত্য হলেও, অখণ্ড বিচারে মূলত অসত্য(তথ্যসূত্র নির্দেশ:‘দ্য কলেক্টেড্ ওয়ার্কস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’)। তিনি আরও জানান, ‘ব্যক্তির ঈশ্বরের সীমানার বাইরেও এক নিরাকার নির্যাস আছে, যা আমাদের বোধবুদ্ধির পরিধির অন্তর্গত নয়’। সেই মহাজাগতিক শক্তি যদিও সম্পূর্ণ নির্গুণ, এমন-কি, ব্যক্তিত্বরহিতও, গান্ধী মনে করতেন, মানুষ তাঁকে আপন ক’রে না-নিয়ে পারে না। মানুষের মন পঞ্চেন্দ্রিয়ের জগতের সঙ্গে এমন ওতপ্রোত জড়িত যে, নির্গুণের প্রেক্ষিতে সেই মহাজাগতিক শক্তিকে ভাবতে বলা হলে তাঁর মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে। তদুপরি, মানুষ কেবল চিন্তাশীল প্রাণী নয়, সে অনুভূতিপ্রবণ জীবও বটে, এবং ‘মস্তিষ্ক’ ও ‘হৃদয়ে’র প্রয়োজনবোধ দু’রকম। সমস্ত গুণমুক্ত মহাজাগতিক শক্তিপুঞ্জ অথবা বিশুদ্ধ ধীশক্তি মানুষের মেধাকে পরিতৃপ্ত করতে পারলেও তার হৃদয়বৃত্তিকে তুষ্ট করার পক্ষে তা বড় বেশি বিমূর্ত, দূরবর্তী, ভাবাবেগবর্জিত। ব্যক্তির হৃদয়ে এমন এক সত্তার প্রয়োজন অনুভূত হয়, যিনি করুণাময়, গভীরতম ভাব জাগ্রত করতে যিনি সক্ষম, এবং যাঁর সঙ্গে ভাবাবেগের নিবিড় সম্পর্ক গ’ড়ে উঠতে পারে; মানুষ এক ব্যক্তিগত ঈশ্বরের প্রয়োজন অনুভব করে।

মহাজাগতিক চেতনাকে গান্ধী এইভাবে ব্যক্ত করেছেন। একজন কর্মযোগী হবার সুবাদে, তিনি ভাবনাজগতের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, কর্মজগতের প্রেক্ষিত থেকে মহাজাগতিক চেতনাকে দেখেছেন। প্রথমত, সেটি কোনও ব্যক্তিবিশেষের চেতনা নয় কারণ তা হলে তা অতিসরলীকৃত হত, সেটি এক বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক, সর্বব্যাপী চেতনা। দ্বিতীয়ত, সেটি যুক্তিসিদ্ধ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কাজ করে, আদৌ স্বেচ্ছাচারী অথবা খামখেয়ালী স্বভাবের নয়। তৃতীয়ত, সেটি সদাসক্রিয় এবং অমিত বল ও তেজের অধিকারী। চতুর্থত, সেটি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ এবং মহাবিশ্বের নির্মাতা-সংগঠক। পঞ্চমত, সেটি হিতৈষী। মহাজাগতিক চেতনা যেহেতু ভাল ও মন্দের ঊর্ধ্বে অবস্থিত, সেহেতু তাঁকে হিতৈষী আখ্যা দিয়ে গান্ধী ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা অস্পষ্ট। এমনও হতে পারে, তিনি মনে করেছেন যে, যদিও সে-চেতনা প্রথাগত নীতিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কল্যাণ–অকল্যাণের পরিধির বাইরে অবস্থিত এবং যদিও তাঁর ক্রিয়া নৈতিক মূল্যায়নসাপেক্ষ নয়, তবু যেহেতু তার অধীনস্থ মহাবিশ্ব শৃঙ্খলাপরায়ণ ও স্থিতিশীল, যেহেতু তা প্রাণীজগতের ধারকও বটে এবং সুস্থ জীবনধারণের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে, সেহেতু এটা প্রমাণিত যে, সে-চেতনায় কল্যাণসাধনের এক প্রবণতা বহমান এবং মঙ্গলময় সত্তার দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত। তাঁর কর্মপদ্ধতিকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যখন নির্মম মনে হয়, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সামাজিক দুর্বিপাকের সময়ে আমরা অনুভব করি, তখনও তাঁর সম্বন্ধে চটজলদি সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে, তাঁকে অজ্ঞেয়, কিন্তু শেষত কল্যাণমুখী এক ক্রিয়ার অংশ হিসাবেই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। ষষ্ঠত, সেই মহাজাতিক শক্তি এই অর্থে ‘অপার রহস্যময়’ যে, তাঁর প্রকৃতি ও কর্মপ্রণালী বিষয়ে মানুষ কিছু দূর পর্যন্ত অবগত হলেও সে-জ্ঞান সীমাবদ্ধ, আংশিক এবং অনেকাংশে অনুমাননির্ভর। শেষত, সর্বত্র বিরাজমান হয়েও সে-শক্তি কিছু–কিছু স্বনির্মিত সীমারেখার দ্বারা আবদ্ধ। মানবমুক্তি তেমন একটা অঞ্চল এবং মহাজাগতিক শক্তি সক্ষম হলেও মানুষকে প্রাক্নির্ধারিত পথে চলতে বাধ্য করে না। তার অসীম শক্তিবলয়ের মধ্যেই মানুষের দুর্বলতা ও তার নিজস্ব মনোনয়নের জন্য স্বাধীন ক্ষেত্র, এমন-কি অকল্যাণের জন্যও জায়গা ছেড়ে দেওয়া আছে। গান্ধীর ভাবনাজগতে, মন্দ কোনও স্বাধীন বিধান নয়, সে সেই মহাজাগতিক শক্তির ‘অনুমতিপ্রাপ্ত’ এক উপাদান মাত্র।
মহাজাগতিক চেতনা যেহেতু কোনো সত্তা বা ব্যক্তিপুরুষ নন, সেহেতু তাঁকে বর্ণনা করবার সময়ে গান্ধী কখনও-কখনও ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহার করেছেন। আবার যেহেতু তা চেতনা ও ধী-র প্রতিনিধিত্ব করছে সেহেতু কখনও-কখনও তিনি পুংলিঙ্গও প্রয়োগ করেছেন(স্ত্রীলিঙ্গ কখনোই নয়)। মহাজাগতিক চেতনা-বিষয়ে গান্ধীর ধারণার বিশেষত্ব আরও কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে, যদি আমরা তাকে অধিকতর পরিচিত খ্রিস্টীয় ধর্মমতে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। খ্রিস্টধর্মের প্রামাণিক ও লোকপ্রিয় উপস্থাপনায় তিনটি বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হয়। প্রথমত, ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে অধিষ্ঠিত এক সত্তা, যিনি কেবল মহাজগতের বাইরেই অবস্থিত নন, মহাজগৎ সৃষ্টিরও পূর্ববর্তী। দ্বিতীয়ত, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলার স্রষ্টাও তিনি, এবং তাঁরই ইচ্ছানুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুশৃঙ্খলরূপে চলমান। তৃতীয়ত, তিনি কেবল পরম করুণাময়ই নন, সর্বশক্তিমানও বটে, কারণ সূর্যসহ সমস্ত নক্ষত্রাদি, সপ্তসিন্ধুর যিনি সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ামক, তিনি তো চোখ–ধাঁধানো ও সম্ভ্রম উদ্রেককারী ক্ষমতার আধার হবেনই। তিনটি বৈশিষ্ট্যই একে অপরের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে যুক্ত। মহাজাগতের সৃষ্টিকর্তা হওয়ার কারণে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে অবস্থিত এক সত্তা হওয়া ঈশ্বরের পক্ষে আবশ্যক এবং অমিত বলের অধিকারী হওয়াও তাঁর বহু গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মহাজাগতিক চেতনাকে গান্ধী ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেহেতু অজর, সেহেতু মূল প্রসঙ্গ সৃষ্টিরহস্য নয়, মূল প্রসঙ্গ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আভ্যন্তরিক গঠন-সঙ্ক্রান্ত সুশৃঙ্খলা। মহাজাগতিক চেতনা তাঁর সম্মুখে সৃষ্টিকর্তার রূপে দেখা দেন না, বরং সে-চেতনা, সুশৃঙ্খলার এক মূলনীতি(প্রিন্সিপাল অফ্ অর্ডার), এক সর্বোত্তম ধী, যা অভ্যন্তর থেকে বিশ্বপ্রকৃতিকে প্রাণিত ও নিয়ন্ত্রণ করছে। কোনও-এক পরমপুরুষের পক্ষে সমগ্রের বহির্দেশে অবস্থান করা সম্ভব, হয়তো-বা আবশ্যিকও, কিন্তু সুশৃঙ্খলার গঠনকে সমগ্রের মধ্যেই অবস্থান করতে হবে। অধিকাংশ ভারতীয় চিন্তকের মতো, বস্তুপৃথিবী নয়, গান্ধীকে বেশি কৌতূহলী করত জীবদেহের রহস্য, নীহারিকাপুঞ্জের সুশৃঙ্খল ও ছন্দোবদ্ধ সঞ্চরণ অথবা সমুদ্রের জলস্তরের ওঠানামার দ্বারা তিনি তত আলোড়িত হতেন না, যতটা তাঁকে বিস্ময়াবিষ্ট রাখত জীবপ্রকৃতি, জীবকোষের ‘রহস্যাবৃত’ জন্মবৃত্তান্ত, প্রাণের বৈচিত্র্য ও প্রাণীদেহের ভিতরের উদ্ভাবনক্ষম ও নানা জটিল যন্ত্রাংশ। প্রাকৃতিক মহাশক্তির নিদর্শনগুলি, চাঞ্চল্যকর কর্মকাণ্ড তাঁকে কৌতূহলী ক’রে তোলা তো দূরের কথা, তাঁকে কিছুমাত্র প্রভাবিতও করত না; তিনি মনে করতেন এগুলিতে মনোনিবেশ করলে ভয় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় বটে, কিন্ত ঈশ্বরের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য, প্রেম ও নিবিড়তা আস্বাদন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। মহাজাগতিক চেতনার ধীশক্তি, সূক্ষ্ম চলন, নৈপুণ্য, অন্তরস্থ শক্তি, এবং যুগপৎ কোমল ও অবোধ্য গতিবিধির উপর তিনি বেশি জোর দিয়েছেন।
মহাজাগতিক চেতনাকে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা যুক্তিধর্মের সাধ্যের অতীত, এ-ব্যাপারে সহমত প্রকাশ করলেও, তার তাৎপর্য সম্পর্কে গান্ধীর মধ্যে মতান্তর ছিল। তিনি মনে করতেন কেবল যুক্তিধর্মের দ্বারা কোনও কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, এমন-কি চেয়ার টেবিলের অস্তিত্বও নয়; সেইজন্য যুক্তিধর্মকে যদি অস্তিত্বের একমাত্র নির্ণায়ক ধার্য করা হয়, তা হলে পৃথিবীর অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা অনিবার্য হয়ে ওঠে। তদুপরি, যা কিছু যুক্তিগ্রাহ্য, কেবল তাদেরই অস্তিত্ব আছে, এ-প্রস্তাব গান্ধী স্বীকার করতে পারেন নি। যুক্তিধর্ম মানুষের সর্বোচ্চ শারীরবৃত্তি, এই অভিমতও গান্ধী প্রত্যাখ্যান করেছেন। যুক্তিধর্ম যদি নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে, তা হলে তার যুক্তি-উপস্থাপন হয়ে দাঁড়ায় চক্রবৎ। যুক্তিধর্ম ছাড়া যে অন্যান্য শারীরবৃত্তি আছে তারাও এই দাবি করে না। যুক্তিধর্ম স্পষ্টতই নানা শারীরবৃত্তির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বৃত্তি এবং তাকে তার উপযুক্ত স্থান অবশ্যই দেওয়া উচিত, কিন্তু তাকে অন্য সব প্রতর্কে মধ্যস্থতা করবার এবং একমাত্র বিচারক রূপে স্বীকার ক’রে নেওয়া অসমীচীন। প্রত্যেক বিশ্বাসকে ‘যুক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ’ হতেই হয়, কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয় এই নয় যে, এমন কোনও বিশ্বাস নেই যা যুক্তিধর্মের পরিধিকে অতিক্রম ক’রে ঊর্ধ্বগামী হতে পারে না। যুক্তিধর্ম ন্যূনতম আবশ্যিক স্তরকে চিহ্নিত করে, সর্বোচ্চকে নয়; কোন্ বিশ্বাস আমাদের গ্রহণ না-করলেও চলবে, যুক্তিধর্ম আমাদের জন্য সেটা নির্ধারণ ক’রে দেয়, কোন্ বিশ্বাস আমাদের গ্রহণ করতেই হবে, তা নির্ধারণ করা যুক্তিধর্মের পরিধির অন্তর্গত নয়।
গান্ধী কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছেন। ভারতীয় ঋষিদের দীর্ঘ পরম্পরা অনুসরণ ক’রে তিনি প্রস্তাব রেখেছেন যে, অভিজ্ঞতার নিরিখে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব। জীবনে অন্য অনেক অতল অভিজ্ঞতার মতোই, ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করবার অভিজ্ঞতা সবার জীবনে আসে না। তার জন্য ধর্মীয় মার্গে দীর্ঘকালীন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, পবিত্র আত্মা হয়ে উঠতে না-পারলে সে-অভিজ্ঞতা আস্বাদনের যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। যাঁরা তা অর্জন করেছেন, তাঁরা অবধারিত ভাবে ঈশ্বরকে ‘অনুভব’ করার, তাঁকে ‘দেখার’, তাঁর ‘কণ্ঠস্বর শোনার’ বিবরণ আমাদের শুনিয়েছেন। গান্ধী দাবি করেছেন তাঁর নিজের জীবনই এই সত্য প্রমাণ করে। অভিজ্ঞতার দ্বারা অবগত ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রমাণ যেহেতু জনসমক্ষে প্রদর্শনযোগ্য নয়, সেহেতু, একজন বিশ্বাসী একজন অবিশ্বাসীকে কেবল এই পরামর্শ দিতে পারেন, তিনি যেন প্রথমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে ঈশ্বরের সত্যাসত্য নিজেই যাচাই ক’রে নেন(তথ্যসূত্র নির্দেশ: ‘দ্য মরাল অ্যান্ড পলিটিকাল রাইটিংস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’ / সম্পাদনা রাঘবন আয়ার)।
গান্ধী এ-বিষয়ে একমত ছিলেন যে, পর্যবেক্ষণক্ষমতা ও যুক্তিধর্মের পরিধি পেরিয়ে যাবার অর্থই হল বিশ্বাসের এলাকায় প্রবেশ করা, কিন্তু এর মধ্যে তিনি কোনো দোষ দেখেন নি। জীবনযাপনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই মানুষ যুক্তিধর্ম পেরিয়ে যায়, কারণ বিশ্বাস ধ’রে রাখতে না-পারলে তাঁদের পক্ষে বেঁচে-থাকাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠত, তা সে আত্মবিশ্বাসই হোক, অথবা আত্মীয়-পরিজন বা বন্ধুবান্ধবদের উপর বিশ্বাস, নিজেদের লক্ষ্যে উপনীত হবার বিশ্বাস হোক, অথবা, এমন-কি, আগামীকাল সূর্যোদয় হবে এবং পৃথিবী আগামীকাল ধ্বংস হয়ে যাবে না, এই বিশ্বাসও। বুদ্ধিসর্বস্ব বৈজ্ঞানিকরাও এই বিশ্বাস নিয়ে চলেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছু নিয়মাবলীর দ্বারা শৃঙ্খলিত, তার একটা যুক্তিগ্রাহ্য গঠনতন্ত্র আছে, যা মানুষের মেধার কাছে বোধগম্য। তাঁদের বিশ্বাস যদিও যুক্তিসঙ্গত, তাকেও শেষত বিশ্বাসের অন্তর্গত ব’লে স্বীকার ক’রে নেওয়া আবশ্যক, কারণ উপস্থাপনের দ্বারা তা জনসমক্ষে প্রদর্শনযোগ্য নয়। অতএব, বিশ্বাস যুক্তিসিদ্ধ, না যুক্তিসিদ্ধ নয়, এটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং একমাত্র বৈধ প্রশ্ন নয়, মূল বিচার্য বিষয় হল, বিশ্বাস কখন যুক্তিসিদ্ধ হয়ে উঠছে, তা সঠিক নির্ধারণ করা, এবং ‘যুক্তিনির্ভর’ বিশ্বাস ও ‘অন্ধ’ বিশ্বাসের প্রভেদ চিহ্নিত করা।
বিশ্বাস যুক্তিসিদ্ধ ও সমর্থনযোগ্য কি না, তার নিষ্পত্তির জন্য গান্ধী প্রায়শ চারটি নির্ণায়ক প্রয়োগ করতেন, যদিও এই মর্মে স্পষ্ট উল্লেখ তিনি কোথাও ক’রে যান নি। প্রথমত, যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের পরিধির বাইরে সে-বিশ্বাস অবস্থান করবে। যেমন, হাতিরা ডানা মেলে উড়তে পারে কি না, এবং পাশের ঘরে বিড়াল আছে কি না, এ–দু’টির কোনোটিই বিশ্বাসের অন্তর্গত নয়, কারণ পর্যবেক্ষণের দ্বারা এদের সত্যাসত্য নির্ধারণ করা যায়। দ্বিতীয়ত, বিশ্বাস কখনও যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের বিরুদ্ধাচরণ করে না। তৃতীয়ত, বিশ্বাস যেহেতু যুক্তিশৃঙ্খলা ও পর্যবেক্ষণের সীমারেখা অতিক্রম ক’রে যায় সেহেতু খুব স্পষ্ট ভাবে দেখাতে হবে যে, বিশ্বাস অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। শেষত, কিছু-কিছু পরিস্থিতিতে, বিশেষত যেখানে তথ্যপ্রমাণ আশানুরূপ নয়, সেখানে বিশ্বাসে আনুগত্য প্রকাশ এক প্রবল ঝুঁকি; তাকে মান্য করবার ফল যদি হিতকর হয়, কেবল তবেই তাকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

গান্ধীর প্রত্যয় জন্মেছিল যে, মহাজাগতিক চেতনায় বিশ্বাস পূর্বোল্লিখিত চারটি শর্তের প্রত্যকটিকেই মান্য করে। মহাজাগতিক চেতনা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার পরিধির বাইরে বিরাজ করে, এবং তাতে বিশ্বাস রাখার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সংঘাত তো নেই-ই, বরং এক ঘনিষ্ঠ সুসম্পর্ক আছে। কেবল প্রাকৃতিক নিয়মাবলী দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। চিরকালীন বিশৃঙ্খলার অধীন না হয়ে মহাবিশ্ব কেন কিছু নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে, কেন সে নিয়মগুলি জীবন ধারণ করবার সহায়ক পরিবেশ গ’ড়ে তুলবে, তার কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। জড়বস্তু কেবল নিজের শক্তির দ্বারা প্রাণ উৎপন্ন করতে অক্ষম, আবার, আমরা এও লক্ষ করি, প্রতিকূল পরিবেশেও ক্ষুদ্রতম প্রাণী কি সূক্ষ্ম উপায়ে জীবনধারণের পথ খুঁজে বার ক’রে নেয়, এর কোনো ব্যাখ্যা জড়বস্তুর জগতের নিয়মাবলীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিনাশ ও ধ্বংসের মধ্যেও জীবনের অপরাজেয় স্পন্দন গান্ধীকে বিস্ময়াবিষ্ট ক’রে রাখত। তাঁর মনে হয়েছিল, ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড় প্রমুখ প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক শক্তিসমূহ অনায়াসে প্রাণ সম্পূর্ণ বিনষ্ট করতে পারে, কিন্তু, আশ্চর্যের কথা, জীবন কেবল টিকেই যায় নি, আরও বৈচিত্র্যসহ নব-নব রূপে বিকশিত হয়েছে, উন্নতর প্রাণীর উন্মেষ দেখা গেছে। আবার, যদিও জগতে ভাল এবং মন্দের সহাবস্থান দেখা যায়, আমরা লক্ষ করি, ভাল কেবল টিকেই যায় নি, দীর্ঘকালীন সময়প্রেক্ষিতে, মন্দকে জয় করতে পেরেছে। স্বল্পদৈর্ঘ্যের সময়ে অথবা বিশেষ–বিশেষ পরিস্থিতিতে হয়তো নয়, কিন্তু ‘সময়ের একটা সুদীর্ঘ প্রেক্ষিত যদি আমরা বিচার করি, দেখব, শয়তানি নয় শুভবুদ্ধিই জগৎসংসারকে শাসন করে’। এমন-কি, আত্মধবংসকারী মন্দও টিকে থাকত না, যদি ভাল তাকে ধারণ না-করত। হত্যাকারীদের দল তাদের চারপাশের সকলকে অবাধে হত্যা ক’রে চললেও, অনন্তপক্ষে নিজেদের মধ্যে তারা পরস্পরকে বিশ্বাস ও সাহায্য করে। মঙ্গল স্বাবলম্বী এবং এর বিপরীতে, অমঙ্গল পরজীবী; মঙ্গল যেমন জীবনের মূলের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত, অমঙ্গল সেভাবে জীবনের সঙ্গে যুক্ত নয়। গান্ধীর প্রতর্কের সারমর্ম এই যে, মহাজাগতিক চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার ক’রে না নিলে, মঙ্গলের প্রতি বিশ্বপ্রকৃতির পক্ষপাতিত্ব এবং তার নৈতিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।
যুক্তিনির্ভর বিশ্বাসের চতুর্থ নির্ণায়ক-বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গান্ধী এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মহাজাগতিক চেতনার অস্তিত্বে আস্থাজ্ঞাপন জীবনের পথ-চলার ক্ষেত্রে অনাস্থাজ্ঞাপনের চেয়ে শ্রেয়। এই আস্থা থাকলে মানুষের জীবনের দুঃখকষ্ট সহনীয় হয়, অন্যকে ভালবাসবার এবং তার সেবাযত্নের দিকে তার মনকে চালিত করে, চারপাশের মানুষের হীনতা ও অকৃতজ্ঞতা থেকে উৎপন্ন নেতি থেকে তাকে সুরক্ষিত রাখে। এ ছাড়াও, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য নিয়মনীতিকে নিজের সুবিধার্থে কাজে লাগানোর প্রলোভনের ফাঁদে পা দেওয়ার থেকে মানুষকে বিরত করে তার বিশ্বাস, আত্মত্যাগের মহৎ আদর্শে তা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, এমনসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অবতীর্ণ হওয়ার শক্তি প্রদান করে, যা সাধারণ অবস্থায় মানুষ এড়িয়ে চলত। মহাজাগতিক চেতনার অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পর্ক সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন না হয়েও সে-বিশ্বাসকে যিনি নিজের মধ্যে ধ’রে রাখতে পারেন, তিনি শুভফল পাবেনই, এবং আস্থা না-থাকার চেয়ে আস্থা বহাল রাখার বিকল্পটি, একটি উন্নততর প্রকল্প।
সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বর বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা ও অধিকর্তা, অনেক বিশ্বাসীদ্বারা প্রচারিত ঈশ্বরের এই প্রখর রূপায়ণ গান্ধীর পছন্দের ছিল না। এরই একটি কোমল রূপায়ণের প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল, যেখানে মৃদু স্বভাবের ‘কোনো-এক’ ঐশ্বরিক শক্তি বিশ্বপ্রকৃতিকে ‘ধীরে-ধীরে’ পথ দেখিয়ে চলেছে। যতই চিত্তাকর্ষক মনে হোক গান্ধীর এই মৃদু স্বভাবের প্রস্তাব, এরও নানা অসঙ্গতির দিক আছে। যেমন, যদিও গান্ধীর দাবি অনুসারে, এ-রূপায়ণে যুক্তিধর্মের সব দিক বিবেচিত, তবু, শেষত, তার স্থান সীমিত এবং সংজ্ঞা অতিসঙ্কীর্ণ ব’লে মনে হয়। কোনও বিশ্বাস যতক্ষণ সরাসরি উদ্ভট বোধ না হচ্ছে, ততক্ষণ সে-বিশ্বাসকে যুক্তিসিদ্ধ ও সঙ্গতিপূর্ণ ব’লে ধ’রে নেওয়া হচ্ছে। এ-ব্যবস্থায় ব্যক্তি কোন্ বিশ্বাস ধারণ করবেন তার উপর কোনও নিয়ন্ত্রণবিধি আরোপ করা অসম্ভব, এমন কি ভূতপ্রেত ও ডাইনির উপরে বিশ্বাসকেও, যুক্তির বিচারে এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া যায় না। এমনও হওয়া সম্ভব, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণপদ্ধতি প্রয়োগ করলে, গান্ধীর সিদ্ধান্তের প্রতিতুলনায়, আমরা একটি ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হব। মানুষের এতদিনের বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা লব্ধ জ্ঞান দিয়ে যদি বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করা হয়, তা হলে মহাজাগতিক চেতনার অস্তিত্ব অনুভব করবার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, এবং গান্ধী যেমন ভেবেছিলেন, তা তত সহজে প্রতীয়মান নয়। মহাজাগতিক চেতনার অস্তিত্বের প্রস্তাবের সহায়তা না নিয়েও বিশ্বপ্রকৃতির শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা, প্রাণের জন্ম প্রভৃতির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বস্তুত, অমঙ্গলের উপরে মঙ্গলের বিজয়লাভের যে দাবি ধ্বনিত হয়েছে, বাস্তব জগতে তা অত্যন্ত সীমিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং, প্রাকৃতিক জগতে এবং মনুষ্যসমাজে যে সর্বাত্মক হিংসাপ্রদর্শন গান্ধীকে শোকাচ্ছন্ন রাখত, তার সঙ্গে হিতৈষী ঐশ্বরিক চেতনাকে মিলিয়ে দেখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞতার দ্বারা মহাজাগতিক চেতনার অস্তিত্ব যাচাই ক’রে নেওয়ার যে-প্রস্তাব গান্ধী রেখেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিকতা থাকলেও, তৎসঙ্ক্রান্ত নানা অপূর্ণতার দিকও উল্লেখনীয়। অভিজ্ঞতা দিয়ে মহাজাগতিক চেতনাকে যাচাই ক’রে যা-যা পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব গান্ধী রেখেছিলেন, তার সবই তাঁর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ পালন করেছিলেন, কিন্তু তিনিও কিছুই খুঁজে পান নি। তদুপরি, সমস্ত অন্তর দিয়ে আমরা যা চাই, তা আমরা পেয়েও যাই; যখন কিছু পাই না তখন এ-অভিযোগ ওঠাই সঙ্গত যে, আমরা তত নিষ্কলঙ্ক হয়ে উঠতে পারি নি, অথবা তত তীব্র ছিল না আমাদের আর্তি, অথবা হয়তো আমাদের প্রশিক্ষণপর্বে কোনও ভ্রান্তি রয়ে গেছিল।
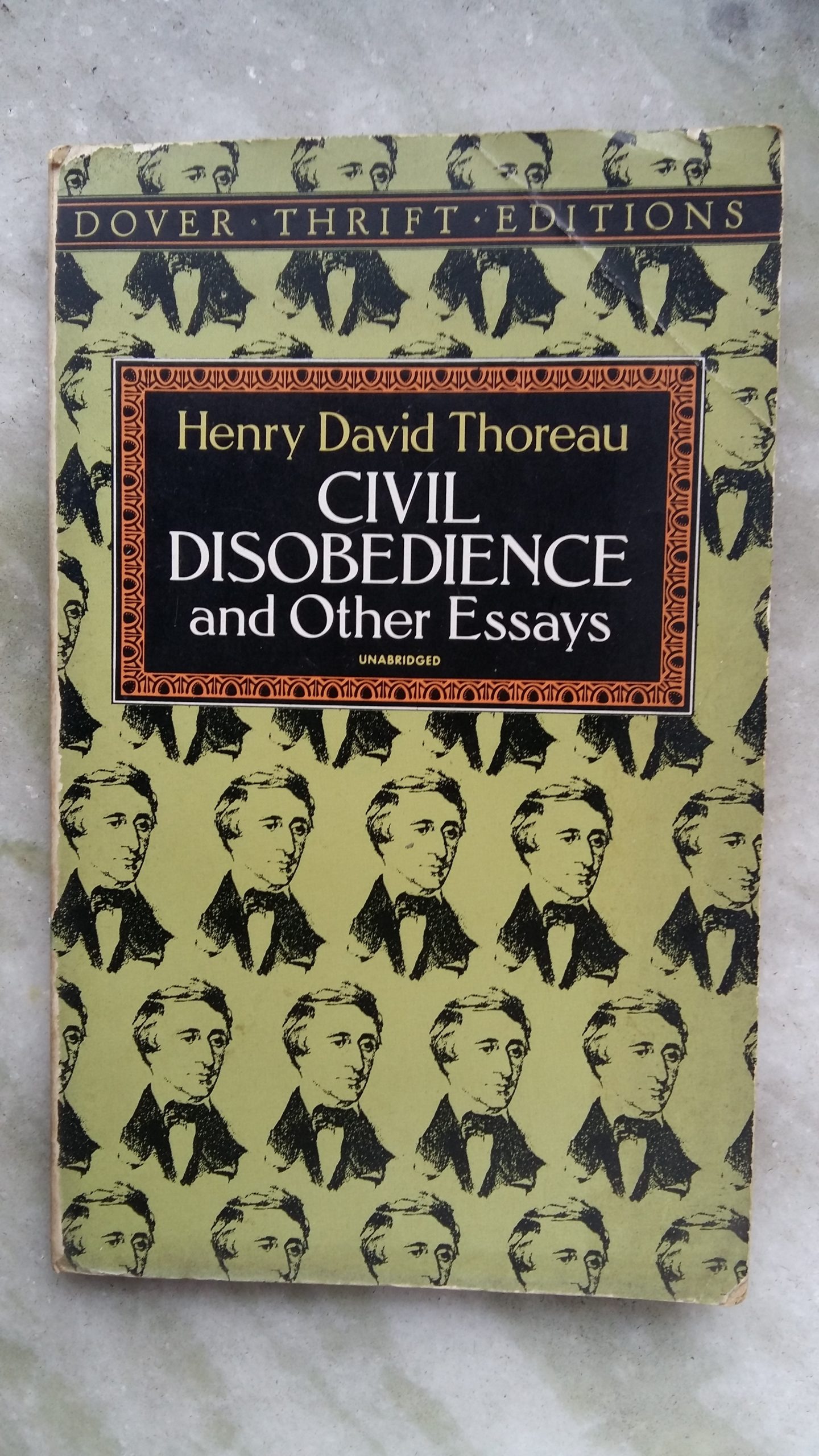
ধর্মমত(রিলিজন)
মানুষের ঈশ্বরভাবনা এবং মানুষ সেই ঈশ্বরের সঙ্গে কীভাবে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করছে, গান্ধীর বিবেচনায় সেটিই মানুষের ধর্মমত(রিলিজন)। একদিকে নৈর্ব্যক্তিক, অন্যদিকে ব্যক্তিগত ─ যেহেতু একইসঙ্গে দুইরকমের ঈশ্বরের ধারণা ছিল তাঁর প্রস্তাবনায়, সেহেতু ধর্মমতকেও হতে হয়েছিল পৃথক, দুই স্তরসম্বলিত।‘আচারনিষ্ঠ’, ‘প্রথাগত’, ‘প্রাতিষ্ঠানিক’ ও ‘ইতিহাস-সঞ্জাত’ ─ সব রকমের ধর্মমতই ঈশ্বরের পৃথক-পৃথক ধারণার উপর ভিত্তি ক’রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং এই ধর্মমতগুলি প্রত্যেকেই নিজেদের প্রয়োজন মতো ক’রে ঈশ্বরকে সীমায়িত ক’রে নিয়ে, ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য ও গুণাবলী মনুষ্যপ্রতিম দেহে(অ্যান্থ্রোপোমরফিক্)প্রতিস্থাপন করে। এর প্রকাশ দেখা যায় প্রার্থনায়, উপাসনায়, আচার-পালনে, ঈশ্বরের কাছে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদভিক্ষায়; এগুলি সবই সাম্প্রদায়িক (সেক্টেরিয়ান) আচরণ। গান্ধী মনে করেন, লোকপ্রিয় হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম, জুডাধর্ম এবং অন্য সমস্ত ধর্মই এই শ্রেণীভুক্ত। ‘প্রকৃত’,‘বিশুদ্ধ’, ‘চিরকালীন’ ধর্মবোধ এইসব আচার-আচরণের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। যাগযজ্ঞ, আচারপালন, গোঁড়ামো পরিহার ক’রে সেই ‘প্রকৃত’ ধর্মমত কেবল মহাজাগতিক চেতনার প্রতি অটল বিশ্বাস চিত্তে ধারণ করে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে প্রকাশিত ও প্রস্ফুটিত করবার জন্য দায়বদ্ধ থাকে। এমন একটি ধর্মমত, বিশুদ্ধতম আধ্যাত্মিকতার প্রতিনিধিত্ব করে এবং একই সঙ্গে স্বীকার করে যে, কোনো বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতই ঐশ্বরিক চেতনার জটিলতাকে সম্পূর্ণ ধারণ করতে পারে না। এই ‘প্রকৃত’ ধর্মমত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতগুলিকে অপসৃত না ক’রে তাদের অতিক্রম ক’রে যায়, তারা প্রত্যেকেই বৈধ, তাদের প্রত্যেকেরই একটি ‘সাধারণ ক্ষেত্র’ আছে, পরস্পরের মধ্যে ‘যোগসূত্র’ আছে, যদিও প্রকৃত ধর্মমতের প্রতিতুলনায় তারা সীমায়িত।
আমার বাড়ির চার পাশে উঁচু পাঁচিল তুলে দিতে এবং জানালাগুলো আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ ক’রে দিতে আমি চাই না। আমি চাই অন্য সমস্ত দেশের কৃষ্টি, মুক্ত বাতাসের ন্যায় আমার বাড়ি ঘিরে বইতে থাকুক। কিন্তু সেই বাতাস আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে, আমার পায়ের নিচে মাটি সরিয়ে, এটা আমি হতে দেব না।
গান্ধীর অভিমত অনুসারে, ব্যক্তির ঘোষিত বিশ্বাস নয়, ব্যক্তি কীভাবে জীবনযাপন করছেন, তা থেকে তাঁর ধর্মমত নির্ধারিত হয়; গোঁড়ারামোর অস্থি থেকে নয়, জীবন্ত প্রত্যয় থেকে(তথ্যসূত্র নির্দেশ:‘দ্য মরাল অ্যান্ড পলিটিকাল রাইটিংস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’ / সম্পাদনা রাঘবন আয়ার)। ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে, যা অতিরিক্ত বৌদ্ধিক চর্চার সংস্পর্শে এসে নিছক গোঁড়ামোয় পর্যবসিত হয় এবং ঘোষিত ধর্মমতকে জীবনচর্যার উপরে স্থান দেয়, তার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। ধর্মতত্ত্ব নয়, গান্ধীর মতানুসারে, নৈতিকতা ধর্মবোধের মূল; খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকরা দাবি করেন, বিশ্বাসের জগতের দার্শনিক সঙ্গতি ও সূক্ষ্মবিচারের উপর নৈতিকতার স্তর নির্ভর করে, গান্ধীর অভিমত ভিন্ন, তিনি মনে করেন, আদর্শবোধকে যা জাগিয়ে তোলে, মানুষের জীবনপ্রণালীকে যা উদ্বুদ্ধ করে, সেটাই ধর্মমতের প্রকৃত পরিচয়। তিনি লিখছেন:

‘ পৃথিবীতে অসত্য প্রচারকদের মধ্য অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে ধর্মতত্ত্ব। এর কোনো চাহিদা নেই এ-কথা আমি বলছি না। সন্দেহভাজন অনেক কিছুরই চাহিদা রয়েছে পৃথিবীতে, তবু দেখা যায়, ধর্মতত্ত্বের চর্চা যাঁদের কর্মজীবনের বৃত্তি, তাঁরাও সেখান থেকে বেঁচে বেরিয়ে এসেছেন। আমি দু’জন খ্রিস্টান বন্ধুকে চিনি, যাঁরা ধর্মতত্ত্ব বর্জন ক’রে যীশুর বাণী অনুসরণ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন (তথ্যসূত্র নির্দেশ : ‘দ্য মরাল অ্যান্ড পলিটিকাল রাইটিংস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’ / সম্পাদনা রাঘবন আয়ার)।
গান্ধীর মতানুসারে প্রত্যেকটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতে ঈশ্বরের স্বতন্ত্র রূপ ফুটে উঠেছে, প্রকাশ পেয়েছে ঈশ্বরের ভিন্ন-ভিন্ন গুণাবলী। ঈশ্বরকে স্নেহশীল পিতার চোখে দেখা এবং সেই সূত্রে সার্বজনিক প্রেম, ক্ষমাদান, ও নীরবে কষ্টস্বীকারের উপর বিশেষ প্রস্বর আরোপ খ্রিস্টধর্মে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী রূপে ফুটে উঠেছে। খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে গান্ধী বলেছেন, ‘আমি এমন কথা বলতে চাই না, একমাত্র এখানেই তা দেখি, অথবা অন্য কোনো ধর্মমতে তা খুঁজে পাওয়া যায় না, বলতে চাই, এখানে তার উপস্থাপনা অদ্বিতীয়।’ অপরদিকে, কঠোর নিয়মনিষ্ঠ একেশ্বরবাদ, মানুষ ও ঈশ্বরের অন্তর্বর্তী সমস্ত পর্যায়ের অপসারণ, মানুষে-মানুষে সমতার আদর্শকে তুলে ধরা ─ এগুলি ‘সবচেয়ে সুন্দর ভাবে’ মূর্ত হয়েছে ইসলামধর্মে। আবার অন্যদিকে, নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বর ও প্রাণের ঠাকুরকে পৃথক ক’রে দেখা, জগৎসংসারে লিপ্ত থেকেও নিজের মধ্যে নিরাসক্তির বোধ ধারণ করা, সর্বপ্রকার প্রাণীদেহে অভিন্নতা উপলব্ধি করা, এবং অহিংসা─ এগুলি একমাত্র হিন্দুধর্মেই লক্ষনীয়। গান্ধী মনে করতেন প্রত্যেক ধর্মমতের এক স্বতন্ত্র নৈতিক ও আত্মিক গোষ্ঠী-পরিচয় আছে, তারা প্রত্যেকেই এমন কিছু ‘আধ্যাত্মিক সৃষ্টিশীলতা’ নিজেদের মধ্যে গ’ড়ে নিয়েছেন যা অভূতপূর্ব এবং অপ্রতিস্থাপনীয়। তারা প্রত্যেকেই সত্যের ধারক, যদিও এর এই অর্থ নয় যে, তাদের সবকিছুই সত্য, কারণ কিছু-কিছু অসত্যও তারা প্রত্যেকে নিজের মধ্যে বহন করে। যেহেতু তারা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়, সেহেতু ‘বিভিন্ন ধর্মমতের আপেক্ষিক গুণবিচার এক অসম্ভব প্রয়াস’। আর গুণাগুণ অনুসারে তাদের শ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয় ইত্যাদি ক্রমে সাজিয়ে নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, ঠিক যেমন, সঙ্গীতের বিভিন্ন পরম্পরা, চিত্রকলার নানা ধারা এবং মহৎ সাহিত্যগ্রন্থকে প্রথম, দ্বিতীয়, এই ক্রমে সাজানো সম্পূর্ণ অর্থহীন এক প্রয়াস (তথ্যসূত্র নির্দেশ : ‘দ্য কলেক্টেড্ ওয়ার্কস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’)।

অন্য অনেক ভারতীয় চিন্তকের মতোই, দৈবাদেশে প্রাপ্ত ধর্মমতের বিষয়ে গান্ধী সংশয়াচ্ছন্ন ছিলেন। যুক্তির দুর্বলতা এবং নীতিবোধের ঘাটতি, এই দুই কারণে প্রত্যাদেশের (রেভ়েলেশ্ন) ধারণা তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি; যুক্তির দিক থেকে এটি দুর্বল, কারণ, আমাদের প্রথমেই ধ’রে নিতে হবে যে, ঈশ্বর বিশেষ এক ব্যক্তি; এবং, নৈতিক দিক থেকেও ভ্রান্ত এই কারণে যে, বিশেষ কোনও মানুষের প্রতি ঈশ্বরের পক্ষপাত মান্যতা পায়। আন্তরিক সন্ধানীদের গভীর সঙ্কটকালে সহায়তা করবার জন্য ঈশ্বর কখনও-কখনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ─ গান্ধী নিজেই এই রকম মার্গদর্শনে উপকৃত হয়েছেন ব’লে দাবি করেছেন ─ কিন্ত তার সঙ্গে মনুষ্যশরীরে আধ্যাত্মিক রহস্যোদ্ঘাটনের সনাতন ধারণার বিস্তর প্রভেদ রয়েছে। গান্ধীর বিবেচনায় যীশু খ্রিস্ট, হজরত মহম্মদ, মসী (মোসেস) প্রমুখ প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক অভিযাত্রী অথবা ‘বৈজ্ঞানিক’ ছিলেন, যাঁদের জীবন দৃষ্টান্তস্থাপনকারী, যাঁরা মানুষের অস্তিত্বের গভীরতম কিছু-কিছু সত্য ‘আবিষ্কার’ করেছিলেন, এবং, যাঁরা সঙ্কটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে পরিমিত পরিমাণে দৈব আশীর্বাদধন্যও, কিন্তু তাঁরা কোনও ভাবেই সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত নন, ঈশ্বরের পুত্র নন, অথবা দেবলোকের দূতও নন। জীবনের গুণগত মান উন্নত ক’রে যাঁরা যোগ্যতা অর্জন করেছেন, রহস্যোদ্ঘাটনের অভিজ্ঞতায় তাঁরাই সমৃদ্ধ হয়েছেন, এবং ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ চরম সঙ্কটকালে সুপরামর্শের রূপ ধরেই তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে।
ঈশ্বর অসীম, সেই কারণে মানুষের সীমায়িত মন তাঁর এক ভগ্নাংশ ধরতে পারে মাত্র, এবং যেহেতু তার মধ্যেও রয়ে যায় নানা অপূর্ণতা, সেহেতু প্রত্যেকটি ধর্মমতও সীমায়িত ও খণ্ডিত (তথ্যসূত্র নির্দেশ : ‘দ্য মরাল অ্যান্ড পলিটিকাল রাইটিংস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’ / সম্পাদনা রাঘবন আয়ার)। দৈবাদেশে প্রাপ্ত ধর্মের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, কারণ, এ-ক্ষেত্রে ত্রুটিযুক্ত মানবসন্তানের সমক্ষে দিব্যবাণী উদ্ঘাটিত হচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে মানুষের নৈসর্গিকভাবে অপূর্ণ ভাষায়। প্রত্যেক ধর্মমত তার অন্তরস্থ বহু ভাবনা অন্য ধর্মমতের সঙ্গে ভাগাভাগি ক’রে নিতে পারে এবং এই ধরনের সহানুভূতিপূর্ণ মতবিনিময়ের দ্বারা সকলেরই উপকার হওয়া সম্ভব। এক ধর্মমতের মনোভাব অন্য ধর্মমতের প্রতি কেবল সহনশীল অথবা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবনত থাকাটাই যথেষ্ট নয়, তাদের মধ্যে সদ্ভাবরক্ষা বিশেষ জরুরী। সহনশীলতার নিহিতার্থ হচ্ছে, অন্য মতটি ভ্রান্ত, তবু নানাবিধ কারণে তাকে সহ্য করা হল, অন্যের কাছ থেকে আমার শেখার কিছু নেই, কারণ আমার ধর্মমত ‘সত্য’ এবং অন্য মতটি ভ্রান্ত; সহনশীলতার মধ্যে ‘আধ্যাত্মিক ঔদ্ধত্য’ ও ‘পৃষ্ঠপোষকতাপূর্ণ মনোভাব’ প্রকট হয়ে ওঠে। এর প্রতিতুলনায় পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের পরিবেশ কিছুটা ইতিবাচক হলেও এখানেও অন্যদের থেকে শিক্ষাগ্রহণে অনীহা এবং তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখার মনোবৃত্তি স্পষ্ট উঠে আসছে। এর সম্পূর্ণ বিপরীতে রয়েছে ‘সদ্ভাব’, যেখানে ‘আধ্যাত্মিক নম্রতা’ ও ‘অন্য ধর্মের প্রতি সহমর্মিতা’, তাঁদের থেকে শিক্ষাগ্রহণ, তাঁদের সমৃদ্ধির জন্য শুভকামনা নিহিত আছে।

Count Leo Nikolayevich Tolstoy (1828 – 1910) the Russian writer, aesthetic philosopher, moralist and mystic inspecting the estate after a bathe in the lake. Original Publication: People Disc – HM0003 (Photo by Hulton Archive/Getty Images)
গান্ধীর বিচারে ধর্মমতই জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর, ব্যক্তির দৈনন্দিন সমস্ত ক্রিয়াকর্মকে তা গঠন ক’রে থাকে। ক্ষেত্র অনুসারে তাকে বিভাজিত করা যায় না, বিশেষ কোনও উপলক্ষের জন্য অথবা সপ্তাহের নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের জন্য তাকে সংরক্ষিত রাখা যায় না, ধর্ম, এমন-কি, পরজন্মের জন্য প্রস্তুতিপর্বও নয়। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হওয়ার অর্থ মহাজাগতিক চেতনার সঙ্গে সর্বক্ষণ বসবাস করা, এবং প্রাত্যহিক কাজকর্মে সেই অবগতি প্রতিফলিত করা। আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্রতম থেকে ব্যক্তিজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সর্বত্রই এর রেখাপাত দেখা যায়; যেমন একজন কীভাবে বসছেন, কীভাবে কথা বলছেন, খাদ্যগ্রহণ করছেন কীভাবে, কীভাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর কর্মজীবন চালিত হচ্ছে, তিনি যদি সর্বজনবিদিত এক ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁর সেই জনসংযোগের জীবন কীভাবে পালিত হচ্ছে, অর্থাৎ, তাঁর ধর্মাচরণ তাঁর জীবনের এ-সমস্তের যোগফল ভিন্ন অন্য কিছু নয়। একজন ব্যক্তি যেহেতু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমন-কি রাজনৈতিক জীবনেও, তাঁর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বাঁচেন, সেহেতু ‘যাঁরা এই মত প্রচার ক’রে থাকেন যে ধর্মবোধের সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই, তাঁরা ধর্মের প্রকৃত অর্থ প্রসঙ্গে অজ্ঞ’(তথ্যসূত্র নির্দেশ:‘দ্য মরাল অ্যান্ড পলিটিকাল রাইটিংস অফ্ মহাত্মা গান্ধী’ / সম্পাদনা রাঘবন আয়ার)। এই ধারণা যেমন ঈশ্বরতন্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করছে না, তেমনই ধর্মনিরপেক্ষতাকে বর্জনও করছে না, কারণ, ধর্মবোধ আন্তরিকতা ও মুক্তচিন্তার ক্ষেত্র, সেখানে বলপ্রয়োগের কোনও স্থান নেই। রাষ্ট্র যেহেতু বলপ্রয়োগের দ্বারা পুষ্ট এক প্রতিষ্ঠান, সেহেতু তার পক্ষে কোনও ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করা, কোনও বিশেষ ধর্মমতের পক্ষ নেওয়া, এমন-কি, সব ধর্মমতকে সমান দৃষ্টিতে দেখা ও সমর্থন করাও অনুচিত। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, রাজনৈতিক জীবন ধর্মবর্জিত হওয়া উচিত এবং ধর্মভিত্তিক আবেদননিবেদনের, প্রতর্কের ও কার্যক্রমের স্থান থাকবে না, কারণ তা হলে তা হবে নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আত্মপরিচয় রক্ষার পরিপন্থী।
বিভিন্ন ধর্মমতকে সাধারণত দ্বাররুদ্ধ জগৎ রূপেই দেখা হয়, যেন-বা তারা এক- একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, নিজেদের সীমান্তপ্রদেশ জুড়ে যারা অষ্টপ্রহর কঠোর পাহারা দিয়ে রয়েছে। কোনও একটি বিশেষ ধর্মমতের অনুগামী, অপরাধবোধে দীর্ণ না হয়ে, অথবা তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাস তরলীকৃত হবার আশঙ্কায় পীড়িত না হয়ে, অন্য ধর্মমতের অনুগামী হবার, অথবা অন্য কোনও ধর্মমতের ভাবনা ও আচার-আচরণ ধার ক’রে আনবার অনুমতি পান না। গান্ধী ভিন্ন মত অবলম্বন করতেন। ধর্ম তাঁর কাছে শাসনতন্ত্র নয়, অবাধ প্রবেশাধিকারবর্জিত, ধারণা ও প্রথার কোনো বৈচিত্র্যহীন সংগঠনও নয়, বরং এক উৎসবিশেষ, যেখান থেকে যার মনে যা ধরে তা-ই ধার করতে কোনো বাধা নেই। সকলের যৌথ সম্পত্তি এটি, এবং মানবসভ্যতার অবিভাজ্য পরম্পরা। প্রত্যেক ব্যক্তি একটি বিশেষ সুগঠিত ধার্মিক পরম্পরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই পরিবেশ তাঁকে গ’ড়ে তোলে, জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মমত তাঁর স্বগৃহ হলেও, অন্য ধর্মমতের দরজাও তাঁর জন্য বন্ধ নয়। গান্ধী বলতেন, জন্মসূত্রে হিন্দু হওয়ার কারণে তিনি হিন্দুধর্মের ঐশ্বর্যশালী ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন, আবার ভারতীয় হওয়ার সূত্রে বিভিন্ন ধর্মের ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হবার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। মানব সন্তান হবার সুবাদে তিনি পৃথিবীর সব মহৎ ধর্মমতেরও উত্তরাধিকারী; জন্মসূত্রে যিনি সেই ধর্মমতাবলম্বী, তাঁর সঙ্গেও গান্ধীর অধিকার ভোগের কোনো প্রভেদ নেই। নিজের ঐতিহ্যে দৃঢ়রূপে প্রোথিত থেকে অন্য ধর্মমতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎস থেকে মুক্ত মনে আহরণ করায় কোনও বাধা তিনি অনুভব করতেন না। শিকড়সচেতনতা ও মুক্তমনের কেন্দ্রীয় ধারণাটি প্রকাশ করবার জন্য তিনি রূপকার্থে একটি বাড়ির উল্লেখ করেছেন যার সবকটি জানালা উন্মুক্ত। বাড়িটির দেওয়ালগুলি তাঁকে নিরাপত্তার বোধ ও নিজের ঐতিহ্যে প্রোথিত থাকার আশ্বাস দেয়, আর খোলা জানালাগুলি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আহ্বান করে অন্য সংস্কৃতির বাতাস, যাতে যে বায়ুমণ্ডলে তিনি শ্বাস গ্রহণ করছেন সেটি যেন হয় আরো ঐশ্বর্যময়।‘আনো ভদ্রা কৃত্যাভ য়ন্তু বিশ্বতাহা’(সর্বদিক হতে উন্নতমনের চিন্তাসকল আসুক আমাদের অন্তরে) ─ এই ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় ধ্রুপদী প্রবচন।
বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত তাঁর স্বঘোষিত স্বাধীনতার পূর্ণ সুযোগ নিতে গান্ধী দ্বিধাবোধ করেন নি। হিন্দুধর্মের কেন্দ্রীয় ভাবনাসূত্র বলতে তিনি যা বুঝতেন, সেগুলি প্রথমে উদ্ধার ক’রে এনে, তাদের একত্রিত ক’রে, তারপর অন্য ধর্মীয় পরম্পরার সঙ্গে তাদের মধ্যে একটা প্রতর্ক, এমন কি, একটা সংঘাত বাধিয়ে দিতেন। এইভাবে অহিংসা-র ধারণাটি ভারতীয় ঐতিহ্য, বিশেষত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম থেকে তিনি আহরণ করেন, কিন্তু মূল ভাবনাবলয়ে ধারণাটি যেহেতু তাঁর নেতিবাচক ও জড়ধর্মী বোধ হয়েছিল, সেহেতু একজন কর্মযোগীর দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে আবার ব্যাখ্যা ক’রে সমাজহিতৈষী খ্রিস্টধর্মের কারিটাস–এর (caritas, শব্দার্থ : দয়া, দানশীলতা) সঙ্গে তাঁকে সংযুক্ত ক’রে দেন।কারিটাস–এর ধারণাটি অতিমাত্রায় আবেগসঞ্চারকারী, এবং, তাঁর আরও মনে হয়েছিল সংশ্লিষ্ট প্রাপকের স্বনির্ভরতাকে তা কিয়দংশে হেয়জ্ঞান করছে; ফলত, হিন্দুধর্মের অনাসক্তি ও নিষ্কাম কর্ম–র আলোকে তিনি তাকে পুনর্সংজ্ঞায়িত করেন। কারিটাস–এর খ্রিস্টীয় ধারণাকে প্রথম ধাপে ভারতীয় ধারণায় রূপান্তরিত ক’রে এবং তারপর, দ্বিতীয় ধাপে আবার সেই ভারতীয় ধারণাকে একটি খ্রিস্টীয় অনুষঙ্গে আলোকিত ক’রে, অর্থাৎ, তিনি যে নতুন ধারণাটি পেলেন সেটি একইসঙ্গে একদিকে কর্মমুখী ও ইতিবাচক এবং অন্যদিকে নিরাসক্ত ও আবেগরিক্ত প্রীতির দৃষ্টান্ত। আবার, হিন্দুধর্মের সনাতন আচার, উপবাসকে (যেখানে নিজের আত্মিক উন্নতির জন্য কৃচ্ছ্রসাধন ও প্রায়শ্চিত্তই প্রধান লক্ষ্য) তিনি গ্রহণ করেন, মিশিয়ে নেন পরের জন্য যাতনাস্বীকার ও পরহিতার্থে প্রায়শ্চিত্তের খ্রিস্টীয় ধারণার সঙ্গে, এর আলোয় ওকে এবং ওর আলোয় একে আলোকিত ক’রে তোলেন, উঠে আসে ‘স্বেচ্ছায় নিজের রক্তমাংসকে ক্রুশবিদ্ধ হতে দেওয়ার’ নতুন ধারণাটি। তাঁর উপবাসের কার্যক্রমে অন্তর্গত ছিল জননেতার দায়িত্ব পালনার্থে অনুচরদের বিপথগামী আচরণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা, যাতে তাঁদের মধ্যে অপরাধবোধ ও অনুশোচনা জাগ্রত করার সঙ্গে-সঙ্গে আত্মসংশোধন শক্তিও সঞ্চারিত হয়।
বিভন্ন ধর্মমত থেকে নিজের ইচ্ছামতো শ্রেষ্ঠ ধারণাগুলি চয়ন ক’রে (রিলিজিঅস এক্লেক্টিসিজ়ম্) সেগুলি পরস্পরের মিশ্রিত করার গান্ধীর এই নীতি অনেক হিন্দু ও খ্রিস্টান গুণগ্রাহীদের বিচলিত করত, তাঁদের দিক থেকে অভিযোগ উঠত, এগুলি গান্ধীর অঙ্গীকারের অভাব ও ধর্মীয় স্বল্পগভীরতার দিকে ইঙ্গিত করছে, ধর্মীয় ঐতিহ্যরক্ষায় তাঁর অযত্নের পরিচায়ক। খ্রিস্টান বন্ধুরা বলতে লাগলেন, খ্রিস্টধর্ম থেকে তিনি যখন এতটাই গ্রহণ করলেন তখন তাঁর ধর্মান্তরিত হওয়াই ন্যায়সঙ্গত। হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভক্তরা বলতে লাগলেন খ্রিস্টধর্ম দিয়ে হিন্দুধর্মকে ‘কলুষিত’ করার এই প্রয়াস অবিলম্বে বন্ধ হোক; হিন্দুধর্মের কেন্দ্রীয় ভাবনার প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করা উচিত। গান্ধী নিজের আচরণের জন্য কোনওরকম অনুশোচনা প্রকাশ করেন নি। তিনি মনে করতেন, তাঁর এই সৃষ্টিশীল সংশ্লেষ প্রকৃতপক্ষে আন্তরিক এবং সত্যান্বেষণের এক অক্লান্ত প্রক্রিয়া; এটি কোনও স্বল্পগভীর প্রয়াস নয়, বরং ঠিক তার বিপরীতাবস্থা, এর দ্বারা কেবল যে তাঁর নিজের এবং হয়তো অন্যের ধর্মীয় ঐতিহ্য গভীরতর হবে তা-ই নয়, দুই ধর্মমতের মধ্যে প্রয়োজনীয় সেতু নির্মাণের কাজটিও সম্পন্ন হবে। তাঁর মতানুসারে, খ্রিস্টধর্মের অন্তর্গত কোনও বিশ্বাস ও প্রথা আহরণ করতে হলে খ্রিস্টান হতে হবে এর পিছনে কোনও যুক্তি নেই। বস্তুত, খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলমান এই বিভাজনগুলিই গভীরতম অর্থে ভ্রান্তিপূর্ণ এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার উৎসমুখ। একে অপরের মধ্যে উঁচু, অনড় পাঁচিল তুলে দিয়ে, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে, ঔচিত্যের মিথ্যা দাবি প্রচার ক’রে, মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক বাধা গ’ড়ে, তারা স্বাস্থ্যকর বিনিময়ের পথ বন্ধ সম্পূর্ণ ক’রে ফেলেছে।
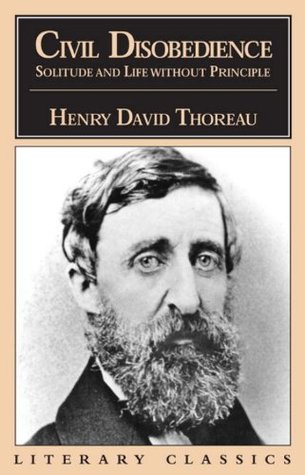
সামগ্রিক বিশ্লেষণে গান্ধী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কেউ হিন্দু নন, খ্রিস্টানও নন, কেবল মানুষ; সেই পরিচয়ের বলে তাঁরা ওই দুই, এবং অন্য ধর্মমতের ভাণ্ডার থেকে সম্পদ আহরণ ক’রে পরস্পরের সহায়তা করছেন (তথ্যসূত্র নির্দেশ : ‘দ্য লাইফ অফ্ মহাত্মা গান্ধী’ / লুই ফিশর)। এক সুমহান আত্মা জ্ঞান ক’রে কেউ যীশু খ্রিস্টকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারেন, আবার একই সঙ্গে গৌতম বুদ্ধ, মসী (মোসেস) ও অন্যান্যদের বিষয়ে তাঁর একই মনোভাব থাকতে পারে। যাঁরা এইরকম মনোভাব ধারণ করেন তাঁরা নিজেদের ধর্মমতের সঙ্গে-সঙ্গে, অন্য ধর্মমতকেও আপন ক’রে নিয়েছেন। তাঁরা খ্রিস্টান, মুসলমান, অথবা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এই অর্থে যে, ওই বিশেষ ধর্মমত তাঁদের নিজস্ব ঘরবাড়ির মতো, ওইভাবেই তাঁদের ধর্মবোধ পুষ্টিলাভ করেছে, তাঁদের সর্বাধিক প্রিয় সম্পদ হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে তাঁরা অন্য ধর্মীয় ঐতিহ্যকেও সমাদর করেছেন, সেখান থেকে সম্পদ আহরণ করেছেন মুক্তমনে, সেই ঐতিহ্যের নানা অংশ তাঁরা তাঁদের নিজেদের অন্তরে ধারণ করেছেন। একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আন্তরিক ঈশ্বর-জিজ্ঞাসু সমস্ত কিছুকে আহ্বান ক’রে নেন, ‘একটি সত্য থেকে অন্য সত্যে’র দিকে এগিয়ে যান, লক্ষ্য তাঁর একটাই: পরমসত্য। গান্ধী বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরকে পাবার জন্য যদি কারুর দুয়ার খোলা থাকে, তা হলে সব ধর্মীয় ঐতিহ্যের জন্যও তাঁর দুয়ার খোলা থাকবেই। যিনি মৌলবাদী, অসীম ঈশ্বরকে একটি বিশেষ ধর্মমতে বন্দী করতে উদ্যোগী, যিনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের তাঁর প্রতিপক্ষ অথবা শত্রু মনে করেন, তিনি নৈতিক দৃষ্টিক্ষীণতা, আধ্যাত্মিক দম্ভ এবং, এমন-কি, ঈশ্বর–নিন্দার অপরাধে অপরাধী।
গান্ধী ও তাঁর সমালোচকদের মধ্যকার মতপার্থক্য লক্ষ করলে ধর্ম ও ধর্মীয় সত্যের দুটি বিপরীতমুখী দৃষ্টিকোণ উঠে আসে। গান্ধীর বিচারে ধর্ম একটি উৎস বিশেষ, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন অভিজ্ঞতার এক ভাণ্ডার, যা থেকে ইচ্ছামতো আহরণ, এক ভাবনার সঙ্গে অপর ভাবনার মিশ্রণ ছাড়াও, বিষয়গুলি নিজের প্রয়োজনমতো ব্যাখ্যা করা যায়। এই মনোভাব গভীরভাবে অনৈতিহাসিক, সম্পূর্ণ বাধামুক্ত, সনাতনধর্মের বিরোধী, উদার, এবং পূর্বপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির মাধ্যমে ধর্মীয় ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করতে অনাগ্রহী। তাঁর সমালোচকদের মতানুসারে, ধর্ম একটি বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত, তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রাধিকার আছে, তা বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের অন্যতম ভিত্তি এবং তাকে সম্যক বুঝতে গেলে মূল ধর্মগ্রন্থগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে হবে। উভয় দৃষ্টিকোণেরই ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক লক্ষনীয়। গান্ধী, ব্যক্তিকে ধর্মজিজ্ঞাসার কেন্দ্রে স্থাপন করেছিলেন, ঐতিহ্যের অন্ধ অনুকরণকারী ও নিছক নিয়মপালনকারীদের কবল থেকে ধর্মকে মুক্ত করেছিলেন, ধর্মগ্রন্থগুলির নতুন পাঠে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন, এবং ধর্মে-ধর্মে মতবিনিময়ের একটা পরিবেশ গ’ড়ে তুলেছিলেন। এর বিপরীতে, তাঁর ধর্মচিন্তার নেতিবাচক দিকগুলিরও উল্লেখ করা যেতে পারে; তাঁর কারণে ধর্মের ঐতিহাসিক ভিত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল, হ্রাস পেয়েছিল ধর্মের সাংগঠনিক শক্তি, এবং, শেষত অযোগ্য অনুচরদের হাতে প’ড়ে এক স্বল্পগভীর নাগরিকতার সঞ্চার ঘটেছিল। তাঁর সমালোচকদের দৃষ্টিকোণে এর বিপরীত দিকের সদ্গুণ ও ত্রুটি লক্ষ করা যায়।

চিত্র- পরিচিতি
শ্রীমদ্ রাজচন্দ্র (১৮৬৭-১৯০১):
জহুরী, মরমিয়া সাধক-কবি ও জাতিস্মর। রায়চন্দ্ভাই নামে পরিচিত হলেও মহাত্মা গান্ধী তাঁকে ‘কবি’ নামেই সম্বোধন করতেন। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী যুবক মোহনদাসের হিন্দুধর্ম বিষয়ে সম্যক জ্ঞান ছিল না, সুদূর ভারতের এক রত্নব্যবসায়ী রায়চন্দ্ভাইকে চিঠি লিখে তিনি হিন্দুধর্ম ও জৈনধর্ম সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গান্ধী লিখেছেন, ‘তিনজন আমার জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন, টলস্টয়, রাস্কিন এবং রায়চন্দ্ভাই…’।
পুতলীবাঈ গান্ধী (১৮৪৪-১৮৯১):
স্বামী করম্চন্দ্ উত্তমচন্দ্ গান্ধী (১৮২২-১৮৮৫), কনিষ্ঠ পুত্র মোহনদাস করম্চন্দ্ গান্ধী। অনেকে মনে করেন পুতলীবাঈের কঠোর উপবাসব্রতপালন, তাঁর পুত্রকে প্রভাবিত করেছিল।
নরসিংহ মেহ্তা (পঞ্চদশ শতাব্দী):
মধ্যযুগের সন্ত-কবি। মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম প্রিয় ভজন ‘বৈষ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে’-র রচয়িতা।
জন রাস্কিন (১৮১৯-১৯০০):
প্রখ্যাত ইংরেজ চিত্রসমালোচক ও শিল্প-ঐতিহাসিক,‘মডার্ন পেন্টার্স’ গ্রন্থমালার রচয়িতা।পরবর্তীকালে, সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক।
লিও টলস্টয় (তৈলচিত্র ১৯০১)
চিত্রশিল্পী: লিওনিড পাস্তারনাক।
হেনরি ডেভ়িড থরো (১৮১৭-৬২)
জীবিতকালে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত মার্কিন কবি-সমাজবিজ্ঞানী-দার্শনিক। তাঁর মাত্র একটি বই ‘ওয়ালডেন’-এর দু-হাজার কপির প্রথম সংস্করণ অল্প সময়ে নিঃশেষিত হয়, কিন্তু বইটি নতুন ক’রে ছাপতে কেউ আগ্রহী হন নি। দাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের এক কর্মী ছিলেন। তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাই মৃত্যুর পরে গ্রন্থিত হয়েছে।অসহযোগ আন্দোলনের আদি পুরুষ।
মহাত্মা গান্ধী (আলোকচিত্র)
জোহেনেসব্যর্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯০৮
অনুবাদ গৌতম বসু

