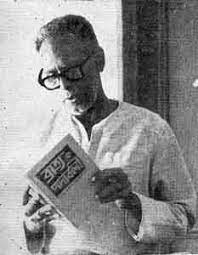
ও আলোর পথযাত্রী
বেবী সাউ

‘কার পাপ আমাদের রক্তের ভিতরে
কার অন্ধকার?
কণ্ঠস্বর
ভেসে আসে, ‘জোর যার’…
মানুষ কি এখনো তোমার
চোখ-রাঙানো প্রেমের চাকর?…
অথচ কোথায় যাব? এ পৃথিবী আমার, তোমারো
‘মারো! যত পারো!’
(অন্ধ পৃথিবী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
একটি শব্দও যেমন অরাজনৈতিক হতে পারে না, তেমন রাজনৈতিক কবিতা মানে তা গভীর ভাবে মানবিক হতে বাধ্য। কিন্তু এ রাজনীতির মূলে যদি কোনও ফ্যাসিস্ট ভাবনা কাজ করে, তবে তা নিশ্চয় রাজনীতিকে গভীর ও উচ্চ কোনও স্থান দেবে না। ঠিক তেমন তা কবিতা বা শিল্পের কাছাকাছিও যাবে না। কেউ কি দেখাতে পারবেন, ফ্যাসিস্ট হিটলারের নাজি পার্টির কারো কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে গভীর রাজনৈতিক মানবিক কবিতা? কিন্তু আমরা দেখাতেই পারি চ্যাপলিনকে, দেখাতেই পারি লোরকাকে, নেরুদাকে, স্পেন্ডারকে, পিকাসোকে এবং আরও অনেককেই। ভুলতে কি পারি মায়াকোভস্কির কথা কিংবা গোর্কির কথা বা সুকান্ত বা সুভাষের কথা? ঠিক তেমন-ই বর্তমান ভারতবর্ষের একপ্রান্তে যেমন একজন গদ্যকার লিখে যাচ্ছিলেন গভীর রাজনৈতিক, উগ্র দেশপ্রেম বিরোধী সব গল্প, ( সে লেখক মান্টো ছাড়া আর কেই বা হবেন), তেমন এখানেও লিখে যাচ্ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর পঞ্চাশ ষাট সত্তর দশকে আরও একজনের জীবন ও কলমের প্রতি আমরা এখনও নতজানু হয়ে থাকি, তিনি কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
এখন সারা বিশ্বেই এবং ভারতবর্ষেও এই অবস্থা। জোর যার, মুলুক তার। চোখ রাঙানো শক্তির প্রদর্শন। ভয় দেখানো শাসক। হয় মেনে চলো, নয় মরে যাও। ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে শাশ্বতকালীন সত্য উচ্চারণ করে গেছেন। তিনি লিখলেন- “ চোখ রাঙালে না হয় গ্যালিলিও/ লিখে দিলেন, ‘পৃথিবী ঘুরছে না!’/ পৃথিবী তবু ঘুরছে , ঘুরবেও/ যতই তাকে চোখ রাঙাও না”! আমরা যদি ভয় পেয়ে সেই শাসকের কণ্ঠে গলা মেলাই, তাদের সমর্থন করি, ভয়ে দরজা জানলা আটকে শুয়ে থাকি, তাহলেও সত্য বদলে যায় না। বদলাবেও না। মাত্র চার লাইনের একটি কবিতায় এই যে নিকানোর পাররার সুলভ তীব্রতার সৃষ্টি করলেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এই ছিল তাঁর শক্তি। একজন কবি তাঁর সময়ের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে থাকেন বলেই, তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই লিখে যান পরবর্তী একশ বছরের কবিতা। ১৯৬০ সালে অস্থিরতার সময়ে তিনি লিখেছিলেন- “ মানুষখেকো বাঘেরা বড় লাফায়/ হেঁড়ে গলায় ঘর দুয়ার কাঁপায়।/ যখন তারা হাঁক পাড়ে বাপসরে/ আকাশ যেন মাথায় ভেঙে পড়ে;/ ভয়ের চোটে খোকাখুকুরা হাঁপায়!/ মানুষখেকো বাঘেরা বড় লাফায়…” ( মানুষখেকো বাঘেরা বড় লাফায়)। আজীবন অপ্রাতিষ্ঠানিক এই কবি জীবনে সমস্ত তথাকথিত সমৃদ্ধির রাস্তা থেকে সরে এসেছিলেন। কখনও আপোষ করেননি কোথাও। কবিতা লেখার জন্য কবিতা লেখেননি তিনি। কিন্তু কবিতার নিয়তিনির্দিষ্ট এই সৈনিক গণ আন্দোলনের পথকেই মহিমান্বিত করে গেছেন তাঁর কবিতায়। যেমন তিনি অন্ধকার এই ভারতবর্ষের কথা লিখেছেন, তেমন-ই একজন প্রকৃত কমিউনিস্টের মতোই সমস্ত ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে ছিলেন। শিল্পী হিসেবে তাঁর এই সমস্ত ক্ষমতা কাঠামোকে অস্বীকার করার পাশাপাশি ছিল রাজনৈতিক ভাবেও সমস্ত ক্ষমতা কাঠামোর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। কমিউনিজম তাঁর কাছে কেবল মাত্র সংসদীয় রাজনীতির রাস্তা ছিল না। ছিল প্রকৃত প্রস্তাবেই পরিবর্তনের এক একটা হাতিয়ার। তিনি এই কমিউনিজমের পথ ধরেই মানুষের মুক্তির কথা ভাবতেন।
আমরা জানি লোরকা স্প্যানিশ ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন। জানি পাররার কবিতার কথা। অ্যান্টি পোয়েট্রির কথাও জানি। আসলে, অ্যান্টি পোয়েট্রির ভিতরের কথা যদি আমরা পড়ি, তবে হয়ত স্বীকার করতে কারো দ্বিধা থাকার কথা নয় যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যদি বাংলায় অ্যান্টি পোয়েট্রির পথিকৃৎ হয়ে থাকেন, তবে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্ভবত সেই রাস্তাকে অনেক অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তা না হলে, তিনি ফুল পাখি আনন্দের তথাকথিত প্রেমের কবিতা না লিখে লিখতে শুরু করলেন খেটে খাওয়া মানুষের কবিতা, লিখলেন ফুটপাথে ধুলোর মধ্যে পড়ে থাকা মানুষের কবিতা। লিখলেন সেই সব ন্যাঙটো ছেলের ধুলোর মধ্যে অভুক্ত অবস্থায় বড় হয়ে ওঠার কবিতা এবং তাদের সামনে থাকা চোখের জল মুছতে মুছতে সামান্য ভাতের স্বপ্ন দেখা তাদের মায়ের কবিতা। জগতের এই আপাত সুখের ও আপাত সমৃদ্ধির অন্তরালে যে প্রবল দুঃখস্রোত কাজ করে চলেছে, তা কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। তাঁর পৃথিবীতে বসন্ত বা হেমন্ত ছিল বিষাদের পাশাপাশি মানুষের জীবনসংগ্রামের। তিনি লিখেছিলেন-‘ কী বা আসে যায় আশ্বিনে যদি আকাশ বিষায় কালো মেঘে/ শরতের রোদ মুছে নিয়ে যায় মরা শ্রাবণের মেঘে মেঘে/ হেমন্তে যদি বাতাস ফোঁপায়, কিংবা পঙ্গপাল আসে/ অসময়ে গাঁয়ে খামারে খঞ্জে বস্তিতে বাঁকা শীত হাসে।/ তাতে আমাদের কতটুকু ক্ষতি, কতটুকু ক্ষতি মিতে/ হাঁ-করা জুতোটা অবাধ্য বড়, ভালো করে বাঁধো ফিতে”। প্রকৃতিপ্রেমের নিখাদ সৌন্দর্যচেতনার কবিতা তিনি লেখেননি, কারণ সেই প্রকৃতির সুন্দর চিত্রের পাশাপাশি ছিল আমাদের অভুক্ত পৃথিবী, আমাদের অসাম্যের পৃথিবী।
প্রত্যেক কবি ও লেখক আসলে একশ বছরের সেই নিঃসঙ্গতার মধ্যেই বেঁচে থাকেন, যে নিঃসঙ্গতার আসলে কোনও বন্ধু নেই। জীবনানন্দ দাশ যেমন লিখেছিলেন- যারা অন্ধ, আজ সবচেয়ে বেশি চোখে দেখা তারা, ঠিক তেমন ভাবেই, কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলেন মানবতার গভীর গভীরতম অবক্ষয়। তিনি হয়ত বুঝতে পারছিলেন পৃথিবীটা আরও বেশি করে মানুষের বসবাসযোগ্য থাকবে না। কেবল অত্যাচার, কেবল শোষণ, আর কেবল ক্ষমতাসীন মানুষের নির্লজ্জ হুংকার ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। মানুষ মানুষের সভ্যতার যে নির্লজ্জ শত্রু, তা কবির কাছে অধরা ছিল না। তিনি জানতেন একটি ক্ষমতা এবং আরেকটি ক্ষমতার মধ্যে শোষণের প্রেক্ষিত থেকে পার্থক্য কিছুই নেই। তাই তো “ রাজা আসে যায় রাজা বদলায়/ নীল জামা গায় লাল জামা গায় / এই রাজা আসে ওই রাজা যায়/ জামাকাপড়ের রঙ বদলায়/ দিন বদলায় না”। যতক্ষণ মানুষ তার নিজস্ব আন্দোলনের পথ ছেড়ে, গণ আন্দোলনের পথ ছেড়ে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথ ছেড়ে, সংসদীয় আপোষের রাজনীতির পথ অবলম্বন করবে, ততক্ষণ আমাদের এই দেশে ক্রমমুক্তি সম্ভব নয়। ততক্ষণ কেবলমাত্র শাসকের পরিবর্তন সম্ভব, কিন্তু তাতে মানুষের অবস্থানের খুব একটা পরিবর্তন হবে না। এখনও এ দেশে হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করে, এদেশে শিশুমৃত্যুর হাত সর্বোচ্চ, এ দেশে এখনো বেকারিত্ব আকাশছোঁয়া, কিন্তু একদিকে বিশ্বায়নের কর্পোরেট অর্থনীতি অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক ধর্মের উন্মত্ততার ফাঁসে হাঁসফাঁস করছে সমগ্র দেশ। মনে হয় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কি সমস্ত কিছুই দেখতে পেয়েছিলেন? তাঁর তীব্র অন্তদৃষ্টি কি বুঝতে পেরেছিল পৃথিবীতে ও আমাদের দেশে আসছে এক তীব্র অবক্ষয়ের সংস্কৃতি। এখানে মানুষের শ্বাসরোধ করা হবে প্রতিনিয়ত। শ্বাস নিতে গেলেও লাগবে অনুমতি। একজন প্রকৃত বামপন্থী কবি আসলে তাঁর তীব্র বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখতে পান আগামী সময় কীভাবে আমাদের গিলে নিতে আসছে। তাই তিনি লেখেন- “ জননী জন্মভূমি/ সব দেখে সব শুনেও অন্ধ তুমি?/ সব জেনে সব বুঝেও বধির তুমি!/ তোমার ন্যাংটো ছেলেটা / কবে যে হয়েছে মেহের আলি;/ কুকুরের ভাত কেড়ে খায়/ দেয় কুকুরকে হাততালি/ তুমি বদলাও না/ সেও বদলায় না/ শুধু পোশাকের রঙ বদলায়/ শুধু পোশাকের ঢং বদলায়”।
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হচ্ছেন সেই কবি, যিনি রাজনৈতিক কবিতা লিখলেও, তাঁর কবিতায় স্লোগান নেই, বরং রয়েছে কবিতার অতি সূক্ষ্মতম সিদ্ধির জায়গা। তিনি তাঁর অনুভূতিমালাকে শুধু মানুষের কষ্টের সাক্ষর দিয়েছেন। সেই কষ্টযাপনে কোনও নির্মাণ নেই, নেই সেই কষ্টযাপনে হীনমন্যতাও। রাগ আছে, কিন্তু সেই রাগ কখনওই মাত্রাছাড়া চিৎকার নয়। কারণ তিনি জানতেন যে, এই অসাম্যের জন্য কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একক দায়ী নয়। দায়ী হল ক্ষমতা, দায়ী হল ব্যবস্থা। তাই ব্যবস্থা পরিবর্তনের লড়াই না করে কেবল আঘাত করে ধ্বজা ওড়ালেই হয় না। তাঁর লিখিত একটি শব্দও যেমন অরাজনৈতিক নয়, তেমন তাঁর লিখিত একটি রাজনৈতিক কবিতাও তাঁর ব্যক্তিগত এই ভাবনা ও বোধ থেকে বেরিয়ে যেতে পারেনি। মার্কসীয় ভাবনাই তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে এক একটি সংকেতময় কবিতা। এই সংকেতগুলিই জন্ম দিয়েছে আমাদের মনে নানান সম্ভাবনার রাস্তার। আমরা বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছি একজন কমিউনিস্ট সন্ন্যাসীর মতো কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই সব রাস্তা একাকী তৈরি করছেন এবং তার পর একাকীই হেঁটে চলেছেন। তিনি যখন লেখেন- “ আসলে ক্রুশবিদ্ধ হওয়াটাই সব নয়; / তাতে একজন মানুষের শরীর রক্তাক্ত হয়/ কিন্তু যারা পেরেক দিয়ে ঐ শরীরকে রক্তাক্ত করে/ তাদের কিছু আসে যায় না।” ( নতুন প্রত্যয়), তখন আমরা বুঝি কী গভীর প্রত্যয়ের দিকে একাকী হেঁটে যাচ্ছে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজনীতি। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা আজও পৌঁছে যেতে পারি সেই সাম্যের, সহাবস্থানের ভারববর্ষে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
এখন চোখ রাঙানির সময়। যার হাতে ক্ষমতা, সে চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়ে বলে, আমার কথাই ঠিক। এই কথাই ফলো করতে হবে তোমাদের। আমি যদি তার ফলোয়ার না হই, তাহলে আমাকে সে ফলো করে যাবে। এই নজরদারির দুনিয়ায়, ক্ষমতা, শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সবসময় চুহাবিল্লি চলছে। চলবে। সময়ের এই কঠিন অবস্থার প্রকৃত রাজনীতিকে কবিতায় নিয়ে এসেও একজন কবি, তাঁর কবিতাগুলিকে শিল্পের উচ্চশীর্ষে রেখেছিলেন। তিনি কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যিনি বলেছেন, চোখ রাঙালে না হয় বলেই দিলাম পৃথিবী ঘুরছে না, “ পৃথিবী তবু ঘুরছে এবং ঘুরবেও, যতই তাকে চোখ রাঙাও না”। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেমন ষাটের কবি, যেমন সত্তরের কবি, আশির কবি, নব্বইয়ের কবি, তেমন এই একবিংশ শতকের এই মুহূর্তেরও কবি। ব্যক্তিগত মতাদর্শ থেকে একবিন্দু বিচ্যুত না হয়েই তিনি রচনা করে গেছেন শিল্পোত্তীর্ণ সব কবিতা। তাঁর কবিতা বাঙালির উচ্চারণ হয়ে উঠেছে এমনভাবেই, যে তাকে আলাদা করা যায় না। কীভাবে বা আমরা ভুলতে পারি বেকার জীবনের পাঁচালীর সেই বিখ্যাত লাইন- “ তাতে আমাদের কতটুকু ক্ষতি, কতটুকু ক্ষতি, মিতে/ হাঁ করা জুতোটা অবাধ্য বড়ো ভালো করে বাঁধো ফিতে”। অথবা যিনি বলেন তীক্ষ্ণস্বরে “ রাজা আসে যায়/ আসে আর যায়/ নীল জামা গায়ে/ লাল জামা গায়ে/ শুধু পোশাকের রঙ বদলায়/ শুধু মুখোশের ঢং বদলায়/ দিন বদলায় না”। শাসকের পোশাক, শাসকের নাম, শাসকের রং বদলে যাচ্ছে, কিন্তু শাসক শাসিতের যে সম্পর্ক তা কি বদলে যাচ্ছে? বরং তা অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠছে। আমরা এই দুহাজার তেইশের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছি পৃথিবীটা মানুষ এবং এই প্রকৃতির ভালো থাকার জন্য নয়। এ পৃথিবীটা এখন কিছু বহুজাতিক কোম্পানির, কিছু বড়লোক, কিছু পুঁজিবাদী কর্পোরেট এবং কিছু যুদ্ধবাজ ফ্যাসিস্টদের। তাঁরা ধর্মকে হাতিয়ার করে মানুষের মেধার ভিতর শাসন চালায়। মানুষকে নিম্নমেধা সম্পন্ন করে রেখে তাদের কলের পুতুলের মতো চালনা করাই তাদের লক্ষ্য। আর সে কারণেই, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই অসাম্যের বিরুদ্ধে আজীবন লিখে গেছেন তাঁর কবিতা।
‘কবিতা, তুমি কেমন আছ?/ যেমন থাকে ভালোবাসার মানুষ / অপমানে’- এই কবিতাটিকে আমরা চিরকালের এক ধ্রুবসত্যও হয়তো বলতে পারি। সারাজীবন ধরে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় উঠে এসে নিপীড়িত মানুষের কথা। লড়াইয়ের কথা। তিনি যেমন জানেন বাস্তবতার নির্মমতাকে, তেমনই জানেন এই নির্মমতার বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই কোন পথে হওয়া উচিত। তাই তাঁর কবিতায় অন্ধকারাচ্ছন্ন বাস্তব থাকলেও তা হতাশায় আচ্ছন্ন নয়। তিনি আগামীর দিকে তাকিয়ে কবিতা লিখেছেন। স্বপ্ন দেখেছেন বৈষম্যহীন এক সমাজের। আর তার জন্য কবিতাকেই করে তুলেছেন তাঁর কণ্ঠস্বর। সারাজীবন ধরে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যপুস্তিকা প্রকাশ করতেন। তাঁর ব্যাগে থাকত ছোট ছোট কবিতার বই। তিনি ঘুরে বেড়াতেন বিভিন্ন জায়গায়। দরিদ্র মানুষের, শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার কথা তিনি বলতেন। কিন্তু তাঁর কবিতা প্রোপাগান্ডিস্ট হয়ে ওঠেনি কখনো। সাম্যবাদের আদর্শ এমনভাবেই তাঁর শিরা উপশিরায় বয়ে যেত, যে তিনি সেই আদর্শকে নিজের অস্তিত্বের থেকে আলাদা করতে পারতেন না। অথচ এই সাম্যবাদী আদর্শকে পুঁজি করে নিজে কোনও প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলতে চাননি। তিনি লিখেছেন, ন্যাংটো ছেলে আকাশে হাত বাড়ায়/ যদিও তার খিদেয় পুড়ছে গা/ ফুটপাথে আজ লেগেছে জ্যোৎস্না। অন্ধকারের মধ্যে আলোর বিন্দুকে চিহ্নিত করার কাজটি আজীবন করে গেছেন এই কবি। যদি আমরা প্রতিকবিতা বা অ্যান্টিকবিতার কথাও ভাবি, তাহলেও, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়দের কথাই উঠে আসে। জীবনই তাঁকে দিয়ে প্রতিকবিতা লিখিয়ে নিত, কিন্তু তিনি কখনো দাবী করেননি, সেই সব কবিতাকে প্রতিকবিতা হিসেবে। কারণ কবিতাও ছিল তাঁর কাছে অস্ত্র। আর সেই অস্ত্রের নাম ছিল মানুষের সঙ্গে সংলাপ চালিয়ে যাওয়া। মানুষকে তার হতদরিদ্র কষ্টকর অপমানিত অবস্থার মধ্যেও ঘুরে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখানো। কবিতার কাজই নতুন জীবনের সঞ্চার করা। আর বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা মানেই আত্মদীপের কবিতা।
যে কবিতা তিনি বিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আট-এর দশক পর্যন্ত লিখে গেছেন, সেই কবিতা আজ অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। এই ভুবনায়ন-লাঞ্ছিত, ফ্যাসিবাদ-লাঞ্ছিত , যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং হিংস্র পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে নতুন করে উচ্চারণ করি তাঁর কবিতা। প্রতি মুহূর্তে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আমাদের কাছে বেঁচে থাকার অস্ত্র হয়ে ওঠে। তিনি বারবার জন্ম নেন আমাদের মধ্যে। বারবার আমাদের দিশা দেখান। এমন কবি যে কোনও ভাষাতেই দুর্লভ। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এমন একজন কবিকে আমরা এই বাংলা ভাষাতেই পেয়েছি। যিনি, মানুষের প্রতিদিনের কবি। যিনি নিজেই এক শতজল ঝরনার ধ্বনি।


বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার খুব প্রিয় কবিদের একজন। তাঁর ওপর এই আলোচনাটিও খুব যথার্থ লেগেছে আমার। আলোচককে আমার কৃতজ্ঞতা।